
দেশের টাকা বিভিন্ন উপায়ে বিদেশে পাচার হয়ে যাচ্ছে বলে জানিয়েছেন কৃষিমন্ত্রী মো. আব্দুর রাজ্জাক। তিনি বলেছেন, ‘বিদেশে অর্থ পাচার বন্ধ করতে হবে। বহু টাকা এ দেশ থেকে কানাডার বেগমপাড়া, দুবাইসহ বিভিন্ন দেশে চলে যাচ্ছে। আন্ডার ভয়েস, ওভার ভয়েসসহ নানাভাবে যে কেউ চাইলেই খুব সহজেই বিদেশে টাকা পাঠাতে পারে। এটিকে কঠোরভাবে দমন করতে হবে। এক্ষেত্রে রাজস্ব বিভাগের কর্মকর্তাদেরকে শক্তিশালী ভূমিকা রাখতে হবে।’
সোমবার বিকেলে রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে কাস্টমস বিষয়ক সেমিনারে মন্ত্রী এসব কথা বলেন। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড রাজস্ব সম্মেলন ২০২৩ উপলক্ষে 'বাংলাদেশ কাস্টমস: স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের সারথি' শীর্ষক এ সেমিনারের আয়োজন করে।
রাজস্ব আরও বাড়ানোর তাগিদ দিয়ে কৃষিমন্ত্রী বলেন, ‘আগের তুলনায় রাজস্ব অনেক বেড়েছে, কিন্তু রাজস্ব- জিডিপি অনুপাতে এখনো অনেক পিছিয়ে আছি। এটিকে আরও বাড়ানো উচিত। বিশেষ করে আয়করে আমরা এখনো সফল হতে পারিনি। সেজন্য, রাজস্ব বিভাগের সক্ষমতা ও দক্ষতা আরও বাড়াতে হবে।’
মন্ত্রী আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বিগত ১৪ বছরে অর্থনীতি, কৃষি, যোগাযোগ, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসহ সকল ক্ষেত্রে দেশের যে অভূতপূর্ব উন্নয়ন হয়েছে, সারা বিশ্ব তার স্বীকৃতি দিচ্ছে, প্রশংসা করছে। বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ, এডিবিসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও আন্তর্জাতিক মিডিয়া বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নের প্রশংসা করছে। সেখানে দেশের ভিতরে কেউ কেউ এ নিয়ে প্রশ্ন তোলে, যা কোনভাবেই কাম্য নয়। জাতি হিসেবে আমাদের আত্মসম্মানবোধ থাকা উচিত।
সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান আবু হেনা মো. রহমাতুল মুনিম। বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের জ্যেষ্ঠ সচিব আহমেদ মুনিরুছ সালেহীন। পৃথক দুটি প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন চট্টগ্রাম কাস্টমস ও বন্ড কমিশনারেটের কমিশনার মাহবুবুর রহমান ও চট্টগ্রাম কাস্টমসের কমিশনার ফাইজুর রহমান।

আগামী ২০২৬-২৭ অর্থবছরের রাজস্ব বাজেট প্রস্তুতে সহায়তার জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ড প্রধান বাজেট সমন্বয়কারী ও তিনজন বাজেট সমন্বয়কারীর নাম ঘোষণা করেছে। তারা নিজ নিজ দাপ্তরিক দায়িত্বের পাশাপাশি বাজেট প্রণয়নের অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করবেন।
গত সোমবার (২৩ ফেব্রুয়ারি) জারি করা এক অফিস আদেশে এ তথ্য জানানো হয়। মঙ্গলবার (২৪ ফেব্রুয়ারি) এনবিআরের জনসংযোগ কর্মকর্তা মো. আল আমিন শেখ বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
প্রধান বাজেট সমন্বয়কারীর দায়িত্ব পেয়েছেন প্রথম সচিব (কাস্টমস: অটোমেশন) এস. এম. শামসুজ্জামান। আর বাজেট সমন্বয়কারী হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে দ্বিতীয় সচিব (কাস্টমস: ক্লাসিফিকেশন অ্যান্ড অ্যাডভান্স রুলিং) তানভীর আহমেদ, দ্বিতীয় সচিব (মূসক বিচার ও আপিল) মো. মেহেবুব হক এবং দ্বিতীয় সচিব (কর অব্যাহতি) তৌহিদুর রহমানকে।
এদিকে আগামী অর্থবছরের জাতীয় বাজেটে আয়কর-সংক্রান্ত বিভিন্ন আইন ও বিধি সংশোধন, সংযোজন কিংবা পরিবর্তনের বিষয়ে প্রস্তাব আহ্বান করেছে এনবিআর। এ লক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন খাতের ব্যবসায়ী প্রতিনিধি ও সরকারি-বেসরকারি অংশীজনদের কাছে মতামত ও সুপারিশ চাওয়া হয়েছে।
বিভিন্ন চেম্বার ও অ্যাসোসিয়েশনের কাছেও এ বিষয়ে আনুষ্ঠানিক চিঠি পাঠানো হয়েছে বলে জানা গেছে।

জনস্বাস্থ্য সুরক্ষা ও খাদ্য নিরাপত্তার স্বার্থে বাংলাদেশসহ বিশ্বের ৪০টি দেশ থেকে মুরগি ও ডিম আমদানি পুরোপুরি বন্ধ করেছে সৌদি আরবের খাদ্য ও ওষুধ কর্তৃপক্ষ।
গত মঙ্গলবার (২৪ ফেব্রুয়ারি) আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম গালফ নিউজের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, বার্ড ফ্লুর উচ্চমাত্রার প্রাদুর্ভাব এবং বৈশ্বিক স্বাস্থ্যঝুঁকি বিবেচনায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সৌদি কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, মহামারীসংক্রান্ত হালনাগাদ তথ্যের ভিত্তিতে দেশগুলোর তালিকা নিয়মিত পর্যালোচনা করা হবে এবং জনস্বাস্থ্যের ঝুঁকি না কমা পর্যন্ত নিষেধাজ্ঞা বহাল থাকবে।
৪০ দেশের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত অনেক দেশের ক্ষেত্রে ২০০৪ সাল থেকেই এ নিষেধাজ্ঞা কার্যকর রয়েছে। সাম্প্রতিক পরিস্থিতি বিবেচনায় নতুন কিছু দেশও যুক্ত হয়েছে। বাংলাদেশ ছাড়াও তালিকায় রয়েছে ভারত, চীন, পাকিস্তান, যুক্তরাজ্য, জাপান, জার্মানি, দক্ষিণ কোরিয়া, মিশর ও মিয়ানমার।
এ ছাড়া যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, ফ্রান্স ও অস্ট্রেলিয়াসহ আরও ১৬টি দেশের নির্দিষ্ট কিছু অঙ্গরাজ্য বা শহর থেকে আংশিক আমদানিতে বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। সৌদি আরব বছরে প্রায় ১০ কোটি ডলারের ডিম আমদানি করে থাকে, যার বড় অংশ আসে ওমান, নেদারল্যান্ডস, জর্ডান ও তুরস্ক থেকে। মুরগির মাংসের অধিকাংশ চাহিদা পূরণ হয় ব্রাজিল থেকে আমদানির মাধ্যমে।
কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, কাঁচা মুরগি ও ডিমের ওপর নিষেধাজ্ঞা থাকলেও নির্ধারিত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা মান পূরণ সাপেক্ষে প্রক্রিয়াজাত মুরগির মাংস ও সংশ্লিষ্ট পণ্য আমদানিতে বাধা নেই। তবে এ ক্ষেত্রে রপ্তানিকারক দেশকে সরকারি সনদ দিতে হবে, যেখানে নিশ্চিত করা থাকবে যে পণ্যটি এমনভাবে প্রক্রিয়াজাত করা হয়েছে যাতে বার্ড ফ্লু ও নিউক্যাসল রোগের ভাইরাস সম্পূর্ণরূপে নির্মূল হয়েছে। পাশাপাশি উৎপাদনকারী স্থাপনাও সংশ্লিষ্ট দেশের সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে।
বর্তমানে সৌদি আরব তাদের মুরগির মাংসের চাহিদার প্রায় ৭০ শতাংশ নিজস্ব উৎপাদন থেকে পূরণ করছে, বাকি অংশ আমদানির মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়।
বৈশ্বিক স্বাস্থ্য সংস্থার প্রতিবেদনের আলোকে নেওয়া এ সিদ্ধান্ত রপ্তানিকারক দেশগুলোর পোল্ট্রি খাতে বড় ধরনের প্রভাব ফেলতে পারে। বিশেষ করে নতুনভাবে তালিকাভুক্ত দেশগুলোকে আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী ভাইরাসমুক্ত উৎপাদন নিশ্চিত করে রপ্তানি বাজার ধরে রাখার চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হবে।
সূত্র: গালফ নিউজ

চলতি ২০২৫-২৬ করবর্ষে ই-রিটার্ন জমার সময়সীমা বাড়ানোর দাবিতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে চিঠি দিয়েছেন বিভিন্ন কর আইনজীবী সমিতি ও ব্যবসায়ী প্রতিনিধিরা। প্রাপ্ত অনুরোধের প্রেক্ষাপটে সময় বৃদ্ধির বিষয়ে সংস্থাটির ইতিবাচক অবস্থান রয়েছে বলে জানা গেছে। অর্থমন্ত্রীর সম্মতি মিললে সময় বাড়ানোর সিদ্ধান্ত আসতে পারে বলে এনবিআর সূত্র জানিয়েছে।
সম্প্রতি বাংলাদেশ ট্যাক্স ল’ইয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন (বিটিএলএ) দুই মাস এবং চট্টগ্রাম কর আইনজীবী সমিতি এক মাস সময় বাড়ানোর আবেদন করে পৃথক চিঠি দিয়েছে। সংগঠন দুটি সময় বাড়ানোর পক্ষে ১৩টি কারণ তুলে ধরে বলেছে, সার্ভার ডাউন ও ধীরগতি, ওটিপি কোড পেতে ঝামেলা, বিভিন্ন ধরনের কাগজ ও চালানের নম্বর ইনপুটে সমস্যা, রিটার্ন দাখিলের সময় বিদ্যুৎ বিভ্রাট, নির্বাচন উপলক্ষে টানা পাঁচ দিন ছুটি, আয়কর আইনের ব্যাপক সংশোধন, দেরিতে আয়কর পরিপত্র পাওয়া, দেশব্যাপী নেটওয়ার্ক সমস্যা, ই-রিটার্ন বিষয়ে করদাতা-আইনজীবীদের দক্ষতার অভাব, দেশের অর্থনৈতিক সংকট, পবিত্র রমজানের ইবাদত-বন্দেগি, ইদুল ফিতর উদযাপন, ই-রিটার্ন সার্ভারে সমস্যার বিষয়গুলো রয়েছে। এসব বিষয় বিবেচনায় নিয়ে সময় বাড়ানোর আহ্বান জানিয়েছে তারা।
আইন অনুযায়ী ৩০ নভেম্বর রিটার্ন জমার শেষ দিন থাকলেও ই-রিটার্নে প্রত্যাশিত সাড়া না পাওয়ায় তিন দফায় সময় বাড়িয়ে তা ২৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়। প্রথমে সময় বাড়িয়ে ৩১ ডিসেম্বর, পরে ৩১ জানুয়ারি এবং সর্বশেষ ২৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত করা হয়। আগের বছরও তিন দফা বাড়িয়ে ব্যক্তি শ্রেণির করদাতাদের জন্য সময় ১৬ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়েছিল।
এনবিআর সূত্রে জানা গেছে, এখন পর্যন্ত অনলাইনে রিটার্ন জমা দিয়েছেন ৩৯ লাখের কিছু বেশি করদাতা। অফলাইনে জমা পড়েছে প্রায় তিন লাখ রিটার্ন। গত বছর মোট ৪৫ লাখ করদাতা রিটার্ন দাখিল করেছিলেন। চলতি করবর্ষে এ সংখ্যা ৫০ লাখ ছাড়াবে বলে আশা করা হয়েছিল।
এ বিষয়ে জানতে চাইলে এনবিআর চেয়ারম্যান আবদুর রহমান খান গণমাধ্যমকে বলেন, আজ বুধবার অর্থমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করে ই-রিটার্ন জমার সময়ের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।
অন্যদিকে রাজস্ব আদায় লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে পিছিয়ে রয়েছে সংস্থাটি। চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবছরের প্রথম সাত মাসে মোট রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্য ছিল দুই লাখ ৮৩ হাজার ৭৫১ কোটি টাকা। এর বিপরীতে আদায় হয়েছে দুই লাখ ২৩ হাজার ৬৩৮ কোটি টাকা। ফলে ঘাটতি দাঁড়িয়েছে ৬০ হাজার ১১৩ কোটি টাকা। যদিও আগের বছরের তুলনায় আদায়ে প্রায় ১৩ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হয়েছে, তবুও নির্ধারিত লক্ষ্যের তুলনায় তা যথেষ্ট নয়।
সংশোধিত বাজেটে চলতি অর্থবছরের জন্য এনবিআরকে পাঁচ লাখ ৫৪ হাজার কোটি টাকা সংগ্রহের লক্ষ্য দেওয়া হয়েছে। সে অনুযায়ী বাকি পাঁচ মাসে প্রায় তিন লাখ কোটি টাকা আদায় করতে হবে। লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রতি মাসে গড়ে প্রায় ৫৮ হাজার কোটি টাকা সংগ্রহ প্রয়োজন, যা অত্যন্ত কঠিন বলে সংশ্লিষ্টরা মনে করছেন। এখন পর্যন্ত সর্বোচ্চ আদায় হয়েছে গত জানুয়ারিতে, ৩৭ হাজার ৩৩ কোটি টাকা।
সংস্থার তথ্য অনুযায়ী সবচেয়ে বেশি ঘাটতি দেখা গেছে আয়কর খাতে। এক লাখ তিন হাজার ৯৮০ কোটি টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে আদায় হয়েছে ৭৫ হাজার ৫৫ কোটি টাকা। এতে এ খাতে ঘাটতি দাঁড়িয়েছে প্রায় ২৮ হাজার ৯২৫ কোটি টাকা।

রেমিট্যান্স প্রবাহ বাড়ায় বাজার থেকে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ডলার সংগ্রহ করছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। এর প্রভাবে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বেড়ে ৩৯ মাস পর আবার ৩৫ বিলিয়ন ডলারের ঘর পার হয়েছে।
মঙ্গলবার দিন শেষে দেশের গ্রস রিজার্ভ দাঁড়িয়েছে ৩৫ দশমিক শূন্য ৫ বিলিয়ন ডলার। সর্বশেষ ২০২২ সালের নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে রিজার্ভ ৩৫ বিলিয়ন ডলারের নিচে নেমে যায়। এরপর ধারাবাহিক পতনের মধ্যে আওয়ামী লীগ সরকার পতনের সময় তা কমে দাঁড়ায় ২৫ দশমিক ৯২ বিলিয়ন ডলারে।
রিজার্ভ শক্তিশালী করতে বাংলাদেশ ব্যাংক বাজার থেকে আরও আট কোটি ৭০ লাখ ডলার কিনেছে। চলতি অর্থবছরের শুরু থেকে এখন পর্যন্ত মোট ৫৪৭ কোটি ডলার কেনা হয়েছে। এর মধ্যে শুধু ফেব্রুয়ারিতেই কেনা হয়েছে ১৫৪ কোটি ডলার, যা রিজার্ভ বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখছে।
আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের বিপিএম৬ পদ্ধতি অনুযায়ী হিসাব করলে গত মঙ্গলবার রিজার্ভের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৩০ দশমিক ৩০ বিলিয়ন ডলার। এর আগে গত ১৯ জানুয়ারি প্রথমবারের মতো এই পদ্ধতিতে রিজার্ভ ৩০ বিলিয়ন ডলার ছাড়ায়। ২০২৩ সালের জুন থেকে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বিপিএম৬ অনুযায়ী রিজার্ভের তথ্য প্রকাশ করছে; তখন এ হিসাব অনুযায়ী রিজার্ভ ছিল ২৪ দশমিক ৭৫ বিলিয়ন ডলার।
দেশের ইতিহাসে ২০২১ সালের আগস্টে প্রথমবারের মতো রিজার্ভ ৪৮ বিলিয়ন ডলার অতিক্রম করেছিল। তবে অর্থ পাচারসহ নানা কারণে তা কমতে থাকে এবং আওয়ামী লীগ সরকার পতনের সময় বিপিএম৬ অনুযায়ী রিজার্ভ নেমে আসে ২০ দশমিক ৪৮ বিলিয়ন ডলারে। নতুন গভর্নর দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে কেন্দ্রীয় ব্যাংক আর কোনো ডলার বিক্রি করেনি।
বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, চলতি মাসের ২৩ তারিখ পর্যন্ত দেশে রেমিট্যান্স এসেছে ২৫৭ কোটি ডলার, যা আগের অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় প্রায় ২৪ শতাংশ বেশি। চলতি অর্থবছরের শুরু থেকে এ পর্যন্ত প্রবাসীদের পাঠানো মোট অর্থের পরিমাণ দুই হাজার ২০০ কোটি ডলার, যা আগের অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় প্রায় ২২ শতাংশ বেশি। গত অর্থবছর রেমিট্যান্স প্রবৃদ্ধি ছিল প্রায় ২৭ শতাংশ।

সপ্তাহের তৃতীয় কার্যদিবস আজ মঙ্গলবার দেশের পুঁজিবাজারে সূচকের ওঠানামার মধ্য দিয়ে লেনদেন শেষ হয়েছে। তবে লেনদেনের পরিমাণ উভয় বাজারেই বেড়েছে।
দেশের প্রধান বাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) এবং অপর বাজার চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ (সিএসই) সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।
ডিএসইতে প্রধান সূচক ডিএসইএক্স ১০ পয়েন্ট কমে ৫ হাজার ৫৪২ পয়েন্টে নেমেছে। শরিয়াহ সূচক ৫ পয়েন্ট কমে ১ হাজার ১০১ পয়েন্টে এবং ডিএসই-৩০ সূচক ৬ পয়েন্ট কমে ২ হাজার ১৪৩ পয়েন্টে অবস্থান করছে।
এদিন ডিএসইতে মোট ৮২৪ কোটি ৮৯ লাখ টাকার শেয়ার ও মিউচ্যুয়াল ফান্ডের লেনদেন হয়েছে, যা আগের কার্যদিবসের তুলনায় ১০৬ কোটি টাকার বেশি। আগের দিন লেনদেন ছিল ৭১৮ কোটি ৫৬ লাখ টাকা।
মঙ্গলবার ডিএসইতে ৩৯৭টি কোম্পানি ও মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ইউনিট লেনদেন হয়েছে। এর মধ্যে ১১৯টির দর বেড়েছে, ২২১টির কমেছে এবং ৫৭টির দর অপরিবর্তিত রয়েছে।
অন্যদিকে সিএসইর সার্বিক সূচক সিএএসপিআই ৫ পয়েন্ট বেড়ে ১৫ হাজার ৪৫৫ পয়েন্টে দাঁড়িয়েছে। এদিন ১৮৭টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৮৩টির দর বেড়েছে, ৬৪টির কমেছে এবং ৪০টির দর অপরিবর্তিত রয়েছে।
সিএসইতে মোট লেনদেন হয়েছে ১৯ কোটি ৪৯ লাখ টাকার শেয়ার ও ইউনিটের, যা আগের দিনের তুলনায় প্রায় এক কোটি টাকা বেশি। আগের দিন লেনদেন ছিল ১৮ কোটি ৪৩ লাখ টাকা।

ভোক্তা পর্যায়ে তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাসের (এলপিজি) দাম কমানো হয়েছে। ফেব্রুয়ারি মাসের জন্য ১২ কেজি সিলিন্ডারের মূল্য ১৫ টাকা কমিয়ে ১ হাজার ৩৪১ টাকা নির্ধারণ করেছে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন (বিইআরসি)।
মঙ্গলবার (২৪ ফেব্রুয়ারি) এ নতুন দর ঘোষণা করা হয়। সংস্থাটি জানায়, সোমবার (২৩ ফেব্রুয়ারি) সন্ধ্যা ৬টা থেকেই সংশোধিত মূল্য কার্যকর হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ফেব্রুয়ারির জন্য ১২ কেজি এলপিজির দাম ১ হাজার ৩৫৬ টাকা থেকে কমিয়ে ১ হাজার ৩৪১ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।
এর আগে চলতি মাসের ২ ফেব্রুয়ারি সর্বশেষ সমন্বয়ে ১২ কেজি সিলিন্ডারের দাম ৫০ টাকা বাড়িয়ে ১ হাজার ৩৫৬ টাকা করা হয়েছিল।
ভোক্তা পর্যায়ে দাম সহনীয় রাখতে এবং জ্বালানি বাজারের স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে স্থানীয় উৎপাদন ও ব্যবসায়ী পর্যায়ে বিদ্যমান ৭.৫ শতাংশ ভ্যাট এবং আমদানি পর্যায়ের ২ শতাংশ আগাম কর প্রত্যাহার করে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)। একই সঙ্গে আমদানি পর্যায়ে ৭ দশমিক ৫ শতাংশ ভ্যাট আরোপ করা হয়। এই পরিবর্তনের ধারাবাহিকতায় এবার এলপিজির দাম কমানো হয়েছে।
একই বিজ্ঞপ্তিতে অটোগ্যাসের দামও হ্রাস করা হয়েছে। ফেব্রুয়ারিতে ভোক্তা পর্যায়ে ২৮ পয়সা কমিয়ে অটোগ্যাসের মূসকসহ মূল্য প্রতি লিটার ৬১ টাকা ৮৬ পয়সা নির্ধারণ করা হয়েছে। এর আগে ২ ফেব্রুয়ারির সমন্বয়ে প্রতি লিটার দাম ২ টাকা ৩৪ পয়সা বাড়িয়ে ৬২ টাকা ১৪ পয়সা করা হয়েছিল।

বাণিজ্য, শিল্প, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী খন্দকার আব্দুল মুক্তাদিরের সঙ্গে বৈঠক করেছেন বাংলাদেশ রিকন্ডিশন্ড ভেহিকেলস ইমপোর্টার্স অ্যান্ড ডিলারস অ্যাসোসিয়েশন (বারভিডা)-এর প্রতিনিধিরা।
মঙ্গলবার বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত এ বৈঠকে সংগঠনের প্রেসিডেন্ট আবদুল হকের নেতৃত্বে প্রতিনিধিদল অংশ নেয়। সভায় বাণিজ্য সচিব মাহবুবুর রহমানও উপস্থিত ছিলেন।
আলোচনায় বারভিডা নেতারা রিকন্ডিশন্ড গাড়ি আমদানিবাণিজ্যের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। দেশের সড়ক পরিবহন খাতে উন্নত প্রযুক্তির পরিবেশবান্ধব ও জ্বালানিসাশ্রয়ী গাড়ি আমদানি ও বিপণনে প্রয়োজনীয় নীতিগত সহায়তা চাওয়া হয়।
মন্ত্রী উপস্থাপিত বিষয়গুলো ধাপে ধাপে পর্যালোচনা করে সমাধানের আশ্বাস দেন।
প্রতিনিধিদলে আরও ছিলেন সংগঠনের সেক্রেটারি জেনারেল রিয়াজ রহমান, সাবেক সেক্রেটারি জেনারেল মোহাম্মদ শহীদুল ইসলাম, ভাইস প্রেসিডেন্ট-১ সাইফুল ইসলাম (সম্রাট), জয়েন্ট সেক্রেটারি জেনারেল সৈয়দ জগলুল হোসেন এবং প্ল্যানিং অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট সেক্রেটারি এস এম মনসুরুল কবির (লিংকন)।

চলতি অর্থবছরের তৃতীয় প্রান্তিকে অর্থনীতিতে ধীরে ধীরে স্থিতিশীলতার ইঙ্গিত মিললেও পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়া এখনো ভঙ্গুর অবস্থায় রয়েছে। রপ্তানি ও রেমিট্যান্সে ইতিবাচক ধারা দেখা গেলেও উচ্চ আমদানি ব্যয় এবং স্থায়ী মূল্যস্ফীতি নীতিনির্ধারকদের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে থাকবে বলে প্রক্ষেপণ করেছে মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (এমসিসিআই)। গত সোমবার এমসিসিআইর ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়।
সংস্থাটি বলছে, বৈশ্বিক অনিশ্চয়তা ও অভ্যন্তরীণ চাপের প্রেক্ষাপটে টেকসই প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করতে সমন্বিত ও সতর্ক নীতিপদক্ষেপ অব্যাহত রাখা প্রয়োজন।
২০২৫-২৬ অর্থবছরের অক্টোবর-ডিসেম্বর সময়ের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি পর্যালোচনায় এ মূল্যায়ন তুলে ধরা হয়েছে।
চেম্বারের বিশ্লেষণে দেখা যায়, প্রধান সামষ্টিক অর্থনৈতিক সূচকে ধীরগতির হলেও ইতিবাচক অগ্রগতির লক্ষণ রয়েছে। তবে উচ্চ মূল্যস্ফীতি ও সম্প্রসারিত বাণিজ্য ঘাটতির চাপ অর্থনীতির ওপর বহাল থাকতে পারে।
গত নয় মাসের প্রবণতা পর্যালোচনা করে সংস্থাটি ধারণা করছে, তৃতীয় প্রান্তিকে রপ্তানি আয় ধারাবাহিকভাবে বাড়তে পারে। জানুয়ারিতে সম্ভাব্য রপ্তানি আয় ৪ দশমিক ৪১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে মার্চে ৪ দশমিক ৫২ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছাতে পারে। বৈদেশিক চাহিদা কিছুটা জোরদার হওয়া এবং চালান বৃদ্ধি এ প্রবৃদ্ধির পেছনে ভূমিকা রাখতে পারে।
অন্যদিকে আমদানিও বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। জানুয়ারিতে সম্ভাব্য আমদানি ব্যয় ৫ দশমিক ৯০ বিলিয়ন ডলার থেকে মার্চে ৬ দশমিক ০৪ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত হতে পারে। শিল্প কার্যক্রম ও অভ্যন্তরীণ চাহিদা বাড়লেও রপ্তানির তুলনায় আমদানি বেশি থাকায় বাণিজ্য ঘাটতির চাপ অব্যাহত থাকতে পারে।
রেমিট্যান্স প্রবাহ কিছুটা স্বস্তি দিতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। জানুয়ারিতে সামান্য কমার পর ফেব্রুয়ারি ও মার্চে প্রবাসী আয় বাড়তে পারে। মার্চে রেমিট্যান্স ৩ দশমিক ২৫ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছানোর পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। এতে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভে ইতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে।
প্রক্ষেপণ অনুযায়ী, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ জানুয়ারির ২৮ দশমিক ৬৮ বিলিয়ন ডলার থেকে মার্চে ২৮ দশমিক ৭৮ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছাতে পারে। বৃদ্ধি সীমিত হলেও এটি বহিঃখাতে ধীর অগ্রগতির ইঙ্গিত দেয়।
মূল্যস্ফীতির চাপ এখনো কাটেনি। ফেব্রুয়ারিতে এটি ৮ দশমিক ৬০ শতাংশ এবং মার্চে সামান্য কমে ৮ দশমিক ৫৫ শতাংশ হতে পারে বলে ধারণা করা হয়েছে। অর্থাৎ মূল্যস্ফীতি পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে না এলেও মার্চে কিছুটা স্বস্তির আভাস রয়েছে।

ঈদুল ফিতর সামনে রেখে তৈরি পোশাক শিল্পে তীব্র নগদ সংকট তৈরি হয়েছে। শ্রমিকদের বেতন-ভাতা ও উৎসব বোনাস সময়মতো পরিশোধ নিশ্চিত করতে সহজ শর্তে ঋণ সহায়তা চেয়েছে বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রফতানিকারক সমিতি (বিজিএমইএ)। এ বিষয়ে গভর্নরের কাছে চিঠি পাঠানো হয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক-এ, যেখানে দুই মাসের মজুরি সমপরিমাণ ঋণ এবং তা পরিশোধে ১২ মাস সময় চাওয়া হয়েছে।
মঙ্গলবার (২৪ ফেব্রুয়ারি) পাঠানো ওই চিঠিতে বিজিএমইএর ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ইনামুল হক খান বলেন, ভূ-রাজনৈতিক অস্থিরতা, বৈশ্বিক মন্দা ও চলমান শুল্কযুদ্ধের প্রভাবে রফতানি আয় ধারাবাহিকভাবে নিম্নমুখী। কার্যাদেশ কমে যাওয়া, ডেফার্ড শিপমেন্ট এবং অর্ডার পিছিয়ে যাওয়ায় কারখানাগুলো চাপে রয়েছে। গত এক বছরে প্রায় ৪০০টি কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে।
ফেব্রুয়ারি থেকে মার্চের ৬০ দিনের মধ্যে প্রায় ২৫ দিন কারখানা বন্ধ থাকবে। অথচ মার্চে নিয়মিত মজুরির পাশাপাশি ঈদ বোনাস এবং মার্চের অগ্রিম ৫০ শতাংশ বেতন পরিশোধ করতে হবে। ফলে এক মাসেই প্রায় দ্বিগুণ অর্থ ছাড়ের চাপ তৈরি হয়েছে। বিদ্যুৎ, গ্যাস, পরিবহন ও পোর্ট চার্জ বৃদ্ধির পাশাপাশি ব্যাংক সুদের হার বাড়ায় পরিস্থিতি আরও কঠিন হয়েছে। সরকারি সহায়তা ছাড়া সময়মতো মজুরি দেওয়া কঠিন হয়ে পড়বে বলে আশঙ্কা জানিয়েছে সংগঠনটি।
রফতানি পরিসংখ্যান তুলে ধরে বিজিএমইএ জানায়, চলতি অর্থবছরের জুলাই-জানুয়ারি সময়ে আগের অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় মোট পোশাক রফতানি আয় দুই দশমিক ৪৩ শতাংশ কমেছে। বিশেষ করে আগস্ট ২০২৫ থেকে আয় ধারাবাহিকভাবে কমছে।
রফতানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি)-র তথ্য অনুযায়ী, জুলাই মাসে প্রবৃদ্ধি থাকলেও পরবর্তী মাসগুলোতে নেতিবাচক ধারা স্পষ্ট হয়। ডিসেম্বর মাসে রফতানি কমেছে ১৪ দশমিক ২৩ শতাংশ। একই সময়ে পোশাকের গড় ইউনিট মূল্য এক দশমিক ৮৫ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে।
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড-এর তথ্য উল্লেখ করে বলা হয়েছে, আন্তর্জাতিক বাজারে মূল্যচাপের কারণে রফতানিকারকেরা প্রত্যাশিত দর পাচ্ছেন না।
চিঠিতে আরও বলা হয়, রফতানি আদেশের ক্ষেত্রে কারখানাগুলো সাধারণত ব্যাক-টু-ব্যাক এলসির মাধ্যমে ৭০ থেকে ৭৫ শতাংশ কাঁচামাল সংগ্রহ করে এবং প্রায় ২০ শতাংশ ব্যয় হয় মজুরি ও পরিচালনায়। কিন্তু ডেফার্ড শিপমেন্ট ও অর্ডার বিলম্বিত হওয়ায় মূলধন দীর্ঘ সময় আটকে থাকছে। একক ঋণগ্রহীতা সীমাও দ্রুত শেষ হয়ে যাচ্ছে। এতে বিশেষ করে ক্ষুদ্র ও মাঝারি কারখানাগুলো আর্থিক ঝুঁকিতে পড়ছে।
এই প্রেক্ষাপটে প্রচলিত ঋণসীমার বাইরে গিয়ে দুই মাসের মজুরির সমপরিমাণ অর্থ ঋণ দেওয়ার অনুরোধ জানানো হয়েছে। প্রস্তাবে তিন মাস গ্রেস পিরিয়ড রেখে ১২ মাসে পরিশোধের সুযোগের কথা বলা হয়েছে।
সংগঠনটির দাবি, দ্রুত সহায়তা না এলে শ্রম অস্থিরতার ঝুঁকি তৈরি হতে পারে, যা দেশের প্রধান রফতানি খাতের জন্য বড় ধরনের নেতিবাচক প্রভাব ডেকে আনতে পারে।

আন্তর্জাতিক বাজারে টানা তিন সপ্তাহ উত্থানের পর মুনাফা তুলে নেওয়ার প্রবণতায় মঙ্গলবার স্বর্ণের দামে পতন হয়েছে। আগের সেশনে ২ শতাংশের বেশি বাড়ার পর বিনিয়োগকারীদের লাভ সংগ্রহের চাপ তৈরি হয়। পাশাপাশি ডলারের শক্ত অবস্থানও দামে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। খবর রয়টার্স।
মঙ্গলবার (২৪ ফেব্রুয়ারি) বাংলাদেশ সময় সকাল ১১টা ৩৮ মিনিটে স্পট গোল্ডের দাম আউন্সপ্রতি ১.২ শতাংশ কমে ৫,১৬৭.২৮ ডলারে দাঁড়ায়। এতে টানা চার সেশনের ঊর্ধ্বগতি থেমে যায়। দিনের শুরুতে তিন সপ্তাহের বেশি সময়ের মধ্যে সর্বোচ্চ পর্যায়ে উঠেছিল স্বর্ণের দাম।
এপ্রিল ডেলিভারির জন্য যুক্তরাষ্ট্রের স্বর্ণ ফিউচার ০.৭ শতাংশ কমে ৫,১৮৭.৪০ ডলারে নেমে আসে।
বৈশ্বিক বাজার বিশ্লেষক প্রতিষ্ঠান টেস্টিলাইভের গ্লোবাল ম্যাক্রো প্রধান ইলিয়া স্পিভাক বলেন, আগের দিন স্বর্ণের দামে উল্লেখযোগ্য র্যালি হয়েছে। এখন বাজারে কিছুটা ‘ডাইজেশন’ বা সমন্বয় দেখা যাচ্ছে।
তিনি আরও বলেন, ওয়াল স্ট্রিটে যে আতঙ্ক দেখা গিয়েছিল, তা এশিয়ার বাজারে একইভাবে ছড়িয়ে পড়েনি—এটিও উল্লেখযোগ্য।
ওয়াল স্ট্রিটে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সংশ্লিষ্ট শেয়ারে নতুন করে বিক্রির চাপ তৈরি হওয়ায় বিনিয়োগকারীদের মধ্যে অস্থিরতা দেখা দেয়। এর প্রভাব এশিয়ার বাজারেও পড়ে। একই সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের শুল্কনীতি এবং ভূরাজনৈতিক উত্তেজনা বাজারের মনোভাবে প্রভাব ফেলেছে।
ডলারের মান কিছুটা বাড়ায় ডলারভিত্তিক স্বর্ণ অন্যান্য মুদ্রার বিনিয়োগকারীদের জন্য তুলনামূলক বেশি দামে পরিণত হয়, যা চাহিদা কমাতে ভূমিকা রাখে।
সোমবার প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প সতর্ক করে বলেন, সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পাদিত বাণিজ্য চুক্তি থেকে কোনো দেশ সরে গেলে ভিন্ন বাণিজ্য আইনের আওতায় তাদের ওপর আরও বেশি শুল্ক আরোপ করা হবে। এর আগে মার্কিন সুপ্রিমকোর্ট তার জরুরি শুল্ক আরোপের সিদ্ধান্ত বাতিল করে দেয়।
অন্যদিকে, ফেডারেল রিজার্ভের গভর্নর ক্রিস্টোফার ওয়ালার বলেছেন, ফেব্রুয়ারির কর্মসংস্থান প্রতিবেদন যদি শ্রমবাজারে স্থিতিশীলতার ইঙ্গিত দেয়, তাহলে মার্চের বৈঠকে সুদের হার অপরিবর্তিত রাখার বিষয়ে তিনি উন্মুক্ত রয়েছেন।
বাজার বিশ্লেষণ সংস্থা সিএমই গ্রুপের ফেডওয়াচ টুল অনুযায়ী, চলতি বছরে বিনিয়োগকারীরা ২৫ বেসিস পয়েন্ট করে তিন দফা সুদহার কমার সম্ভাবনা দেখছেন।
অন্যান্য মূল্যবান ধাতুর বাজারেও ভিন্নধর্মী চিত্র দেখা গেছে। স্পট রুপার দাম ০.৯ শতাংশ কমে আউন্সপ্রতি ৮৭.৩৯ ডলারে নেমেছে, যা আগের দিন দুই সপ্তাহের বেশি সময়ের মধ্যে সর্বোচ্চ অবস্থানে ছিল। স্পট প্লাটিনাম ০.৫ শতাংশ কমে ২,১৪২.৩৫ ডলারে দাঁড়িয়েছে। তবে প্যালাডিয়ামের দাম ০.৪ শতাংশ বেড়ে ১,৭৫০.৯৮ ডলারে উন্নীত হয়েছে।
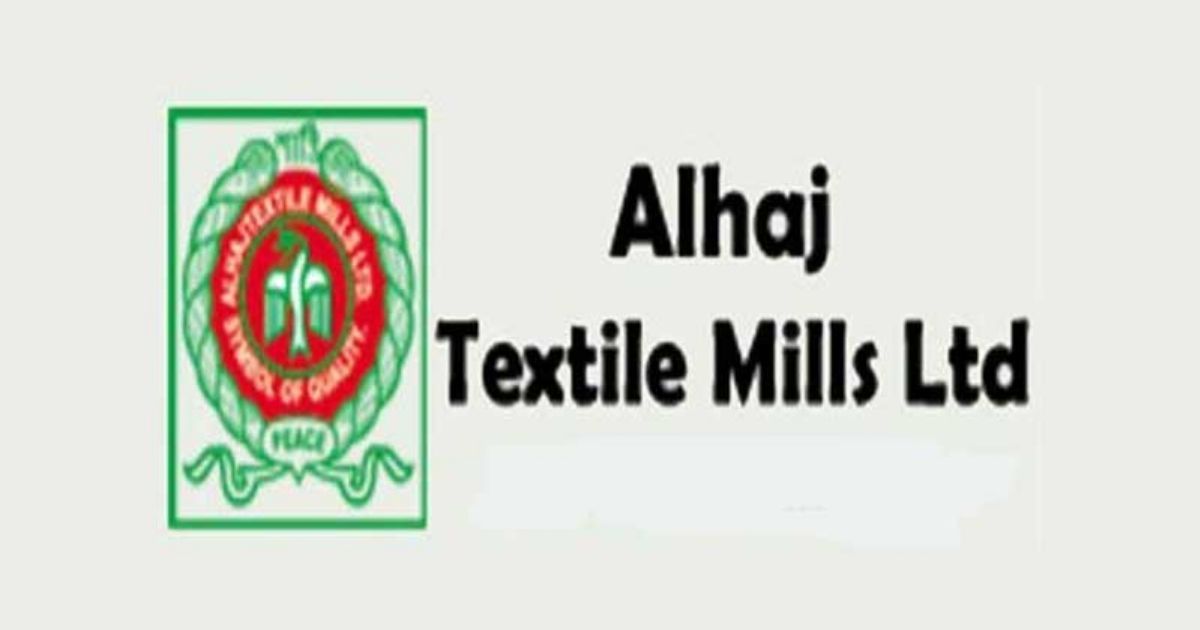
পুঁজিবাজারে বস্ত্র খাতে তালিকাভুক্ত কোম্পানি আলহাজ টেক্সটাইল মিলস লিমিটেডের ঘোষিত স্টক বা বোনাস লভ্যাংশ দেওয়ায় পুনরায় অসম্মতি জানিয়েছে নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি)। সমাপ্ত ২০২৩-২৪ হিসাব বছরের জন্য ঘোষিত ৩৫ শতাংশ স্টক লভ্যাংশ নিয়ে আপত্তি বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি)-এর।
আলোচ্য বছরের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদনে অসংগতি পাওয়ায় কমিশন এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে জানিয়েছে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই)।
কোম্পানির পর্ষদ ২০২৩-২৪ হিসাব বছরে মোট ৪০ শতাংশ লভ্যাংশ ঘোষণা করেছিল, যার মধ্যে ৫ শতাংশ নগদ এবং ৩৫ শতাংশ স্টক লভ্যাংশ ছিল। ওই বছরে শেয়ারপ্রতি আয় দাঁড়ায় ১০ টাকা ৭ পয়সা। আগের বছরে শেয়ারপ্রতি লোকসান ছিল ৭৮ পয়সা। ৩০ জুন ২০২৪ শেষে শেয়ারপ্রতি নিট সম্পদমূল্য দাঁড়িয়েছে ১৮ টাকা ৫২ পয়সা।
এর আগে ২০২২-২৩ হিসাব বছরে কোনো লভ্যাংশ দেয়নি কোম্পানিটি। সে সময়ে শেয়ারপ্রতি লোকসান ছিল ৭৮ পয়সা, যেখানে আগের বছরে ইপিএস ছিল ৯১ পয়সা। ৩০ জুন ২০২৩ শেষে এনএভিপিএস ছিল ৮ টাকা ৪৫ পয়সা।
২০২১-২২ হিসাব বছরে ৩ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ দেওয়া হয়। ওই সময়ে ইপিএস ছিল ৯১ পয়সা, যা আগের বছরের ২৬ পয়সার তুলনায় বেশি। ৩০ জুন ২০২২ শেষে এনএভিপিএস দাঁড়ায় ৯ টাকা ৫২ পয়সা।
আরও আগে, ২০২০-২১ হিসাব বছরে ১ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ ঘোষণা করা হয়েছিল। সে বছরে ইপিএস ছিল ২৬ পয়সা, আগের বছরে যেখানে শেয়ারপ্রতি লোকসান ছিল ৯৩ পয়সা। ৩০ জুন ২০২১ শেষে এনএভিপিএস ছিল ৮ টাকা ৬১ পয়সা।
১৯৮৩ সালে পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানিটির অনুমোদিত মূলধন ৫০ কোটি টাকা এবং পরিশোধিত মূলধন ২২ কোটি ২৯ লাখ ৯০ হাজার টাকা। রিজার্ভে রয়েছে ১৮ কোটি ৯৯ লাখ টাকা। মোট শেয়ার সংখ্যা ২ কোটি ২২ লাখ ৯৮ হাজার ৫৪৯টি। এর মধ্যে ৩০ দশমিক ৬৫ শতাংশ উদ্যোক্তা পরিচালকদের হাতে, ১৪ দশমিক শূন্য ৭ শতাংশ প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের কাছে এবং বাকি ৫৫ দশমিক ২৭ শতাংশ সাধারণ বিনিয়োগকারীদের দখলে।
ডিএসইতে গত সোমবার কোম্পানিটির শেয়ারের সমাপনী মূল্য ছিল ১৩২ টাকা ৮০ পয়সা। গত এক বছরে শেয়ারটির দর ১১৫ টাকা ১০ পয়সা থেকে ১৮৭ টাকা ৫০ পয়সার মধ্যে ওঠানামা করেছে।
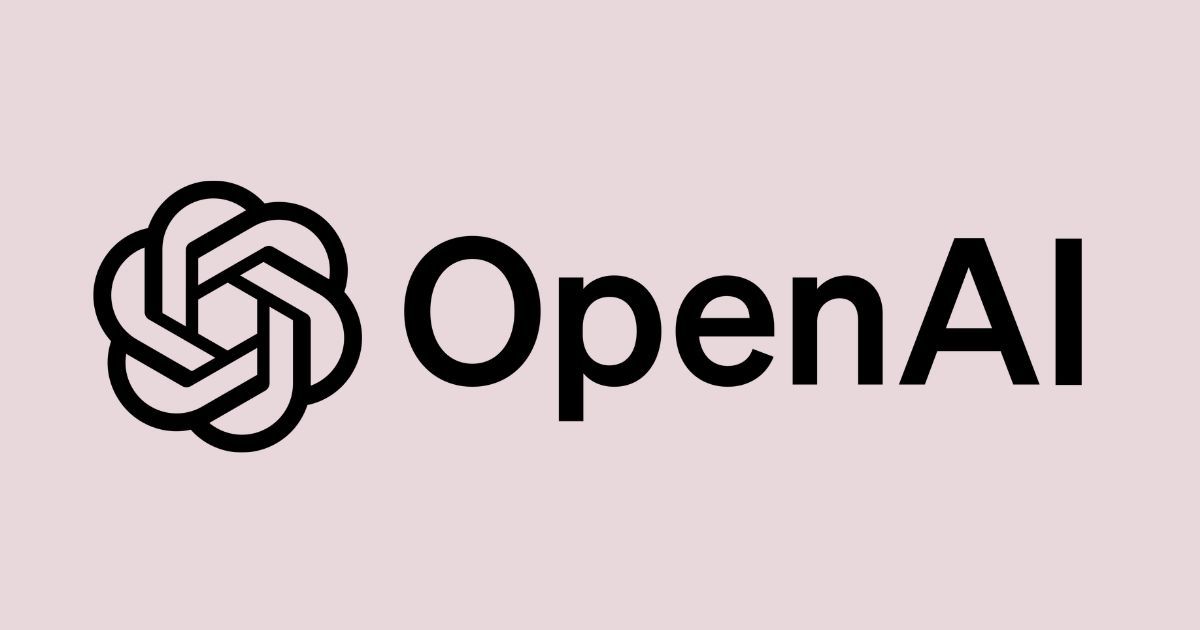
কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা খাতের বিস্তারকে সামনে রেখে চ্যাটজিপিটি নির্মাতা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) দীর্ঘমেয়াদি ও নির্দিষ্ট বিনিয়োগ রূপরেখা প্রকাশ করেছে।
প্রতিষ্ঠানটি জানিয়েছে, ২০৩০ সালের মধ্যে কম্পিউটিং সক্ষমতা বাড়াতে প্রায় ৬০০ বিলিয়ন বা ৬০ হাজার কোটি ডলার ব্যয় করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। বিনিয়োগকারীদের উদ্দেশে পাঠানো সাম্প্রতিক এক বার্তায় এই পরিকল্পনার কথা তুলে ধরা হয়। খবর সিএনবিসি।
প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, কয়েক মাস আগে প্রতিষ্ঠানটির প্রধান নির্বাহী স্যাম অল্টম্যান এআই অবকাঠামো গড়ে তুলতে প্রায় ১ দশমিক ৪ ট্রিলিয়ন ডলার বিনিয়োগের সম্ভাবনার কথা বলেছিলেন। তবে এবার তুলনামূলক কম অঙ্ক এবং নির্দিষ্ট সময়সীমা উল্লেখ করে নতুন লক্ষ্য প্রকাশ করা হয়েছে। মূলত বিপুল ব্যয়ের বিপরীতে প্রত্যাশিত আয় নিয়ে বিনিয়োগকারীদের উদ্বেগের প্রেক্ষাপটেই ব্যয়ের পরিকল্পনা পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে।
বিশ্লেষকদের মতে, প্রযুক্তিগত প্রতিযোগিতায় এগিয়ে থাকতে উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন প্রসেসর, সার্ভার এবং বৃহৎ ডেটা সেন্টার স্থাপনেই এ অর্থের বড় অংশ ব্যয় হবে। একই সঙ্গে বাজার পরিস্থিতি ও সম্ভাব্য আয়ের দিক বিবেচনায় রেখেই বিনিয়োগের পরিমাণ কিছুটা সংযত করা হয়েছে।
প্রতিষ্ঠানটির অভ্যন্তরীণ পূর্বাভাস বলছে, ২০৩০ সালে মোট আয় ২৮০ বিলিয়ন বা ২৮ হাজার কোটি ডলার ছাড়াতে পারে। নাম প্রকাশ না করার শর্তে সংশ্লিষ্ট সূত্র সিএনবিসিকে জানিয়েছে, ভোক্তা সেবা এবং করপোরেট বা এন্টারপ্রাইজ খাত থেকে প্রায় সমান হারে আয় আসার প্রত্যাশা করা হচ্ছে। বিনিয়োগকারীদের সামনে যে ব্যয় পরিকল্পনা উপস্থাপন করা হয়েছে, তা সম্ভাব্য আয়ের প্রবৃদ্ধির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সাজানো হয়েছে বলে সূত্রগুলো জানিয়েছে।

২০২৫ সালে দেশের শেয়ারবাজারে বিদেশি বিনিয়োগে স্পষ্ট দুর্বলতা লক্ষ্য করা গেছে। অর্থনৈতিক চাপ, বাজারের অস্থিরতা এবং নির্বাচন-পূর্ব অনিশ্চয়তার প্রভাবে সারা বছরজুড়ে বিদেশি বিনিয়োগকারীরা মোট ২৭০ কোটি টাকা তুলে নিয়েছেন। এ তথ্য জানিয়েছে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই)।
ডিএসইর পরিসংখ্যান বলছে, ২০২৫ সালে বিদেশিরা ২ হাজার ৯৫ কোটি টাকার শেয়ার বিক্রি করেছেন। বিপরীতে তারা কিনেছেন ১ হাজার ৮২৫ কোটি টাকার শেয়ার। ফলে বছর শেষে নিট বিনিয়োগ ২৭০ কোটি টাকা কমে যায়।
বাজার বিশ্লেষকদের মতে, ফেব্রুয়ারি ২০২৬-এর নির্বাচনকে ঘিরে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা বিনিয়োগকারীদের সতর্ক অবস্থানে রেখেছিল। সে কারণে পুরো বছর ধরেই বিদেশিরা ধীরে ধীরে বিনিয়োগ কমিয়েছেন।
তবে নির্বাচন-পরবর্তী সময়ে কিছুটা ইতিবাচক ইঙ্গিত মিলছে। ফেব্রুয়ারির প্রথম পনেরো দিন, অর্থাৎ ১ থেকে ১৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সময়ে বিদেশিদের মোট লেনদেন আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় ৪৮ শতাংশ বেড়ে ১৭৩ কোটি টাকায় পৌঁছেছে। এক বছর আগে এ অঙ্ক ছিল ১১৬ কোটি ৬৩ লাখ টাকা।
ডিএসইর তথ্য অনুযায়ী, ২০২৪ সালেও বিদেশিদের নিট বিনিয়োগ ২৬১ কোটি টাকা কমেছিল। গত আট বছরের মধ্যে সাত বছরেই বিদেশিদের অবস্থান ছিল ঋণাত্মক। কেবল ২০২৩ সালে তাদের নিট বিনিয়োগ ইতিবাচক ছিল, যার পরিমাণ ৬৪ কোটি টাকা।
২০২৫ সালের ১২ মাসের মধ্যে পাঁচ মাসে বিদেশিদের অবস্থান ছিল ইতিবাচক। বিশেষ করে মে থেকে আগস্ট সময়ে তারা সক্রিয়ভাবে শেয়ার কেনেন, যার প্রভাবে ডিএসইএক্স সূচক ঊর্ধ্বমুখী হয়। তবে সেপ্টেম্বর থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত টানা শেয়ার বিক্রি করে তারা বিনিয়োগ কমিয়ে নেন।
অন্যদিকে, ২০২৫ সালে বিদেশিদের মোট লেনদেন, অর্থাৎ কেনা-বেচা মিলিয়ে, আগের বছরের তুলনায় ৮ শতাংশ বেড়ে ৩ হাজার ৯২০ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে।