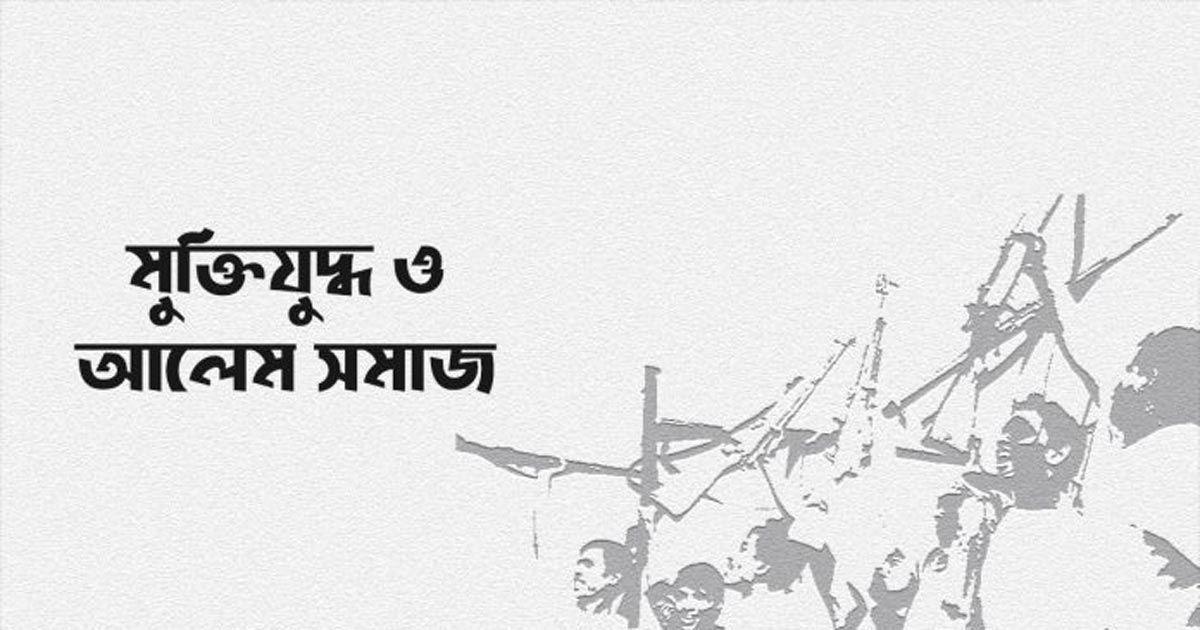
প্রথম কিস্তির পর শেষ কিস্তি
১৯৪৭ সালে শেষ পর্যন্ত ‘পাকিস্তান’ নামক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে সমকালে সংঘটিত মুসলিম লীগবিরোধী সব আন্দোলনে আলেম সমাজ সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। ১৯৫২ সালের ৩১ জানুয়ারি যখন সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি (ঢাকা বার লাইব্রেরিতে) গঠিত হয় তাতে সভাপতিত্ব করেছিলেন মওলানা ভাসানী। তমুদ্দুন মজলিশ, ইসলামী ভ্রাতৃসংঘ, খেলাফতে রব্বানী পার্টি, পূর্ব পাকিস্তান মোহাজর সমিতি প্রভৃতি সংগঠনও এতে যোগদান করে। এসব সংগঠন ছিল মূলত আলেম সমাজের প্রভাবাধীন। একুশে ফেব্রুয়ারি দিন শহীদের অনেক লাশ সরকার গায়েব করে দিয়েছিল। আলেমরা লাশ ছাড়াই ২২ ফেব্রুয়ারি গায়েবানা জানাজা পড়ার আয়োজন করেন। লাখ লাখ লোকের সমাবেশ হয়েছিল এসব গায়েবানা জানাজায়। মেডিকেল কলেজের ছাত্রাবাসের ভেতরও আলাদাভাবে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হলে মুসলিম লীগ সরকারের হুমকি উপেক্ষা করে আলেম সমাজ তাতে নেতৃত্ব দিয়ে গায়েবানা জানাজায় ইমামতি করে।
১৯৫২ সালের এই ভাষা আন্দোলনে ঢাকার মাদ্রাসার ছাত্ররা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। মাদ্রাসা শিক্ষিতদের মধ্যে মাওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ, মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, মাওলানা আকরাম খাঁ প্রথম থেকেই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন এবং নেতৃপর্যায়ে থেকে আন্দোলনকে বেগবান করেন। ২১ ফেব্রুয়ারি মাদ্রাসা খোলা ছিল এবং সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের প্রোগ্রামও তাদের জানা ছিল। মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মাওলানা জিয়াউল হক এবং শিক্ষক মাওলানা মোস্তাফিজুর রহমান মাদ্রাসার ছাত্রদের উৎসাহিত করে মিছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবনে পাঠান। মাওলানা আতিকুল মাওলা (প্রকাশনা সংস্থা মাওলা ব্রাদার্সের মালিক) মাদ্রাসার ছাত্রদের মিছিলে নেতৃত্ব দেন এবং ১৪৪ ধারা ভঙ্গে আন্দোলনে যুক্ত হন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন ঢাকা হলের পাশে মুসা খাঁ মসজিদের ইমান মাওলানা লোকমান আহমদ আমীমীও এই মিছিলে অংশগ্রহণ করেন। (বিস্তারিত দেখতে পারেন, এই লেখকের বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের, প্রথম অখণ্ড)।
১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের পর তৎকালীন পূর্ব বাংলার সবচেয়ে বড় ঘটনা ছিল ১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচন। মুসলিম লীগবিরোধী একটি জোট গঠিত হয়, যার নাম দেয়া হয় ‘যুক্তফ্রন্ট’। যুক্তফ্রন্টের প্রধান ব্যক্তিত্ব ছিলেন শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক। শেরেবাংলার দল কৃষক প্রজা পার্টি দল হিসেবে খুব সংগঠিত ছিল না, কিন্তু তার ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তা বাংলার মানুষের কাছে ছিল আকাশচুম্বী। (এ বিষয়ে দেখুন, বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত আত্মজীবনী, পৃষ্ঠা ২২)। সে জন্য যুক্তফ্রন্ট করার জন্য শেরেবাংলার প্রয়োজন ছিল সবচেয়ে বেশি। শেরেবাংলা মুসলিম লীগের রাজনীতি ও কৌশল বুঝতেন। নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টকে ‘কমিউনিস্ট’ এবং ‘ভারতের চর’ বলে কোণঠাসা করে ফেলতে পারে ভেবে শেরেবাংলা যুক্তফ্রন্টে আলেমদের সংগঠন নেজামে ইসলামকে নেন। যদিও যুক্তফ্রন্টের অনেকেই এ কৌশল বুঝতে পারেননি, ফলে তারা প্রথমে বিরোধিতা করলেও পরে নেজাম ইসলামকে মেনে নেন। কারণ আলেম সমাজ জোটে থাকলে মুসলিম লীগ, যুক্তফ্রন্টকে ‘কমিউনিস্ট’ এবং ‘ভারতের চর’ বলে জনগণকে বিভ্রান্ত করতে পারবে না। নির্বাচনে মাওলানা আশরাফ উদ্দিন চৌধুরী, মাওলানা আতাহর আলী প্রমুখ বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। আর বাস্তবে তা-ই ঘটেছিল, আলেমরা যুক্তফ্রন্টে থাকার কারণে সদ্য প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তানে মুসলিম লীগের ভরাডুবি ঘটে।
১৯৬৬ সালে বঙ্গবন্ধু যখন তার রাজনৈতিক কর্মসূচি হিসেবে ছয় দফা পেশ করেন, তখন সারা পাকিস্তানের রাজনীতি এর পক্ষে-বিপক্ষে দুই ভাগ হয়ে যায়। প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান থেকে শুরু করে বিরোধী দলের অন্যতম নেতা মওলানা ভাসানী পর্যন্ত ছয় দফার বিপক্ষে অবস্থান নেন। কিন্তু কওমি মাদ্রাসার আলেমদের সংগঠন এ সময়ে বঙ্গবন্ধুর পাশে দাঁড়ান। শেখ মুজিবুর রহমান মুক্তি এবং আওয়ামী লীগের কর্মসূচি ছয় দফা পেশ করার অধিকারের দাবি করে আলেমরা সংবাদপত্রে বিবৃতি দেন। (দেখুন, দৈনিক ইত্তেফাক ১৩ মে, ১৯৬৬)। এ ছাড়া দেশের বিভিন্ন স্থানে আঞ্চলিক ধর্মীয় নেতা এবং আলেমরা ছয় দফার পক্ষে সরাসরি বিবৃতি দান করেন। ময়মনসিংহের মুক্তাগাছার ধর্মীয় নেতা মাওলানা সৈয়দ মনজুর হোসেন খোরাসানি এক বিবৃতিতে বলেন, ‘ছয়-দফা দাবি পাকিস্তানের অখণ্ডতা ও সংহতি নষ্ট তো করিবেই না, বরং ৬-দফা দাবি পূরণের মাধ্যমে পাকিস্তান আরো শক্তিশালী ও দৃঢ় ভিত্তির উপর গড়িয়ে উঠিবে।’ (দৈনিক ইত্তেফাক, ১৮ মার্চ, ১৯৬৬)।
ছয় দফা প্রশ্নে সারা পাকিস্তানের সরকারি দল, প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান, গভর্নর মোনায়েম খান, মুসলিম লীগ, জামায়াতে ইসলামী, ভাসানী ন্যাপ যখন একাট্টা, তখন দেশের আলেম সমাজ বঙ্গবন্ধুর পাশে থেকে শক্তি জোগায়। আলেমদের সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত গভীর। সিলেটের মাওলানা অলিউর রহমান লিখেছিলেন, ‘শরিয়তের দৃষ্টিতে ছয়দফা’ শীর্ষক পুস্তিকা। এ জন্য ১৯৭১ সালে আলবদররা তাকে হত্যা করে। শহীদ বুদ্ধিজীবীদের তালিকায় তার নাম রয়েছে।
ষাটের দশকে জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার পর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের চিন্তাচেতনা ও কথাবার্তার মধ্যে পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। তার সঙ্গে আলেমদের সম্পর্কের কারণে তিনি সমাজতন্ত্র ও ইসলামের মধ্যে একটা সম্পর্ক তৈরি করতে চান। ১০ সেপ্টেম্বর (১৯৬৯) চট্টগ্রাম মুসলিম ইনস্টিটিউট হলে বঙ্গবন্ধু বলেন, ‘তার দল ছয় দফা কর্মসূচির ভিত্তির দেশে সমাজতন্ত্র কায়েমের পক্ষপাতী। তিনি বলেন, ইসলাম সমাজতন্ত্রের পরিপন্থী নয়। কারণ ইসলাম চায় সামাজিক ন্যায়বিচার। তিনি আরও বলেন, দুরভিসন্ধি চরিতার্থ করার জন্য কারও ইসলামের নাম ব্যবহার করা উচিত নয়।’ (দৈনিক পাকিস্তান, ১১ সেপ্টেম্বর ১৯৬৯)। এ সময় বঙ্গবন্ধু জামায়াতে ইসলামীর স্বরূপও উন্মোচন করেন। ৭ জুন (১৯৭০) রোববার ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে এক বিশাল জনসভায় বঙ্গবন্ধু বলেন, ‘জামায়াতে ইসলামী, ইসলামের ঠিকাদার হতে চায়। তিনি বলেন, এ দলটি তিন বছরে ১১টি পত্রিকার মালিক হয়েছে এবং প্রচুর বইপত্র ছাপিয়েছে, এরা এত টাকা কোথায় পায়?’ (দৈনিক পাকিস্তান, ৮ জুন, ১৯৭০)।
বঙ্গবন্ধুর মতো পাকিস্তানের আলেমরাও নিরন্তর এই জামায়াতে ইসলামীর বিরুদ্ধে দেশবাসীকে সতর্ক করে গেছেন। ১৯৬৯ সালের ৫ সেপ্টেম্বর ঢাকায় জমিয়তে ওলামায়ে ইসলামের নেতা মওলানা গোলাম গাউস হাজারভী এক বিবৃতিতে বলেন, জামায়াতে ইসলামী হচ্ছে ইংরেজ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের সাহায্যপুষ্ট একটি প্রতিষ্ঠান। ২ নভেম্বর (১৯৬৯) পীর মোহসেনউদ্দিন দুদু মিঞা ও মাওলানা মহিউদ্দিন এক বিবৃতিতে বলেন, “মওদুদী ও তার বেতনভোগী কর্মীরা ইসলামের নামে পাকিস্তানে পুঁজিবাদী ও সাম্রাজ্যবাদকে মজবুত করার দায়িত্ব পালন করছে। মওদুদী সাহেব ইহুদিদের ন্যায় অশ্লীল ভাষায় সাহেবায়ে কেরামের সমালোচনা করে রাফেজি মতবাদের সমর্থক বলে নিজেকে প্রমাণ করেছেন। এজন্যে উপমহাদেশের সকল আলেম-সমাজ মওদুদীকে ‘গোমরাহ’ তথা সুন্নত আল জামাতের বহির্ভূত বলে বক্তব্য দিয়েছেন।” (দৈনিক পাকিস্তান, ৬ সেপ্টেম্বর ১৯৬৯ এবং ৩ নভেম্বর ১৯৬৯)। ১৯ অক্টোবর (১৯৬৯) পীর মোহসেনউদ্দিন দুদু মিয়া ঢাকায় এক বিবৃতিতে বলেন, “তিনি বেশ কিছুদিন ধরে মওদুদীর কার্যকলাপে আশাঙ্কিত হয়ে পড়েছেন, কারণ মওদুদী এখন সকল জায়গাতেই কমিউনিজমের গন্ধ পাচ্ছেন। এমনকি মসজিদ-মাদ্রাসাতেও মওদুদী কমিউনিস্ট খুঁজে বেড়াচ্ছেন। পীর সাহেব আরও বলেন, মওদুদী সাহেব নিজে কোনো সনদপত্র প্রাপ্ত মওলানা নন। হায়দারাবদের নিজামের দরবারে তদানীন্তন সাম্রাজ্যবাদী প্রভুদের তুষ্ট করার জন্যে তিনি কাজ করতেন। সেই প্রভুদের থেকেই তিনি ‘মওলানা’ খেতাব পান।” (দৈনিক পাকিস্তান, ২০ অক্টোবর ১৯৬৯)। অ্যাবোটাবাদ থেকে ৩০ অক্টোবর পাকিস্তানের ১৩ জন আলেম এক যৌথ ফতোয়ায় বলেন, মওলানা মওদুদী বিপথগামী এবং তার অনুসারীদের পেছনে নামাজ পড়া না-জায়েজ। ১২ ফেব্রুয়ারি (১৯৭০) ঢাকায় নিখিল পাকিস্তান ইসলামী বিপ্লবী পরিষদের চেয়ারম্যান মওলানা মোহাম্মদ ওবায়দুল্লাহ বিন সাইদ এক বিবৃতিতে মওদুদী ও জামায়াতে ইসলামী সমর্থক ইমামদের পেছনে নামাজ না পড়ার আবেদন জানান। (দৈনিক পাকিস্তান ৩০ অক্টোবর ১৯৬৯ এবং ১৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৭০)। আলেম সমাজের এ ভূমিকার কারণে জামায়াতে ইসলামীর বিরুদ্ধে বঙ্গবন্ধুর সংগ্রামটা একটা তাত্ত্বিক ভিত্তি পায়।
১৯৭০ সালের ১৭ মার্চ ছিল বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন। বায়তুল মোকাররম মসজিদে আসর নামাজের পর মওলানা শেখ মোহাম্মদ ওবায়দুল্লাহ বিন সায়িদ জালালাবাদী বঙ্গবন্ধুর জন্মদিনে তার দীর্ঘায়ু কামনা করে মোনাজাত পরিচালনা করেন। (দৈনিক ইত্তেফাক ১৮ মার্চ ১৯৭১)।
পাকিস্তানি সৈন্যরা দিকে দিকে যেভাবে বাংলাদেশের মানুষকে হত্যা করতে শুরু করে, তার বিরুদ্ধে ১৯ মার্চ শুক্রবার বাদ জুমা মসজিদে মসজিদে শহিদানের আত্মার মাগফিরাত কামনায় এবং আহতদের আরোগ্য কামনায় বিশেষ মোনাজাত করা হয়। বাংলার আলেম সমাজ মসজিদে মসজিদে মোনাজাত পরিচালনা করে জনগণকে পাকিস্তানি বর্বরদের বিরুদ্ধে উজ্জীবিত করে তোলে। (আজাদ, ২০ মার্চ ১৯৭১)।
১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ ঢাকায় পাকিস্তান সৈন্যদের বর্বরোচিত হামলার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত আলেম সমাজ বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখে। ২০ মার্চ পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আগত রাজনীতিক মিয়া মোমতাজ দৌলতানা ও মওলানা মুফতি মাহমুদ বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে তার সঙ্গে একান্ত বৈঠকে মিলিত হন। পরে কালো পতাকা, জয় বাংলা ও বাংলার মানচিত্র খচিত সবুজ লাল পতাকা শোভিত বঙ্গবন্ধুর গাড়িতে করে তারা হোটেলে ফিরে যান। (সংবাদ, ২১ মার্চ ১৯৭১)। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে থেকেই পশ্চিম পাকিস্তান ও পূর্ব পাকিস্তানের আলেম সমাজ জেনারেল ইয়াহিয়া, জুলফিকার আলী ভুট্টো ও জামায়াতে ইসলামীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে গেছেন। কিন্তু ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাত থেকে যখন বাঙালির মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলো, তখন সবচেয়ে বেশি দ্বিধা ও সংকটের সম্মুখীন হয় বাংলাদেশের আলেম সমাজ। কারণ পাকিস্তানিরা প্রচার ও প্রপাগান্ডায় ইসলাম ও পাকিস্তানকে সব সময় এক পাল্লায় বেঁধে রাখত। সাধারণ মানুষের মধ্যেও এই একটা চিন্তা সব সময় জেগে উঠত যে ‘পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বললে না জানি ইসলামের বিরুদ্ধেই বলা হয়ে যায়, আসলে পাকিস্তান ও ইসলাম কখনোই এক ছিল না। ১৯৪৭ থেকে এই ২০২৩ সাল পর্যন্ত প্রায় ৭০ বছর বয়সের পাকিস্তানে একজন প্রেসিডেন্ট অথবা প্রধানমন্ত্রীও ইসলামের সুন্নতের ওপর ছিলেন না, এখনো নেই। ১৯৪৭ সালে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ দিয়ে শুরু, ২০২৩ সালে ইমরান খান-শাহবাজ শরিফ পর্যন্ত সবার পোশাকেই পাশ্চাত্যের স্যুট-কোট-বুট ছিল, ইসলামি জোশ হাঁকালেও কেউই দাড়ি-টুপির মধ্যে ছিলেন না। কিন্তু জনগণকে ধাপ্পা দিতে সব সময়ই তারা ইসলামের নাম নিতেন। পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামী এসব নেতার জন্য ইসলামি রসদ জোগাত। জনগণ তাই ছিল বিভ্রান্ত। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের জনগণকে সব সময় এই বলে সতর্ক করতেন যে এদের ইসলামি বুলি শুধু পূর্ব বাংলাকে দাবায়ে রাখতে।
২৫ মার্চে ভয়াবহ ঘটনার পর বাংলার আলেম সমাজের কাছে এ পরিস্থিতিতে নতুন কর্তব্য হাজির হয়। তাঁরা পাকিস্তানি জালেম শাহীর বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করেন। আমরা এ রকম বহু ঘটনা পাব যেখানে আলেমরা পাকিস্তানি মিলিটারি ও তাদের সহযোগীদের হাতে শহীদ হয়েছেন। মোহাম্মদপুরের মসজিদের ইমাম বিহারিদের দ্বারা এই অভিযোগে আক্রমণের শিকার হন যে তিনি কেন আস্তে-স্বরে মোনাজাত করেন, নিশ্চয়ই তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য আস্তে আওয়াজে দোয়া করেন। মোহাম্মদপুরের বিহারিরা দাবি করে, বাঙালি ইমামকে জোরে মোনাজাত করতে হবে। ইমাম এতে রাজি না হওয়ায় তাকে ইমামতি থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়। এ সম্পর্কে একটি সাক্ষ্য দিয়েছেন তৎকালীন মোহাম্মদপুর জামে মসজিদের পেশ ইমাম মওলানা লোকমান আহমদ আমীমী। (দৈনিক খবর, ৮ মার্চ ১৯৯০)।
মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর পরাধীন ঢাকার নতুন গভর্নর হন জেনারেল টিক্কা খান। তার সঙ্গে ৫ ও ৬ এপ্রিল পৃথক পৃথকভাবে সাক্ষাৎ করেন নূরুল আমীন, হামিদুল হক চৌধুরী, গোলাম আযম, আবদুল জাব্বার খদ্দর, মোহন মিয়া, এম এ মতিন, তোহা-বিন-হাবিব, মেজর আফসার উদ্দিন প্রমুখ। (দৈনিক সংগ্রাম, ৭ই এপ্রিল ১৯৭১)। কোনো আলেমের নাম এখানে পাওয়া যায় না, যাদের নাম সংবাদপত্রে ছাপা হয়েছিল, তারা সবাই পাকিস্তানপন্থি বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা।
এর আগে ১০ এপ্রিল ১৯৭১ সালে ঢাকায় মুক্তিযুদ্ধবিরোধী শান্তি কমিটি গঠিত হয়। এর আহ্বায়ক নিযুক্ত হন খাজা খয়েরউদ্দিন। সদস্য ছিলেন এ বি এম শফিকুল ইসলাম, ফরিদ আহম্মদ, অধ্যাপক গোলাম আযম, মাহমুদ আলী, এ এস এম সোলায়মান, আবুল কাশেম, আতাউল হক খান প্রমুখ। এরা সবাই ছিলেন পাকিস্তানপন্থি রাজনৈতিক নেতা, কেউ আলেম নন। এদের বেশির ভাগেরই দাড়ি-টুপি ছিল না। যদি কারও নামের আগে ‘মওলানা’ শব্দ থেকেও থাকে, তাও তিনি আলেম হিসেবে গণ্য হবেন না, যেমনটা গোলাম আযমের নামের আগে ‘অধ্যাপক’ শব্দ রয়েছে, এ জন্য অধ্যাপক-বুদ্ধিজীবীরা তার দায় নেবেন না। তারা রাজনৈতিক নেতা হিসেবেই বিবেচিত হবেন।
তবে আলেম সমাজের একটি অংশ যারা বিভিন্ন ইসলামপন্থি রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, তারা নিজেদের ভূমিকা দেশের মানুষের কাছে স্পষ্ট করতে পারেননি। আর পাকিস্তানিরা প্রচার চালাত যে আলেম সমাজ তাদের সঙ্গেই আছে। অবশ্য জমিয়তে ওলামায়ে ইসলামের সঙ্গে যুক্ত আলেম সমাজ মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে অবস্থান নেয়, কিন্তু নেজামে ইসলামের সঙ্গে যুক্ত আলেমরা তা করতে পারেননি। তারা পাকিস্তানিদের জুলুমের প্রতিবাদ করলেও ভারত-জুজুর ভয়ে মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে একাত্ম হতে পারেননি। যেমনটা পারেননি চীনপন্থি অনেক কমিউনিস্টও। এদের মধ্যে কমরেড মোহম্মদ তোয়াহা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে ছিলেন, কিন্তু ভারত-জুজু তাদের মধ্যেও কাজ করেছিল। কমরেড আবদুল হক তো পুরোপুরি পাকিস্তানের পক্ষেই যুদ্ধ করেছেন।
১৯৭১ সালে পাকিস্তানি সৈন্যদের সঙ্গে বাঙালির মুক্তিযুদ্ধে বিরোধিতাকারী সবচেয়ে সক্রিয় দল ছিল এই পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামী। এ দলটি সচেতনভাবে মুক্তিযুদ্ধের শুধু বিরোধিতা করেনি, তার সহযোগী সংগঠন ইসলামী ছাত্রসংঘকে (পরবর্তীকালে এর নাম রাখা হয় ইসলামী ছাত্রশিবির) নিয়ে পাকিস্তান রক্ষার জন্য তারা বিভিন্ন সশস্ত্র দল পর্যন্ত গড়ে তোলে। সারা দেশে পাকিস্তানি সৈন্যদের সঙ্গে হত্যা, ধ্বংস, লুট ও নারী ধর্ষণকে এরা শুধু সমর্থন, প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ ও সহযোগিতাই করেনি, শিক্ষিত মধ্যবিত্ত, ছাত্র, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী ও সাংবাদিকদের এরাই নির্বিচারে ধরে ধরে এনে অমানুষিকভাবে হত্যা করে এবং ‘গণিমতের মাল’ বলে ধর্ষণকে সিদ্ধ বলে ঘোষণা করে। কিন্তু আদর্শবাদের নামে জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী ছাত্রসংঘের এই নিষ্ঠুর পৈশাচিক আচরণের কারণ অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে, এটা তাদের জন্য মোটেই অস্বাভাবিক কিছু ছিল না। কারণ যে আদর্শবাদে এ দলটি সংগঠিত, তার অনিবার্য পরিণতি হচ্ছে এই ফ্যাসিবাদী কার্যকলাপ।
বামপন্থি বুদ্ধিজীবী ও কথাসাহিত্যিক শওকত ওসমান তার ডায়েরিতে একটি তথ্য লিপিবদ্ধ করেছেন, যাতে বোঝা যায়, ২৫ মার্চ (১৯৭১)-এর রাতে শত শত বাঙালির রক্তের সঙ্গে আলেমের রক্তও মুক্তিযুদ্ধকে স্নাত করেছিল: ‘হাতিরপুল মসজিদের ইমাম ২৬শে মার্চের ভোরে বেরিয়েছিল আজান দিতে।... মসজিদ প্রাঙ্গণেই তিনি গুলি খেয়ে লুটিয়ে পড়েন’। (শওকত ওসমান: স্মৃতিখণ্ড মুজিবনগর, বিউটি বুক হাউস, ১৯৯২, পৃষ্ঠা ৬৩)।
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ ‘ইনশাআল্লাহ’ বলে মুক্তিযুদ্ধের যে সূচনা করেন তা বরকতময় হয়ে ওঠে। দুনিয়ার ইতিহাসে আর কোনো মুক্তিযুদ্ধ এত দ্রুত সফলতা লাভ করেনি। এ যুদ্ধের উপদেষ্টা পরিষদের সভাপতি হয়েছিলেন মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী। যুদ্ধে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন তাজউদ্দীন আহমদ, যিনি ছিলেন কোরআনে হাফেজ। পাকিস্তান আমলে সর্বদা বঙ্গবন্ধুর পাশে থেকে লড়াই করেছেন সালঙ্গা বিদ্রোহের নায়ক মাওলানা আবদুর রশিদ তর্কবাগিশ।
মাওলানা উবায়দুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী ও মাওলানা আবদুল্লাহ বিন সাঈদ দুই ভাই রাজনৈতিকভাবে ছিলেন বঙ্গবন্ধুর সহযোগী। মাওলানা খায়রুল ইসলাম যশোরীসহ তারা স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের শব্দসৈনিক ছিলেন। মাওলানা আবু তাহের ও মাওলানা আবদুল বারী পশ্চিমবঙ্গের মাদ্রাসার শিক্ষক। তারাও স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে ধর্মীয় অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন।
মাওলানা আবদুর রহমান (কুমিল্লার রামপুর) এবং মাওলানা আবদুর রব (রাজারবাগ পুলিশ লাইন), মাওলানা মোস্তাফিজুর রহমান (হালিশহর) সরাসরি গেরিলা যুদ্ধে অংশ নেন। মুফতি আবদুস সোবহান চট্টগ্রামে আওয়ামী লীগ নেতা আখতারুজ্জামান বাবুর অধীনে মুক্তিযোদ্ধাদের রিক্রুট করেন। মাওলানা আবু ইসহাক রাঙ্গুনিয়ায় নিজের সন্তানদের সহ যুদ্ধে অংশ নেন। তার ছেলে মাওলানা আবুল কালাম চট্টগ্রাম দামপাড়ায় অবস্থিত রাজাকার ক্যাম্পে অপারেশনে অংশ নেন, যেখানে রাজাকাররা সমূলে ধ্বংস হয়। মাওলানা আবদুল মালিক, চট্টগ্রামে আওয়ামী লীগ নেতা এম এ আজিজের নেতৃত্বে গেরিলা দলে যোগ দেন। মাওলানা আবদুল সোবহান, মাওলানা কাজী আবুল ইসুফ চট্টগ্রামের বিভিন্ন খণ্ডযুদ্ধে অংশ নেন। মাওলানা দলিলুর রহমান ১৬ ডিসেম্বরের আগেই স্বাধীন হওয়ায় রাঙ্গুনিয়ায় প্রথম স্বাধীন পতাকা উত্তোলন করেন। মাওলানা মতিউর রহমান কওমি মাদ্রাসার ছাত্রদের মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিতে রিক্রুটের দায়িত্ব পালন করেন।
মাওলানা মৌলবী সৈয়দ বাঁশখালীতে ‘কমান্ডার মৌলবি সৈয়দ’ নামেই পরিচিত ছিলেন। এখানে তিনি ট্রেনিং ক্যাম্প স্থাপন করেন। ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধু হত্যার প্রতিবাদও তিনি করেছিলেন। ফলে ১৯৭৭ সালের ১১ আগস্ট জেনারেল জিয়ার সামরিক শাসনামলে তাকে হত্যা করা হয়।
পটিয়ায় পাকিস্তানি সেনাদের অভিযানকালে মাদ্রাসায়ও হামলা চালানো হয়। এখানে এ সময় শহীদ হন মাওলানা দানেশ। মাওলানা শরিফ পটিয়ার মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয় দেন। বেলাল মোহাম্মদের লেখা ‘স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র’ গ্রন্থে পটিয়া মাদ্রাসায় স্বাধীন বাংলার বেতার যন্ত্র লুকিয়ে রাখা এবং এ মাদ্রাসা পাকিস্তানি সৈন্যদের জ্বালিয়ে দেয়ার প্রসঙ্গ উল্লেখিত আছে।
মাওলানা নোমান মুক্তিযোদ্ধাদের গোপন আশ্রয়কেন্দ্র ও খাদ্যের জোগান দিতেন। মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার আবদুল কাদের চৌধুরীর বাহিনীর ইনফরমার হিসেবে অংশ নেন মাওলানা আবদুল মতিন মজুমদার। মাওলানা নূরুল আফসার, কর্নেল জাফর ইমামের নেতৃত্বে বিভিন্ন অপারেশনে অংশ নেন। মাওলানা আবদুল মতিন ও কারি মেসবাহুল ইসলাম, কুমিল্লায় ক্যাপ্টেন সুজাত আলীর নেতৃত্বে বিভিন্ন খণ্ডযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন।
নারায়ণগঞ্জে মাওলানা মতিউল ইসলামের বাড়ি থেকে মুক্তিযোদ্ধারা গোপনে বিভিন্ন পয়েন্টে হামলা চালাত। ক্যাপ্টেন বুরহানুদ্দীন ও কর্নেল নওয়াজেশের নেতৃত্বে নারায়ণগঞ্জে মুক্তিবাহিনীর ইনফরমার হিসেবে কাজ করতেন মাওলানা শামসুল হুদা ও মাওলানা মির্জা নূরুল হক। গঙ্গাচরার সংসদ সদস্য সিদ্দিক ও শামসু মাস্টারের বাহিনীতে যুক্ত হয়ে যুদ্ধ করেন মাওলানা আশিকুর রহমান। মাওলানা মোহাম্মদ আলী ও মাওলানা আবদুস সালাম ভারত থেকে প্রশিক্ষণ শেষে রংপুরে বিভিন্ন অপারেশনে অংশ নেন।
যশোরে লাইনে দাঁড়িয়ে পাকিস্তানি বাহিনী প্রকাশ্যে গুলি করে হত্যা করে মাওলানা আবুল হাসান যশোরীকে। অভিযোগ ছিল- তারা মাদ্রাসায় মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয় দিয়েছেন। যশোর রেলস্টেশন মাদ্রাসায় এখনো রয়েছে গণকবরটি। বঙ্গবন্ধুর ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিলেন মাওলানা আবদুল আউয়াল, তিনি উর্দুওয়ালাদের বক্তৃতা-বিবৃতি অনুবাদ করে বঙ্গবন্ধুকে দিতেন। ১৯৭১ সালে তিনি কলকাতায় অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকারের কাছে ঢাকার অবস্থার রিপোর্ট করতেন, মুক্তিযোদ্ধারা এ রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করে অপারেশন চালাত। মাওলানা আহমেদুর রহমান আজমী মুক্তিযুদ্ধে প্রবাসী উপদেষ্টা পরিষদে নীতিনির্ধারণী কাজে অংশ নিয়েছেন। মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, মাওলানা ফরিদউদ্দীন মসউদ প্রমুখসহ অসংখ্য আলেম এভাবে মুক্তিযুদ্ধে পরোক্ষ অথবা প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেন। এ রকম শত ঘটনার একটি সংগ্রহ গভীর ভালোবাসায় তৈরি করেছেন শাকের হোসাইন শিবলি ও তার বন্ধুরা ‘আলেম মুক্তিযোদ্ধার খোঁজে’ গ্রন্থে।
কালজয়ী কথাসাহিত্যিক হুমায়ূন আহমেদ তার ‘জোছনা ও জননীর গল্প’তে একটি সত্যি ঘটনা উল্লেখ করে জানিয়েছেন, ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি বাহিনী নেত্রকোনায় মাওলানা ইরতাজউদ্দিন নামে এক আলেমকে কীভাবে উলঙ্গ করে শহর ঘুরিয়েছিল এবং পরে নদীপাড়ে তাকে গুলি করে হত্যা করেছিল।
আলেমদের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণটি নানা রকমভাবে বর্ণিল এবং ঘটনাবহুল। জামায়াতে ইসলামীর অপকর্মের কারণে এ দেশের ইতিহাসবিদ ও লেখক-গবেষকদের কাছে আলেম সমাজ অবিচারের শিকার। বাংলাদেশের দীর্ঘ মুক্তিসংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে আলেমদের অবদান বাস্তব এক সত্য। যারা এটাকে অস্বীকার করে মূলধারায় অথবা গৌণ মনে করে, তারা খণ্ডিত এক ইতিহাস নিয়ে পড়ে আছে। (সমাপ্ত)
লেখক: ইতিহাসবিদ এবং ‘মুক্তিসংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধে আলেম সমাজের ভূমিকা’ শীর্ষক গ্রন্থের লেখক
১৯৮/সি, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮
©দৈনিক বাংলা
