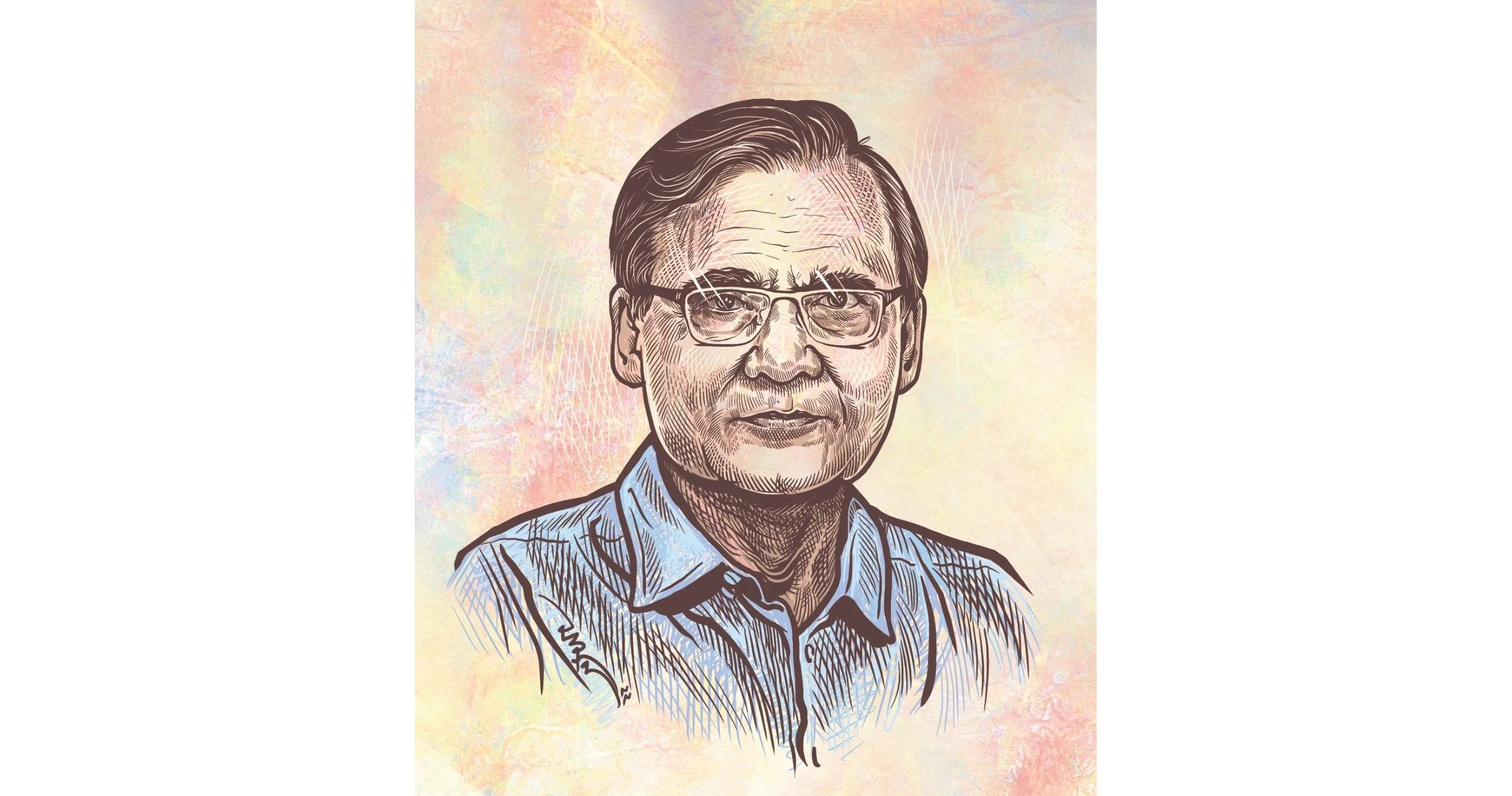
বদরূল ইমাম
বাংলাদেশ এখন যে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হওয়ার স্বপ্ন দেখছে, সেখানে পৌঁছতে স্বনির্ভর বিদ্যুৎ এবং জ্বালানি খাত প্রতিষ্ঠা করা ছাড়া উপায় নেই। আমদানিনির্ভর জ্বালানি নীতি শুধু অর্থনীতির ওপরেই চাপ সৃষ্টি করবে না, উপরন্তু এই স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করবে। দুঃখজনক হলেও সত্যি যে, বাংলাদেশের বিদ্যমান জ্বালানিসংক্রান্ত তৎপরতার মধ্যে সাময়িক সংকটকে এই নীতির ওপর জোর দিয়ে লাঘব করার চেষ্টা চলছে। কিন্তু এই নীতি বর্তমান সংকটকে কতটুকু লাঘব করবে, সেটাও বড় ধরনের প্রশ্ন তৈরি করেছে। বরং সংকট নিরসন না হয়ে অর্থনৈতিক চাপকে বৃদ্ধি করে উন্নয়নের প্রবাহকে বাধাগ্রস্ত করার শঙ্কাই বেশি রয়েছে।
স্বাধীনতার পরে বঙ্গবন্ধু স্বনির্ভর জ্বালানির বিষয়টি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তিনি দেশের নিজস্ব জ্বালানি সম্পদ উত্তোলন ও ব্যবহার করে স্বনির্ভরতা অর্জন করার নীতি গ্রহণ করেছিলেন। সেটা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে শেল অয়েল কোম্পানির কাছ থেকে পাঁচটি বৃহৎ গ্যাসক্ষেত্র দেশের পক্ষে কিনে নেয়া হয়, যেগুলো এখনও আমাদের দেশীয় উৎপাদনের সিংহভাগ জোগান দেয়। পরবর্তী সময় সেই নীতি থেকে বাংলাদেশ অনেকটা সরে এলেও বর্তমান বঙ্গবন্ধুরই নেতৃত্বদানকারী দলের সরকার ২০০৮-এ নির্বাচিত হয়ে নবম জাতীয় সংসদের অনুমিত হিসাব সম্পর্কিত কমিটির প্রথম রিপার্টে (২০১০-এ প্রকাশিত) স্বনির্ভর বিদ্যুৎ এবং জ্বালানি খাত গড়ে তোলার অঙ্গীকার করেছিল। কিন্তু দীর্ঘ সময় পর্যন্ত ক্ষমতায় থাকা একই দলের নেতৃত্বাধীন সরকারের এই সংক্রান্ত নীতি বাস্তবায়ন অনেকটা দূরে সরে গেছে। তারা হয়তো এখনকার সংকট মেটাতে তড়িঘড়ির আশ্রয় নিয়েছেন, কিন্তু সেটা বুমেরাং হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে বেশি। আমাদের দেশকে আগামীতে সমৃদ্ধ করতে হলে বঙ্গবন্ধুর পথেই হাঁটতে হবে। বিশেষজ্ঞ মহলের ধারণা, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সংকট মোকাবিলায় দ্বিমুখী তথা স্বল্পমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি জ্বালানি ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করা আবশ্যক।
বাংলাদেশে ১৯৭০-এর দশক থেকে ক্রমাগতভাবে বার্ষিক গ্যাস উৎপাদন হার বেড়েছে। বর্তমান সরকার ২০০৯ সালে ক্ষমতায় আসার পরও উৎপাদন বৃদ্ধির হার অব্যাহত ছিল এবং ২০১৬ সালে তা সর্বোচ্চ ৯৭৩ বিলিয়ন ঘনফুটে পৌঁছে। কিন্তু ২০১৭ থেকে বার্ষিক গ্যাস উৎপাদন ও সরবরাহ কমতে থাকে। গ্যাস সরবরাহ বৃদ্ধির জন্য ২০১৮ সাল থেকে দেশে লিকুইড ন্যাচারাল গ্যাস বা এলএনজি আমদানি শুরু হয়। পরবর্তী সময় বিশ্ববাজারে এলএনজির মূল্য বৃদ্ধি এবং পরে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ এলএজি স্পটে মূল্য আকাশচুম্বী হয়ে পড়ে। বর্তমানে এলএজি স্পটে দাম ইউনিটপ্রতি ৩০ ডলারের ওপরে থাকায় এই গ্যাস আমদানি করতে দেশ আর্থিক চাপে পড়ে। এর ফলে সাময়িকভাবে স্পট মার্কেট থেকে বাংলাদেশ এলএনজি ক্রয় করা বন্ধ করে। ভবিষ্যতে দেশীয় উৎস থেকে গ্যাস উৎপাদন আরও কমে গেলে এলএনজির ওপর নির্ভরতা বাড়ানোর পরিকল্পনা রয়েছে। কিন্তু এর ফলে আমাদের অর্থনীতির ওপর যে চাপ বাড়বে, তাতে আমাদের ভবিষ্যৎ সমৃদ্ধ অর্থনীতি হওয়ার সম্ভাবনা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।
পেট্রোবাংলার হিসাব মতে, এলএনজি আমদানি করতে প্রতিবছর ৪৪ হাজার কোটি টাকা ব্যয় হয় এবং তা কেবল মোট গ্যাস সরবরাহের ২০% মেটায়। বাকি ৮০% সরবরাহকৃত গ্যাস আসে দেশীয় গ্যাস উৎপাদন থেকে, যার জন্য খরচ হয় ২০ হাজার কোটি টাকার কম। তাই আমাদের দেশীয় গ্যাস উৎপাদনের ওপর জোর দেয়াই বাঞ্ছনীয় হবে।
দেশের নীতিনির্ধারণী মহলে উচ্চপর্যায়ের কেউ কেউ প্রচার করছেন, বাংলাদেশে গ্যাস সম্পদ প্রায় শেষ এবং নতুন গ্যাস মজুত পাওয়ার সম্ভাবনা নেই তেমন। কিন্তু এই ধারণা পোষণ করার কোনো বৈজ্ঞানিক সূত্র নেই। দেশে এখনও অনাবিষ্কৃত গ্যাস সম্পদের সম্ভাবনার পর দেশি ও বিদেশি মূল্যায়নসমূহে একই চিত্র পাওয়া গেছে, বাংলাদেশে অনাবিষ্কৃত গ্যাস সম্পদের পরিমাণ যথেষ্ট। প্রকৃতপক্ষে, এই মহলটিই এক সময় বিদেশি কোম্পানির স্বার্থে ‘দেশে আর গ্যাস নেই’-এর প্রচারণা চালিয়েছে। মূলত তারাই ভারতে গ্যাস রপ্তানির লক্ষ্যে ‘বাংলাদেশ গ্যাসের সাগরে ভাসছে’-এর প্রচারণাকারীদের উত্তরসূরি। উল্লেখ্য, সে সময় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনের উপস্থিতিতে ঘোষণা করেছিলেন, বাংলাদেশ নিজের ব্যবহারের জন্য ৫০ বছরের মজুত না রেখে গ্যাস রপ্তানি করবে না। এটি ছিল দেশের বাইরে গ্যাস রপ্তানির চিন্তাকে মাটিচাপা দেয়ার একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ।
দেশে অনাবিষ্কৃত গ্যাস সম্পদের ওপর একাধিক আন্তর্জাতিকভাবে খ্যাতিসম্পন্ন প্রতিষ্ঠান বৈজ্ঞানিক মূল্যায়ন করেছে। ২০০১ সালে ইউনাইটেডে স্টেট জিওলজিক্যাল সার্ভে (ইউএসজিএস) এবং পেট্রোবাংলার যৌথ মূল্যায়নে জানা যায় বাংলাদেশে ৫০ শতাংশ সম্ভাবনায় ৩২ দশমিক পাঁচ কিউবিক ফুট (টিসিএফ) অনাবিষ্কৃত গ্যাস পাওয়া যেতে পারে। এই মূল্যায়নে অবশ্য তথ্যের অভাবে বাংলাদেশের গভীর সমুদ্রকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। প্রায় একই সময়ে নরওয়ের রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান নরোজিয়ান পেট্রোলিয়াম ডাইরেক্টেট (এনপিডি) এবং বাংলাদেশের হাইড্রোকার্বন ইউনিটের অপর একটি মূল্যায়নে মত প্রকাশ করা হয়, ৫০ শতাংশ সম্ভাবনায় দেশে অনাবিষ্কৃত গ্যাসের পরিমাণ ৪২ টিসিএফ। সর্বশেষ ২০১১ সালে ইউরোপিয়ান গ্যাস মূল্যায়ন প্রতিষ্ঠান গুভতাফসান অ্যাসোসিয়েটের মূল্যায়নে দেশে অনাবিষ্কৃত গ্যাসের পরিমাণ বলা হয়েছে ৩৪ টিসিএফ। আমার মতে, এসব বৈজ্ঞানিক সমীক্ষাকে উপেক্ষা করা সর্বোতভাবে অযৌক্তিক। তাই বলা যায়, বাংলাদেশের অনাবিষ্কৃত গ্যাসের অনুসন্ধানের বিকল্প নেই।
দুঃখজনক বিষয় হলো, বাংলাদেশ অতি গ্যাস সম্ভাবনাময় হওয়া সত্ত্বেও এখানে অনুসন্ধান কূপের সংখ্যা বিশ্বের অন্যান্য গ্যাস ধারক বেসিনগুলো থেকে অনেক অনেক কম। পার্শ্ববর্তী ভারতের একটি ছোট রাজ্য ত্রিপুরা (১০,০০০ বর্গকিমি) এ পর্যন্ত অনুসন্ধান কূপ খনন করেছে ১৭০টি, অথচ বাংলাদেশে (১৪৭,০০০ বর্গকিমি) অনুসন্ধানকৃত কূপের সংখ্যা মাত্র ৯৮টি। সমুদ্রবক্ষে অনুসন্ধান কাজের ধারা আরও হতাশাব্যঞ্জক। ২০১২ সালে বাংলাদেশ মিয়ানমার সমুদ্রসীমানা বিরোধ নিষ্পত্তি হওয়ার পর থেকে আজ পর্যন্ত মিয়ানমারের সমুদ্রবক্ষে অনেক সংখ্যক গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কার হলেও বাংলাদেশে তা হয়নি। এজন্য অনতিবিলম্বে স্বল্পমেয়ামি ব্যবস্থাপনায় নিম্নোল্লিখিত কয়েকটি পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরি হয়ে পড়েছে :
১. দেশের আবিষ্কৃত অথচ উৎপাদন স্থগিত রাখা গ্যাস (যেমন ছাতক গ্যাসক্ষেত্র) মজুতসমূহকে উৎপাদনে নিয়ে আসা।
২. আবিষ্কৃত কিন্তু উৎপাদনে আনা হয়নি (ভোলা নর্থ, জকিগঞ্জ ইত্যাদি) তা উৎপাদনের আওতায় নিয়ে আসা।
৩. দেশের পুরোনো পরিত্যক্ত কূপগুলোকে ওয়ার্কওভার কার্যক্রমের মাধ্যমে পুনর্মূল্যায়ন করে যেখানে সম্ভব তা থেকে গ্যাস উৎপাদন শুরু করা।
৪. দেশের চলমান গ্যাসক্ষেত্রের কূপ প্রতি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কূপগুলোর কারিগরি কাঠামোতে প্রয়োজনীয় সংযোজন, পরিবর্তন করা এবং এর জন্য ইতিপূর্বে নিয়োগকৃত কারিগরি পরামর্শকের সুপারিশগুলো কার্যকর করা।
উপরোক্ত বিষয়গুলো ছাড়াও দেশের উত্তরাংশে অবস্থিত কয়লা মজুতগুলোকে উত্তোলন ও বিদ্যুৎ উৎপাদনে ব্যবহার করা অত্যাবশ্যক। দেশের সৌর জ্বালানির সম্ভাবনাকে যথাযথভাবে কাজে লাগিয়ে সরকার নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা এবং অন্যান্য নবায়নয়োগ্য জ্বালানির বাস্তবায়নের ওপর গুরুত্ব দেয়া আবশ্যক।
২.
এখন আমাদের দেশে নবায়নযোগ্য জ্বালানির সম্ভাবনাকেও খতিয়ে দেখা দরকার। এক্ষেত্রে সারা বিশ্বই এখন নবায়নযোগ্য জ্বালানির পথে হাঁটার চিন্তা করছে। ১৯৯০-এর দশকে আন্তর্জাতিক জ্বালানি বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক পিটার ওডেল ভবিষ্যদ্বাণী করেন, ২০৪০ সাল পর্যন্ত বিশ্ব সনাতনী জ্বালানি তেল, গ্যাস ও কয়লার ওপর মূলত নির্ভর করে থাকবে। ২০৬০ থেকে তেল-গ্যাস-কয়লা সনাতনী জ্বালানির সঙ্গে সৌর, বায়ু ও অন্যান্য নবায়নযোগ্য জ্বালানির প্রতিযোগিতা চরমে পৌঁছাবে এবং ২০৭০ সালের পরই এ প্রতিযোগিতায় নবায়নযোগ্য জ্বালানি বিজয়ের পথ দেখতে পাবে। ডেনমার্ক বা অনেক ইউরোপীয় দেশে নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যাপক প্রসার দেখে অনেকেই প্রশ্ন করছেন, তবে কি নবায়নযোগ্য জ্বালানির বিশ্ববিজয় ২০৭০ সালের আগেই ঘটে যাবে?
ডেনমার্ক বা অন্যান্য ইউরোপীয় দেশে পর্যাপ্ত সূর্যের আলো সহজলভ্য নয়, যেমনটি বাংলাদেশে রয়েছে। তথাপি বাংলাদেশে জ্বালানি মিশ্রণে নবায়নযোগ্য জ্বালানির (সৌর, বায়ু, জৈব ইত্যাদি) অংশীদারত্ব মাত্র ৩ শতাংশ, যা কি না ডেনমার্কের তুলনায় অনেক অনেক কম। সরকারি পরিকল্পনা অনুযায়ী, ২০১৫ সালে বাংলাদেশে নবায়নযোগ্য জ্বালানির অংশীদারত্ব মোট জ্বালানি ব্যবহারের ৫ শতাংশ হওয়ার কথা থাকলেও তা বাস্তবায়িত হয়নি। বাংলাদেশে ২০২১ সালের মধ্যে জ্বালানি মিশ্রণে নবায়নযোগ্য জ্বালানির অংশীদারত্ব ১০ শতাংশ হবে বলে সরকার প্রাক্কলন করে। সে অনুযায়ী ২০২১ সালে নবায়নযোগ্য জ্বালানিনির্ভর বিদ্যুৎ উৎপাদন ২ হাজার ৪০০ মেগাওয়াট (সে সময় পরিকল্পিত মোট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ২৪ হাজারের ১০ শতাংশ) হওয়ার কথা। অর্থাৎ আগামী পাঁচ বছরে নবায়নযোগ্য জ্বালানি (মূলত সৌর ও জলবিদ্যুৎনির্ভর) বিদ্যুতের পরিমাণ বর্তমান ৪৫০ মেগাওয়াট থেকে বেড়ে ২ হাজার ৪০০ মেগাওয়াট হওয়ার কথা। অথচ সেই লক্ষ্য অর্জনের জন্য পর্যাপ্ত প্রকল্প দৃশ্যমান না থাকায় তা বাস্তবায়িত হবে বলে পর্যবেক্ষক মহল মনে করে না।
বাংলাদেশে জ্বালানি মিশ্রণে সৌর জ্বালানির অংশ খুব কম, তথা ২ শতাংশের নিচে। তবু সৌর জ্বালানি এ দেশে এক অর্থে সফলতা অর্জনের দাবি রাখে এ কারণে যে, এ দেশে বিশ্বের দ্রুততম গতিতে সোলার হোম সিস্টেমের (এসএমএস) প্রসার ঘটে চলেছে। দেশে প্রতি মাসে প্রায় ৬০ হাজার এসএমএস স্থাপিত হয়ে থাকে, যার মাধ্যমে এ পর্যন্ত প্রায় ৪৫ লাখ বাড়িতে সৌরবিদ্যুৎ পৌঁছেছে, যাদের মোট উৎপাদন ক্ষমতা ১৯৫ মেগাওয়াট। পরিমাণগত দিক থেকে এ পরিমাণ বিদ্যুৎ সামান্যই বটে (দেশে বিদ্যুতের মোট উৎপাদন ক্ষমতা ১৩ হাজার মেগাওয়াট)। কিন্তু এটির অবদান এই অর্থে বিশাল যে, এর ফলে দেশের গ্রিডহীন ও দূরবর্তী অঞ্চলে বিরাট এক সুবিধাবঞ্চিত গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর কাছে বিদ্যুৎ পৌঁছেছে। এই জনগোষ্ঠী গ্রিড লাইনের মাধ্যমে কখনও বিদ্যুতের সুবিধা পেত না। সৌরবিদ্যুৎ তাদের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি করে নীরব বিপ্লব ঘটিয়েছে।
দূরবর্তী এক গ্রামীণ বাসস্থানে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেয়া এক কথা আর দ্রুত ও ব্যাপক শিল্পায়নের লক্ষ্য নিয়ে অপেক্ষমাণ একটি বিরাট জনগোষ্ঠীর বিদ্যুৎ চাহিদা মেটানো ভিন্নতর বটে। এটি একটি বড় চ্যালেঞ্জ। বাংলাদেশ বর্তমানে জ্বালানি-সংকটে রয়েছে। দেশটিকে উচ্চ-মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হতে হলে বাংলাদেশের জনপ্রতি আয় বৃদ্ধি করতে হবে, যার জন্য জনপ্রতি জ্বালানি ব্যবহার আরও বৃদ্ধি করা অত্যাবশ্যক।
আমার মতে, নিকট ও মধ্যবর্তী (২০২০-৩০) ভবিষ্যতের জ্বালানি সংকট এড়াতে জ্বালানি আমদানি নির্ভরশীলতা কমিয়ে বাংলাদেশের উচিত অনতিবিলম্বে দেশে, বিশেষ করে সমুদ্রের গ্যাস অনুসন্ধানের জোরালো ও চূড়ান্ত কার্যক্রম শুরু করা, সম্ভাব্য সর্বোচ্চ মাত্রায় সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন করা ও দেশীয় কয়লা উত্তোলনে বাস্তবধর্মী পদক্ষেপ নেয়া। মধ্যম ও দূরবর্তী (২০৩০-৫০) ভবিষ্যতের জন্য বাংলাদেশকে নেপাল, ভুটান ও ভারতের জলবিদ্যুৎ প্রকল্প এবং বাস্তবায়ন সাপেক্ষে আন্তদেশীয় পাইপলাইন গ্যাসসংযোগ প্রকল্প (ইরান-পাকিস্তান-ভারত অথবা তুর্কমেনিস্তান-আফগানিস্তান-পাকিস্তান-ভারত) সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে হবে। অতি দূরবর্তী ভবিষ্যতে (২০৬০ ও তারপর) কেবল বাংলাদেশই নয়; বরং সমগ্র বিশ্বের জ্বালানি বাজারে নবায়নযোগ্য (মূলত সৌর, বায়ু ও জৈব) জ্বালানি সাশ্রয়ী ও সহজলভ্য হয়ে দেখা দেবে এবং ক্রমান্বয়ে এগুলো বিশ্ব জ্বালানি বাজারকে সম্পূর্ণভাবে গ্রাস করবে। সে সময়টি (২০৮০) বাংলাদেশের জন্য অপেক্ষাকৃত সুখকর হতে পারে যখন তেল-গ্যাস-কয়লার মতো জ্বালানিগুলো কেবল ইতিহাসের পাতায় স্থান করে নেবে।
লেখক: অধ্যাপক, ভূতত্ত্ব বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
১৯৮/সি, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮
©দৈনিক বাংলা
