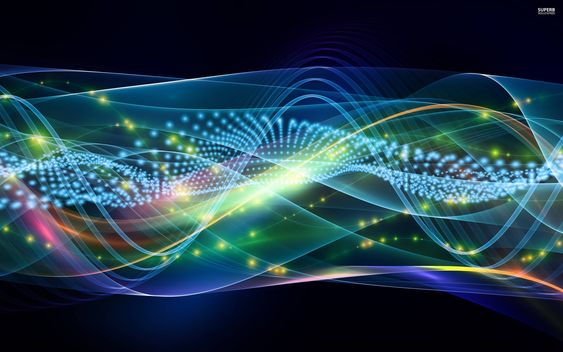
পাঠ্যবইয়ে ‘তরঙ্গ ও শব্দ’ অধ্যায়ে তরঙ্গ নিয়ে যে আলোচনা করা হয়েছে, সেটা মূলত যান্ত্রিক তরঙ্গের আলোচনা। যান্ত্রিক তরঙ্গ হলো সেই সব তরঙ্গ, যেগুলো সঞ্চালনের জন্য স্থিতিস্থাপক মাধ্যম অর্থাৎ জড় মাধ্যম বা এক কথায় পদার্থ দরকার পড়ে। যেমন শব্দ এক প্রকার যান্ত্রিক তরঙ্গ, কারণ ইহা শূন্য মাধ্যমে চলতে পারে না।
আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কথা হলো ‘উপরিপাতন’ কিন্তু তরঙ্গের হয়। সুতরাং আলোক তরঙ্গেরও উপরিপাতন হয়, তবে আলো সঞ্চালন করার সময় কোনো প্রকার স্বচ্ছ মাধ্যম না থাকলেও তা শূন্য মাধ্যমেই সঞ্চালিত হতে পারে। তোমাদের বইয়ে যেহেতু জড় মাধ্যমের তরঙ্গগুলো নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, সেহেতু জড় মাধ্যমে তরঙ্গের উপরিপাতন বিষয়ে মোটামুটি ধারণা রাখলেই তোমাদের চলবে। আলোচনা সরাসরি শুরু করার আগে আরও একটুখানি কথা না বললেই নয়।
তুমি হয়তো জানো- যখন কোনো মাধ্যমের মধ্য দিয়ে তরঙ্গ অর্থাৎ শক্তি সঞ্চালিত হয়, তখন সঞ্চালন অংশে মাধ্যমের কণাগুলো সরল রৈখিক পথে দুপাশে ভাইব্রেট বা স্পন্দিত হতে থাকে। সরল স্পন্দনের সময় মাধ্যমের কণাগুলো বারবার মধ্যবিন্দু বা সাম্যাবস্থার দিকে ফিরে আসতে চায় পদার্থের জড়তা বা স্থিতিস্থাপকতা নামক ধর্মগুলোর কারণে।
তরঙ্গের ‘দশা’ সম্বন্ধেও হয়তো তুমি কিছুটা জানো। ‘দশা’ বলতে মূলত বোঝায় তরঙ্গে উপস্থিত কোনো কণার বেগ, ত্বরণ, সরণ ইত্যাদি অর্থাৎ কণাটির গতির মান এবং দিক সবকিছুই বোঝনো হয় দশা নামক একটা রাশি ব্যবহার করে। কোনো জড় মাধ্যম দিয়ে যান্ত্রিক তরঙ্গ যাওয়ার সময় মাধ্যমের কণাগুলো তরঙ্গের সঙ্গে এগিয়ে যায় না, বরং তরঙ্গের গতিতেই কণার গতির অবস্থা বা দশা এগিয়ে যায় (তোমাকে অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে, তরঙ্গের গতি এবং কণার গতি এ ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ভিন্ন)।
তরঙ্গের উপরিপাতন (Superposition) নিয়ে এবার আলোচনায় শুরু করা যাক।
(১) মনে করো কোনো একটা জড় মাধ্যমের মধ্য দিয়ে তরঙ্গ যাচ্ছে। যেহেতু মাধ্যমটি জড় মাধ্যম, তাই সেখানে নিশ্চয় পদার্থ আছে, অর্থাৎ অণু-পরমাণু আছে যাদের তুমি কণা বলতে পারো। এবার সেখানে একটি তরঙ্গ চলার পথে মাধ্যমের একটি কণাকে কল্পনা করো। তরঙ্গটি এসে কণাটির ওপর আছড়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে কণাটি তার সাম্যাবস্থানের দুপাশে দুলতে শুরু করল। এতে কণাটি যেকোনো একটা দিকে সর্বাধিক যে দূরত্ব অতিক্রম করল অর্থাৎ কণাটির যেটুকু সরণ ঘটল সেটি হলো কণাটির বা উক্ত তরঙ্গটির বিস্তার। এরপর কণাটি তার আগের অবস্থান অর্থাৎ সাম্যাবস্থানের ফিরে এলো এবং বিপরীত দিকেও পূর্বের বিস্তারের সমান বিপরীত সরণ ঘটল। মনে করো সাম্যাবস্থান থেকে একদিকে কণাটির সরণ প্রথমে ঘটেছিল +২ সে.মি., সাম্যাবস্থানে ফিরে এসে বিপরীত দিকে তার সরণ ঘটেছিল -২ সে.মি.। তাহলে তুমি বলতে পারো তরঙ্গটিরও বিস্তার ২ সে.মি.। এভাবে যতক্ষণ তরঙ্গ চলমান থাকল কণাটি নির্দিষ্ট সময় পরপর একইভাবে স্পন্দিত হতে থাকল।
(২) এবার মনে করো একই রেখা বরাবর ২ সে.মি. বিস্তারের সমজাতীয় দুটি তরঙ্গ বিপরীত দিক থেকে কণাটির ওপর একই সঙ্গে এসে পড়ল। যদি তরঙ্গ দুটি একই সময়ে, একই সঙ্গে না এসে পৃথক পৃথকভাবে কণাটির ওপর আপতিত হতো এবং উভয় তরঙ্গের ক্ষেত্রেই কণাটির সরণ প্রথমে +২ সে.মি. এবং পরে -২ সে.মি. এভাবে হতো, তাহলে আমরা বলতে পারি তরঙ্গ দুটি সমদশা নিয়ে কণাটির ওপর মিলিত হয়েছিল। একই সঙ্গে সমান দশা ও বিস্তার নিয়ে একই জাতের দুটি তরঙ্গ যদি মাধ্যমের কোনো কণার ওপর মিলিত হয়, তাহলে কণাটির স্পন্দনের সময় তার যে সরণ হবে, সেটা হবে তরঙ্গ দুটির বিস্তারের যোগফলের সমান। অর্থাৎ একই সময়ে +২ সে.মি. বিস্তারের দুটি সমদশার তরঙ্গের ক্রিয়ার জন্য কণাটির মোট বিস্তার হবে +৪ সে.মি. (বিপরীত দিকের জন্য -৪ সে.মি.)। তরঙ্গের বিস্তার বড়ো হওয়া মানেই তরঙ্গের শক্তি বা তীব্রতার পরিমাণ বেড়ে যাওয়া। কিন্তু দুটি সমজাতীয় এবং একই বিস্তারের তরঙ্গ যদি বিপরীত দশা নিয়ে কণার ওপর আপতিত হয়, তখন কণাটির বিস্তার হবে (+২ -২) = ০ সে.মি.। অর্থাৎ তরঙ্গ দ্বয়ের মিলিত প্রভাবে কণাটি তখন আর কোনো দিকেই স্পন্দিত হবে না। একটি মাধ্যমে যেহেতু অসংখ্য কণা থাকে, তাই তরঙ্গ দুটি যুক্ত হওয়ার সময় সেখানকার কণাগুলোর সরণ শূন্য হবে। অর্থাৎ মিলিত তরঙ্গের মোট বিস্তার শূন্য হবে ফলে তরঙ্গের শক্তি বা তীব্রতার সমষ্টিও শূন্য হবে। ওপরের ঘটনা দুটি হলো তরঙ্গের উপরিপাতন।
এর সংজ্ঞা আমরা লিখতে পারি-
দুটি তরঙ্গ একই সঙ্গে কোনো মাধ্যমের একটি কণাকে অতিক্রম করলে ওই কণা তরঙ্গ দুটির সম্মিলিত প্রভাবে আলোড়িত হবে এবং সাম্যাবস্থান থেকে কণাটির লব্ধি সরণ হবে পৃথকভাবে তরঙ্গ দুটি কণাটির যে সরণ সৃষ্টি করে তাদের ভেক্টর যোগফলের সমান।
অর্থাৎ একটি তরঙ্গের জন্য মাধ্যমের কোনো কণার সরণ যদি y1 এবং অন্য একটি তরঙ্গের জন্য কণাটির সরণ যদি y2 হয় তাহলে উপরিপাতনের নীতি অনুযায়ী উভয় তরঙ্গের জন্য কণাটির সরণের লব্ধি হবে,
y= y1+y2
এবং y1 বিপরীত দশায় মিলিত হলে তখন লব্ধি হবে,
y= y1-y2
সমান কমাঙ্ক ও সমান দশার তরঙ্গ দ্বয় বিপরীত দিক থেকে এসে কণাটিকে অতিক্রম না করে উভয়ে একই দিক থেকে সমদশায় বা বিপরীত দশায় কণাটিকে অতিক্রম করতে পারে। যেদিক থেকেই তারা অতিক্রম করুক, উভয় ক্ষেত্রেই কণার লব্ধি সরণ উপরিপাতনের নীতি মেনেই ঘটবে।
দুটি তরঙ্গের উপরিপাতনের ফলে মাধ্যমের কণাগুলো প্রভাবিত হলেও তরঙ্গ দুটি মোটেও প্রভাবিত হয় না। অর্থাৎ উপরিপাতনের পূর্বে তরঙ্গ দুটি যেদিকে যাচ্ছিল, উপরিপাতনের পরও তরঙ্গ দুটি তাদের নিজ নিজ কম্পাঙ্ক, বিস্তার, তরঙ্গ দৈর্ঘ্য, বেগ অর্থাৎ স্ব স্ব বৈশিষ্ট্যকে অক্ষুণ্ণ রেখে সেই একই দিকেই যেতে থাকবে। মনে হবে যেন এরা কখনোই একে অপরের সঙ্গ কখনো কোথাও মিলিত-ই হয়নি!
উপরিপাতনের ফলেই তরঙ্গের ব্যতিচার (Interference) ঘটে। একাধিক তরঙ্গের উপরিপাতনের ফলে লব্ধ তরঙ্গের তীব্রতা বেড়ে যাওয়া বা বিস্তার বেড়ে যাওয়াকে গঠনমূলক ব্যতিচার (Constructive Interference) বলে। একইভাবে লব্ধ তরঙ্গের বিস্তার বা তীব্রতার হ্রাস পাওয়াকে ধ্বংসাত্মক ব্যতিচার (Destructive Interference) বলে।
স্থির পানিতে কাছাকাছি দুটি ঢেউ সৃষ্টি করলে পানির যে বিন্দুতে দুটি তরঙ্গের চূড়া মিলিত হয়, সে বিন্দুতে তরঙ্গের উচ্চতা বেড়ে যায়। আবার যে বিন্দুতে দুটি তরঙ্গ খাঁজ মিলিত হয়, সে বিন্দুতে তরঙ্গের গভীরতা বেড়ে যায়। পক্ষান্তরে যে বিন্দুতে তরঙ্গ চূড়া এবং তরঙ্গ খাঁজ এসে মিলিত হয়, সে বিন্দুতে দুটি তরঙ্গ নাকোচ হয়। এসব ঘটনা উপরিপাতনের সাধারণ উদাহরণ।
লেখক: শিক্ষক, কৃষ্ণগোপালপুর দ্বিমুখী উচ্চ বিদ্যালয়, রাজশাহী
১৯৮/সি, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮
©দৈনিক বাংলা
