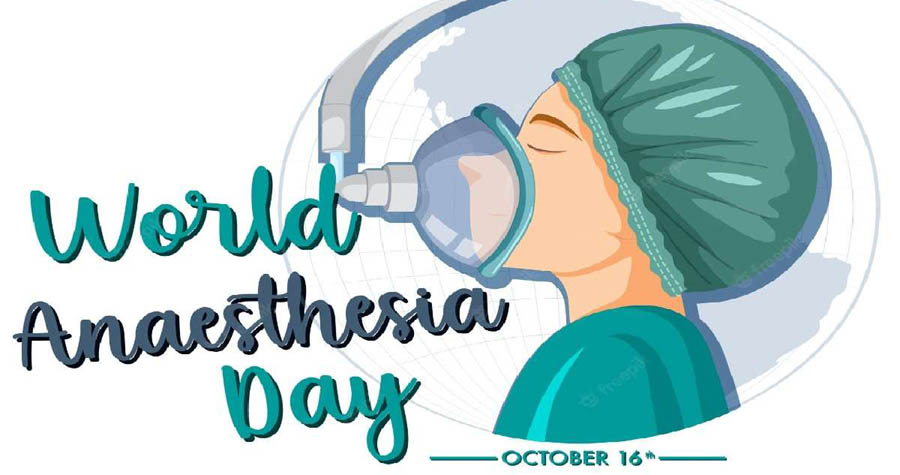
জাকিয়া আহমেদ
যেকোনো উন্নত দেশে এক লাখ মানুষের বিপরীতে ন্যূনতম ৫ থেকে ১০ জন অ্যানেস্থেসিওলজিস্ট বা অবেদনবিদ থাকেন। আর উন্নয়নশীল দেশগুলোয় সে সংখ্যা পাঁচজন। কিন্তু বাংলাদেশে প্রতি এক লাখ মানুষের জন্য অবেদনবিদ রয়েছেন মাত্র একজন।
অথচ যেকোনো অস্ত্রোপচারে একজন অবেদনবিদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আর করোনাকাল অবেদনবিদের এই সংকট চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে। মহামারির এই সময়ে একদিকে মানুষ আইসিইউর জন্য ছুটেছে হাসপাতাল থেকে হাসপাতালে, অন্যদিকে অবেদনবিদের অভাবে যথাসময়ে সঠিক চিকিৎসা ও অস্ত্রোপচার করা যায়নি অনেকের।
এই প্রেক্ষাপটে আজ রোববার বাংলাদেশসহ বিশ্বজুড়ে পালিত হচ্ছে ১৭৬তম ওয়ার্ল্ড অ্যানেস্থেসিয়া ডে। এবার দিবসটির প্রতিপাদ্য ‘লেটস ওয়ার্ক টুগেদার টু ইমপ্রুভ মেডিসিন সেফটি’।
সংশ্লিষ্টরা বলছেন, সাধারণত অস্ত্রোপচার, আইসিইউ ও পেইন ম্যানেজমেন্ট করতে অ্যানেস্থেসিওলজিস্ট দরকার হয়। আইসিইউ ব্যবস্থাপনায় দক্ষ ও প্রশিক্ষিত অবেদনবিদ না থাকলে রোগীদের ঝুঁকি অনেক বেড়ে যায়। কিন্তু দেশে প্রয়োজনের তুলনায় অবেদনবিদের সংখ্যা অত্যন্ত কম।
বাংলাদেশ সোসাইটি অব অ্যানেস্থেসিওলজিস্ট, ক্রিটিক্যাল কেয়ার অ্যান্ড পেইন ফিজিশিয়ানসের (বিএসএ-সিসিপিপি) তথ্যমতে, যেকোনো উন্নত দেশে এক লাখ মানুষের জন্য নিদেনপক্ষে ২০ জন অ্যানেস্থেসিওলজিস্ট থাকেন। উন্নয়নশীল দেশে এ সংখ্যা ৫ থেকে ১০ জন হয়। কিন্তু বাংলাদেশে প্রতি এক লাখ মানুষে মাত্র একজন অ্যানেস্থেসিওলজিস্ট রয়েছেন।
বিএসএসিসিপিপির মহাসচিব এবং বারডেম হাসপাতালের অ্যানেস্থেসিয়া, সার্জিক্যাল আইসিইউ এবং পেইন ম্যানেজমেন্ট বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডা. কাওছার সরদার দৈনিক বাংলাকে বলেন, ‘বাংলাদেশে প্রতি এক লাখ মানুষের জন্য মাত্র একজন অ্যানেস্থেসিওলজিস্ট রয়েছে, অথচ দরকার কমপক্ষে পাঁচজন। হাসপাতালগুলোয় প্রয়োজনীয়সংখ্যক পদ নেই। এই কিছুদিন আগ পর্যন্ত সার্জারির এত ডিসিপ্লিন (বিভাগ) ছিল না। বিভাগ যত বেড়েছে, অ্যানেস্থেসিওলজিস্টের সংকট তত বেড়েছে। কিন্তু অ্যানেস্থেসিওলজিস্টও তৈরি হয়নি, সরকারও পোস্ট তৈরি করেনি সেভাবে।’
করোনা মহামারির পর দেশের সব জেলা হাসপাতালে ১০ শয্যার আইসিইউ তৈরি করতে সরকারের পরিকল্পনা প্রায় চূড়ান্ত। করোনার সময় ৪০৯ জন অ্যানেস্থেসিওলজিস্ট নিয়োগ দেয় সরকার। কিন্তু সে সময়ে সবাই সরকারি হাসপাতালগুলোয় যোগদান করেননি।
অ্যানেস্থেসিওলজিস্টের সংকটের কারণ সম্পর্কে অধ্যাপক ডা. কাওছার সরদার বলেন, ‘প্রাইভেট প্র্যাকটিসে অ্যানেস্থেসিওলজিস্টদের যে পরিশ্রম, সে অনুযায়ী সম্মানী নেই। এ কারণে মেডিকেল শিক্ষার্থীরা এ সেক্টরের প্রতি আগ্রহী হন না।’ তিনি বলেন, অ্যানেস্থেসিয়ার পাশাপাশি তার যে সাব-স্পেশালিটি অর্থাৎ ক্রিটিক্যাল কেয়ার এবং পেইন ম্যানেজমেন্টকে উন্নতির জন্য আরও অ্যানেস্থেসিওলজিস্ট নিয়োগ হওয়া প্রয়োজন। কারণ ২০৩০ সালের মধ্যে এসডিজির যে অভীষ্ট অর্জন করতে হবে, সেখানে সাব-স্পেশালিটির উন্নয়ন ছাড়া এই লক্ষ্য অর্জন কঠিন হবে। এ জন্য বিএসএসিসিপিপি কাজ করে যাচ্ছে।
বাংলাদেশ সোসাইটি অব অ্যানেস্থেসিওলজিস্ট, ক্রিটিক্যাল কেয়ার অ্যান্ড পেইন ফিজিয়ান্সের (বিএসএ-সিসিপিপি) সভাপতি অধ্যাপক ডা. দেবব্রত বনিক দৈনিক বাংলাকে বলেন, তবে বর্তমানে ক্রিটিক্যাল কেয়ার বিশেষজ্ঞ এবং অ্যানেস্থেসিওলজিস্ট (অবেদনবিদ) মিলিয়েই আইসিইউতে চিকিৎসা দেয়া হয়। সম্প্রতি এ বিষয়ে চিকিৎসক নিয়োগ দেয়া হলেও তাতেও স্বল্পতা রয়েছে।
১৯৮/সি, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮
©দৈনিক বাংলা
