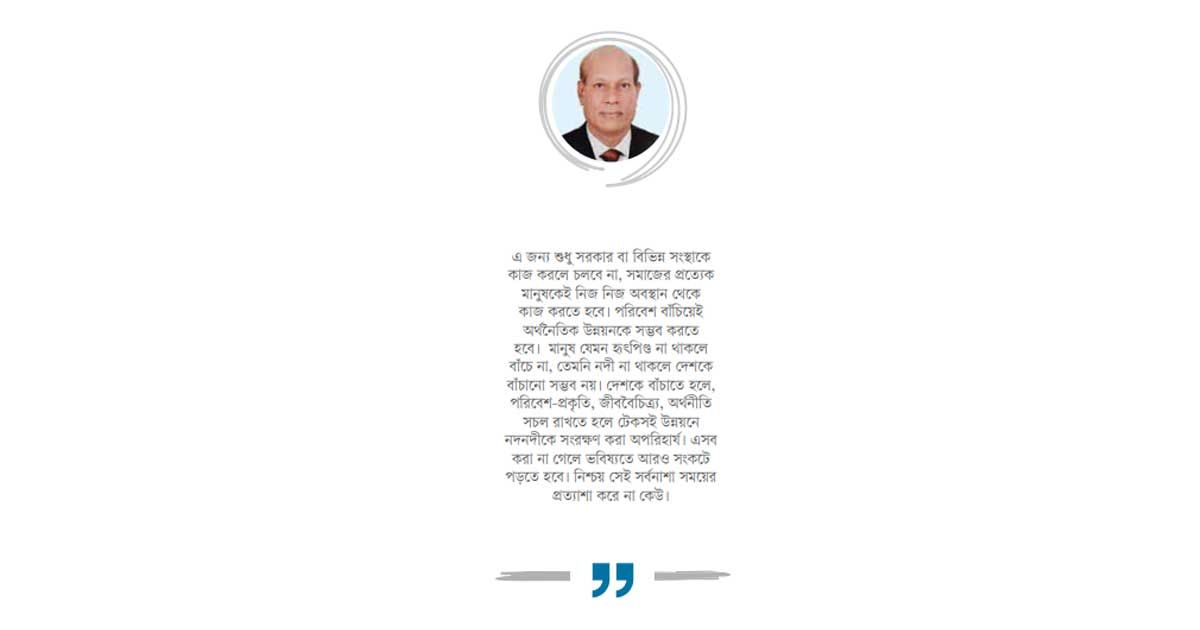
পৃথিবীর অধিকাংশ শহর-বন্দর গড়ে উঠেছে সমুদ্রকে ঘিরে। একইভাবে মানব সভ্যতা, সংস্কৃতির বিকাশও নদনদীকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছে। আমাদের দেশ নদী মাতৃক। জালের মতো নদী জড়িয়ে রেখেছে বাংলাদেশকে, বাংলাদেশের মানুষকে। কিন্তু ‘দাঁত থাকতে মানুষ যেমনি দাঁতের মর্যাদা বুঝে না, তেমনি নদী থাকতে নদীর মর্যাদা দিচ্ছি না আমরা।’ অর্থনীতি, জীবন প্রবাহকে সচল রাখা নদীগুলোকে প্রতিনিয়ত আমরা হত্যার মহোৎসবে লিপ্ত রয়েছি। এসব করছে স্বয়ং সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তর ও সংস্থা। এর সঙ্গে জড়িত রয়েছে বিভিন্ন ব্যক্তি, শিল্পপ্রতিষ্ঠানও। এটি জাতির জন্য, অর্থনীতির জন্য, জীবন প্রবাহের জন্য দুঃসংবাদ। তাই আমাদের প্রাণ রসায়ন সচল রাখতে, জীবন প্রবাহকে গতিশীল রাখতে নদী রক্ষার কার্যকর উদ্যোগ অপরিহার্য। একই সঙ্গে নদী দেশের অর্থনীতি, নদীকেন্দ্রিক মানুষের জীবন-যাপন, খাদ্য, পানি, নৌপথে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে মানুষ ও পণ্য পরিবহন, নদীকেন্দ্রিক পর্যটন ব্যবস্থায় নদীই একমাত্র ভরসা। একই সঙ্গে নদী আমাদের আত্মা, আমাদের দেহে রক্ত সঞ্চালক, হৃদয়ের স্পন্দন। এসব গুরুত্ব বিবেচনায় নদীকে নদীর মতো থাকতে না দিলে অর্থনীতি, সভ্যতা, সংস্কৃতি, নদীকেন্দ্রিক গড়ে ওঠা শহর, বন্দর, যোগাযোগ, পণ্য পরিবহন, পরিবেশ, প্রকৃতি, জীববৈচিত্র্য, নদীতে থাকা রূপালী মৎস্য সম্পদ, খনিজ সম্পদ, লৌহজাত মূল্যবান পদার্থ সবই পড়বে হুমকিতে।
সম্প্রতি বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের তালিকায় দেশে নদনদীর সংখ্যা ৪০৫ উল্লেখ করা হয়েছে। এর মধ্যে রংপুর বিভাগে ৮০ নদীর তথ্য উঠে এসেছে। আর জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের খসড়া তথ্যে, দেশের ৯০৭টি নদীর মধ্যে রংপুর বিভাগে নদীর সংখ্যা ১২১টির উল্লেখ আছে। এই ১২১ নদীর বাইরে আরও শতাধিক নদী আছে ওই অঞ্চলে। রিভারাইন পিপলের পক্ষে সেই শতাধিক নদীর নাম কমিশনের কাছে দিয়েছে। এর মধ্যে ৬৩টি সচিত্র, ১৬টি সংক্ষিপ্ত পরিচিতিসহ আরও ২৬টির নাম দেয়া আছে। ইতোমধ্যে কমিশন সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের কাছে অনেকগুলো নদীর তথ্য চেয়ে চিঠিও দিয়েছে। চিঠিতে তারা আশঙ্কা ব্যক্ত করে বলেছে, ‘নদী না বাঁচলে দেশ বাঁচবে না, প্রকৃতি বাঁচবে না, পরিবেশের সুরক্ষা হবে না, এমনকি টেকসই উন্নয়নও সম্ভব নয়।’ নদীগুলো সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও নদী রক্ষায় তেমন কোনো কার্যকর পদক্ষেপ নেই। বাংলাদেশ আন্তর্জাতিকভাবে গৃহীত ‘রামসার কনভেনশন ১৯৭১’ এবং ‘রিও কনভেনশন ১৯৯২’ স্বাক্ষর করায় ভূমি ও জলজ পরিবেশ রক্ষায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এ কনভেনশন দুটির প্রথমটি জলজ পাখির আবাস সংরক্ষণ-সংক্রান্ত, যা নদী ও জলাভূমির প্রাকৃতিক পরিবেশকে রক্ষার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয়। তাছাড়া ভূমি ও জলের সব প্রজাতির উদ্ভিদ ও জীববৈচিত্র্য রক্ষায়ও সহায়ক। দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের টাঙ্গুয়ার হাওর ও সুন্দরবন এলাকা ‘রামসার সাইট’ হিসেবে সংরক্ষণ করা হচ্ছে। হাকালুকি হাওর এবং সুন্দরবনকে পরিবেশ অধিদপ্তর থেকে ‘পরিবেশগত স্পর্শকাতর এলাকা’ ঘোষণা করায় ওই দুই এলাকার নদী ও জলাভূমিগুলো সংরক্ষণের বেলায় সরকারি দায়বদ্ধতাও রয়েছে। কিন্তু এর বাইরে দেশের আরও অনেক জলাভূমিকে ‘রামসার সাইট’ হিসেবে এবং ‘পরিবেশগত স্পর্শকাতর এলাকা’ হিসাবে ঘোষণা ও সংরক্ষণের দাবি রাখে।
বর্তমানে সারা দেশেই আগ্রাসী থাবায় নদীগুলো বিপর্যস্ত। যেকোনো নদীর পাড়ে তাকালেই দখল-দূষণের চিত্র দৃশ্যমান হয়। এ অবস্থায় বহু নদনদীর অস্তিত্বই এখন হুমকির সম্মুখীন। বাস্তবে অনেক নদী ইতোমধ্যেই হারিয়ে গেছে। শুধু দখল ও দূষণের কারণে গত ৪ দশকে দেশের ৪০৫টি নদনদীর মধ্যে বিলুপ্তির পথে ১৭৫টি। বাকি ২৩০টিও রয়েছে ঝুঁকির মুখে। ২৪ হাজার কিলোমিটার নৌপথ কমে বর্তমানে দাঁড়িয়েছে ১৬ হাজার কিলোমিটারে। কৃষি, যোগাযোগ, পরিবেশ, জীববৈচিত্র্য, মানুষের জীবনযাত্রা সবকিছুর জন্যই এটা ভয়াবহ হুমকিস্বরূপ। নদী-জলাশয় রক্ষার প্রয়োজনীয়তা নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না।
সাম্প্রতিক এক গবেষণা বলছে, ঢাকা-চট্টগ্রামের বিভিন্ন নদীর পানিতে ১১ ধরনের ক্ষতিকর ধাতুর দেখা মিলেছে। গবেষণায় যেসব নদী, হ্রদ বা খালের দূষণের তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে, সেগুলোর মধ্যে আছে ব্রহ্মপুত্র, বুড়িগঙ্গা, তুরাগ, বালু, শীতলক্ষ্যা, ধলেশ্বরী, বংশী, ধলাই বিল, মেঘনা, সুরমা, কর্ণফুলী, হালদা, খিরু, করতোয়া, তিস্তা, রূপসা, পশুর, সাঙ্গু, কাপ্তাই লেক, মাতামুহুরী, নাফ, বাঁকখালি, কাসালং, চিংড়ি, ভৈরব, ময়ূর, রাজখালি খাল। আর এসব জলাধারের পানিতে গ্রহণযোগ্য মাত্রার চেয়ে বেশি পরিমাণে জিঙ্ক, কপার, আয়রন, লেড, ক্যাডমিয়াম, নিকেল, ম্যাঙ্গানিজ, আর্সেনিক, ক্রোমিয়াম, কার্বন মনোক্সাইড ও মার্কারির উপস্থিতি পাওয়া গেছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, গত ৪০ বছরে ঢাকা, চট্টগ্রামসহ আশপাশের অবিচ্ছিন্ন নদীগুলো চরম মাত্রার দূষণের শিকার হয়েছে। বরিশালের কীর্তনখোলা, বরগুনার খাকদোন নদীও মরে যাচ্ছে। নদীগুলো যে দখলই হচ্ছে তা নয়, শিল্পবর্জ্যের ভারী ধাতু পানিতে মিশে নদীর তলদেশে মারাত্মক দূষণ তৈরি করে। বিশেষ করে শুকনো মৌসুমে নদীর পানিতে ক্ষতিকর ধাতুর ঘনত্ব বেশি পাওয়া যায়। দেশে নদ-নদীর প্রকৃত সংখ্যা নিরূপণে ২০১৯ সালে তালিকা প্রণয়ন শুরু করে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন (এনআরসিসি)। প্রায় চার বছর কাজ শেষে গত ১০ আগস্ট সংস্থাটির ওয়েবসাইটে ৯০৭টি নদ-নদীর খসড়া তালিকা প্রকাশিত হয়। এ সংখ্যা নিয়ে এরই মধ্যে প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছেন নদী গবেষকরা। এমনকি সরকারি-বেসরকারি সংস্থার প্রকাশিত নদনদীর তথ্যের সঙ্গেও এনআরসিসির খসড়ার তথ্য মিলছে না।
এদিকে, দেশের ৪০৫টি নদনদী নিয়ে ২০১১ সালে একটি সমীক্ষা চালিয়েছিল পানি উন্নয়ন বোর্ড (পাউবো)। এ নিয়ে ছয় খণ্ডের বইও প্রকাশ করেছিল সংস্থাটি। ওই ৪০৫টি নদ-নদীর মধ্যে ১৩৯টিই এনআরসিসির খসড়া থেকে বাদ পড়েছে। ‘বাংলাদেশের নদ-নদী’ নামে ছয় খণ্ডে প্রকাশিত সিরিজের সঙ্গে এনআরসিসির খসড়া তালিকার নদনদীর তথ্যে ব্যাপক গরমিল রয়েছে বলে দাবি গবেষণা সংস্থা রিভার অ্যান্ড ডেল্টা রিসার্চ সেন্টারের। তাদের মতে, পাউবোর সমীক্ষার ১৩৯টি নদীর নাম এনআরসিসির তালিকা থেকে বাদ পড়েছে। এর মধ্যে সিলেট বিভাগের আমরি, ইসদার, উমিয়াম, কর্ণঝরা, কর্ণবালজা, কাঁচামাটিয়াসহ ২৭ নদীর নাম তালিকাভুক্ত করেনি এনআরসিসি। অনুরূপ রাজশাহী বিভাগের ১৬, রংপুরের ১০, ময়মনসিংহের ২৭, বরিশালের সাত, ঢাকার ৩০, চট্টগ্রামের ১২ ও খুলনা বিভাগের ১০টি নদী তালিকাভুক্ত করেনি এনআরসিসি।
গবেষকদের মতে, দেশের টেকসই উন্নয়ন, অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে সামাজিক ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় নদনদী রক্ষা করা জরুরি। গবেষণা অনুযায়ী গত ৫০ বছরে মানুষের কারণে ২০ শতাংশ চাষযোগ্য জমি, ৩০ শতাংশ বনভূমি এবং ১০ শতাংশ চারণভূমি হারিয়ে গেছে। শুধু আবাসন ও শিল্পায়নের কারণে প্রতি বছর ১ শতাংশ কৃষিজমি কমছে। একই সঙ্গে জীববৈত্র্যিও বিলুপ্ত হচ্ছে। ইতোমধ্যে অর্ধেকেরও বেশি নদী বিলুপ্ত হয়ে গেছে। বাকিগুলো দূষণে ও দখলে বিপর্যস্ত। টেকসই উন্নয়নের জন্য যে অর্থনীতি প্রয়োজন, সেই অর্থনীতি প্রতিষ্ঠা করতে হলে নদীকে তার হারানো গৌরব ও যৌবন ফিরিয়ে দিতে হবে, সচল রাখা জরুরি এর গতিপ্রবাহ। কারণ নদীর সঙ্গে আমাদের প্রকৃতি, অর্থনীতি, পর্যটন, যাতায়াত, পরিবেশের সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িত। টেকসই উন্নয়ন ও নদী রক্ষায় সম্মিলিতভাবে সামনে এগোতে হবে। নদীর ব্যবহার এখন বহুমাত্রিক। মানুষ বুঝে না বুঝে নদীকে ব্যবহার করছে। নদীর কাছেই গড়ে উঠেছে বড় বড় কল-কারখানা, নদীতে চলে এখন হাজার হাজার লঞ্চ-স্টিমার। নদীতে শত শত বাঁধ। নদী দখল, নদীদূষণসহ যখন যেভাবে প্রয়োজন, তখন সেভাবেই নদীকে ব্যবহার করা হচ্ছে। প্রসঙ্গত, দেশের প্রতি জেলায় নদী রক্ষা কমিটি রয়েছে জেলা প্রশাসকের নেতৃত্বে। বাস্তবে এই কমিটির তৎপরতা লক্ষণীয় হচ্ছে না নদী ভরাট, বালু উত্তোলন, দূষণ ও অবৈধ দখলের বিরুদ্ধে। অথচ স্থানীয় মানুষকে সঙ্গে নিয়ে সম্মিলিতভাবে এই কমিটি, নদী খননের প্রশাসনিক, আইনি কার্যাদি সম্পাদন ও নদী রক্ষায় নানা সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টিমূলক কাজ করলে নদী বাঁচবে, পরিবেশ বাঁচবে, মানুষ বাঁচবে, অর্থনীতির গতিপ্রবাহ সচল থাকবে।
জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের গঠন করা বিভাগীয় নদী, খাল, বিল, জলাশয়বিষয়ক কমিটি কার্যকর থাকলে নদী চিহ্নিত করা সহজ হবে। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের উচিত হবে নদীর সংখ্যা চূড়ান্ত না করা। কারণ যখন যে নদীর নাম-তথ্য পাওয়া যাবে, তখনই সেগুলো যুক্ত করার কাজ চলমান রাখা। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন সেই লজ্জা দূর করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। নদীর তালিকা শতভাগ বস্তুনিষ্ঠ হোক- এটাই আমাদের প্রত্যাশা।
দেশের নদী রক্ষা, জলাশয় সংরক্ষণ এবং নদী দখল রোধে উচ্চ আদালতের কঠোর নির্দেশনা থাকা সত্ত্বেও জেলা প্রশাসন তা আমলে নিচ্ছে না। আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন, নদী ও জলাশয়ে রয়েছে অনেক সম্পদ। কিন্তু মানুষ নিজের স্বার্থে প্রতিনিয়ত নদীকে ঝুঁকিতে ফেলছে, জীবন ধারণের স্থান ক্রমেই সংকুচিত হচ্ছে। নিজের স্বার্থে পরিবেশ রক্ষায় নিজ নিজ অবস্থান থেকে সম্মিলিতভাবে এগিয়ে আসতে হবে। কারণ সবাই সচেতন, আন্তরিক না হলে শুধু আইন প্রয়োগে খুব বেশি সফলতা আসবে না। পরিবেশকে বিবেচনায় না রেখে একটি সুন্দর পৃথিবীর অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। পরিবেশ আর উন্নয়নের মধ্যকার সম্পর্ক পরস্পরবিরোধী নয়। উন্নয়নের সঙ্গে পরিবেশের রয়েছে এক নিবিড় সম্পর্ক। পরিবেশকে রক্ষা করে দেশের উন্নয়ন না করলে তা টেকসই হবে না। এ জন্য শুধু সরকার বা বিভিন্ন সংস্থাকে কাজ করলে চলবে না, সমাজের প্রত্যেক মানুষকেই নিজ নিজ অবস্থান থেকে কাজ করতে হবে। পরিবেশ বাঁচিয়েই অর্থনৈতিক উন্নয়নকে সম্ভব করতে হবে। মানুষ যেমন হৃৎপিণ্ড না থাকলে বাঁচে না, তেমনি নদী না থাকলে দেশকে বাঁচানো সম্ভব নয়। দেশকে বাঁচাতে হলে, পরিবেশ-প্রকৃতি, জীববৈচিত্র্য, অর্থনীতি সচল রাখতে হলে টেকসই উন্নয়নে নদনদীকে সংরক্ষণ করা অপরিহার্য। এসব করা না গেলে ভবিষ্যতে আরও সংকটে পড়তে হবে। নিশ্চয় সেই সর্বনাশা সময়ের প্রত্যাশা করে না কেউ।
লেখক : সাংবাদিক
১৯৮/সি, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮
©দৈনিক বাংলা
