
বাংলাদেশে বড় কৃষকের সংখ্যা মোট কৃষকের শতকরা ২ ভাগ। মাঝারি কৃষক ১৮ ভাগ। ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকের সংখ্যা শতকরা ৮০ ভাগ। এই ৮০ ভাগ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকই কৃষির মূল চালিকা শক্তি। আন্তর্জাতিক সংস্থা ইন্টারন্যাশনাল ফুড পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউট (ইফপ্রি) বলছে, এনজিও, আত্মীয়স্বজন, বেসরকারি ব্যাংক ও দাদন ব্যবসায়ীসহ বিভিন্ন বেসরকারি উৎস থেকে কৃষক ৮১ শতাংশের বেশি ঋণ গ্রহণ করে। এসব ঋণের সুদ ১৯ থেকে ৬৩ শতাংশ। আর সরকারের কৃষি ব্যাংক ৯ শতাংশ সুদে যে কৃষিঋণ দেয়, তার পরিমাণ মাত্র ৬ শতাংশ। এ থেকেই বোঝা যায় সিংহভাগ কৃষক সরকারি বিশেষায়িত ও বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো থেকে ফসল চাষের জন্য প্রয়োজনীয় কৃষিঋণ পান না।
আবার এটা ঠিক যে, অনেকে কৃষক না হয়েও কৃষিঋণ গ্রহণ করছেন। সেই ঋণ তারা ব্যবহার করছেন অন্য কোনো অলাভজনক খাতে। এরাই পরে যখন খেলাপিতে পরিণত হন তখন দায় পড়ে কৃষকের ওপর।
দেশের চলমান পরিস্থিতি বিবেচনা করে খাদ্য উৎপাদন বাড়াতে সরকার বেশ কিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- কৃষকের দরজায় ঋণ নিয়ে যাবে ব্যাংক; ব্যাংকের শাখায় চালু করতে হবে কৃষিঋণ বুথ এবং এনজিওর মাধ্যমে ঋণ বিতরণ কমাতে হবে। সরকারের এই সিদ্ধান্তকে আমরা স্বাগত জানাই। চিনিকলে কৃষকদের মধ্যে উপকরণ ও নগদ টাকা হিসাবে যে ঋণ বিতরণ করা হয়, তা আখ উন্নয়ন কর্মীরা (সিডিএ) কৃষকের বাড়ি বাড়ি গিয়ে পৌঁছে দেন। সিডিএরা শুধু ঋণই দেন না। কৃষকের আখ চাষের আধুনিক প্রযুক্তি হাতে-কলমে শিখিয়ে দেন। আখ বিক্রির জন্য প্রয়োজনীয় অনুমতি পত্র (পুর্জি) প্রদানের ক্ষেত্রেও মুখ্য ভূমিকা পালন করেন। ফলে প্রতিটি চিনিকলেই এখন শতভাগ কৃষিঋণ আদায় হয়।
বেশির ভাগ বেসরকারি ব্যাংক সরাসরি কৃষিঋণ বিতরণ করে না। বরং ঋণ বিতরণের জন্য বেসরকারি সংস্থাকে নিয়োগ করে। এনজিওর মাধ্যমে বিতরণ করা ঋণের সুদ ২৪ শতাংশ পর্যন্ত হয়। বর্তমানে বেসরকারি ব্যাংকগুলো তাদের কৃষিঋণের ৭০ শতাংশ বিতরণ করে এনজিওর মাধ্যমে। অন্যদিকে সরকারি ব্যাংকগুলো বিতরণ করছে ৮ শতাংশ সুদে।
সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে বলা হয়েছে, যত দ্রুত সম্ভব এনজিওগুলোর ঋণ বিতরণের হার ৩০ শতাংশে নামিয়ে আনতে হবে। কারণ যখনই এনজিওগুলো ঋণ বিতরণ করে, তখনই সুদের হার বেড়ে যায়। এনজিওগুলোর সুদের হার কমাতে বাংলাদেশ ব্যাংককে ব্যবস্থা নিতে বলা হয় বৈঠকে। দেশের সব ব্যাংক শাখায় একটি কৃষিঋণ বুথ খুলতে বলা হয়, যাতে কৃষক বুঝতে পারেন কোথায় যেতে হবে ঋণের জন্য? সভায় অংশ নেয়া ব্যাংকগুলোকে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে কৃষিঋণ মেলার আয়োজন করতে বলা হয়েছে, যেখানে ব্যাংকার ও কৃষক অংশ নেবেন। কারণ কৃষকরা মাঠে ব্যস্ত থাকেন। ব্যাংকে যাওয়ার সময় তাদের নেই। তাই মেলায় অংশ নেয়া ব্যাংকগুলো কৃষকদের মাঝে তাৎক্ষণিক আবেদনপত্র বিতরণ ও গ্রহণ এবং ঋণ অনুমোদন করবে।
কৃষিঋণ নীতিমালা অনুযায়ী ব্যাংকগুলোকে মোট ঋণের ২.১০ শতাংশ কৃষি খাতে বিতরণ করতে হবে। এর মধ্যে ৬০ শতাংশ ফসল, ১০ শতাংশ মাছ চাষ, ১০ শতাংশ পশুসম্পদ এবং ২০ শতাংশ অন্যান্য কৃষি উপখাতে বিতরণ করতে হবে। বাংলাদেশ ব্যাংক চলতি অর্থবছরে ৩০ হাজার ৯১১ কোটি টাকা কৃষিঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে, যা গত অর্থবছরে ছিল ২৮ হাজার ৩৯১ কোটি টাকা। তবে ব্যাংকগুলো বিতরণ করেছিল ২৮ হাজার ৮৩৪ কোটি টাকা।
কিছুদিন আগে ঋণের দায়ে কৃষকদের জেলে পুরে দেয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে কৃষক ও কৃষি সংশ্লিষ্টদের মনে কৃষিঋণ নিয়ে এক ধরনের আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে। প্রশ্ন জেগেছে- যে কৃষক করোনার ভয়াবহ সময়ে মৃত্যুর ঝুঁকি নিয়ে ফসল ফলিয়ে আমাদের জীবন বাঁচিয়েছেন, তারা সামান্য ঋণের দায়ে জেলে যাবেন কেন? কেন তাদের কোমরে রশি পরানো হবে? আর যারা তথাকথিত ব্যবসার নামে ব্যাংক থেকে কোটি কোটি টাকা ঋণ গ্রহণ করে খেলাপি হয়ে বুক ফুলিয়ে বাংলার সবুজ প্রান্তরে ঘুরে বেড়ায়, তাদের নামে কেন মামলা হবে না- বিষয়টি মোটেও বোধগম্য নয়।
তবে এটাও পরিষ্কার যে, ব্যাংক অনেক ক্ষেত্রে একজন লোক আদৌ কৃষক কি না বা কৃষিকাজ করার ক্ষেত্রে তার কোনো প্রশিক্ষণ আছে কি না, তা যাচাই না করেই ঋণ বিতরণ করে থাকে। তাই আমাদের কথা, কৃষি, মৎস্য ও পশুপালন খাতে ঋণের সঙ্গে প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। বিনিয়োগকারীকে দিতে হবে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ। সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে বিনিয়োগকারীর থাকতে হবে পূর্ব অভিজ্ঞতা। এ ছাড়া উৎপাদিত পণ্যের সুষ্ঠু বাজারজাতকরণের ব্যবস্থাও থাকতে হবে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে কৃষককে বাঁচানোর জন্য থাকতে হবে কৃষি বিমার ব্যবস্থা। এসব ছাড়া কৃষিঋণ বিতরণ একবারেই অর্থহীন।
লেখক: সাবেক মহাব্যবস্থাপক (কৃষি), বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্যশিল্প করপোরেশন

বিশ্বের অন্যতম পরিচিত মেগাসিটি আমাদের রাজধানী ঢাকা। এক সময় সবুজ গাছপালা আর খোলামেলা পরিবেশের জন্য নাম ছিল এই ঢাকার। তবে আধুনিক হয়ে উঠতে গিয়ে শহরটি হারিয়েছে সেই প্রাকৃতিক জৌলুস।
আজ ঢাকার যেদিকেই তাকানো হবে, দেখা যাবে সুউচ্চ সব ভবন, কতশত কারখানা; সবমিলিয়ে একদম আধুনিকতায় মোড়ানো ব্যস্ততম এক মহানগরী। তবে বিনিময়ে হারিয়েছে সেই সবুজ পরিবেশ, বাসযোগ্যতা ও বায়ুমান নিয়ে তৈরি হয়েছে গুরুতর উদ্বেগ।
একদিকে গাছপালার প্রাকৃতিক বাতাসের পরিবর্তে ঢাকার ঘরবাড়ি ও অফিসগুলোতে জায়গা করে নিয়েছে শীতাতপনিয়ন্ত্রণ যন্ত্র (এসি)। অন্যদিকে, আশঙ্কাজনকহারে কমে আসছে সবুজ বনভূমির পরিমাণ।
মহানগরী ঢাকা একসময় পরিচিত ছিল ‘বাগানের শহর’ নামে। তবে ১৯৮১ সাল থেকে ব্যাপক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে গেছে শহরটি। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নগর সম্প্রসারণ হয়েছে, অবকাঠামোগত উন্নয়ন হয়েছে। কিন্তু পরিবেশ ব্যবস্থাপনায় দুর্বলতার কারণে রাজধানীর সবুজের পরিমাণ, বিশেষত গাছপালা আশঙ্কাজনকভাবে বিলীন হয়েছে।
অপরিকল্পিত নগরায়নের ফলে হাজার হাজার গাছ কাটা পড়েছে। ফলে বর্তমান সময়ে এসে অতিরিক্ত গরম, বায়ুদূষণ ও জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকিতে পড়েছে ঢাকা।
১৯৮১ সালের নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের (ইউডিডি) এক জরিপ অনুযায়ী, ঢাকার প্রায় ১৯ শতাংশ ভূমি সবুজে আচ্ছাদিত ছিল।
আশির দশকের উপগ্রহ চিত্রে দেখা যায়, রমনা পার্ক, সোহরাওয়ার্দী উদ্যান, এমনকি ধানমণ্ডি, মিরপুর ও উত্তরার মতো আবাসিক এলাকাগুলোর সড়কের পাশে ও বাড়ির আঙিনায় প্রচুর গাছ ছিল।
সংখ্যায় বলতে গেলে সে সময় ঢাকার কেন্দ্রীয় এলাকায় (তৎকালীন ঢাকা সিটি করপোরেশন অঞ্চলে) আনুমানিক ১ লাখ ৭০ হাজার থেকে ২ লাখ পূর্ণবয়স্ক গাছ ছিল।
ঢাকায় গাছ কাটার হার আধুনিকায়নের গতিকে ছাড়িয়ে গেছে বলে মন্তব্য করেন বিশেষজ্ঞরা। নতুন ভবন, রাস্তা ও বাণিজ্যিক স্থাপনা নির্মাণের জন্য পার্ক ও খোলামেলা জায়গা নিশ্চিহ্ন হচ্ছে, ফলে নগর উন্নয়ন ও পরিবেশগত স্থায়িত্বের ভারসাম্য হুমকির মুখে পড়েছে বলে সতর্ক করেছেন তারা।
পরিবেশ বিজ্ঞানী ড. রেহানা করিম বলেন, ‘ঢাকায় অবকাঠামো বাড়ছে, কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে তা হচ্ছে পরিবেশের বিনিময়ে। উচ্চ ভবন ও বাণিজ্যিক এলাকার জন্য গাছ কাটা হচ্ছে। ইতোমধ্যেই তাপমাত্রা বৃদ্ধি ও বায়ুদূষণে ভূমিকা রাখছে শুরু করেছে এই সবুজের অভাব।’
শুধু বিশেষজ্ঞরা নন, ঢাকার গাছপালা আশঙ্কাজনভাবে কমার কারণে শহরটির বসবাসকারীরাও উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।
মিরপুরের বাসিন্দা তারেক রহমান বলেন, ‘এখন সব জায়গায় এসি লাগানো হচ্ছে, কিন্তু প্রাকৃতিক ছায়ার যে আরাম ও স্বাস্থ্য উপকারিতা তা এসিতে নেই। যেসব উপাদান এই শহরটিকে বাসযোগ্য করে তুলেছিল, আমরা সেগুলোই হারিয়ে ফেলছি।’
অতিরিক্ত উত্তপ্ত শহর ঢাকা

১৯৮১ সালের হিসাব তো আগেই দেখানো হয়েছে, এবার আসা যাক বর্তমান সময়ে। ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের পরিবেশ বিভাগ জানিয়েছে, তাদের হিসাবে ২০২৫ সালে ঢাকা শহরের রাস্তার পাশে থাকা পূর্ণবয়স্ক গাছের সংখ্যা ৫০ হাজারেরও কম। আশির দশকের ১৯ শতাংশ বনভূমি এসে এখন ঠেকেছে ৬ শতাংশেরও নিচে।
বর্তমান হিসাব অনুযায়ী, প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য সবুজ জায়গা মাত্র ০ দশমিক ৪২ বর্গমিটার, যেখানে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সুপারিশ অনুযায়ী যেটি হওয়া উচিত ৯ বর্গমিটার।
এতে শহরের তাপমাত্রায় এক লক্ষণীয় পরিবর্তন দেখা গেছে। ১৯৮১ সালের পর থেকে গ্রীষ্মের গড় তাপমাত্রা ২.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে। এ ছাড়া, ধুলাবালি কণার (পিএম ২.৫) মাত্রায় বিশ্বব্যাপী সবচেয়ে দূষিত পাঁচটি শহরের তালিকায় নিয়মিত থাকতে দেখা যায় ঢাকাকে। এর অন্যতম কারণ হচ্ছে গাছের বিশুদ্ধ বাতাসের অভাব।
অনেকদির ধরেই সরকারের কাছে নগর পরিকল্পনায় বাধ্যতামূলক সবুজ এলাকা ও বৃক্ষরোপণের কড়া নীতি গ্রহণের দাবি জানিয়ে আসছে পরিবেশবাদী সংগঠনগুলো। তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ না নিলে ঢাকা তীব্র তাপপ্রবাহ, বায়ুদূষণ বৃ্দ্ধি ও জনস্বাস্থ্যের অবনতির মতো মারাত্মক পরিবেশগত বিপর্যয়ের মুখে পড়বে বলেও সতর্ক করেছে তারা।
দশকের পর দশক ধরে বন উজাড়ে

আধুনিকতার পথে অগ্রগতির সঙ্গে টেকসই পরিবেশ বজায় রাখতে গিয়ে ঢাকা আজ একটি প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে—প্রাকৃতিক পরিবেশের বলি না দিয়ে আধুনিক হতে পারবে ঢাকা?
এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হলে ঢাকার ক্রমবর্ধমাণ জনসংখ্যা সম্পর্কে ধারণা থাকা জরুরি। সরকারি হিসাব বলছে, ১৯৮১ সালে যেখানে ঢাকার জনসংখ্যা ছিল ৩৪ লাখ, ২০২৫ সালের মধ্যে তা বেড়ে ২ কোটি ৩০ লাখ ছাড়িয়ে গেছে।
এতে ১৯৮১-১৯৯১ পর্যন্ত এই দশ বছরে দ্রুত নগরায়নের প্রাথমিক লক্ষণস্বরূপ সড়ক সম্প্রসারণ ও প্লট উন্নয়নের কারণে ১০ থেকে ১৫ হাজার গাছ কাটা পড়েছে। পরের ১০ বছরে অর্থনৈতিক মুক্ত বাজার নীতির পর নির্মাণ প্রবৃদ্ধির সময় ২৫ থেকে ৩০ শতাংশ গাছ নিধন করা হয়েছে।
এর পরের দশকে মহাখালী ও খিলগাঁও উড়ালসড়কসহ বড় রিয়েল এস্টেট প্রকল্পের কারণে কাটা হয়েছে আরও অন্তত ৪০ হাজার গাছ।
তবে সবচেয়ে বেশি গাছ কাটা হয়েছে ২০১১ থেকে ২০২১ সালের মধ্যে। মেট্রোরেল ও এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণে বিভিন্ন এলাকায় বিশেষত উত্তরা, ফার্মগেট ও শাহবাগ এলাকায় প্রায় ৫০ হাজার গাছ কাটা হয়েছে।
এরপর ২০২১ থেকে ২০২৫ সাল পর্যন্ত এই চার বছরে ৫ থেকে ৮ হাজার গাছ কমেছে ঢাকার। বনায়ন নীতি থাকলেও নির্মাণ চলমান থাকায় গাছের পরিমাণ কমেই চলেছে।
এসিতে কেউ পাচ্ছেন ঠান্ডা হাওয়া, কেউ পুড়ছেন গরমে

একসময় কেবল ধনী মানুষের বিলাসের সামগ্রী হিসেবে বিবেচিত হত এসি। কিন্তু এখন ঢাকার তীব্র গরমে এটি একপ্রকার প্রয়োজনীয়তায় পরিণত হয়েছে।
তবে বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এই যে এসির ব্যবহার বাড়ছে, এতে যে শুধু তাপমাত্রাই বাড়ছে না, এটি বিদ্যুৎতের চাপ, বায়ুদূষণ ও সামাজিক বৈষম্যকেও বাড়িয়ে দিচ্ছে।
বাংলাদেশ টেকসই জ্বালানি কর্তৃপক্ষের তথ্যমতে, ঢাকায় এসির সংখ্যা গত ১৫ বছরে চারগুণ বেড়েছে। ২০১০ সালের দেড় লাখ ইউনিট থেকে এটি ২০২৪ সালে সাড়ে ৭ লাখে পৌঁছেছে।
আরও পরিষ্কারভাবে বলা হলে, রাজধানীর প্রায় তিনটি মধ্যবিত্ত পরিবারের মধ্যে একটি এখন এসির মালিক। তাপমাত্রা বাড়তে থাকায় এই সংখ্যা আরও বাড়বে বলে ধারণা করছেন সংশ্লিষ্টরা।
বিশেষজ্ঞরা জানান, ঢাকায় গ্রীষ্মকালে আবাসিক বিদ্যুতের প্রায় ৪০ শতাংশ এসি ব্যবহারেই ব্যয় হয়। ফলে জাতীয় গ্রিডের ওপর চাপ বাড়ে এবং জীবাশ্ম জ্বালানির ওপর নির্ভরতা বৃদ্ধি পায়।
নগর অধিকারকর্মী ফারুক হোসেন বলেন, ‘ধনীরা এসি চালিয়ে স্বস্তিতে থাকেন, অথচ দরিদ্ররা লোডশেডিং আর অসহনীয় গরমে কষ্ট করে।’ বিশেষ করে বস্তিবাসী ও নিম্নআয়ের শ্রমজীবীরা এতে সবচেয়ে ঝুঁকিতে রয়েছেন বলে জানান তিনি।
বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্যমতে, পুরনো মডেলের এসিগুলো হাইড্রোফ্লোরোকার্বন গ্যাস ছাড়ে, যা অত্যন্ত শক্তিশালী গ্রিনহাউজ গ্যাস। যথাযথ নিয়ন্ত্রণ না থাকলে ঢাকার এই শীতলকরণ প্রবণতা জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক প্রতিশ্রুতিগুলো (কিগালি সংশোধনী ও প্যারিস চুক্তি) ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে বলেও সতর্ক করেছেন তারা।
পরিবেশবান্ধব স্থাপত্যবিদ শিরিন কবির বলেন, ‘ঢাকা যদি তার গাছ, পার্ক ও প্রাকৃতিক বাতাস চলাচলের পথ সংরক্ষণ করত, তাহলে এত বেশি কৃত্রিম শীতলকরণের প্রয়োজন হতো না। আমরা এমন শহর তৈরি করছি, যেটিকে বাসযোগ্য রাখতে যন্ত্রের ওপর নির্ভর করতে হচ্ছে।’
বেঁচে থাকার জন্য বনায়ন

ঢাকার পরিবেশকে রক্ষা করতে হলে বনায়নের কোনো বিকল্প নেই বলে মন্তব্য করেছেন বিশেষজ্ঞরা।
মিশন গ্রিন বাংলাদেশের নির্বাহী পরিচালক আহসান রনি ইউএনবিকে বলেন, ‘তীব্র গরম, বায়ুদূষণ ও দ্রুত সবুজ হারানো প্রতিরোধে ঢাকার জন্য পুনরায় বনায়ন অপরিহার্য। ঢাকায় বনায়ন এখন শুধু পরিবেশগত চাহিদা নয়, এটি টিকে থাকার কৌশল। শহরটি দ্রুত তার সবুজ আচ্ছাদন হারাচ্ছে, আর সঙ্গে হারাচ্ছে পরিষ্কার বাতাস, ছায়া ও জীববৈচিত্র্য।’
এ কারণে তিনি মিশন গ্রিন বাংলাদেশের মাধ্যমে গ্রিন ভলান্টিয়ার প্রোগ্রাম শুরু করেছেন বলে জানান। সেখানে তরুণদের সরাসরি শহরকে সবুজ করায় যুক্ত করার আশাও প্রকাশ করেন তিনি।
এই তরুণ পরিবেশকর্মী আরও জানান, তারা গাছ লাগানোর অনুষ্ঠান আয়োজন করেন, সচেতনতা কার্যক্রম চালান এবং ছোট শহুরে বনও তৈরি করে থাকেন। যেমন: ৫৫টি কদমগাছ নিয়ে গড়া ‘কদমতলা ইনিশিয়েটিভ’।
তিনি বলেন, ‘আমার লক্ষ্য পরিবেশগত কাজকে সহজলভ্য, হাতে-কলমে ও সমাজভিত্তিক করে তোলা। আমি বিশ্বাস করি, আজ আমরা যে গাছ লাগাচ্ছি, তা আগামী দিনের জন্য একটি সুস্থ ও বাসযোগ্য ঢাকার প্রতিশ্রুতি।’
সরকার ও বিভিন্ন এনজিওর সৌজন্যেও একাধিক বৃক্ষরোপণ অভিযান চালানো হয়েছে। ২০২০ সাল থেকে এক লাখের বেশি চারা রোপণ করা হয়েছে এই শহরে। তবে রক্ষণাবেক্ষণের অভাব, ভাঙচুর, অবহেলা বা অনুপযুক্ত (বিদেশি বা দুর্বল মূলবিশিষ্ট) প্রজাতির গাছের চারা ব্যবহারের কারণে এগুলোর অন্তত ৩০ শতাংশ প্রথম বছরেই মারা গেছে।

ভূমিকা: সমুদ্র বলছে – আমরা কি শুনছি?
ভারতের মহাসাগরের নীল জলরাশির নিচে চলছে এমন এক সংকট যা কোনো একটি দেশের একার নয়—এটি বৈশ্বিক। প্রবাল প্রাচীরগুলো বিবর্ণ হয়ে যাচ্ছে, দুর্লভ সামুদ্রিক প্রজাতিগুলো বিলুপ্তির পথে, কিন্তু এই সমুদ্রের আর্তনাদ ঢাকা পড়ে যাচ্ছে মানুষের শোরগোলে। এমন এক সংকটময় সময়েই আমি সুযোগ পেয়েছি বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করার, তাও সম্পূর্ণভাবে অর্থায়িত প্রতিনিধি হিসেবে, মালদ্বীপের মাফুশি দ্বীপে অনুষ্ঠিত ইউনিভার্সাল ইয়ুথ লিডারশিপ সামিট (UYLS) ২০২৫-এ।
এই সামিটের আয়োজন করে ইউনিভার্সাল ইয়ুথ মুভমেন্ট (UYM), যেখানে বিশ্বের নানা প্রান্ত থেকে তরুণ নেতৃত্ব একত্রিত হয়েছিল—উদ্দেশ্য ছিল আমাদের গ্রহের প্রধান সংকটগুলো নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে কার্যকর সমাধান বের করা। আমাদের দলের প্রেজেন্টেশন ছিল:
‘আমাদের সাগর বাঁচান: বিপন্ন সামুদ্রিক প্রাণী’।
এটি কেবল একটি সম্মেলন ছিল না—এটি ছিল এক জাগরণ, একটি বার্তা, যেখানে পরিবেশ রক্ষায় তরুণদের নেতৃত্বকে তুলে ধরা হয়েছে। আমার জন্য, এটি ছিল জীবনের অন্যতম গভীর ও গুরুত্বপূর্ণ অভিজ্ঞতা।
সংকট: বিপন্নতার মুখে সাগরের অভিভাবক–সামুদ্রিক কচ্ছপ: সাগরের অতল গহ্বরে, প্রাগৈতিহাসিক এক প্রাণী—সামুদ্রিক কচ্ছপ, যেটি গত দশ লক্ষ বছর ধরে টিকে রয়েছে, আজ মানুষের লোভ ও দায়িত্বহীনতার কারণে বিলুপ্তির পথে। আমাদের কল্পিত দেশের প্রকৃত অবস্থা বর্তমান পৃথিবীর বাস্তব প্রতিচ্ছবি। আমরা দেখেছি কীভাবে পাচার ও বেআইনি শিকারের ফলে কচ্ছপের সংখ্যা দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে, নির্মাণ কাজ ও পর্যটনের চাপে ধ্বংস হচ্ছে কচ্ছপের ডিম পাড়ার উপকূল ,প্লাস্টিক দূষণ ও সামুদ্রিক বর্জ্যতে মৃত্যু ঘটছে প্রজাতিগুলোর, বাণিজ্যিক জাল ব্যবহারে কচ্ছপেরা হয়ে যাচ্ছে অনিচ্ছাকৃত শিকার। আমরা বুঝে গিয়েছিলাম—এটি কেবল একটি দলীয় অ্যাসাইনমেন্ট নয়, বরং বাস্তব জীবনের সংকট যার সমাধান আজ জরুরি।
আমাদের ভূমিকা: একটি জাতিসংঘ ভিত্তিক প্রেস কনফারেন্সের রূপে উপস্থাপনা: আমাদের দল একটি জাতিসংঘভিত্তিক সংবাদ সম্মেলনের আদলে উপস্থাপন করেছিল। আমি অভিনয় করেছিলাম সরকারের পরিবেশ সংক্রান্ত আইন উপদেষ্টা হিসেবে। আমাদের দলে ছিল: সামুদ্রিক জীববিজ্ঞানী, পরিবেশ NGO-র প্রতিনিধি, মিডিয়া সাংবাদিক, পরিবেশমন্ত্রী, স্থানীয় সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি । আমরা কঠিন প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলাম এবং তুলে ধরেছিলাম বহুমাত্রিক সমাধান।
স্বল্পমেয়াদি সমাধান: প্লাস্টিক বর্জ্য নিষিদ্ধকরণ, সামুদ্রিক সংরক্ষিত এলাকা চিহ্নিতকরণ, উপকূলীয় উন্নয়ন স্থগিত রাখা ডিম পাড়ার মৌসুমে, কচ্ছপ উদ্ধার হেল্পলাইন চালু করা, জেলেদের সচেতনতা বাড়ানো ও বিকল্প টেকনোলজি দেওয়া।
দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা: সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ আইন প্রণয়ন, পাঠ্যসূচিতে সমুদ্র শিক্ষার অন্তর্ভুক্তি, স্যাটেলাইটের মাধ্যমে কচ্ছপ পর্যবেক্ষণ, ইকো-ট্যুরিজম প্রচার, আন্তঃদেশীয় চুক্তি ও সমুদ্র সংরক্ষণ সহযোগিতা।
আমার আইনজীবী পরিচয় আমাকে সাহায্য করেছিল বাস্তব সম্মত ও কার্যকর নীতিমালা উপস্থাপন করতে। আমরা বুঝাতে পেরেছিলাম—পরিবেশ সংরক্ষণ কোনো স্বপ্ন নয়, এটি বাস্তবায়নযোগ্য একটি নৈতিক দায়িত্ব।
মালদ্বীপের শিক্ষা: স্বর্গপৃথিবীও ঝুঁকিতে: সামিটের ভেন্যু মালদ্বীপ ছিল এক জীবন্ত শিক্ষা। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধিতে দেশটি ইতোমধ্যে ঝুঁকির মুখে পড়েছে। প্রবাল প্রাচীরের ধ্বংস, সমুদ্রদূষণ, এবং অনিয়ন্ত্রিত পর্যটন—সব মিলিয়ে এখানকার সামুদ্রিক প্রাণীরা আজ বিপন্ন।সাগরপাড়ে হাঁটতে হাঁটতে মনে হয়েছিল—এই দ্বীপ কি একদিন কেবল মানচিত্রে বেঁচে থাকবে?
বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট: আমাদের সাগরের গল্পও কি আলাদা?
বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চল ও বঙ্গোপসাগরও একই চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। আমরা যেমন ভোগ করছি প্লাস্টিক দূষণ, তেল নিঃসরণ, বর্জ্য ব্যবস্থার অভাব, তেমনি ভোগ করছি অজ্ঞতা ও দায়িত্বহীনতার খেসারত। সুন্দরবনের পার্শ্ববর্তী মানুষরাও জানে না তারা কী হারাতে বসেছে। আমার লক্ষ্য এখন এই শিখন কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকায় সচেতনতামূলক প্রকল্প শুরু করা, যেখানে স্থানীয় স্কুল ও মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের নিয়ে সমুদ্র সংরক্ষণ নিয়ে কাজ করব।
ভবিষ্যতের রূপরেখা: আইন, শিক্ষা এবং সচেতনতার মিলনস্থল
একজন আইনজীবী হিসেবে আমি বিশ্বাস করি যে শক্তিশালী আইন এবং স্থানীয় জনসম্পৃক্ততা মিলেই হতে পারে স্থায়ী সমাধানের চাবিকাঠি। আমি একটি প্রকল্প চালু করতে চাই—‘কমিউনিটি ওশান স্কুল’, যেখানে মোবাইল ক্লাসের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শেখানো হবে: সামুদ্রিক প্রাণী রক্ষা, প্লাস্টিক ব্যবস্থাপনা, মাছ ধরার নিরাপদ পদ্ধতি, পরিবেশ-সম্পর্কিত আইনি অধিকার । এই স্কুল হবে সচেতনতা তৈরির কেন্দ্র, আইনগত সহায়তার সেতুবন্ধন, এবং সমাজের একটি জাগরণ কেন্দ্র।
সমাপ্তি: আমরা না বাঁচালে, কে বাঁচাবে?
আজকের তরুণদের প্রতি আমার আহ্বান—আমাদের কণ্ঠই হোক প্রাকৃতিক সম্পদের রক্ষাকবচ। সমুদ্রের গভীরতা যতই গভীর হোক না কেন, আমাদের দায়বদ্ধতা যেন হয় ততটাই অটল। আমরা যেন সেই প্রজন্ম না হই যারা কেবল বিবৃতি দিয়েছে—কিন্তু কিছু করেনি। আমরা যেন হই সেই প্রজন্ম যারা গর্জে উঠেছে, দাঁড়িয়েছে, এবং প্রভাব ফেলেছে।
লেখক: যুব নেতৃত্ব প্রশিক্ষক ও অ্যাডভোকেট

ঢাকার বায়ুদূষণ, কার্বন নিঃসরণ ও স্বাস্থ্যঝুঁকি: টেকসই উন্নয়নের পথে অদৃশ্য বাধা
ঢাকার একটি ব্যস্ত সকাল। হাজারো মানুষ জীবিকার তাগিদে ছুটছে, বাস-রিকশা-প্রাইভেটকার-ট্রাক- সব চলছে নিজের ছন্দে। কিন্তু সেই ছন্দের মাঝেই বাতাসে মিশছে এক ধরনের শ্বাসরুদ্ধকর ভার। রাস্তায় দাঁড়ানো মাত্র চোখে জ্বালা, গলায় খুসখুসে কাশি, আর মনে হয় যেন ফুসফুসে ধোঁয়া ঢুকে যাচ্ছে। আমরা যত উন্নয়নের গল্প শুনি, ঢাকার বাতাস ঠিক ততটাই নীরবে বিষাক্ত হয়ে উঠছে। এই শহরের রাস্তার কালো ধোঁয়া, ধুলাবালি, অতিরিক্ত কার্বন ইমিশন এখন কেবল পরিবেশগত ইস্যু নয়—এটি স্বাস্থ্য, অর্থনীতি ও টেকসই উন্নয়নের অন্যতম বড় বাধা।
Bangladesh Air Quality Index(AQI) ২০২৪-এর তথ্য বলছে, ঢাকার বাতাসে PM2.5 এর গড় মাত্রা ৭৮ মাইক্রোগ্রাম/ঘনমিটার—যা WHO গাইডলাইনের চেয়ে ১৫ গুণ বেশি। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) ৫ µg/m³ কে নিরাপদ বললেও ঢাকার বাস্তবতা এর বহু গুণ বেশি। যানবাহনের ইঞ্জিন থেকে নির্গত কালো ধোঁয়ায় থাকে কার্বন মনোক্সাইড, নাইট্রোজেন অক্সাইড ও সালফার ডাই-অক্সাইডের মতো গ্যাস। এগুলো শুধু বায়ু দূষণই নয়, বরং মানবদেহে দীর্ঘমেয়াদি ক্ষতি ডেকে আনে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, দূষিত বাতাস এখন সারা বিশ্বের মানুষের জন্য চতুর্থ প্রধান মৃত্যুঝুঁকির কারণ। আর ঢাকার মতো ঘনবসতিপূর্ণ শহরে এ ঝুঁকি বহুগুণে বেড়ে যায়। শিশুদের মধ্যে হাঁপানি, বয়স্কদের হৃদরোগ এবং কর্মজীবী মানুষের প্রোডাক্টিভিটি হ্রাস—সবকিছু এই দূষণের ফল।
Air Quality Life Index অনুযায়ী, শুধু বায়ুদূষণের কারণে বাংলাদেশে গড় আয়ু ৬.৮ বছর পর্যন্ত কমে যেতে পারে। বিশ্বব্যাংকের ২০২২ সালের রিপোর্ট বলছে, বায়ুদূষণ ও স্বাস্থ্য সমস্যার কারণে বাংলাদেশের GDP প্রতিবছর ৩.৯–৪.৪% পর্যন্ত ক্ষতির সম্মুখীন হয়।এই তথ্যগুলো কেবল সংখ্যাই নয়—এর মানে হলো, দূষণের কারণে আমাদের অর্থনীতি দুর্বল হচ্ছে, মানুষের আয়ু কমে যাচ্ছে, চিকিৎসা ব্যয় বাড়ছে, এবং স্বাস্থ্যসেবার ওপর চাপ সৃষ্টি হচ্ছে। বায়ুদূষণের মূল উৎস হলো: পুরনো ডিজেলচালিত যানবাহন, ট্রাফিক জ্যাম, নির্মাণসাইটের খোলা ধুলাবালি এবং দুর্বল নগর ব্যবস্থাপনা। বাংলাদেশ ২০৩০ সালের মধ্যে গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন ১৫% হ্রাসের প্রতিশ্রুতি দিলেও, রাজধানী প্রতিদিন বিপুল পরিমাণ কার্বন ইমিশন করছে।
আমাদের সমাধান অবশ্যই সম্ভব। প্রথমত, পরিবহন খাতে সংস্কার আনতে হবে। পুরনো ডিজেলচালিত গাড়ি নিষিদ্ধ করতে হবে। সিএনজি ও ইলেকট্রিক যানবাহনের ব্যবহার বাড়াতে হবে এবং গণপরিবহনকে জনবান্ধব করতে হবে। দ্বিতীয়ত, নির্মাণ কার্যক্রমে পরিবেশগত নিয়ম মানা নিশ্চিত করতে হবে। খোলা বালি ও সিমেন্ট ঢেকে রাখা, ধুলাবালি নিয়ন্ত্রণে পানি ছিটানো, এবং নির্মাণসাইট বেষ্টনীর ব্যবস্থা থাকা জরুরি। তৃতীয়ত, নাগরিকদের সচেতন হতে হবে। ব্যক্তিগত পর্যায়ে গাড়ি ব্যবহারে সংযম, মাস্ক পরা এবং গাছ লাগানোর মতো ছোট ছোট অভ্যাসগুলো পরিবেশ রক্ষায় বড় ভূমিকা রাখে। সরকারের পক্ষ থেকে Air Pollution Control Rules 2022 কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন এবং ফিটনেস পরীক্ষার কঠোরতা নিশ্চিত করাও সময়ের দাবি।
এই শহরের বাতাস আমাদের সন্তানদের ফুসফুসে যাচ্ছে—এই বাস্তবতা মেনে নিয়ে আমাদের কাজ শুরু করতে হবে। উন্নয়ন তখনই অর্থবহ হবে, যখন সেই উন্নয়নের ভেতরেই থাকবে মানুষ, স্বাস্থ্য, এবং পরিবেশের ভারসাম্য। আর শুদ্ধ বাতাসের চেয়ে বড় কোনো মৌলিক অধিকার হতে পারে না। ঢাকার রাস্তায় গাড়ির কালো ধোঁয়া, ধুলাবালি আর কার্বন ইমিশনের ছায়া থেকে শহরকে বাঁচাতে হলে সিদ্ধান্ত নিতে হবে এখনই । ঢাকা বাঁচলে আমরা বাঁচব। বাতাস বিশুদ্ধ হলে, ভবিষ্যৎ হবে উজ্জ্বল।
লেখক: পরিবেশ অর্থনীতিবিদ ও গবেষক

সাংবাদিকতা এক সময় ছিল সমাজ বদলের একটি মহৎ হাতিয়ার। কলম ছিল প্রতিবাদের সবচেয়ে কার্যকর অস্ত্র। সত্যের পক্ষে দাঁড়ানো মানেই ছিল সাংবাদিকতা- ভয়ডরহীন, অনুসন্ধানী, দায়িত্বশীল। অথচ আজকের বাস্তবতা এতটাই ভিন্ন, যেন আমরা এক ভয়াবহ ট্র্যাজেডির মঞ্চে দাঁড়িয়ে আছি। কলমের কালি মুছে গিয়ে, জায়গা করে নিয়েছে ইউটিউব সাবস্ক্রাইবার, টিকটক ফলোয়ার আর লাইভ ভিডিওর নাটক।
আজকাল সাংবাদিকতার চেহারা অনেকটা পলিথিনে মোড়ানো আমের শরবতের মতো- দেখতে চকচকে; কিন্তু গন্ধেই ধরা পড়ে আসল নকল। সাংবাদিকের সংজ্ঞা যেন কেউ আর বুঝতেই চায় না। যার হাতে ক্যামেরা, যার গলায় কার্ড- সে-ই সাংবাদিক! কেউ যদি বলে, ‘আমি মিডিয়া’- তাহলেই তার বিশেষাধিকার! পুলিশ থেমে যায়, ট্রাফিক হ্যান্ডস্যালুট দেয়, আর গ্রামের মানুষ তাকে ভক্তিভরে ‘স্যার’ ডাকে।
আজকাল একজন মানুষ সকালে জুতা বিক্রি করে, বিকালে বিয়ের অনুষ্ঠানে ঢুকে গলা ফাটিয়ে বলে, ‘লাইভ চলছে’! আর রাতে ‘জেলা প্রতিনিধি’ নাম দিয়ে ফেসবুকে নিউজ শেয়ার করে। যিনি কাল পর্যন্ত চায়ের দোকানে কাজ করতেন, আজ তার পকেটে ঝুলছে একটি রঙিন প্রেস কার্ড। কে বানাল? কীভাবে পেল? প্রশ্ন তোলার সাহস কই? সাংবাদিকতার নামে এই মঞ্চে আজ অনেকেই অভিনয় করছেন এমন এক চরিত্রে, যার পেছনে আছে চাঁদাবাজি, ব্ল্যাকমেইলিং, দলীয় প্রভাব, আর অপসংস্কৃতির বীজ।
টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া, রাজশাহী থেকে রাঙামাটি- যেদিকে তাকাই, সেদিকেই তথাকথিত ‘মিডিয়া অফিস’। চায়ের দোকান, বিউটি পার্লার, মোবাইল সার্ভিসিং সেন্টারের পাশেই ঝোলানো ব্যানার- ‘অফিস অব দি ক্রাইম রিপোর্টার, জেলা প্রতিনিধি: জনাব নিজাম সাহেব’! কে তাকে নিয়োগ দিল? সে কোন পত্রিকায় কাজ করে? এগুলোর জবাব নেই, প্রয়োজনও নেই। দরকার শুধু কার্ড, ক্যামেরা আর গলা ফাটানো কিছু সংলাপ।
আর এসব কার্ডের উৎস? এক শ্রেণির তথাকথিত ‘মিডিয়া মালিক’। যাদের কাছে সাংবাদিকতা ব্যবসা, সম্মান নয়। তারা প্রেস কার্ড বিক্রি করেন ঈদের অফারের মতো- ‘প্যাকেজ নিন, পদ পান!’ টাকা যত বেশি, পদ তত বড়- ইনভেস্টিগেটিভ চিফ রিপোর্টার, স্পেশাল করেসপন্ডেন্ট, চিফ এডিটর, এমনকি প্রেসিডেন্ট অব নিউজ। বানান ভুল থাকলেও চলে, কারণ কার্ড দেখে কেউ বানান মিলিয়ে দেখে না!
এই কার্ডযুদ্ধের ফলে অনেক প্রকৃত সাংবাদিক আজ বিব্রত। যারা জীবন উৎসর্গ করেন ফ্যাক্ট চেকিং, তথ্য সংগ্রহ, রাতজাগা রিপোর্ট তৈরিতে, তাদের জায়গা দখল করে নিচ্ছে কিছু ‘স্মার্ট ফোন হিরো’। তারা বড় বড় অফিসারদের হুমকি দিয়ে, ভিডিও করে, ফেসবুকে পোস্ট দিয়ে চাঁদা আদায় করে। এক দুঃখজনক ঘটনা মনে পড়ে- এক উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ফেক সাংবাদিকদের ‘চাঁদাবাজি’র বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিলে, উল্টো তার বিরুদ্ধেই বানোয়াট নিউজ ছড়িয়ে পড়ল। প্রশ্ন একটাই, এদের রুখবে কে?
এটা শুধু কিছু ছদ্ম সাংবাদিকের সমস্যা নয়। এর পেছনে রয়েছে রাজনৈতিক ছত্রছায়া, স্থানীয় ক্ষমতার অপব্যবহার, প্রশাসনের নিষ্ক্রিয়তা এবং সর্বোপরি পাঠকের নীরবতা। একজন সাংবাদিকের প্রধান শক্তি হওয়া উচিত নৈতিকতা, তথ্যের প্রতি দায়বদ্ধতা এবং জনস্বার্থে কাজ করার সংকল্প। অথচ এখন সাংবাদিকতা যেন এক খোলা বাজার- যেখানে মরিচা ধরা বিবেক আর মিথ্যার চকচকে মোড়কেই মিডিয়া বলা হয়।
অপরাধীরাও এখন সাংবাদিকের খোলস পরে। একজন খুনের আসামি কীভাবে চিফ রিপোর্টার হয়ে যায়? একজন চাঁদাবাজ রাতারাতি ফেসবুকে ‘ইনভেস্টিগেটিভ রিপোর্টার’ হয়ে কীভাবে থানায় ঢুকে যায়? কিছু মিডিয়ার মালিকরা এসব জানেন, দেখেন, তবু চুপ থাকেন, কারণ তারাও তো ভাগীদার!
আর আসল সাংবাদিকরা? যারা সম্মান নিয়ে বাঁচতে চান, তাদের চাকরি নেই, স্যালারি নেই, সামাজিক স্বীকৃতি নেই। বরং এসব ভুয়া ‘কার্ডবাজদের’ কারণে তারা হন সন্দেহের চোখে দেখা একজন। পুলিশের কাছে জবাবদিহি করতে হয়, কারণ সাংবাদিক মানেই এখন ‘মিডিয়া’ নয়, অনেকের চোখে চাঁদাবাজ, রাজনৈতিক দালাল কিংবা ভিডিও ভ্লগার।
সংবাদপত্রকে সমাজের দর্পণ বলা হয়। এই দর্পণ তৈরি করেন সাংবাদিকরা। রাষ্ট্রের চতুর্থ স্তম্ভ হিসেবে সরকার এবং সব দলের পথনির্দেশনা তৈরি করে দেয় সংবাদপত্র। এর কারিগর হলো সাংবাদিক সমাজ। সাংবাদিক সমাজ আজ দ্বিধা বিভক্ত। অপসাংবাদিকদের ভিড়ে প্রকৃত সাংবাদিকদের মর্যাদার আজ ধুলায় ভুলুণ্ঠিত। কেন এমন হচ্ছে?
একজন সাংবাদিক দেশে ও সমাজের কল্যাণে নিবেদিত হবেন; সাংবাদিকতায় এটি স্বতঃসিদ্ধ। কিন্তু কী হচ্ছে দেশে? মহান পেশার আদর্শ উদ্দেশ্য উল্টে ফেলা হচ্ছে; সৎ সাংবাদিকদের বিতর্কিত করা হচ্ছে; নানা স্বার্থে সংবাদপত্রকে জড়িয়ে ফেলা হচ্ছে। কারা করছে এসব? আজ কেন সাংবাদিকতা বাণিজ্যের ভিড়ে সংবাদপত্র এবং প্রকৃত সাংবাদিকরা অপসৃয়মাণ? কেন মর্যাদাসম্পন্ন পেশা, মর্যাদা হারাচ্ছে।
কেন শুদ্ধতার মাঝে ঢুকে পড়েছে নাম সর্বস্ব অপসাংবাদিকতা। দুর্নীতি ঢুকে গেছে এ পেশায়। পেশা নয় অসুস্থ ব্যবসা। অশিক্ষিত, কুশিক্ষিতরা অর্থের বিনিময়ে আন্ডারগ্রাউন্ড পত্রিকার পরিচয়পত্র সংগ্রহ করে মানুষকে ভয়ভীতি; আর সরলতার সুযোগ নিয়ে হরদম প্রতারণা করছে। যা সাংবাদিকতা আর সংবাদপত্রের জন্য হুমকিস্বরূপ।
যারা হলুদ সাংবাদিকতা করেন কিংবা ৫০০ টাকায় আন্ডারগ্রাউন্ড পত্রিকার কার্ড এনে দাপট দেখান তারা আমার এ লেখার কোথাও কোথাও বেশ মজা পেয়েছে তাই না? এ বিষয়গুলো আপনাদের জন্য নয়। ভুয়া আর হলুদ সাংবাদিকে ভরে গেছে দেশ। এরা সাংবাদিক নয়, সমাজের কীট। এরা মানুষকে ব্লাকমেইলিং করে টুপাইস কামাচ্ছেন বেশ।
এদের কাছ থেকে সবাইকে সাবধান হতে হবে। এদের কারণে, সংবাদপত্র, সাংবাদিক, সাংবাদিকতা বিষয়ে দেশের বেশির ভাগ মানুষেরই স্বচ্ছ ধারণা নেই। সাংবাদিক মানেই ধান্ধাবাজ, প্রতারক, ব্লাকমেইলার ও ভীতিকর ব্যক্তি এমন ধারণাই পোষণ করে দেশের গরিষ্ঠ মানুষ।
প্রকৃত সাংবাদিকরা এর কোনোটাই নন। সাংবাদিকতা একটা মহান পেশা। এটা কেবল পেশা নয়, একজন সাংবাদিক এ সেবায় থেকে মানুষকে সেবা দিতে পারেন। দেশের কিছু অসৎ সম্পাদক, সাংবাদিক অর্থের বিনিময়ে সারা দেশে নানা অপরাধে জড়িত ব্যক্তিদের সাংবাদিকতার পরিচয়পত্র দিয়ে এ পেশার সম্মানহানি করছে। এরা সাংবাদিক নন। সাংবাদিক নামধারী। সমস্যাটা এখানেই। দেশে হরেদরে সাংবাদিক পরিচয় ব্যবহারের সুযোগ আছে। এই সুযোগ নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। নিয়ন্ত্রণ আরোপে প্রকৃত সাংবাদিকদের সাহসী উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন। বাংলাদেশে সাংবাদিক হতে কোনো সুনির্দিষ্ট শিক্ষাগত যোগ্যতা লাগে না।
হুট করেই সাংবাদিক হয়ে যেতে পারে যে কেউ। না, এ ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতাও কোনো বিষয় নয়! সুশিক্ষিত ও মানসম্পন্ন সাংবাদিক ও কলামিস্ট এ দেশে অনেকেই আছেন, যারা তাদের ক্ষুরধার ও বুদ্ধিদীপ্ত লেখনী দ্বারা সমাজের অনেক অসঙ্গতি সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলে আমাদের সমাজ সচেতন করে তোলেন প্রায়ই।
সেই গুটিকয়েক নমস্য সাংবাদিকের সঙ্গে মিশে গেছে সাংবাদিক নামধারী (লেবাসধারী) কিছু নর্দমার কীট; আসলে এরাই বর্তমানে সংখ্যায় বেশি। এসব অপসাংবাদিকতা ইদানীং সাংঘাতিক রকম বেড়ে গেছে। অপ-সাংবাদিক সৃষ্টি এক ধরনের সাংবাদিকতা নির্যাতন। আমরা চাই, সাংবাদিকতা পেশা যেন আগের সৎ ও নির্ভীক চেহারায় ফিরে আসে। এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে যারা এসব অপসাংবাদিক তৈরি করছে তারা সংবাদপত্র এবং সাংবাদিকতার মতো মহান পেশাকে প্রশ্নবিদ্ধ করার লক্ষ্যেই তা করছে। এটা কোনো সুদূরপ্রসারী ষড়যন্ত্রও হতে পারে। এসব ষড়যন্ত্রকারীদের চিহ্নিত করতে হবে। তাদের প্রতিহত করতে হবে। নইলে বড্ড বেশি ক্ষতি হয়ে যাবে এ মহান পেশায়।
সাংবাদিক নামধারী অপসাংবাদিকদের বিষয়ে কিছু না বলে পারছি না। সাংবাদিকতা একটি স্পর্শকাতর পেশা। যে কারও হাতে যেভাবে ছুরি-কাঁচি তুলে দিয়ে অপারেশনের সার্জন বানিয়ে দেওয়া গ্রহণযোগ্য হয় না, একইভাবে যে কারও হাতে পরিচয়পত্র, কলম-ক্যামেরা-বুম তুলে দিয়ে তাকে সংবাদ সংগ্রহ ও প্রচারের দায়িত্ব দেওয়াটাও গ্রহণযোগ্য হওয়া উচিত নয়।
আজকাল মাঠপর্যায়ে গিয়ে এ পেশা সম্পর্কে নানা নেতিবাচক মন্তব্য অনেকের কাছে শুনতে হয়। আজকের এ নিবন্ধ ধান্দাবাজ, হলুদ সাংবাদিক এবং অপসাংবাদিককে ঘিরে, যারা সাম্প্রতিক কালে এ মহান পেশাকে কলুষিত করে রেখেছেন, অপেশাদার মনোভাব তৈরি করে সাংবাদিকতা-বাণিজ্য চালু করেছেন। এদের রাহুগ্রাস থেকে সংবাদপত্র এবং সাংবাদিকদের বেরিয়ে আসতে হবে। এমনিতেই নিরাপত্তার অভাবে রুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে মুক্ত সাংবাদিকতার দ্বার। এভাবে চলতে পারে না। চলতে দেওয়া যায় না।
এই বাস্তবতায় প্রশ্ন একটাই: কে ফিরিয়ে আনবে সত্যিকারের সাংবাদিকতা? তথ্য মন্ত্রণালয়? প্রেস কাউন্সিল? নাকি সেই পাঠক, যিনি মুখে কিছু বলেন না, কিন্তু হৃদয়ে এখনো সত্য আর মর্যাদার জন্য অপেক্ষা করেন? সময় এসেছে সাংবাদিকতার সংজ্ঞা পুনর্গঠনের। সময় এসেছে বলার: সাংবাদিকতা কার্ডে নয়, চরিত্রে। মিডিয়া অফিসে নয়, মানুষের আস্থায়।
আসুন, আমরা সেই সাংবাদিকদের পাশে দাঁড়াই, যারা আজও নীরবে সত্যের পক্ষে কলম চালান। যাদের হাতে আজও অন্ধকারে আলো জ্বালানোর সাহস আছে। না হলে খুব শিগগিরই হয়তো হেডলাইন হবে:
‘প্রেস কার্ডসহ ডাকাত গ্রেপ্তার!’
মীর আব্দুল আলীম
সমাজ গবেষক
মহাসচিব – কলামিস্ট ফোরাম অব বাংলাদেশ

প্রধান উপদেষ্টা দায়িত্ব গ্রহণের পর পরই ৬টি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগে জনআকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সংগতি রেখে প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধনের জন্য ৬টি সংস্কার কমিশন গঠন করলেন। তিনি আরও ঘোষণা দিলেন সংস্কার শেষে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব জাতীয় নির্বাচনের ব্যবস্থা করে জনগণকে গণতান্ত্রিক সরকার উপহার দেবেন। জাতি আশাবাদী হয়ে দিন গুনছিল সংস্কারে পরিশুদ্ধ একটি নতুন গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ দেখার; কিন্তু জুলাই অভ্যুত্থানের সমর্থক প্রতিটি রাজনৈতিক দল- যারা জনপ্রতিনিধিত্ব আদেশ বলে নির্বাচন করার যোগ্যতা রাখে এবং দল নিরপেক্ষ জনগণ যারা একটি নিরপক্ষে, সুন্দর নির্বাচনের জন্য তৈরি হচ্ছিল তাদের মধ্যে সংস্কার আর নির্বাচনের রোডম্যাপ নিয়ে ভিন্নমত মাথাচাড়া দেওয়ায় বহুবছর ধরে ভোট দেওয়া থেকে বঞ্চিত সাধারণ জনগণ এখন হতাশ। কেন এমনটি হলো?
একজন রাজনীতি বিশ্লেষক হিসেবে নয়, একজন দল নিরপেক্ষ নাগরিক হিসেবে আমার একটা উত্তর এখানে দাঁড় করানোর চেষ্টা করলাম। আমরা যদি দলীয় ভাবাদর্শের ঊর্ধ্বে থেকে নিরপক্ষেভাবে চিন্তা করি তাহলে আমার মতামতের সঙ্গে অনেকের বিবেকের ভাবনাটা মিলেও যেতে পারে।
জুলাই আন্দোলনের কৃতিত্ব নিয়ে যারা এখন সরব বা নিজেদের মধ্যে কাদা ছোড়াছুড়ি করছেন তারাই মূলত সংস্কার ও গণতন্ত্রের পথে এগিয়ে যাওয়ার প্রধান অন্তরায়। তারা দল তৈরি, দল পুনর্গঠন ও নির্বাচনী প্রচারণা নিয়ে এতই ব্যস্ততায় নিমজ্জিত আছেন, বাস্তবতার দিকে নজর রাখার সময় কিংবা আগ্রহ তাদের নেই। জুলাই চেতনার পক্ষধারী একপক্ষ ডিসেম্বরের মধ্যে নির্বাচনের বিষয়ে অনড় কিন্তু প্রার্থিতা নিয়ে এখনো মাাঠে নামেননি পক্ষান্তরে আরেক পক্ষ সংস্কার ও শেখ হাসিনার বিচারের আগে নির্বাচন নয় বলে মাঠ কাঁপালেও প্রকাশ্যেই তারা সারা দেশে প্রার্থিতা ঘোষণা করছেন এবং তলে তলে বিভিন্ন জোটবদ্ধ হওয়ার চেষ্টা করছেন। এই হচ্ছে গণতন্ত্রের পথে আমাদের যাত্রার বর্তমান বাস্তবতা।
জনগণ কি এই বাস্তবতা দেখার জন্য জুলাই আন্দোলনকে সমর্থন দিয়েছিল? এক বাক্যে যদি বলি তা হলে সবাই বলবেন না। জুলাই আন্দোলনের পটভূমি যাই হোক শেষ পর্যন্ত হাসিনা সরকারের দমন-পীড়নের মুখে সেটি সরকার পতনের আন্দোলনে রূপ নেয়। সরকারের পতনের পর আন্দোলনকারীদের ও মাস্টারমাইন্ডদের মনে হলো এই রাষ্ট্রযন্ত্রেও এ ধারা ও নিয়মকানুন প্রচলিত থাকলে স্বৈরাচার বা ফ্যাসিস্ট বারবার পয়দা হবে। তাই তারা প্রতিটি স্তরে সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন এবং সংস্কার দাবি করলেন। সমগ্র জাতি ভালো করে জানে বিরোধী দলগুলো ১৬ বছরেও আওয়ামী সরকারের বিরুদ্ধে কোনো কার্যকর আন্দোলন গড়ে তুলতে পারেনি। কাজেই হাসিনার অপকর্ম বা অপশাসনের দায় তাদের ওপরও বর্তায়। বিষয়টি তারা ভালোভাবেই জানেন এবং বোঝেন বলেই অতিদ্রুত এবং সুকৌশলে তারা সরকার পতনের বিজয় মিছিলে ঢুকে যায় এবং নানার রকম সমর্থন আর যুক্তি দাঁড় করিয়ে এই আন্দোলনের ফসল নিজ নিজ ঘরে তোলার অপ্রিয় খেলায় মেতে ওঠে। নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকার জন্য বৈষম্যবিরোধী ছাত্রসমাজ ও সমন্বককারীদের মাথায় তুলে নেয় এবং সংস্কারের পক্ষে সাফাই গাইতে শুরু করে। এই পর্যন্ত জুলাই চেতনা বিশ্বাসীদের ঐক্যে কোনো ফাটল ছিল না। বৈষম্যবিরোধী ছাত্রসমাজ চিরায়ত কায়দায় জড়িয়ে গিয়ে ক্ষমতার স্বাদকে চিরস্থায়ী করতে রাজনৈতিক দল গঠন করে পুরোনো কায়দায় নির্বাচনী প্রচারণা শুরু করলেন। এই প্রক্রিয়ায় আন্দোলনের প্রধান শক্তিরা অপরাপর রাজনৈতিক দলের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে গেলেন। শুরু হয়ে গেল চিরায়ত মতবিরোধ- কখনো আদর্শগত, কখনো ক্ষমতার। সরকার পতনের পর জাতির ভেতর যে মিলনের সুর বেজে উঠেছিল তার রেশ শেষ হতে আর বেশি সময় লাগল না। আশাহত হলো সাধারণ জনগণ। যাদের একটা নতুন বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখানো হচ্ছিল।
তাহলে গণতন্ত্রের পথে আমাদের নতুন অভিযাত্রা কি থেমে যাবে? না, কোনো সুযোগ নেই। কারোর ভুলের জন্য এই সুবর্ণ সুযোগ হাতছাড়া করা হবে আত্মঘাতী। এমতাবস্থায় সরকার, রাজনৈতিক দল ও সাধারণ জনগণকে ভেদাভেদ ও দলীয় সংকীর্ণতা উপেক্ষা করে আজকের অনৈক্য ও বিবদমান পরিস্থিতির গভীর পর্যালোচনা করে সমস্যা চিহ্নিত ও সঠিক সমাধানের উদ্যোগ নিতে হবে। আমার বিবেচনায় সমস্যাগুলো দেশকেন্দ্রিক না হয়ে সংস্কার, নির্বাচন বা ক্ষমতাকেন্দ্রিক হয়ে গেছে। যা অনেক রক্তের বিনিময়ে তৈরি হওয়া জাতীয় ঐক্যকে নড়বড়ে করে দিচ্ছে।
আগেই বলেছি জুলাই বিপ্লব শুধু ক্ষমতার হাতবদলের জন্য সংঘটিত হয়নি। ক্ষমতার পালাবদলের জন্য গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সাধারণ নির্বাচন অত্যন্ত জরুরি। কিন্তু যে নির্বাচনী ব্যবস্থা বা সরকারি বিধিমালা একটা সরকারকে স্বৈরাচারী বা বিপথগামী করতে বাধ্য করে সর্বাগ্রে প্রয়োজন তার আমূল পরিবর্তন বা সংস্কার। ছাত্র-জনতার চাওয়া এবং সরকারের সদিচ্ছা তেমনি ছিল দেখে জনগণ আশান্বিত হয়েছিল; কিন্তু অন্য একটি বড় রাজনৈতিক দল ও তাদের সমর্থকরা সংস্কার আগে না নির্বাচন আগে ইস্যু তৈরির সুযোগ নিয়ে মাঠ গরম করা শুরু করলেন। তাদের বক্তব্য ও মতামতের যথেষ্ট যুক্তি আছে। তারা বলছেন বা আমরা বিশ্বাস করি সংস্কার একটা চলমান প্রক্রিয়া। সময় ও চাহিদার আলোকে এই প্রক্রিয়া চলতেই থাকবে। অতএব, নির্বাচনের সঙ্গে সংস্কারের সরলরেখা টানাটা জরুরি নয়। তবে নির্বাচনকে প্রশ্নবিদ্ধ না করতে, জনগণকে স্বাধীনভাবে, প্রভাবমুক্ত পরিবেশে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে এবং রাষ্ট্রযন্ত্রেও যে জায়গাগুলো ব্যবহার করে ক্ষমতাসীন বা বিজয়ী দলগুলো অনিয়ম আর দুর্নীতির আশ্রয় নেয় সেই জায়গাগুলোতে প্রয়োজনীয় সংস্কার করে নির্বাচনের ব্যবস্থা করার পক্ষে বিশ্লেষকরা মনে করে থাকেন।
এদিকে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারীবাহিনীর উপস্থিতির মধ্যেই মাঠ-ঘাট-বাজার-জমি দখল ও চাদাঁবাজির দৌরাত্ম্যে কোনো পরিবর্তন জনগণ দেখছে না। নিবন্ধিত বা অনিবন্ধিত নতুন রাজনৈতিক দলের নেতারা চিরায়ত ভঙ্গিমায় মোটরসাইকেল ও গাড়ি বহর নিয়ে এলাকায় শোডাউন করছে। ধর্ষণ, খুন, ছিনতাই বুদ্ধির পাশাপাশি বাজার সিন্ডিকেট পুরোনো ধারায় বেশ সক্রিয়।
উপরোক্ত বিষয়গুলো আমজনতার সামনে এবং জুলাই চেতনাধারী সব ছাত্র-জনতা ও রাজনৈতিক শক্তিগুলোর সামনে প্রকটভাবে দৃশ্যমান হওয়ায় সরকারের সঙ্গে একটা দূরত্ব ও দলগুলোর মধ্যে অনৈক্যর সুর ক্রমশ বাড়ছে। আমরা মনে করি নির্বাচন বা সংস্কার যেটাই হউক সবার আগে সরকার ও তার সমর্থক সব দলের মধ্যে চিন্তায়, কার্যকলাপ ও আচরণের মধ্যে পতিত মানসিকতার পরিবর্তন আনতে হবে। আগে যা ঘটেছে তা যদি জনস্বার্থবিরোধী হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই ওই কাজ বা আচরণের পুনরাবৃত্তি ঘটানো যাবে না। সোজা বাংলায় জনগণ প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে অতীতের ঠিক উল্টোটা দেখতে চায়। পুরোনো ধারায় যে অনিয়মগুলো এখনো দৃশ্যমান তা থেকে জনগণকে যদি মুক্তি দেওয়া যায় তাহলে সরকারের প্রতি এবং নতুন বন্দোবস্তের প্রতি মানুষের আস্থার জায়গাটা বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে। আর তখনি নির্বাচন আগে না সংস্কার আগে- এ বিতর্কের এবং এ ইস্যুতে ঐক্যের জায়গাটাও তৈরি হবে।
বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের বয়স ৮ মাস অতিক্রম হয়েছে; কিন্তু তার জনপ্রিয়তা ও দায়িত্বপালনের ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জগুলোকে অগ্রাধিকার দিয়ে যদি সেগুলোর সমাধানের চেষ্টা করে তাহলে ব্যাপক জনসমর্থন তাকে অভিষ্ঠ লক্ষ্যে পৌঁছাতে দ্বিধাহীন শক্তি জোগাবে। তাই নির্বাচন ও সংস্কার দুটোকেই মাথায় রেখে সবাইকে অগ্রাধিকার দিতে হবে জনগণের মৌলিক প্রত্যাশার দিকে। বহুবছর ধরে একটা সঠিক গণতন্ত্রহীন পরিবেশ থেকে জাতিকে মুক্তি দেওয়াটা যেমন সর্বাগ্রে প্রয়োজন, তেমনি উপড়ানো দরকার সরকারের সব কালাকানুন এবং পতিত মানসিকতার চর্চা। জাতি উন্মুখ হয়ে আছে একটি গণমুখী নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্ত ও গণতন্ত্রের সুবাতাস আশ্বাদনের জন্য। আমাদের কাদা ছোড়াছুড়িতে রক্তাক্ত জুলাই বিপ্লবের আশা-আকাঙ্ক্ষার যেন অপমৃত্যু না হয় সেদিকে সচেতন ও সতর্ক থাকার দায়িত্ব সবার। সুশাসন আর গণতন্ত্রের পথে আমাদের অভিযাত্রা সংকটমুক্ত হোক- জাতির প্রত্যাশা এখন সেটাই।
লেখক: প্রাবন্ধিক ও কলামিস্ট

মুক্তবাজার অর্থনীতি চালু হওয়ার পর থেকে বিশ্ববাণিজ্যে নানা ধরনের মেরুকরণ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বর্তমান তীব্র প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে এককভাবে টিকে থাকা খুবই কঠিন। বিশেষ করে অর্থনৈতিকভাবে তুলনামূলক দুর্বল দেশগুলোকে নানা জটিল চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হচ্ছে। মুক্তবাজার অর্থনীতির নিয়ম-কানুন যেন শুধু দুর্বল দেশগুলোর জন্যই প্রযোজ্য। অর্থনৈতিক এবং সামরিকভাবে তুলনামূলক সক্ষম দেশগুলো চাইলেই মুক্তবাজার অর্থনীতির সাধারণ নিয়মগুলো লঙ্ঘন করতে পারে।
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সম্প্রতি প্রায় ৬০টি দেশের ওপর অতিরিক্ত হারে শুল্কারোপ করেছে। এর মধ্যে চীনের ওপর ২৪৫ শতাংশ বর্ধিত শুল্কারোপ করা হয়েছে, যা রীতিমতো উদ্বেগজনক। চীন যুক্তরাষ্ট্রের আমদানি পণ্যের ওপর একতরফা শুল্কারোপের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে। দেশটি যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমদানি পণ্যের ওপর ১২৫ শতাংশ বাড়তি শুল্কারোপের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বব্যাপী তীব্র প্রতিবাদের মুখে বর্ধিত শুল্কারোপের সিদ্ধান্ত তিন মাসের জন্য স্থগিত ঘোষণা করেছে। কিন্তু চীন থেকে আমদানিকৃত পণ্যের ওপর বর্ধিত শুল্কহার স্থগিত করা হয়নি। এতে বোঝা যায়, যুক্তরাষ্ট্র বিশেষ উদ্দেশ্যে চীন থেকে আমদানিকৃত পণ্যের ওপর বর্ধিত শুল্কারোপের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।
অনেকদিন ধরেই যুক্তরাষ্ট্র চীনের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে অনৈতিকতার অভিযোগ উত্থাপন করে আসছে। বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রের অভিযোগ-চীন পণ্য উৎপাদক ও রপ্তানিকারকদের অনৈতিক সুবিধা দেওয়ার জন্য স্থানীয় মুদ্রার মূল্যমান ইচ্ছা করেই কমিয়ে রাখছে; কিন্তু চীন বারবার এ অভিযোগ অস্বীকার করে আসছে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থা খুব একটা ভালো নেই। ইউক্রেন যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর যুক্তরাষ্ট্রের মূল্যস্ফীতি বিগত ৪০ বছরের রেকর্ড ভঙ্গ করে ৯ দশমিক ১ শতাংশে উন্নীত হয়েছিল। সেই সময় যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় ব্যাংক ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক অব আমেরিকা (ফেড) বারবার পলিসি রেট বৃদ্ধি করে।
পাশাপাশি আরও কিছু ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে মূল্যস্ফীতির হার সহনীয় পর্যায়ে নেমে আসে ঠিকই, কিন্তু দেশটিতে ব্যক্তি খাতে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে স্থবিরতা নেমে আসে। অভ্যন্তরীণভাবে বিভিন্ন পণ্যের উৎপাদন কমে যায়। দেশটি অধিকমাত্রায় আমদানিনির্ভর হয়ে পড়ে। যুক্তরাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ভারসাম্য দেশটির প্রতিকূলে রয়েছে। বিশেষ করে চীনা পণ্য যুক্তরাষ্ট্রের বাজার দখল করে আছে। স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত মার্কিন পণ্য আমদানিকৃত চীনা পণ্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় কুলিয়ে উঠতে পারছে না। যুক্তরাষ্ট্র যে ৬০টি দেশের ওপর বর্ধিত শুল্কারোপ করেছে, তার অধিকাংশের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্যের ভারসাম্য যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিকূলে রয়েছে।
বিশ্ববাণিজ্যের রীতি অনুযায়ী, কোনো দেশ একতরফাভাবে আমদানি পণ্যের শুল্ক বাড়াতে পারে না। কিন্তু দেশটি যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। তাই তার কাছে সব নিয়মনীতি উপেক্ষিত হচ্ছে। এটি নিশ্চিত করেই বলা যেতে পারে, আগামীতে যুক্তরাষ্ট্র ও চীন ভয়াবহ বাণিজ্যযুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে যাচ্ছে। কাজেই চীনকে তার আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের গতি ধরে রাখার জন্য বিকল্প চিন্তা করতে হবে।
একটি আন্তর্জাতিক গবেষণা সংস্থা কয়েক বছর আগে উল্লেখ করেছিল, চীন যেভাবে এগিয়ে যাচ্ছে, তা অব্যাহত থাকলে ২০৫০ সালের আগেই দেশটি যুক্তরাষ্ট্রকে অতিক্রম করে বিশ্বের এক নম্বর অর্থনৈতিক শক্তিতে পরিণত হবে। কয়েক বছর আগে চীন পারচেজিং পাওয়ার প্যারেটি (পিপিপি) বিবেচনায় যুক্তরাষ্ট্রকে অতিক্রম করে গেছে। যদিও এখনো দেশটি গ্রস ডমেস্টিক প্রডাক্টের (জিডিপি) ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের চেয়ে অনেকটাই পিছিয়ে রয়েছে।
বিশ্বব্যাংকের পরিসংখ্যান মোতাবেক, ২০২৩ সালে যুক্তরাষ্ট্রের মোট জিডিপির পরিমাণ ছিল ২৭ হাজার ৭২০ দশমিক ৭১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা মোট বিশ্ব জিডিপির ২৬ দশমিক ২৯ শতাংশ। অন্যদিকে একই সময়ে চীনের মোট জিডিপির পরিমাণ ছিল ১৭ হাজার ৭৯৪ দশমিক ৭৮ বিলিয়ন ডলার, যা বিশ্ব জিডিপির ১৬ দশমিক ৮৮ শতাংশ। চীনের মোট রপ্তানি আয়ের ১৬ দশমিক ২২ শতাংশ অর্জিত হয় যুক্তরাষ্ট্র থেকে। আর চীনের মোট আমদানি পণ্যের ৬ দশমিক ৫৯ শতাংশ আসে যুক্তরাষ্ট্র থেকে। চীনের মোট সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগের পরিমাণ হচ্ছে ৬৯ দশমিক ৯৩ বিলিয়ন ডলার। চীন সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি থেকে বেরিয়ে এসে নিজস্ব আঙ্গিকে মুক্তবাজার অর্থনীতিকে ধারণ করার পর দেশটি প্রায় তিন দশক ধরে উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে। চীন ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড অবস্থার সুযোগ বেশ ভালোভাবেই কাজে লাগিয়েছে। কয়েক বছর আগে চীন বিশ্ব অর্থনীতিতে জাপানের ৪৪ বছরের আধিপত্য খর্ব করে দ্বিতীয় স্থানে উঠে এসেছে। তবে যুক্তরাষ্ট্রের শুল্কহার বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত চীনের জন্য মোটেও সুখকর হবে না।
বাংলাদেশের রপ্তানি পণ্যের ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের শুল্ক বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত কিছুটা হলেও মিশ্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করতে পারে। একক দেশ হিসাবে যুক্তরাষ্ট্র হচ্ছে বাংলাদেশি পণ্যের সবচেয়ে বড় গন্তব্য। যে সামান্য কটি দেশের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্যের ভারসাম্য বাংলাদেশের অনুকূলে রয়েছে, যুক্তরাষ্ট্র তার মধ্যে সবার শীর্ষে। ২০০৫ সালে যুক্তরাষ্ট্র যখন বাংলাদেশকে দেওয়া কোটা সুবিধা বাতিল করে, তখন অনেকেই আশঙ্কা করেছিলেন, বাংলাদেশের তৈরি পোশাকশিল্প খাত সম্ভবত গতি হারিয়ে ফেলবে। কিন্তু কার্যত তা হয়নি।
আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলাদেশের তৈরি পোশাকশিল্পের সবচেয়ে বড় প্রতিযোগী হচ্ছে ভিয়েতনাম। চীন বিশ্ববাজারে তৈরি পোশাক রপ্তানির ক্ষেত্রে অনেকদিন ধরেই শীর্ষস্থানে রয়েছে। চীন আন্তর্জাতিক বাজারে যে পরিমাণ তৈরি পোশাক রপ্তানি করে, বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানির পরিমাণ তার চেয়ে অনেক কম। তবে দ্বিতীয় স্থান নিয়ে ভিয়েতনামের সঙ্গে আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলাদেশের প্রতিযোগিতা চলছে অনেকদিন ধরেই। চীন ও ভিয়েতনামের ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্র অনেক বেশি পরিমাণে বর্ধিত শুল্কারোপ করেছে। কাজেই বাংলাদেশ এ সুযোগ কাজে লাগাতে পারে। তারপরও সমস্যা থেকে যাবে।
আগামী বছর থেকে বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশের চূড়ান্ত তালিকায় উত্তীর্ণ হবে। সেই অবস্থায় বিশ্ব বাণিজ্যে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ হিসাবে যেসব সুবিধা পেত, তা বাতিল হয়ে যাবে। ইউরোপীয় ইউনিয়ন বলছে, তারা বাংলাদেশকে ২০২৯ সাল পর্যন্ত জিএসপি সুবিধা দেবে। তারপর জিএসপি+ নামে এক ধরনের শুল্কমুক্ত রপ্তানি সুবিধা দেওয়া হবে; কিন্তু জিএসপি+ সুবিধা পেতে হলে যেসব শর্ত পরিপালন করতে হবে, তা বাংলাদেশের পক্ষে সম্ভব হবে বলে মনে হয় না। এ অবস্থায় বাংলাদেশকেও বিকল্প পন্থা খুঁজে বের করতে হবে।
বর্ণিত পরিপ্রেক্ষিতে দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়ার দেশগুলো মিলে একটি নতুন অর্থনৈতিক জোট গঠনের সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলো নিয়ে বেশ কয়েকটি অর্থনৈতিক জোট গঠিত হয়েছে। কিন্তু সেসব অর্থনৈতিক জোট খুব একটা ফলপ্রসূ হয়নি। এক্ষেত্রে সাউথ এশিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর রিজিওনাল কো-অপারেশনের (সার্ক) প্রসঙ্গ উল্লেখ করা যেতে পারে। বাংলাদেশের শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান সর্বপ্রথম সার্কের স্বপ্ন দেখেছিলেন। সন্নিহিত এলাকায় অবস্থিত দক্ষিণ এশীয় দেশগুলোকে নিয়ে একটি আঞ্চলিক জোট গঠনের লক্ষ্যে প্রাথমিক যোগাযোগ শুরু করা হয়েছিল; কিন্তু জিয়াউর রহমানের নির্মম হত্যাকাণ্ডের পর সার্ক গঠন প্রক্রিয়া অনেকটাই স্থবির হয়ে পড়ে। পরবর্তীকালে সামরিক শাসক এইচএম এরশাদের সময় ১৯৮৫ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত দক্ষিণ এশিয়ার সাতটি দেশ-বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলংকা, মালদ্বীপ, নেপাল ও ভুটানের সমন্বয়ে সার্ক গঠিত হয়। পরে আফগানিস্তানও সার্কের সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হয়।
সার্ক গঠনের পর ভারত শর্তারোপ করে, সার্কে কোনো দ্বিপক্ষীয় ইস্যু আলোচনা করা যাবে না। ভারতের এ শর্ত মেনে নেওয়ার কারণে সার্ক মূলত একটি অকার্যকর জোট পার্টিতে পরিণত হয়। জিয়াউর রহমান যে সার্কের স্বপ্ন দেখেছিলেন, তার উদ্দেশ্য ছিল দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মাঝে বিদ্যমান সমস্যা দূরীকরণের মাধ্যমে এ অঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করে যাওয়া। কিন্তু ভারতের শর্তের কারণে সেই লক্ষ্য ব্যর্থ হয়। উল্লেখ্য, ভারত এমন একটি রাষ্ট্র, যার সঙ্গে তার কোনো প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সুসম্পর্ক নেই। বাস্তবতা হচ্ছে এটাই, দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলো নিয়ে যদি কোনো অর্থনৈতিক অথবা রাজনৈতিক জোট গঠন করা হয়, সেখানে ভারত ও পাকিস্তানকে অন্তর্ভুক্ত করলে সেই জোটের সফল হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে খুবই ক্ষীণ। পাকিস্তানকে বাদ দিয়ে বিমসটেক জোট গঠন করা হয়েছে; কিন্তু এ জোটও খুব একটা সফল হবে বলে মনে হয় না।
বিদ্যমান বাস্তবতায় চীন, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, আফগানিস্তান, ইরান ও তুরস্ককে নিয়ে একটি নতুন অর্থনৈতিক জোট গঠনের চিন্তাভাবনা করা যেতে পারে। বিগত শতাব্দীর ষাটের দশকে পাকিস্তান, ইরান ও তুরস্ক মিলে রিজিওনাল কো-অপারেশন ফর ডেভেলপমেন্ট (আরসিডি) নামে একটি অর্থনৈতিক জোট গঠিত হয়েছিল। যদিও পরবর্তীকালে এ জোটের কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়। আরসিডির অনুকরণে সিপিবিএআইটি (চীন, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, আফগানিস্তান, ইরান ও তুরস্ক) গঠন করা যেতে পারে। বর্ণিত দেশগুলো মোটামুটি একই মনমানসিকতা ধারণ করে। তারা আন্তর্জাতিক ফোরামে বিভিন্ন ইস্যুতে পরস্পরকে সহায়তা করে থাকে। অর্থাৎ দেশগুলোর মধ্যে কিছুটা হলেও আদর্শিক মিল রয়েছে। কোনো অর্থনৈতিক জোট সফল হওয়ার জন্য দেশগুলোর মধ্যে রাজনৈতিক বোঝাপড়া থাকতে হয়। রাজনৈতিক বোঝাপড়া এবং পারস্পরিক সহযোগিতার মনোভাব না থাকলে কোনো জোট সফল হতে পারে না। বিশ্ব অর্থনীতিতে চীনের মতো গুরুত্বপূর্ণ ও শক্তিশালী একটি দেশ যদি কোনো অর্থনৈতিক জোটের নেতৃত্ব দেয়, তাহলে সেই জোটের সফল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। চীন বর্তমান বিশ্ব অর্থনীতিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে রয়েছে।
সন্নিহিত এলাকায়, এমনকি দূরবর্তী স্থানে অবস্থিত দেশগুলোর মধ্যে অর্থনৈতিক জোট গঠিত হতে পারে। তবে শর্ত হচ্ছে, জোটভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে মতাদর্শগত মিল থাকতে হবে অথবা জোটের স্বার্থে নিজের সংকীর্ণ স্বার্থ ত্যাগ করার মতো মানসিকতা থাকতে হয়। যুক্তরাষ্ট্র সম্প্রতি ভারতকে অসহযোগী দেশের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করেছে। অর্থাৎ ভারত নামের দেশটি আঞ্চলিক অথবা দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের ক্ষেত্রে উদারতা ও সহযোগিতার মনোভাব প্রদর্শন করতে পারছে না।
চীন যেহেতু এ মুহূর্তে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্য বিরোধে জড়িয়ে পড়েছে, তাই চীনের নেতৃত্বে নতুন অর্থনৈতিক জোট গঠনের উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে। অর্থনৈতিক জোট গঠন করে চীন এবং জোটভুক্ত অন্যান্য দেশ যদি তাদের বাজার উন্মুক্ত করে, তাহলে প্রতিটি দেশই উপকৃত হতে পারে। সদস্য দেশগুলো নিজ নিজ বাজার উন্মুক্তকরণের মাধ্যমে একক বাজার তৈরি করতে পারে। চীন বাংলাদেশ বা অন্য সদস্য দেশে তাদের কারখানা স্থানান্তরের মাধ্যমে তুলনামূলক কম শুল্কে যুক্তরাষ্ট্রে পণ্য রপ্তানির সুবিধা নিতে পারে। নতুন অর্থনৈতিক জোট গঠনের বিষয়টি গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করা যেতে পারে।
ড. আনোয়ারউল্লাহ চৌধুরী : সাবেক উপাচার্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; বাহরাইনে নিযুক্ত বাংলাদেশের সাবেক রাষ্ট্রদূত

বোরো মৌসুমে হাওরাঞ্চল দেশের ৩০ শতাংশের মতো চালের জোগান দেয়। সাত জেলার হাওরে এ বছর বোরো আবাদ হয়েছে ৪ লাখ ৫২ হাজার হেক্টর জমিতে, আর হাওর ও হাওরের বাইরে উঁচু জমি মিলে মোট বোরো আবাদ হয়েছে ৯ লাখ ৫৩ হাজার হেক্টর জমিতে, উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ৪০ লাখ টন চাল। এবার বৃষ্টি না হওয়ায় হাওরের সব ধান কৃষকের ঘরে উঠবে- এটা আশা করা যায় এবং কিশোরগঞ্জের অষ্টগ্রাম, মিঠামইন ও ইটনা উপজেলায় এবার ধানের বাম্পার ফলন হয়েছে। কয়েকটি হাওরে সরজমিনে দেখা গেল, বোরো ধান কাটার এ উৎসবে শুধু কিষান-কিষানিই নয়, বাড়ির সব বয়সি মানুষই এসে হাত লাগিয়েছে ধানকাটা, মাড়াই এবং গোলায় তোলার উৎসবে। এদের কেউ খেত থেকে ধান কাটছে, কেউ কেউ খেতেরই ফাঁকা ধানের ‘খলা’ তৈরিতে ব্যস্ত, ধান কাটা শেষে ইঞ্জিনচালিত ট্রাক্টর দিয়ে তা জমি থেকে খলায় নিয়ে আসা হচ্ছে, খলায় মেশিন (মাড়াই কল) দিয়ে চলে মাড়াই, পরে সেখানেই শুকানো হচ্ছে মাড়াইকৃত ধান। তীব্র রোদে শুকানো ধান বস্তাভর্তি করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে গোলায়, বিভিন্ন উপজেলার হাওরে লেগেছে বোরো ধান কাটা ও মাড়াইয়ের ধুম। এটি মাত্র একটি জেলার চিত্র।
সিলেট অঞ্চলের হাওরের চিত্র ভিন্ন : তবে তবে বৃহত্তর সিলেট অঞ্চলের হাওরের ৯০ শতাংশ ফসলই এখনো কাঁচা। নেত্রকোনার হাওরেও পাকেনি বেশির ভাগ জমির ধান। এর মধ্যে ভারী বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর, যা চিন্তায় ফেলেছে ওই অঞ্চলের কৃষকদের। তারা জানিয়েছেন, মাঠের সব ধান পাকতে আরও সপ্তাহ দুয়েক লাগতে পারে। তার আগে অতিবৃষ্টি হলে জলাবদ্ধতা সৃষ্টির পাশাপাশি উজানের ঢলে হাওর রক্ষা বাঁধ ভেঙে ডুবে যেতে পারে ফসল। তাই আকাশে মেঘ করলেই বাড়ে আতঙ্ক। গত কয়েক দিনের বৃষ্টিতে এরই মধ্যে বাড়তে শুরু করেছে নদীর পানি। আগাম বন্যার শঙ্কায় কাটছে দিন। কৃষি বিভাগের তথ্যমতে, এবার সুনামগঞ্জের বোরো ধানের আবাদ হয়েছে ২ লাখ ২৩ হাজার ৫০২ হেক্টর জমিতে। এখনো সিংহভাগ জমির ফসল কাঁচা। তবে এ পর্যন্ত পর্যন্ত হাওরসহ উঁচু এলাকার ১৮ ভাগ ধান কাটা হয়েছে বলে জানিয়েছে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর। সবচেয়ে বেশি হাওর অধ্যুষিত জেলা সুনামগঞ্জের কৃষি বিভাগ আগাম বন্যা ও পাহাড়ি ঢলের আশঙ্কায় পাকা ধান দ্রুত কাটতে কৃষকদের পরামর্শ দিয়েছে। উজানে ভারী বৃষ্টির এমন পূর্বাভাসে সুনামগঞ্জের বিভিন্ন হাওরের কৃষকরা চিন্তিত। কারণ ধান এখনো পুরোপুরি পাকেনি। একফসলি এসব জমির দিকে সারা বছর তাকিয়ে থাকেন হাওর অধ্যুষিত সাত জেলার কৃষক। তবে সবচেয়ে বেশি ধান হয় নেত্রকোনা ও সুনামগঞ্জ জেলায়। তবে ১৫ থেকে ২৫ এপ্রিল পর্যন্ত ধান কাটার চূড়ান্ত মুহূর্তে বৃষ্টিপাত ও উজানের ঢলের আশঙ্কা রয়েছে। তাই দ্রুত ধান কাটার তাগিদও দিয়েছে জেলা প্রশাসন। এদিকে নেত্রকোনার হাওরাঞ্চলে বোরো ধান কাটা শুরু হলেও গত তিনদিন ধরে বৈরী আবহাওয়ার কারণে কৃষকদের কপালে চিন্তার ভাঁজ। বজ্রপাতের কারণেও কৃষকদের সতর্কতায় প্রশাসন মাইকিং করেছে। গত বুধ ও বৃহস্পতিবার জেলার ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া ভারী বর্ষণে আগাম বন্যার শঙ্কা নিয়ে ফসল ঘরে তুলতে ব্যস্ত কৃষক-কিষাণীরা। এরই মধ্যে হাওর এলাকায় ৩১ ভাগ ধান কাটা হয়েছে জানিয়ে ৩০ এপ্রিলের মধ্যে শতভাগ ধান কাটা শেষ হবে বলে আশা করছে কৃষি বিভাগ।
নেত্রকোনার বোরো ধান আবাদ: নেত্রকোনার ১০ উপজেলার মধ্যে মদন, মোহনগঞ্জ ও খালিয়াজুরী উপজেলা হাওরপ্রধান হলেও কলমাকান্দা, আটপাড়া ও কেন্দুয়া উপজেলায় বেশকিছু হাওর রয়েছে। এসব হাওরে বর্তমানে দ্রুতগতিতে চলছে বোরো ধান কাটা ও মাড়াইয়ের কাজ। এ বছর হাওরে স্বল্পজীবনকালীন ও উচ্চফলনশীল জাতের ব্রি-ধান-৮৮, ব্রি-ধান-৯২-এর মতো হাইব্রিড জাতের ধান রেকর্ড পরিমাণে চাষ করেছেন কৃষক। খালিয়াজুরী উপজেলার নূরপুর বোয়ালী গ্রামের কৃষক বলেন, ‘এলাকার কৃষকরা আনন্দের সঙ্গে ধান কাটার কাজে ব্যস্ত সময় পার করছেন। দুইদিনের বৃষ্টিতে ধান কাটায় কিছুটা ভাটা পড়েছে। তবে তেমন ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা নেই। এখন ভয়ের কারণ বজ্রপাত।’ জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর সূত্র জানায়, জেলায় এ বছর মোট ১ লাখ ৮৫ হাজার ৪৬০ হেক্টর জমিতে বোরো আবাদ করা হয়েছে। এর মধ্যে হাওরে আবাদ হয়েছে ৪১ হাজার ৭৫ হেক্টর জমিতে। এরই মধ্যে ১২ হাজার ৭৩৩ হেক্টর জমির ধান কর্তন হয়েছে, যার পরিমাণ ৩১ ভাগ ধান কাটা সমাপ্ত হয়েছে। নেত্রকোনা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক বলেন, বোরো মৌসুমে হাওরের কৃষকরা যাতে আগাম বন্যা থেকে ফসল রক্ষা করতে পারেন সেজন্য কৃষি শ্রমিকের পাশাপাশি এক হাজারেরও বেশি কম্বাইন্ড হারভেস্টার মেশিন রাখা হয়েছে। এরই মধ্যে ১২ হাজার ৭৩৩ হেক্টর জমির ধান কাটা হয়েছে, যা রোপণ করা ধানের ৩১ ভাগ।’ ৩০ এপ্রিলের মধ্যে হাওরে শতভাগ ধান কাটা শেষ হবে বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি। বৃষ্টির পাশাপাশি নেত্রকোনার হাওরাঞ্চলের কৃষকের মাঝে বজ্রপাতের আতঙ্কও রয়েছে। খালিয়াজুরীর পৃথক স্থানে সম্প্রতি বজ্রপাতে তিনজনের মৃত্যু হয়েছে, আহত হন একজন। তাই প্রাকৃতিক এ দুর্যোগের বিষয়ে সতর্ক থাকার জন্য মাইকিংও করা হয়েছে প্রশাসনের পক্ষ থেকে। নেত্রকোনার জেলা প্রশাসক বলেন, ‘দুই সপ্তাহ আগে থেকে হাওরাঞ্চলের কোনো কোনো জায়গায় বিশেষ করে মদন, মোহনগঞ্জ ও খালিয়াজুরী এলাকায় বোরো ধান কাটা শুরু হয়েছে। বৃষ্টিতে তেমন কোনো সমস্যা দেখা দেবে না বলে আশা করছি। এর আগেই ধান কাটা শেষ হবে। তবে হাওর এলাকায় বৃষ্টির সঙ্গে বজ্রপাতের কারণে কৃষকদের সতর্ক থাকার জন্য প্রশাসনের পক্ষ থেকে মাইকিং করা হয়েছে।’
আবহাওয়া অধিদপ্তরের ভারী বর্ষণের পূর্বাভাস : আবহাওয়া অধিদপ্তরের পাশাপাশি বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্রও সম্প্রতি ভারতের উজানে ভারী বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস দিয়েছে। এতে সপ্তাহব্যাপী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনার কথা বলা হয়েছে। এরই মধ্যে বৃষ্টিও শুরু হয়েছে। সবচেয়ে বেশি হাওর অধ্যুষিত জেলা সুনামগঞ্জের কৃষি বিভাগ আগাম বন্যা ও পাহাড়ি ঢলের আশঙ্কায় পাকা ধান দ্রুত কাটতে কৃষকদের পরামর্শ দিয়েছে। উজানে ভারী বৃষ্টির এমন পূর্বাভাসে সুনামগঞ্জের বিভিন্ন হাওরের কৃষকরা চিন্তিত। কারণ ধান এখনো পুরোপুরি পাকেনি। শান্তিগঞ্জ উপজেলার পাখিমারা হাওরের কৃষক বলেন, ‘আমি এবার চার একর জমিতে ধান আবাদ করেছি। আগাম জাতের এক একরের ধান পেকে যাওয়ায় কেটে ঘরে তুলেছি। বাকি ধান পাকতে আরো সপ্তাহ খানেক সময় লাগবে। এখন বৃষ্টিপাতের যে খবর শুনছি তাতে ভয়ে আছি।’ দেখার হাওরের কৃষক বলেন, ‘আমার জমির ধান এখনো পাকেনি। ডিসি সাহেব (জেলা প্রশাসক) ধান কাটতে বলেছেন। এখন আমি কি কাঁচা ধান কাটব? ভারি বৃষ্টিপাত হলে তো আমরা মাঠে মারা যাব। একদিকে বাঁধভাঙা, অন্যদিকে জলাবদ্ধতা নিয়ে দুশ্চিন্তায় আছি।’ সুনামগঞ্জ জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক বলেন, ‘যেহেতু আবহাওয়া খারাপ হওয়ার পূর্বাভাস রয়েছে, তাই কালক্ষেপণ না করে কৃষকদের দ্রুত ধান কাটার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। শুধু কৃষি নয়, হাওরসংশ্লিষ্ট সব দপ্তরের ছুটি বাতিল করা হয়েছে।’
এখন পর্যন্ত সুনামগঞ্জ সদর ও শান্তিগঞ্জ উপজেলার বিভিন্ন হাওরে বেশির ভাগ জমির ফসল কাঁচা অবস্থায় রয়েছে। কিছু জমিতে ধান কাটা হলেও তার পরিমাণ খুবই কম। শান্তিগঞ্জের পশ্চিম বীরগাঁও ইউনিয়ন পরিষদের বলেন, ‘আমার ইউনিয়নে এখনো ৯০ ভাগ জমির ফসল কাঁচা। পুরোপুরি ধান পাকতে আরও সময় লাগবে। এখন বৃষ্টিপাত হলে কৃষকরা ক্ষতিগ্রস্ত হবেন।’ দিরাই উপজেলার তাড়ল গ্রামের রাজন চৌধুরী ১০ একর জমিতে ধান লাগিয়েছেন এবার। আগাম জাতের ধান কাটা শুরু করেছেন, আবহাওয়া ভালো থাকলে দ্রুত সময়ে বাকি ধানও কাটা শেষ করতে পারবেন বলে জানান। ধল গ্রামের আব্দুল খালিক বলেন, ‘শ্রমিকের কিছুটা সংকট রয়েছে। তবে অনেক শ্রমিক এসেছেন। শুধু আবহাওয়াটা খারাপ না হলে আশা করা যায় দ্রুত ধান তোলা যাবে।’ সামারচর গ্রামের বাসিন্দা অরবিন্দ বলেন, ‘বৃহস্পতিবার রাতেও বৃষ্টিপাত হয়েছে। তবে সব এলাকায় নয়। আবহাওয়া অফিসের পূর্বাভাস সত্য হলে ধান তোলার ব্যাপারে ঝুঁকি আছে।’
পানি উন্নয়ন বোর্ডের বার্তা : ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাসে আতঙ্কিত না হয়ে দ্রুত ধান কাটার ব্যবস্থা করার পরামর্শ দিয়েছেন পানি উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তারা। এ বিষয়ে সংস্থাটির সুনামগঞ্জের নির্বাহী প্রকৌশলী মামুন হাওলাদার বলেন, ‘আগামী এক সপ্তাহ স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি বৃষ্টিতে হাওরের নিচু এলাকার জমির ধান নষ্ট হতে পারে। আতঙ্কিত না হয়ে দ্রুত ধান কাটার ব্যবস্থা করতে হবে।’
জেলা প্রশাসনের বার্তা : এক ফসলি এসব জমির দিকে সারা বছর তাকিয়ে থাকেন হাওর অধ্যুষিত সাত জেলার কৃষক। তবে সবচেয়ে বেশি ধান হয় নেত্রকোনা ও সুনামগঞ্জ জেলায়। তবে ১৫ থেকে ২৫ এপ্রিল পর্যন্ত ধান কাটার চূড়ান্ত মুহূর্তে বৃষ্টিপাত ও উজানের ঢলের আশঙ্কা রয়েছে। তাই দ্রুত ধান কাটার তাগিদও দিয়েছে জেলা প্রশাসন।
শেষ কথা: কৃষি ক্যালেন্ডার অনুসারে এপ্রিল-মে মাসেই বোরো ধান কাটার সময় এবং বন্যা শিলাবৃষ্টির ঝুঁকিতে কৃষকরা দিন কাটায়; কিন্তু এ বছরটি ব্যতিক্রম বিশেষত: অনাবৃষ্টির কারণে বোর ধানসহ সব কৃষি উৎপাদনের ওপর এর প্রভাব লক্ষণীয়। অন্যান্য বছরের মতো এবার কৃষিশ্রমিকের ঘাটতির সম্ভাবনা রয়েছে ।এখন করণীয় হলো- ১. বোরো ফসল কাটার সময় কৃষিশ্রমিকের ঘাটতি মেটাতে যান্ত্রিক হারভেষ্টরের সংখ্যা বাড়াতে হবে ; ২. ধান কাটা ও মাড়াইয়ের যন্ত্র গত বারের মতো এবারও সরকার প্রস্তুত রেখেছে এবং আগ্রহী উদ্যোক্তাদের ক্রেডিটসহ প্রশিক্ষণেরও ব্যবস্থা করছে। ২০২০ সাল থেকে বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও কোভিড-১৯-এর প্রাদুর্ভাব দেখা দেওয়ায় দেশের স্বাভাবিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বিঘ্নিত হচ্ছে। এর ফলে অন্যান্য খাতের মতো কৃষি খাতও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে কৃষি খাতে স্বল্পসুদে ঋণ সরবরাহ নিশ্চিত করে কৃষকদের স্বাভাবিক উৎপাদনশীল কার্যক্রমে ফিরিয়ে আনাসহ কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে এ খাতে ঋণ/বিনিয়োগের সুদ/মুনাফা হার হ্রাস করা প্রয়োজন। সরবরাহ পরিস্থিতি বাড়াতে এরই মধ্যে সরকারিভাবে চাল আমদানি করা হচ্ছে। এ ছাড়া বেসরকারিভাবে চাল আমদানিতে উৎসাহিত করা হচ্ছে। আমরা আশা করছি—সব বাধা দূরীভূত হবে এবং আমরা আমাদের পূর্বের রেকর্ড ধরে রাখতে সক্ষম হব ধান-চাল উৎপাদনে- সেটাই হোক আমাদের অঙ্গীকার।
লেখক : অধ্যাপক (অর্থনীতি), সাবেক পরিচালক, বার্ড (কুমিল্লা), সাবেক ডিন (ব্যবসায় প্রশাসন অনুষদ) ও সিন্ডিকেট সদস্য, সিটি ইউনিভার্সিটি, ঢাকা

আঠারো ও উনিশ শতকের ক্রান্তিকালে বাংলার সমাজে চলছিল গভীর টানাপড়েন- বহিরাগত শাসনের নিপীড়ন, অভ্যন্তরীণ শোষণের বেদনা আর নিজস্ব পরিচয় নিয়ে এক অন্তর্গত সংগ্রাম। এই সময়েই আত্মপরিচয়, সংস্কৃতি ও অধিকারবোধ নিয়ে ভাবতে শুরু করেন বিদগ্ধ সমাজচিন্তক ও রাজনৈতিক নেতারা। জাতীয় রাজনীতির কোলাহলে যখন অধিকাংশ নেতা ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন ও সাংবিধানিক প্রশ্নে ব্যস্ত, তখন শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক স্বীয় রাজনৈতিক প্রজ্ঞা দিয়ে একেবারে শিকড় থেকে বদল আনার কথা চিন্তা করেছেন। তিনি বাঙালি সংস্কৃতির বহুমাত্রিক ঐতিহ্যে- ভাষা, সাহিত্য, ধর্ম, আচার-অনুষ্ঠানের পাশাপাশি কৃষিনির্ভর জীবনের সংমিশ্রণে খুঁজতে চেয়েছেন এক পরিপূর্ণ জাতিসত্তা। ফলে স্বাধীনতা সংগ্রাম ও জাতীয় রাজনীতিতে তিনি ছিলেন জমিদারি শোষণ ও নিপীড়নের শিকার, ঋণের জালে বন্দি নিঃস্ব ও নিরন্ন, অধিকারবঞ্চিত প্রান্তিক কৃষকের কণ্ঠস্বর।
শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক ১৮৭৩ সালের ২৬ অক্টোবর তৎকালীন বরিশাল জেলার রাজাপুর উপজেলার সাতুরিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। জন্মসূত্রে এক মধ্যম জমিদার পরিবারে বেড়ে ওঠায় ফজলুল হক শৈশব থেকেই প্রান্তিক মানুষের জীবনের কষ্ট, অবহেলা ও বঞ্চনাকে খুব কাছ থেকে দেখেছেন। আর এ কারণেই পরবর্তীতে কৃষক-শ্রমিকের পক্ষে দাঁড়ানো তার রাজনীতির মৌলিক ভিত্তি হয়ে ওঠে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মতো অমানবিক জমি ব্যবস্থার নির্মমতা তাকে আরও ক্ষুব্ধ করে তোলে। কেননা হাল টেনে, ঘাম ঝরিয়ে ফসল ফলানো কৃষকশ্রেণিই ছিল অত্যাচারের মূল শিকার। তাদেরই ওপর চাপানো হতো অযৌক্তিক হারে খাজনা। সেই খাজনা দিতে না পারলে ছিল জমি হারানোর ভয়। অন্যদিকে জমিদাররা নিজেদের আরাম-আয়েশের খরচ জোগাতে কৃষকদের রক্ত-ঘামে অর্জিত ফসলে ভাগ বসাতো। আর কৃষকদের ভাগ্যে জুটতো অনিশ্চয়তা, অনাহার আর ঋণের জাঁতাকলে পিষ্ট হয়ে বেঁচে থাকা। ফলে জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ ও মহাজনি শোষণ বন্ধ করার লক্ষ্যে শেরে বাংলার নেতৃত্বে বাংলায় শক্তিশালী প্রজা আন্দোলন গড়ে ওঠে। এই প্রেক্ষাপটে ১৯২৯ সালে তিনি গড়ে তোলেন ‘নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতি’ যা পরবর্তীতে ১৯৩৬ সালে ‘কৃষক প্রজা পার্টি’ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। যা ছিল কৃষকদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় প্রথম বাস্তব পদক্ষেপ। তার নেতৃত্বে দলটি কৃষকদের সমস্যাগুলো সামনে এনে শুরু করে বাস্তবধর্মী পদক্ষেপ।
১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের ফলে ১৯৩৭ সালে ব্রিটিশ শাসিত প্রদেশগুলোতে প্রথমবারের মতো নির্বাচনের আয়োজন হয়। বিপুল জনসমর্থনে অবিভক্ত বাংলার প্রথম মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচিত হন এ কে ফজলুল হক। দায়িত্ব নেওয়ার পর তিনি একের পর এক সংস্কার শুরু করেন। বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারি প্রথা উচ্ছেদের বিষয়টি তদন্ত করে দেখার জন্য ১৯৩৮ সালে তিনি ‘ফ্লাউট কমিশন’ গঠন করেন। জমিদাররা যাতে বিনা কারণে ইচ্ছেমতো জমির প্রকৃত চাষি অর্থাৎ প্রজাকে উচ্ছেদ করতে না পারে, সেই জন্য তিনি ওই বছরই বঙ্গীয় প্রজাসত্ত আইন সংশোধন করে জমিদারের অধিকার হ্রাস এবং কৃষকদের অধিকার বৃদ্ধি করেন। এটি ছিল জমিদার শাসনের বিরুদ্ধে এক সাহসী পদক্ষেপ।
এরপর ১৯৩৫ সালের Bengal Agricultural Debtors Act অনুসারে ১৯৩৮ সালে তিনি গঠন করেন ঋণ-সালিশি বোর্ড, যা ছিল কৃষকের ঋণ সমস্যা সমাধানে আদালতের বিকল্প একটি মানবিক পথ। Bengal Agricultural Debtors Act অনুসারে গঠিত এই বোর্ডে স্থানীয় প্রতিনিধিরা সিদ্ধান্ত নিতেন কৃষকের ঋণের ন্যায্য পরিমাণ, অতিরিক্ত সুদ মাফ করে দিতেন, আর সহজ কিস্তিতে ঋণ পরিশোধের সুযোগ তৈরি করতেন। এর ফলে বহু কৃষক ঋণের জাল থেকে মুক্ত হয়ে আবার চাষাবাদ শুরু করতে সক্ষম হন; কিন্তু সবকিছু সহজ ছিল না। জমিদার-মহাজনরা বোর্ডে যেতে কৃষকদের ভয় দেখাত, বাধা দিত। এমনকি ঊর্ধ্বতন ব্রিটিশ প্রশাসনও এই মানবিক প্রচেষ্টাকে সন্দেহের চোখে দেখত। কিন্তু শেরে বাংলার অদম্য নেতৃত্বে এই বোর্ড অনেক কৃষকের জীবনে আশার আলো জ্বালাতে সক্ষম হয়।
ব্রিটিশ শাসনামলে বাংলার কৃষিতে চরম পশ্চাৎপদতা লক্ষণীয় ছিল। আধুনিক কৃষি শিক্ষা, গবেষণা বা প্রযুক্তির কোনো ব্যবস্থাই ছিল না। ফলে ফসলের উৎপাদনশীলতা ছিল কম এবং কৃষকের জীবন ছিল দুর্বিষহ। তাই মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে ক্ষমতায় এসে শেরে বাংলা কৃষকের উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দেন। তার প্রত্যক্ষ উদ্যোগে ১৯৩৮ সালে ঢাকার শেরেবাংলা নগরে প্রতিষ্ঠিত হয় বেঙ্গল এগ্রিকালচার ইনস্টিটিউট, যা ছিল পূর্ব বাংলার প্রথম কৃষি শিক্ষার উচ্চতর প্রতিষ্ঠান। এর মূল লক্ষ্য ছিল আধুনিক কৃষি শিক্ষা প্রদান, গবেষণার সুযোগ সৃষ্টি এবং কৃষককে আধুনিক প্রযুক্তি ও জ্ঞানে সমৃদ্ধ করা। যা ছিল বাংলার কৃষকের প্রতি একটি কার্যকর দায়বদ্ধতার প্রকাশ। এই ইনস্টিটিউটই পরবর্তীতে ২০০১ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা লাভ করে শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় নামে যাত্রা শুরু করে, যা আজও বাংলাদেশের কৃষি শিক্ষার অন্যতম মূল স্তম্ভ হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে।
১৯৪০ সালে তিনি প্রণয়ন করেন আরেকটি যুগান্তকারী আইন- Bengal Moneylenders Act। এই আইন মহাজনদের লাগাম টানার প্রথম বড় পদক্ষেপ। এতে ঋণের সর্বোচ্চ সুদের হার ৬-৯ শতাংশ নির্ধারণ করা হয়, মৌখিক ঋণের বদলে লিখিত হিসাব বাধ্যতামূলক করা হয়, এবং অতিরিক্ত সুদের ভিত্তিতে মামলা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। মহাজনদের লাইসেন্স বাধ্যতামূলক করার মাধ্যমে তাদের শোষণক্ষমতা সীমিত করা হয়। যদিও অনেক মহাজন পরে ভুয়া হিসাব বা ‘কাঁচা খাতা’ দেখিয়ে আইনকে পাস কাটানোর চেষ্টা করে, তবুও এই আইন স্পষ্ট বার্তা দেয়- রাষ্ট্র এবার কৃষকের পক্ষে দাঁড়িয়েছে।
১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের পর পূর্ববাংলা একটি নতুন ভূরাজনৈতিক বাস্তবতার মুখোমুখি হয়। এ সময় শেরে বাংলা কৃষিনীতি এবং কৃষকের উন্নয়নকে সর্বাগ্রে বিবেচনায় নেন। তিনি পূর্ববাংলার কৃষিনির্ভর সমাজের স্বার্থরক্ষায় নতুন প্রশাসনিক কাঠামোর প্রস্তাব দেন, যার মূল লক্ষ্য ছিল কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ থেকে কৃষিকে বের করে এনে স্থানীয় বাস্তবতা ও প্রয়োজনের ভিত্তিতে নীতিনির্ধারণ করা। এই কাঠামোতে গ্রামাঞ্চলে কৃষি সম্প্রসারণ, প্রযুক্তি হস্তান্তর, কৃষকদের সরাসরি অংশগ্রহণ এবং স্থানীয় পর্যায়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। তার এই পদক্ষেপ পূর্ববাংলার কৃষিনীতিকে একটি স্বাধীন ও কার্যকর ভিত্তি দেয়, যা পরবর্তীতে কৃষি গবেষণা, সেচব্যবস্থা এবং খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির পথে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।
অন্যদিকে, ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট সরকারের অধীনে ভূমি সংস্কার ও কৃষি উন্নয়নকে শেরে বাংলা সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেন। সেই কারণে তিনি জমির সর্বোচ্চ মালিকানা সীমা নির্ধারণ, খাজনা হ্রাস, বর্গাদারদের সুরক্ষা এবং কৃষকদের জন্য ঋণসুবিধা নিশ্চিতকরণের মতো পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। এই সংস্কার কর্মসূচি সামন্ততান্ত্রিক জমিদার প্রথাকে দুর্বল করে কৃষকের অধিকার প্রতিষ্ঠায় এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে।
শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকের কৃষি ও কৃষক-কেন্দ্রিক রাজনীতি ও মানবিক রাষ্ট্রচিন্তা ছিল এক ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত, যা আজও আমাদের জন্য দিকনির্দেশনা হয়ে ওঠে। তিনি বিশ্বাস করতেন, রাষ্ট্র তখনই শক্তিশালী হয়, যখন তার সবচেয়ে প্রান্তিক নাগরিকও ন্যায় ও মর্যাদা নিয়ে বাঁচতে পারে। কৃষকদের শুধু উৎপাদক নয়, রাষ্ট্রের দায়িত্ববান ও অধিকারপ্রাপ্ত নাগরিক হিসেবে প্রতিষ্ঠা দেওয়ার জন্য তার যে অগ্রণী ভূমিকা, তা বাংলার ইতিহাসে একটি গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। ১৯৬২ সালের ২৭ এপ্রিল ৮৮ বছর বয়সে এই কিংবদন্তি নেতার জীবনাবসান ঘটে; কিন্তু কৃষকের অধিকার প্রতিষ্ঠায় তার ত্যাগ, সাহস ও দূরদর্শিতা আজও আমাদের অনুপ্রেরণা দিয়ে যায়।
শেরে বাংলার যুগান্তকারী পদক্ষেপগুলোর সবই ছিল এক অর্থবহ সামাজিক চুক্তির অংশ, যেখানে কৃষকের কষ্টকে রাষ্ট্রীয় নীতিতে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছিল। জমিদার-মহাজন ও ঔপনিবেশিক শোষণের চক্রে পিষ্ট কৃষকের পক্ষে দাঁড়িয়ে তিনি যেভাবে কৃষিবান্ধব প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে তোলার চেষ্টা করেছেন, তা আজও আমাদের সামনে এক অনুকরণীয় পথ।
তবে দুঃখজনক হলেও সত্য, আজকের বাংলাদেশেও শেরে বাংলার স্বপ্নের সেই কৃষকবান্ধব রাষ্ট্র বাস্তবায়িত হয়নি। এখনো আমরা দেখি- কৃষক কখনো নিজের ফসলের ন্যায্যমূল্য না পেয়ে ক্ষোভে নিজ হাতে তা পুড়িয়ে দেন, ন্যায্যমূল্য না পেয়ে অথবা প্রাকৃতিক দুর্যোগে সর্বস্ব হারিয়ে বেছে নেন আত্মহননের পথ। ঋণের দুঃসহ ভারে ক্লিষ্ট হয়ে, সারা জীবন শ্রম দিয়ে উৎপাদন করেও তিনি পান না নিজের প্রাপ্য সম্মান বা সুরক্ষা।
তাই বর্তমান বাস্তবতাকে গভীরভাবে উপলব্ধি করে আমাদের আবারও কৃষিকে জাতীয় উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দুতে তুলে আনতে হবে। যেখানে কৃষক হবে সম্মানিত, স্বনির্ভর এবং ভবিষ্যৎ গঠনে সক্রিয় অংশীদার। এতে বাস্তবায়িত হবে একটি মানবিক, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও কৃষকবান্ধব বাংলাদেশের স্বপ্ন।
অধ্যাপক ড. মো. আব্দুল লতিফ
উপাচার্য, শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

বর্তমান অত্যাধুনিক যুগে জীবন চলার পথে যেকোনো কাজেই এগিয়ে যান না কেন, আঙ্গুলের ছাপ ছাড়া প্রশ্নবিদ্ধসহ প্রতিবন্ধকতায় সম্মুখীন হবেন। আর আপনিই যে আপনি, তা কেবল আঙ্গুলের ছাপেই শনাক্তপূর্বক বলে দিবে। মজার ব্যাপার হলো যে আপনার আঙ্গুলের ছাপ শুধুই আপনার; সারা পৃথিবীতে প্রায় সাড়ে ৮০০ কোটি মানুষের ছাপের সঙ্গে কোনো মিল হবে না। শুধু তাই নয়, সৃষ্টির গোড়া থেকে শুরু করে যত মানুষ এই ধরায় এসেছেন এবং পৃথিবী ধ্বংস হওয়ার আগ পর্যন্ত যত মানুষ আসবেন, কারও আঙ্গুলের ছাপের সঙ্গে মিল তথা এক হবে না। আঙ্গুলের এই ব্যতিক্রম ছাপের ব্যাপারে এখন বিজ্ঞানীরা জোর গলায় বললেও এ কথাটি ১৪০০ বছর আগেই পবিত্র কোরআন শরিফের সুরা ক্বিয়ামাহ (মক্কায় অবতীর্ণ)-তে উল্লেখ করা হয়েছে। আর যেভাবেই বলি না কেন, আঙ্গুলের ছাপ আল্লাহতায়ালার মহাবিস্ময়কর সৃষ্টি।
এ প্রেক্ষাপটে উল্লেখ্য, বর্তমানে আধুনিক বিজ্ঞান কি বলেছে জানেন? এ ব্যাপারে বিজ্ঞান বলে যে গর্ভাবস্থায় যখন ভ্রূণের মাত্র ১০ সপ্তাহ বয়স, তখন তার আঙ্গুলের ছাপ গঠিত হয়। আর সেটা সারাজীবন একই থাকে; পরিবর্তন হয় না। কোনো দুই ব্যক্তির আঙ্গুলের ছাপ কখনই এক হয় না। এমনকি জমজ ভাই-বোনদের ক্ষেত্রেও না। কিন্তু কেন? এর কারণ মায়ের গর্ভে প্রতিটি শিশুর বেড়ে ওঠার পরিবেশ একেবারেই আলাদা হয়; যা তাদের আঙ্গুলের ছাপের ওপর প্রভাব ফেলে। এ ছাড়া আপনার আঙ্গুলের ছাপে আরও অনেক রহস্য লুকিয়ে আছে? এ ক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে আঙ্গুলের ছাপ কেবল আপনাকে শনাক্ত করবে, তাই নয়। একইসঙ্গে আপনার জ্বিনগত দিক দিয়ে স্বাস্থ্য সম্পর্কিত তথ্য বহন করে। গবেষণায় দেখা গেছে, যাদের আঙ্গুলের ছাপ আঁকা-বাঁকা, তাদের বহুমূত্র ও উচ্চ রক্তচাপের ঝুঁকি বেশি থাকে। এই রকম আরও নানা রোগের চিহ্ন বহন করে থাকে, যা এখনো গবেষণার পর্যায়ে আছে।
এক সময় শুধু অপরাধীকে ধরতে আঙ্গুলের ছাপ ব্যবহার করা হতো। কিন্তু এখন বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে নাগরিকদের পরিচয়ের জন্য; যেমন- আইডেন্টেটি কার্ড ও পাসপোর্ট বইসহ বায়োমেট্রিক্স তথ্য সংরক্ষণ করার ক্ষেত্রে এই ছাপ ব্যবহার করা হয়। তা ছাড়া বাংলাদেশে মোবাইল সিম কিনতে আঙ্গুলের ছাপ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এমনকি, অনেক অফিসে ও ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে পাসওয়ার্ডের পরিবর্তে ফিঙ্গারপ্রিন্ট ব্যবহৃত হচ্ছে। এই আঙ্গুলের ছাপের বিষয়টি আল্লাহর কুদরতের এক অকাট্য প্রমাণ বৈ কিছু নয়। পবিত্র কোরআনে ১৪০০ বছর আগেই আল্লাহতায়ালা এই সৃষ্টির কথা বলেছিলেন। আর এতে এটাই প্রমাণ করে, কোরআন কখনো মানুষের লেখা নয়; বরং মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত এক পরিপূর্ণ জীবনবিধান। ১৬৮৪ সালে সর্বপ্রথম ইংলিশ ফিজিশিয়ান, উদ্ভিদ বিজ্ঞানী এবং অনুবীক্ষণ যন্ত্রবিদ ‘নিহোমিয়া গ্রিউ’ বৈজ্ঞানিক দৈনিক-ই প্রকাশ করে এতে করতল ও আঙ্গুলের ছাপের রহস্যের সংযোগ সূত্রের ধারণার উত্থাপন করেন। তবে ১৬৮৪ সালের পূর্বে ফিঙ্গার প্রিন্ট সম্পর্কে আর কোনো বিজ্ঞানীর আলোকপাতের কথা পাওয়া যায় না। এর পরবর্তীতে দীর্ঘ বিরতির পর ১৮০০ সালের পর ফিঙ্গার প্রিন্ট পুনরায় জোরভাবে বৈজ্ঞানিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং এ ক্ষেত্রে তারা বিভিন্ন আঙ্গিকে গুরুত্ব দেন। এসব বিজ্ঞানীদের মধ্য উল্লেখযোগ্য হলেন, জেন জিন্সেন, সৈয়দ মুহাম্মাদ কাজী আজিজুল হক (খুলনা) ও ব্রিটিশ কর্মকর্তা এওয়ার্ড হেনরি। অবশ্য ১৬৮৫ সালে ডার্চ ফিজিসিয়ান ‘গোভার্ড বিডলো’ এবং ইটালিয়ান বিজ্ঞানী ‘মারসিলো বিডলো’ এনাটমির ওপর বই প্রকাশ করে ফিঙ্গার প্রিন্টের ইউনিক গঠনের ওপর নানা বিষয় তুলে ধরেন। প্রকাশ থাকে, খ্রিষ্টপূর্ব ৫০০ অব্দে ব্যবসায়িক কাজে ছোট ছোট শুকনো কাদার খণ্ডে ব্যাবিলিয়ানদের আঙ্গুলের ছাপ দেওয়ার রীতি প্রচলিত ছিল। আর ১৮৯১ সালে আর্জেন্টিনার হুয়ান ভুসেটিস অপরাধী ধরার পদ্ধতি আবিষ্কার করার মাধ্যমে আধুনিক যুগের আঙুলের ছাপের ব্যবহার শুরু করেন।
কথা প্রসঙ্গে আবার আল কোরআনের কথাই ফিরে আসি। এ ক্ষেত্রে উল্লেখ্য, আল্লাহতায়ালা যখন কোরআনে বারবার বিচার দিবস ও পুনরুত্থানের কথা বলেছেন। তখন কাফিররা এই বলে হাসাহাসি করত যে পচাগলা হাড়গুলোকে কীভাবে একত্রিত করা যাবে? একজনের অস্থির সঙ্গে অন্যজনেরগুলো কি বদল হবে না? এ ব্যাপারে আল্লাহ রাব্বুল আল আমিন প্রতি-উত্তরে বলেছেন, ‘মানুষ কি মনে করে যে আমি তার অস্থিসমূহ একত্রিত করতে পারব না? বরং আমি তার অঙ্গুলিগুলোর ডগা পর্যন্ত সঠিকভাবে সন্নিবেশিত করতে সক্ষম’ (আল কিয়ামাহ, আয়াত ৩-৪)। বস্তুত এখানে মহান রব ফিঙ্গার প্রিন্টের সক্রিয়তার ওপর ইঙ্গিত দিয়েছেন। আর আল্লাহতায়ালা কেবল মানুষের অস্থিতে মাংস পরিয়েই উত্থিত করবেন না; বরং এমন নিখুঁতভাবে মানুষকে পুনরায় জীবিত করবেন, যেমন- জীবদ্দশায় তার আঙ্গুলের সূক্ষ্ম রেখা পর্যন্ত সুবিন্যস্ত ছিল। এখানে এটাই ইঙ্গিত করা হয়েছে যে পুনরুত্থানে কত নিখুঁতভাবে পুনরায় মানুষকে হুবহু অবয়ব দেওয়া হবে। কাফিররা বলে গলা পচা অস্থি একজনেরগুলোর সঙ্গে অন্যজনেরগুলো কি মিশ্রিত হবে না? এ ক্ষেত্রে আল্লাহ বুঝিয়ে দিয়েছেন যে অস্থি মিশ্রিত হওয়া তো দূরে থাক; বরং নিখুঁতভাবে তিনি মানুষকে পুনরুত্থিত করবেন।
আসলে যেভাবেই বলি না কেন, ফিঙ্গার প্রিন্ট প্রকারান্তরে ডেটা ব্যাংক বলে অভিহিত। কেননা জ্বিনের মধ্য সন্নিবেশিত প্রায় সব বৈশিষ্ট্য, শুধু শারীরিক গঠনই নয় বরং চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য পর্যন্ত আঙ্গুলের ছাপে এনকোড করা থাকে। তাই আল্লাহ এখানে কাফিরদের জবাব ও জ্ঞানীদের জন্য নিদর্শন দিয়েছেন যে শুধু মাত্র আঙ্গুলের ডগার প্রিন্ট দিয়ে যদি একটি মানুষের সম্যক বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করা সম্ভব হয়। তবে প্রত্যেক মানুষকে তার নিজের অস্থি দিয়ে পুনর্বিন্যস্ত করা কোনো ব্যাপারই না। এ সূত্র ধরে হয়তো অনেকেই বায়োমেট্রিকস বায়োলজিক্যাল ডেটা পরিমাপ এবং বিশ্লেষণ করার প্রযুক্তি সম্পর্কে অবহিত আছেন। এখানে গ্রিক শব্দ ইওঙ, যার অর্থ জীবন বা প্রাণ এবং গবঃৎরপ হলো পরিমাপ করা। মূলত বায়োমেট্রিকস এমন একটি প্রযুক্তি, যেখানে কোনো ব্যক্তির গঠনগত এবং আচরণগত বৈশিষ্ট্যের ওপর ভিত্তি করে অদ্বিতীয়ভাবে চিহ্নিত বা শনাক্ত করা হয়। এ ক্ষেত্রে ফিঙ্গার প্রিন্টের ব্যাপারে আগেই উল্লেখ করেছি, একজনের আঙ্গুলের ছাপ বা টিপ-সই অন্য কোনো মানুষের সঙ্গে মিল নেই। আর এটি মাথায় রেখে প্রথমেই আঙ্গুলের ছাপ ডেটাবেইসে সংরক্ষণ করা হয় এবং পরবর্তী সময়ে ফিঙ্গার প্রিন্ট রিডারের মাধ্যমে আঙ্গুলে ছাপ ইনপুট নিয়ে ডেটাবেইজে সংরক্ষিত আঙ্গুলের ছাপের সঙ্গে তুলনাপূর্বক যেকোনো ব্যক্তিকে চিহ্নিত করা হয়। আসলে ফিঙ্গার প্রিন্ট রিডার হচ্ছে বহু ব্যবহৃত একটি বায়োমেট্রিক ডিভাইস, যার সাহায্যে মানুষের আঙ্গুলে ছাপ বা টিপসইগুলো ইনপুট হিসেবে গ্রহণ করে, তা পূর্ব থেকে সংরক্ষিত আঙ্গুলের ছাপ বা টিপসইয়ের সঙ্গে মিলিয়ে পরীক্ষা করা হয়ে থাকে। তবে যারা দৈহিকভাবে আঙ্গুলের কাজ করেন, সে ক্ষেত্রে রেখাগুলো মিলে বা মুছে গেলে, এই পরীক্ষায় জটিলতার কথা উড়িয়ে দেওয়া যায় না।
উপর্যুক্ত বর্ণনার প্রেক্ষিতে এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না, আঙ্গুলের ছাপ আল্লাহতায়ালার মহাবিস্ময়কর সৃষ্টি।
লেখক: বিশিষ্ট গবেষক, অর্থনীতিবিদ এবং লেখক হিসেবে মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সম্মাননা ও পদকপ্রাপ্ত।

স্বাধীনতার ঘোষক শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ছিলেন বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ ও বহুদলীয় গণতন্ত্রের প্রবক্তা। তার ১৯ দফা কর্মসূচি বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদের মূল তন্ত্র হিসেবে স্বীকৃতি ছিল। ১৯ দফাতেই স্বনির্ভর বাংলাদেশের বিষয়টি উল্লেখ ছিল। তার আমলে জনপ্রিয় খালকাটা কর্মসূচি চালু করে ‘তলাবিহীন ঝুড়ির’ অপবাদ থেকে দেশকে শস্য ভাণ্ডারে রূপান্তরিত করে। তাইত জিয়া অল্পদিনেই জনগণের জনপ্রিয় নেতা হতে সক্ষম হয়েছিল। সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন দেশনেত্রী খালেদা জিয়া জাতির ক্রান্তিলগ্নে জনগণের সামনে নিয়ে আসেন ভিষণ ২০৩০। এরই আলোকে ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সমন্বয়ে ও আরও সুপরিসরে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও ভরসা হিসেবে সমাদৃত হয়েছে রাষ্ট্র মেরামতের লক্ষ্যে তারই ৩১ দফা কর্মসূচি।
তার ৩১ দফা কর্মসূচির মাধ্যমে অনেক জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী দলকে একই প্ল্যাটফর্মেও আনতে সক্ষম হয়েছে। ইতোমধ্যে ‘সবার আগে বাংলাদেশ’ এ দর্শন নিয়ে দেশে অনুষ্ঠিত কনসার্টগুলো অন্যমাত্রা এনে দিয়েছে। সবার আগে বাংলাদেশ এই টাইটেলের মাধ্যমে দেশকে ভালোবাসার কথা মমত্ববোধের কথা যেন ধ্বনিত হচ্ছে। তার এ তত্ত্বের মাধ্যমে যেন আমরা শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের সেই বিশেষ বাক্যটি যেন উচ্চারিত হচ্ছে- ‘ব্যক্তির চেয়ে দল বড় আর দলের চেয়ে দেশ বড়।’
স্বৈরাচারী শেখ হাসিনা সরকার ১৭ বছরে দেশের রাষ্ট্রের এমন কোনো খাত নেই যেখানে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেননি। গণতন্ত্রকে হত্যা করেছে মানুষের ভোটের অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে। ছাত্র-জনতার দুর্বার আন্দোলনের মুখে শেখ হাসিনা পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। সেই অবস্থায় দেখতে পাই তারেক রহমানের ভূমিকা। দৃঢ় কণ্ঠে তার কর্মীদের ধৈর্যধারণ ও প্রতিহিংসা পরিহার করার জন্য আহ্বান জানান। তার আহ্বানে বেশ সাড়া মেলে। যেহেতু রাষ্ট্রের সব কাঠামো ধ্বংস হয়ে গেছে তা মেরামত করার আহ্বান জানিয়েছেন তারেক রহমান। মেরামত করার লক্ষ্য নিয়ে জনগণের সামনে গবেষণার ফসল ৩১ দফা কর্মসূচি পেশ করেছেন। তিনি এ ৩১ দফা কর্মসূচি নিয়ে এরই মধ্যে প্রশিক্ষণ শুরু করেছেন। ওয়ার্ড পর্যায়, ইউনিয়ন, পৌরসভা, থানা এবং জেলাপর্যায়ে ৩১ দফার কর্মসূচির প্রশিক্ষণ চলছে। অনেক ক্ষেত্রে তারেক রহমান ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে রাতদিন মিটিং-এ অংশগ্রহণ করে দিক-নির্দেশনা দিচ্ছেন। কর্মীদের প্রতিটি ঘরে ঘরে ৩১ দফার কর্মসূচির বিষয়টি জানানোর জন্য আহ্বান করা হচ্ছে।
রাষ্ট্র কোনো ব্যক্তির ইচ্ছা-অনিচ্ছার ফসল নয় বরং রাষ্ট্র হলো আপামর জনতার আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন। রাজা চতুর্দশ লুই বলেছিলেন ‘আমিই রাষ্ট্র’। এই আমিত্ববোধের জন্য সেই চতুর্দশ লুইকে প্রাণ দিতে হয়েছিল গিলোটিনে। স্বৈরশাসক শেখ হাসিনা ও নিজেকে মনে করতেন তিনিই বাংলাদেশ; কিন্তু গণভবনের পেছনের দরজা দিয়ে তাকেও পালিয়ে বাঁচতে হয়েছে। স্বৈরাচার এরশাদকেও এক সময় ক্ষমতা ত্যাগ করতে হয়েছে। বিএনপি ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান মনে করেন ৩১ দফা বাস্তবায়নের ভেতর দিয়ে বাংলাদেশের মালিকানা হবে দেশের সব জনগণের এবং যে রাষ্ট্রব্যবস্থা পরিচালিত হবে ন্যায্যতা ও সাম্যের ভিত্তিতে এবং সব মানুষের অংশগ্রহণের ভেতর দিয়ে। তারেক রহমান তার প্রতিটি বক্তব্যে বারবার বলেছেন দলীয় নেতা-কর্মীকে জনগণের মনকে জয় করতে হবে আর জনগণের মন জিতে নেওয়ার ভেতর দিয়েই জনগণের দলে পরিণত হতে হবে। তিনি মনেপ্রাণে চান বিএনপি যেন জনগণের দল হয়। তাই তো বলেন, মনে রাখতে হবে আগামীর বাংলাদেশ হবে জনগণের ইচ্ছার প্রতিফলনের ভেতর দিয়ে একটি উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি ভিত্তিমূল হিসেবে কাজ করবে বহুল কাঙ্ক্ষিত ৩১ দফা।
তারেক রহমান মনে করেন তার প্রতি তার পরিবার ও দলীয় নেতা-কর্মীর ওপর যে অত্যাচার ও নির্যাতন হয়েছে সেটির জবাব দিতে ৩১ দফার সফল বাস্তবায়নের কোনো বিকল্প নেই। তিনি মনে করেন ৩১ দফার সফল বাস্তবায়নের ভেতর দিয়ে ভোটের অধিকার আদায় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা এবং সুশাসন নিশ্চিত করতে পারলেই একটি বসবাসযোগ্য আগামীর রাষ্ট্র নির্মাণ করা সম্ভব। অতি সম্প্রতি নিজের একটি বক্তব্যে উল্লেখ করেন তার পিতাকে হত্যা করা হয়েছে তার মাতা দেশনেত্রী খালেদা জিয়াকে সীমাহীন কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে তার কনিষ্ঠ ভাইকে হত্যা করা হয়েছে, তাকে ঠেলে দেওয়া হয়েছে এক নির্বাসিত জীবনে। তিনি বলেছেন এসব ভুলে গিয়ে তিনি ৩১ দফার নিরিখে নির্মাণ করতে চান ভারতের নাগপাশ থেকে মুক্ত একটি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ।
স্বাধীনতার পর থেকেই ভারতীয় আধিপত্যবাদের আগ্রাসনে বাংলাদেশের জনগণ অতিষ্ঠ। গত ১৭ বছরে আওয়ামী শাসনামলে এটি অমন হয়েছিল যে শিল্প ব্যবসা-বাণিজ্য, স্বাস্থ্য খাত, অবকাঠামো উন্নয়নে ভারতের অংশগ্রহণ ছাড়া যেন অকল্পনীয় ছিল। জনগণ এটাকে নেতিবাচক হিসেবে নিয়েছিল। ক্রমান্বয়ে দেশ যেন ভারত নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিল। এরা আমাদের স্থিতিশীলতা গণতন্ত্র বিকাশ অর্থনৈতিক সক্ষমতার ক্ষেত্রে বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়ে দেশের সার্বভৌমত্ব বিপন্নের দিকে ধাবিত হচ্ছিল। আগামীর রাষ্ট্রনায়ক বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের ঘোষিত ৩১ দফা হচ্ছে ভারতীয় আগ্রাসন মুক্ত সেই সার্বভৌম ও স্বনির্ভর বাংলাদেশ গড়ার বীজ যে বাংলাদেশ ছিল শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের আজন্ম লালিত স্বপ্ন।
বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ঘোষিত ৩১ দফার প্রথম দফায় এক যুগান্তকারী ঘোষণা দেওয়া হয়েছে যেখানে বলা আছে ‘প্রতিহিংসা ও প্রতিশোধের রাজনীতির বিপরীতে সব মত ও পথের সমন্বয়ে বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক বৈষম্যহীন সম্প্রীতিমূলক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা হবে।’ বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদে অগ্রগণ্য রেখে সব মত ও পথকে এক সুতোয় গাঁথার কর্মযজ্ঞ ইতোমধ্যে তারেক রহমানের বক্তব্যের ও দেশব্যাপী দেশের মানুষকে ৩১ দফার আলোয় আলোকিত করার নানান কর্মসূচির মধ্যে ইতোমধ্যে দৃশ্যমান হয়েছে।
শিক্ষা সংস্কারের বিষয়টি নিয়ে তারেক রহমানের ভাবনা হলো- আমাদের শিক্ষার মান যাচ্ছেতাই অবস্থা। বিগত সরকার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বৃদ্ধি করেছে কিন্তু শিক্ষার মান বৃদ্ধি করতে পারেনি। ৩১ দফায় শিক্ষার বিষয়ে উল্লেখ আছে, ‘বর্তমানে শিক্ষা ক্ষেত্রে বিরাজমান নৈরাজ্য দূর করে নিম্ন ও মধ্যপর্যায়ে চাহিদাভিত্তিক শিক্ষা ও উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে জ্ঞানভিত্তিক শিক্ষাকে প্রাধান্য দেওয়া হবে। গবেষণায় বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হবে। একই মানের শিক্ষা ও মাতৃভাষায় শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব গড়ে তুলতে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে নিয়মিত ছাত্র সংসদ নির্বাচন দেওয়া হবে। যোগ্য ও দক্ষ মানবিক জনগোষ্ঠী গড়ে তোলার লক্ষ্যে জাতীয় বাজেটে শিক্ষা খাতে জিডিপি ৫ শতাংশ অর্থ বরাদ্দ রাখা হবে। ক্রীড়া উন্নয়নে অর্থ বরাদ্দ পর্যাপ্ত থাকবে। অনৈতিক সংস্কৃতি অগ্রাসন রোধ করা হবে।’ রাষ্ট্র সংস্কারের সঙ্গে বিএনপির ৩১ দফা কর্মসূচি এখানে মিল পাওয়া যায় যেমন- পরপর দুই টার্মের অতিরিক্ত কেউ প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করতে পারবেন না এবং বিদ্যমান সংসদীয় ব্যবস্থার পাশাপাশি বিশেষজ্ঞ জ্ঞানের সমন্বয়ে রাষ্ট্র পরিচালনার লক্ষ্যে দেশের বিশিষ্ট নাগরিক, প্রতিযশা শিক্ষাবিদ, পেশাজীবী রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, সমাজবিজ্ঞানী ও প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তিদের সমন্বয়ে সংসদে ‘উচ্চ কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা’ প্রবর্তন করা হবে। সমাজে দুর্নীতি যেন রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছেয়ে আছে ফ্যাসিবাদী সরকার ব্যাংক লুটের মাধ্যমে, প্রকল্পের অর্থের নয়ছয় করে বিদেশে অর্থ পাচার করেছে। দুর্নীতির ব্যাপারে ৩১ দফা কর্মসূচিতে উল্লেখ আছে- ‘দুর্নীতির ক্ষেত্রে কোনো আপস করা হবে না।বিগত দেড়দশকব্যাপী সংগঠিত অর্থ পাচার ও দুর্নীতি অনুসন্ধান করে একটি শ্বেতপত্র প্রকাশ করা এবং শ্বেতপত্রে চিহ্নিত দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। দেশের বাইরে পাচারকৃত অর্থ ফেরত আনার প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক ও আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। দুর্নীতি দমন কমিশন ও দুর্নীতি দমন আইন সংস্কারের পাশাপাশি পদ্ধতিগত সংস্কারের মাধ্যমে দুদকের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হবে। সংবিধান অনুযায়ী ন্যায়পাল নিয়োগ করা হবে।’
দারিদ্র্য মুক্ত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে দারিদ্র্য বিমোচন না হওয়া পর্যন্ত সুবিধা বঞ্চিত হত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী আরও সম্প্রসারিত করা হবে। শহীদ জিয়া কৃষি খাতকে বেশি অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন ৩১ দফার ক্ষেত্রে এর নমুনা দেখতে পাচ্ছি, যথা: কৃষি পণ্যের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করা হবে। পর্যায়ক্রমে সব ইউনিয়নে কৃষিপণ্যের জন্য সরকারি ক্রয় কেন্দ্র স্থাপন করা হবে। প্রয়োজনে ভর্তকি দিয়ে হলে ও শস্য বিমা, পশু বিমা, মৎস্য বিমা এবং পোলট্রি বিমা চালু করা হবে। কৃষি জমির অকৃষি ব্যবহার নিরুৎসাহিত করা হবে। কৃষি মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতের উন্নয়ন এবং গবেষণার জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কর্মকৌশল প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। এতদসংশ্লিষ্ট রপ্তানিমুখী কৃষি প্রক্রিয়াকরণ শিল্প খাতকে প্রণোদনা দেওয়া হবে। দেশের সম্পদ হলো যুবসমাজ তাদের নিয়ে ও কর্মসূচি আছে, যেমন- যুবসমাজের ভীষণ চিন্তা আকাঙ্ক্ষাকে ধারণ করে আধুনিক যুগোপযোগী যুবউন্নয়ন নীতিমালা প্রণয়ন করা হবে। এক বছরমেয়াদি অথবা কর্মসংস্থান না পর্যন্ত যেটাই আগে হবে শিক্ষিত বেকারদের বেকার ভাতা প্রদান করা হবে। বেকারত্ব দূরীকরণের লক্ষ্যে নানামুখী বাস্তবসম্মত কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে।
জিয়াউর রহমান স্বাধীনতার ঘোষক এবং স্বাচ্ছা মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন। তারই সন্তান তারেক রহমান রাষ্ট্রের দায়িত্ব পেলে দেশেই স্বাধীন সার্বভৌমত্ব সবচেয়ে বেশি সুরক্ষা পাবে। তারই ইচ্ছার প্রতিফলন ৩১ দফা কর্মসূচির মাধ্যমে অর্থনৈতিক মুক্তি বৈষম্যহীন সমাজ গড়তে সহায়ক ভূমিকা রাখবে বলে জাতির প্রত্যাশা।
লেখক:
মিজানুর রহমান
সাবেক ব্যাংকার ও কলামিস্ট

এবারকার এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষার ফল প্রকাশে নেই কোনো উত্তাপ, নেই কোনো আনন্দ কিংবা কিছু অর্জনের সাফল্যগাধা আর উত্তেজনা। আমরা জানি এসএসসি ও এইচএসসির পড়াশোনা এবং ফলাফলের মধ্যে সাধারণত বড় একটি গ্যাপ থাকে।
যারা এসএসসিতে ভালো ফল লাভ করেন তারা সবাই এইচএসসিতে সেভাবে করেন না, অথচ এবার সেই এসএসসির ফলের ওপরেই এইচএসসির ফল তৈরি করতে হয়েছে। অতএব, কোনো কিছু প্রাপ্তির যে আনন্দ সেটি থেকে শিক্ষার্থীরা যেমন বঞ্চিত হয়েছেন তেমনি প্রতিষ্ঠান, অভিভাবক এবং সর্বোপরি দেশ ফল লাভের আনন্দ থেকে বঞ্চিত হলো।
এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষার ফল প্রকাশ উপলক্ষে এবার কোনো কেন্দ্রীয় অনুষ্ঠান হয়নি। নিজ নিজ বোর্ড অফিস থেকে ফল প্রকাশ করা হয়েছে। শিক্ষার্থীরা প্রতিবছরের মতো এবারও এসএমএস, ওয়েবসাইট ও নিজ নিজ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে গিয়ে ফল জেনেছেন। সরকারপ্রধান বর্তমানে প্রধান উপদেষ্টা কিংবা শিক্ষা উপদেষ্টা ফল প্রকাশ অনুষ্ঠানে ছিলেন না। এই আনুষ্ঠানিকতা এবার দেখা যায়নি। তবে, কেন্দ্রীয় নির্দেশনা অনুযায়ী সব বোর্ড একই সময়ে অর্থাৎ সকাল ১১টায় ওয়েবসাইটে ফল প্রকাশ করেছে।
একই সময়ে সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানও ফল পেয়ে গেছে। নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানে ফলাফল টাঙিয়ে দেওয়ার কথাও বলা হয়েছে। শিক্ষাবোর্ডগুলো স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান কিন্তু স্বায়ত্তশাসনের বিশেষ করে প্রশাসনিক ও একাডেমকি বিষয়ে উন্নয়নের জন্য বোর্ডগুলো বোধ করি কোনো ধরনের স্বায়ত্তশাসন ভোগ করে না। এমনকি পরীক্ষার ফল প্রকাশ করার সময়ও দেখা যায় রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ নির্বাহী, শিক্ষামন্ত্রী, শিক্ষাসচিব সবার উপস্থিতিতে ফল প্রকাশ করা হয় যেখানে বোর্ডগুলোর চেয়ারম্যানদের কোনো ভূমিকার উল্লেখ থাকে না বা দেখা যায় না, তারা সর্বদাই তটস্থ থাকেন। সেই ট্রাডিশন থেকে এবার বিষয়টি বেরিয়ে এসেছে, এটিকে সাধুবাদ জানাই।
আমরা জানি, সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এসএসসি বা সমমান পরীক্ষার নম্বরের ভিত্তিতে যা ‘বিষয় ম্যাপিং’ নামে পরিচিত মাঝপথে বাতিল হওয়া এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষার ফল তৈরি করা হয়েছে। এ প্রক্রিয়ায় একজন পরীক্ষার্থী এসএসসিতে একটি বিষয়ে যত নম্বর পেয়েছিলেন, এইচএসসিতে সেই বিষয় থাকলে তাতে এসএসসির প্রাপ্ত পুরো নম্বর বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। আর এসএসসি ও এইচএসসি এবং সমমান পরীক্ষার বিষয়ে ভিন্নতা থাকলে বিষয় ম্যাপিংয়ের নীতিমালা অনুযায়ী নম্বর বিবেচনা করে ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে। এবারের এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষা শুরু হয়েছিল গত ৩০ জুন। মোট পরীক্ষার্থী ছিল ১৪ লাখ ৫০ হাজার ৭৯০ জন। ৭টি পরীক্ষা হওয়ার পর সরকারি চাকরিতে কোটাব্যবস্থা সংস্কারের দাবিতে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। এ পরিস্থিতিতে কয়েক দফায় পরীক্ষা স্থগিত করা হয়। তখন পর্যন্ত ছয়টি বিষয়ের পরীক্ষা বাকি ছিল।
এ ছাড়া ব্যবহারিক পরীক্ষাও বাকি। একপর্যায়ে কোটা সংস্কার আন্দোলন সরকার পতনের এক দফায় রূপ নেয়। ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে ৫ আগস্ট শেখ হাসিনার সরকারের পতন হয়। পরে সিদ্ধান্ত হয়, ১১ আগস্ট থেকে নতুন সময়সূচিতে পরীক্ষা নেওয়া হবে; কিন্তু শিক্ষার্থীদের একাংশের দাবির মুখে অবশিষ্ট পরীক্ষাগুলো বাতিল করে সরকার। আমাদের স্মরণে আছে এইচএসসির ফলাফল প্রকাশের দাবি নিয়ে শত শত পরীক্ষার্থী নজিরবিহীনভাবে ২০ আগস্ট দুপুরে প্রশাসনের কেন্দ্রবিন্দু সচিবালয়ে ঢুকে পড়ে। পরে তাদের প্রতিনিধিদের নিয়ে বৈঠকে বসে শিক্ষা মন্ত্রণালয় অবশিষ্ট পরীক্ষা বাতিলের সিদ্ধান্ত নেয়। পরে সিদ্ধান্ত হয়, এসএসসি বা সমমানের পরীক্ষার নম্বরের ভিত্তিতে (বিষয় ম্যাপিং) হবে মাঝপথে বাতিল করা এইচএসসি বা সমমানেও পরীক্ষার ফলাফল। ইতোমধ্যে যেসব বিষয়ের পরীক্ষা হয়ে গেছে সেগুলোর উত্তরপত্র মূল্যায়ন করে ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে। আর যেসব বিষয়ের পরীক্ষা হয়নি, সেগুলোর ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে এসএসসি বা সমমানের পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে বিষয় ম্যাপিং করে।
এবার এইচএসসি ও সমমানের সব বোর্ডের পাসের গড় হার ৭৭ দশমিক ৭৮ শতাংশ যা গত বছর ছিল ৭৭ দশমিক ৬৪ শতাংশ অর্থাৎ ফল প্রায় একই। নয়টি সাধারণ শিক্ষাবোর্ডে এইচএসসিতে পাসের হার ৭৫ দশমিক ৫৬ শতাংশ যা গতবার ছিল ৭৫ দশমিক ৯ শতাংশ। গতবার মোট জিপিএ-৫ পেয়েছিলেন ৭৮ হাজার ৫২১জন শিক্ষার্থী। এবার এইচএসসিতে ১ লাখ ৩১ হাজার ৩৭৬ জন জিপিএ-৫ পেয়েছেন। এইচএসসি বিএম ভোকেশনালে জিপিএ-৫ পেয়েছেন ৪ হাজার ৯২২ জন। ঢাকা বোর্ডে পাসের হার ৭৯ দশমিক ২১ শতাংশ, রাজশাহী বোর্ডে ৮১ দশমিক ২৪ শতাংশ, দিনাজপুর বোর্ডে ৭৭ দশমিক ৫৬ শতাংশ, বরিশাল বোর্ডে ৮১ দশমিক ৮৫ শতাংশ , সিলেট ৮৫ দশমিক ৩৯ শতাংশ, ময়মনসিংহ ৬৩ দশমিক ২২ শতাংশ, কুমিল্লা ৭১ দশমিক ১৫ শতাংশ। এইচএসসি বিএম-ভোকেশনাল বোর্ডে পাসের হার ৮৮ দশমিক ০৯ শতাংশ, আলিমে প্রতি বছরের মতোই সবার ওপরে, এবারও ৯৩ দশমিক ৪০ শতাংশ কিন্তু কীভাবে তার কোনো সঠিক ব্যাখ্যা আমরা পাই না। আলিমে জিপিএ-৫ প্রাপ্তির সংখ্যা ৯ হাজার ৬১৩ জন।
কতিপয় শিক্ষার্থী শিক্ষাবোর্ডে গিয়ে সবাইকে পাস করিয়ে দেওয়ার একটি দাবি তুলেছেন। তরুণ এসব শিক্ষার্থীর আবেগের কাছে বারবার মাথা নত করা যাবে না কারণ সমাজ, বাস্তবতা, বৈশ্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে শিক্ষায় বারবার এভাবে ছাড় দেওয়া মোটেই ঠিক নয়। শিক্ষার মানের সঙ্গে কোনো আপস নয় আর তাই এখন থেকে কঠোর হতে হবে এবং এ ক্ষেত্রে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। সব জায়গাতেই মেকি, সব জায়গাতেই অনুপযুক্ত লোক, সর্বত্রই ভুয়াদের দাপট থাকলে সমাজ টিকবে না। পরিশ্রম করে যা অর্জন করা হয়, তাই ঠিক। পরিশ্রমের জন্য কেউ কষ্ট করতে চায় না, পড়াশোনা না করেই সবকিছু পেতে চায়। এখানে সমাজের নিয়ন্ত্রণ থাকতে হবে। সাত বিষয়ে নম্বরের ভিত্তিতে মূল্যায়ন করা হলেও ১৩ বিষয়ে সাবজেক্ট ম্যাপিংয়ের মাধ্যমে ফলাফল তৈরি করা হয়েছে অর্থাৎ ১৩ বিষয়ে অটোপাস দেওয়া হয়েছে। তার পরেও লাখো শিক্ষার্থীর নাম অকৃতকার্যের খাতায়। কারণ ৯টি সাধারণ বোর্ড, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে অনুষ্ঠিত পরীক্ষাগুলোতে এবার অনুপস্থিত ছিলেন ৯৬ হাজার ৯৯৭ জন পরীক্ষার্থী। আর বহিষ্কার হন ২৯৭ জন। নিয়মানুযায়ী পরীক্ষায় অনুপস্থিত থাকলে কিংবা বহিষ্কার হলে সামগ্রিক ফলাফল অকৃতকার্য আসে। পরীক্ষার মাধ্যমে যে সাতটি বিষয়ের ফলাফল তৈরি করা হয়েছে, সেখানে কতজন ফেল করেছেন, সেটা জানা প্রয়োজন। সচিবালয়ে একটা অনভিপ্রেত পরিস্থিতির মধ্যে কর্তৃপক্ষকে তাৎক্ষণিক পরীক্ষাগুলো বাতিলের ঘোষণা দিতে হয়েছিল কিন্তু পরীক্ষাগুলো নিতে পারলে ভালো হতো। এসএসসিতে যারা কোনো বিষয়ে অনুত্তীর্ণ হওয়ার কারণে পরবর্তী বছরে আবার পরীক্ষার সুযোগ নিয়েছে সে ফলাফলও নেওয়া হয়েছে। কাজেই চূড়ান্ত ফলাফলে যারা উত্তীর্ণ হবেন না, তারা বঞ্চিত হয়েছে বলার সুযোগ নেই।
এসএসসি এবং এইচএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা উচ্চশিক্ষায় প্রবেশ করেন, প্রকৌশল, মেডিকেল, কৃষিসহ সাধারণ শিক্ষায় তারা প্রবেশ করেন। এই দুই স্তরে দুর্বল থাকার কারণে ভর্তি পরীক্ষায় সমস্যা হওয়ার পরে গোটা শিক্ষাজীবনে তার ছাপ পড়ে এবং পিছিয়ে থাকে আন্তর্জাতিক দৌড়ে। পেশাগত জীবনে যখন প্রবেশ করে তখনও আমরা দেখতে পাই তাদের দুর্বলতার চিত্র। যে কাজে যান তাদের মধ্যে নগন্য সংখ্যক পেশায় প্রকৃত পেশাদারিত্বের ছাপ রাখতে পারেন, অধিকাংশ সময়ই তারা ভুল, দুর্বল সিদ্ধান্ত ও অপরিপক্ব সিদ্ধান্ত দিয়ে থাকেন। সেজন্য জাতিকে অনেক ভুগতে হয়। সেখান থেকে ওপরে ওঠার জন্য অবৈধ সিঁড়ি ব্যবহার করেন।
পেশিশক্তি, রাজনীতির দুষ্টশক্তি ও চক্র ব্যবহার করেন যা পেশাদারিত্ব থেকে বহু দূরে। সারাজীবন চলতে থাকে এর ফল। এখন উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো যাতে কোনো ধরনের কম্প্রোমাইজে না আসে সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে। এই সংক্ষিপ্ত সিলেবাসে পড়া, পরীক্ষা না দিয়ে ফলের প্রকৃত চিত্র প্রদর্শনের জন্য উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর একটি দায়িত্ব রয়েছে। তারা যদি ভর্তি পরীক্ষাটা ঠিকভাবে নেয় তাহলে শিক্ষার্থীরা বুঝতে পারবে তাদের ভুল, জাতি বুঝতে পারবে যে এ ধরনের সংক্ষিপ্ত সিলেবাসের এবং পড়াশোনা না করে অটোপাসে যে কত বড় ক্ষতি হয় সেটি। কাউকে না কাউকে এগিয়ে আসতেই হবে, শিক্ষাকে তো এভাবে চলতে দেওয়া যায় না।
লেখক: শিক্ষা বিশেষজ্ঞ ও গবেষক (সাবেক ক্যাডেট কলেজ, রাজউক কলেজের শিক্ষক, চিফ অব পার্টি ব্র্যাক এডুকেশন এবং কান্ট্রি ডিরেক্টর-ভাব বাংলাদেশ)
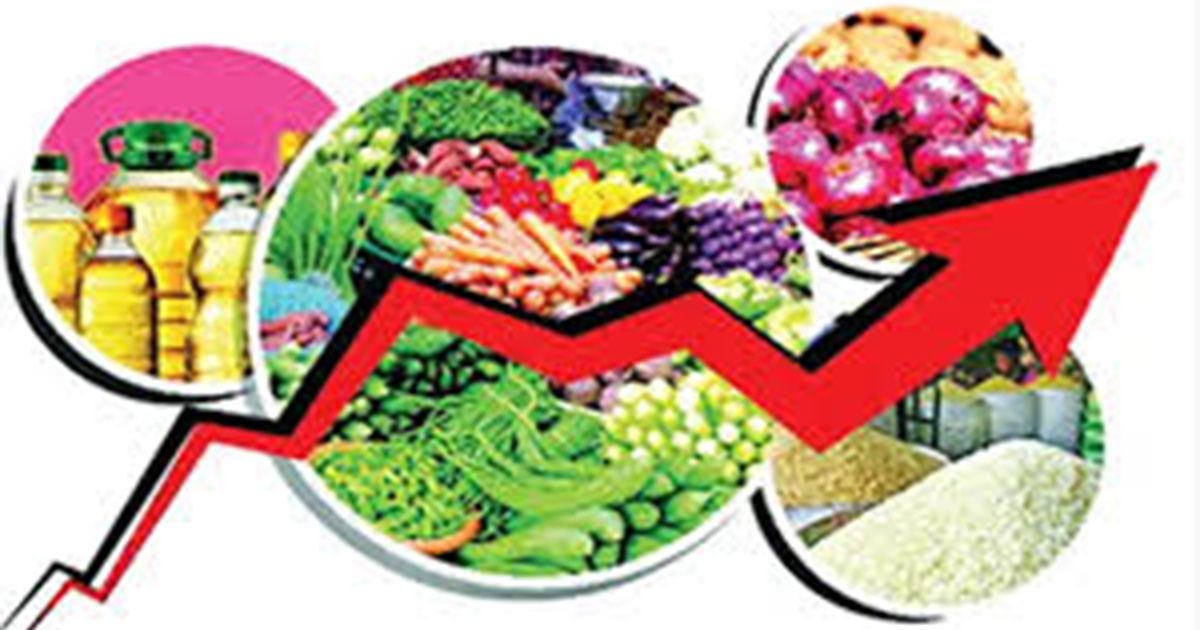
নিত্যপণ্যের দাম নিয়ে স্বস্তিতে আছে বিশ্ববাসী। বিশ্বখাদ্য কর্মসূচি (এফএও) জানিয়েছে, গত ফেব্রুয়ারি মাসে বিশ্বে খাদ্যপণ্যের দাম তিন বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন স্তরে ছিল। যদিও একই সময়ে নিত্যপণ্যের দাম নিয়ে প্রায় দিশাহারা ছিল বাংলাদেশের মানুষ। কারণ এখানে গত তিন বছরে চাল, ডাল, ভোজ্যতেল, আলু, চিনিসহ কয়েকটি পণ্যের দাম ন্যূনতম ১৪ থেকে সর্বোচ্চ ১৪০ শতাংশ পর্যন্ত বেড়েছে। এই বাড়ার চিত্র খোদ সরকারি হিসাবে, বাস্তবে তা আরও বেশি। সম্প্রতি এফএও তাদের মাসিক ‘ফুড প্রাইস ইনডেক্স’ বা খাদ্যপণ্যের মূল্যসূচক প্রকাশ করেছে। সেই সূচকে দেখা যায়, গত ফেব্রুয়ারিতে তিন বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন স্তরে থাকা খাদ্যপণ্যের মূল্য মার্চ মাসে এসে সামান্য বৃদ্ধি পেয়েছে।
ফেব্রুয়ারি মাসে খাদ্য মূল্যসূচক ছিল ১১৭ পয়েন্ট (১০০ পয়েন্ট হচ্ছে ভিত্তি)। আর মার্চ মাসেতা সামান্য বেড়ে হয়েছে ১১৮ পয়েন্ট। ফেব্রুয়ারির খাদ্য মূল্যসূচক ১১৭ পয়েন্টে পৌঁছানোর আগে ২০২১ সালে ফেব্রুয়ারিতে খাদ্য মূল্যসূচক এই স্তরে ছিল। এফএও বলছে, মার্চ মাসে যে বিশ্ববাজারে খাদ্য মূল্যসূচক সামান্য বৃদ্ধি পেয়েছে, এটা মূলত ভোজ্যতেলের বাড়তি চাহিদার কারণেই হয়েছে। তবে এখনো বিশ্ববাজারে বেশির ভাগ পণ্যের দাম কমতির দিকে বলে জানিয়েছে সংস্থাটি।
বিশ্ববাজারের ঠিক উল্টো চিত্র দেখা গেছে বাংলাদেশের বাজারে। বিশ্ববাজারের দোহাই দিয়ে এখানে কয়েক বছর ধরে জিনিসপত্রের দাম লাগামহীন বাড়িয়েছেন আমদানিকারকরা। এরই ধারাবাহিকতায় পাইকারি ও খুচরা ব্যবসায়ীরা বাড়িয়েছেন পণ্যের দাম। রাষ্ট্রায়ত্ত বিপণন সংস্থা টিসিবির ২০২১ সালের তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, ২০২১ সালের ৪ মার্চে সরু চালের কেজিপ্রতি দাম ছিল সর্বোচ্চ ৬৫ টাকা। একই চাল তিন বছর পর ৭৬ টাকায় বিক্রি হয়। দাম বেড়েছে ১৬ দশমিক ৯২ শতাংশ। তিন বছরে খোলা আটার দাম কেজিতে বেড়েছে ৩২ দশমিক ৩৫ শতাংশ। প্যাকেট আটার দাম বেড়েছে ৭১ দশমিক ৫৩ শতাংশ।
এ ছাড়া লুজ সয়াবিন তেলের দাম ২৫ শতাংশ, বোতলজাত সয়াবিনের দাম ১৫ দশমিক ৭১ শতাংশ ও পাম অয়েলের দাম বেড়েছে ২৩ দশমিক ৮১ শতাংশ। বড় দানা ডালের দাম বেড়েছে ৫৭ দশমিক ১৪ শতাংশ। দেশি ডালের দাম বেড়েছে ২৭ দশমিক ২৭ শতাংশ। দেশি পেঁয়াজের দাম বেড়েছে ২৫ শতাংশ আর আমদানি করা পেঁয়াজের দাম বেড়েছে ১৪০ শতাংশ। দেশি রসুনের দাম বেড়েছে ১২৮ দশমিক ৫৭ শতাংশ। আর আমদানি করা রসুনের দাম বেড়েছে ৯১ দশমিক ৬৬ শতাংশ। দেশি আদার দাম বেড়েছে ২২০ শতাংশ। আমদানি করা আদার দাম বেড়েছে ১০৯ শতাংশ।
গরুর মাংসের দাম বেড়েছে ৩০ শতাংশ, ব্রয়লার মুরগির দাম বেড়েছে ৬৬ দশমিক ৬৬ শতাংশ, আলুর দাম বেড়েছে ১২৫ শতাংশ ও চিনির দাম বেড়েছে ১০০ শতাংশ। প্রতিবার দাম বাড়ানোর সময় একেক অজুহাত দেখিয়েছেন ব্যবসায়ীরা। কখনো কোভিড, কখনো ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধ আবার ডলারের দর বাড়া। তবে বাজার বিশ্লেষকরা জানান, যতই তারা যুক্তি দেখান না কেন, এখানে অতিমুনাফালোভী চক্র সক্রিয় থাকার কারণেই মূলত জিনিসপত্রের দাম এত লাগামহীন বেড়েছে। কারণ এ সময়ে আমদানি করা পণ্যের দাম যেমন বেড়েছে, একই তালে দেশে উৎপাদিত পণ্যের দামও বেড়েছে। অথচ এসব পণ্য আমদানিতে ডলার লাগেনি, জাহাজ ভাড়া দিতে হয়নি কিংবা যুদ্ধের কারণে সরবরাহ ব্যবস্থায়ও কোনো বাধা তৈরি হয়নি।
এ বিষয়ে কৃষি অর্থনীতিবিদ সমিতির সাধারণ সম্পাদক বলেন, ‘বাংলাদেশে ডলারের বিনিময় হারের যে অস্থিতিশীলতা, জিনিসপত্রের দাম অসহনীয় করার ক্ষেত্রে এটিকে কারণ হিসেবে দেখানো হচ্ছে। এ ছাড়া সাম্প্রতিক সময়ে আমদানির ঋণপত্র খোলায় সংকটকেও দায়ী করা হয়। স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত পণ্যের দাম বাড়ার পেছনেও বিদ্যুৎ-জ্বালানির দাম বাড়া, আমদানি করা কাঁচামালের দাম বাড়া ও পরিবহনের খরচকে দায় দেওয়া হয়। তবে নিয়ন্ত্রক সংস্থার পদক্ষেপ যথাযথ হলে দাম বাড়া আরও সহনীয় মাত্রায় রাখা যেত। এ সময়ে বাজার নিয়ন্ত্রণে দুর্বলতা ছিল। সরকার জিনিসপত্রের দাম নির্ধারণ করে দিচ্ছে অথচ নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না। তাহলে এ দাম ঠিক করে দেওয়ার অর্থ কী? এটি একটি ভুল পথ।
তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যায়, বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এ সময়ে জিনিসপত্রের দাম সহনীয় পর্যায়ে আছে ভারত, শ্রীলঙ্কা, নেপাল কিংবা ভুটানের মতো প্রতিবেশী দেশগুলোতে। অথচ এ সময়ে ব্যতিক্রম বাংলাদেশ। জিনিসপত্রের অতিরিক্ত দামের কারণে উচ্চ মূল্যস্ফীতিতে পড়েছে বাংলাদেশের অর্থনীতি। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) হিসাব অনুযায়ী, জিনিসপত্রের অতিরিক্ত দামের কারণে ফেব্রুয়ারি মাসে বাংলাদেশের সার্বিক মূল্যস্ফীতি ছিল ৯ দশমিক ৬৭ শতাংশ। জানুয়ারিতে এটি ছিল ৯ দশমিক ৮৬ শতাংশ। বলা যায়, তারও প্রায় এক বছর আগে থেকেই বাংলাদেশে মূল্যস্ফীতির এই উচ্চহার বজায় থাকে।
অথচ এ বছরের জানুয়ারিতে জিনিসপত্রের দাম সহনীয় হওয়ায় ভারতের মূল্যস্ফীতি ছিল মাত্র ৫.১৯ শতাংশ। প্রায় দেউলিয়া হয়ে যাওয়া শ্রীলঙ্কা রীতিমতো খাদের কিনার থেকে ফিরে এসেছে। দেশটির মূল্যস্ফীতিও ঈর্ষণীয়ভাবে কমেছে। জিনিসপত্রের মূল্যে শক্ত নজরদারির কারণে দেশটির মূল্যস্ফীতি চলতি মার্চে শূন্য দশমিক ৯ শতাংশে এসে পৌঁছেছে বলে জানিয়েছে দেশটির পরিসংখ্যান অফিস। প্রতিবেশী নেপালের মূল্যস্ফীতির হার চলতি বছরের জানুয়ারিতে হয়েছে ৫ দশমিক ৩ শতাংশ। একই সময়ে ভুটানের মূল্যস্ফীতি হয়েছে ৪ দশমিক ২ শতাংশ। শুধু প্রতিবেশী দেশ বলেই নয়, জিনিসপত্রের উত্তাপে পানি ঢেলে দিয়েছে উন্নত দেশ যুক্তরাষ্ট্রেও। দেশটিতে ফেব্রুয়ারিতে মূল্যস্ফীতি নেমে এসেছে ৩ দশমিক ২ শতাংশে।
বাংলাদেশে জিনিসপত্রের দাম এখনো কেন সহনীয় পর্যায়ে আসেনি জানতে চাইলে জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বলেন, ‘আসলে আমদানি করা পণ্যের দামের পেছনে তো ব্যবসায়ীদের একটা অজুহাত থাকে। তারা দাম বাড়ায়, আমরা কিছু অভিযান করলে আবার দাম কমে আসে। পেঁয়াজ, ডিম, আলুর অবস্থা তো সবাই জানেন। আসলে কেনাকাটায় সবার সচেতন হওয়ার ব্যাপার আছে। মানুষ সচেতনও হচ্ছে। তরমুজের দাম কমে যাওয়া কিন্তু সচেতনতারই ফল। বিগত জুলাই-আগস্টে কোটা সংস্কার আন্দোলনে নতুন অন্তর্বর্তী সরকার ক্ষমতায় আসিন হয় এবং সবাই আশা করেছিল বাজার ব্যবস্থার একটা গুণগত পরিবর্তন হবে। কিন্তু বাস্তবে অবস্থার অবনতি হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় সবজির বাজারে যেন লাগাম দেওয়ার কেউ নেই। নতুন করে কয়েকটির দাম আরও বেড়েছে।
ফলে হাতেগোনা তিন-চারটি ছাড়া বেশির ভাগ সবজির দর শতক ছাড়িয়েছে। শুধু শহর নয়, উৎপাদন এলাকায়ও চড়া দাম শাকসবজির। ফলে সীমিত আয়ের মানুষের কাছে সবজিও হয়ে উঠেছে অনেকটা বিলাসী পণ্য। তবে চিনি, ডিম ও গরুর মাংসের দাম কিছুটা কমতির দিকে। আবার আগের মতোই উচ্চদরে স্থির রয়েছে চাল, ডাল, তেলসহ কয়েকটি নিত্যপণ্য। তাতে বেশ হিমশিম খেতে হচ্ছে নিম্ন ও মধ্য আয়ের পরিবারগুলোকে। সবজির দর বাড়ার পেছনে নানা কারণ তুলে ধরছেন কৃষি বিভাগের কর্মকর্তা, কৃষক ও পাইকারি ব্যবসায়ীরা। তারা জানিয়েছেন, এ বছর অসময়ে টানা বৃষ্টিতে সবজির চারা ও ফুল নষ্ট হয়ে যাওয়ায় উৎপাদন কমেছে। পাশাপাশি আগাম শীতকালীন সবজি চাষ করার জন্য অন্য বছরের তুলনায় এবার অধিক পরিমাণ জমি পতিত রাখা হয়েছে। এটিও উৎপাদন কম হওয়ার অন্যতম কারণ।
গণঅভ্যুত্থানে শেখ হাসিনার পতনের পর বাজারে সব ধরনের সবজির দর তিন ভাগের এক ভাগে নেমে এসেছিল। স্বস্তিদায়ক সেই পরিস্থিতি মাসখানেকের মতো ছিল। এরপর থেকেই পুরোনো চেহারায় ফিরেছে সবজির বাজার। সরকারের সংশ্লিষ্টদের দাবি, দাম বাড়ার মূল কারণ টানা বৃষ্টি। তবে প্রতিদিনই বাজার তদারকি হচ্ছে। আমদানির অনুমতি, শুল্ক কমানোসহ কিছু ইতিবাচক উদ্যোগে ইতোমধ্যে কয়েকটি পণ্যের দর কমতে শুরু করেছে।
ঢাকায় অনেক সবজির সেঞ্চুরি চলছে। বাংলাদেশ পাইকারি কাঁচামাল আড়ত মালিক সমিতির সভাপতি বলেন, এ বছর ঘন ঘন বৃষ্টি হচ্ছে। কোথাও বৃষ্টির পরিমাণ অস্বাভাবিক। তাতে সবজি খেত ডুবে গেছে। উঁচু এলাকায় না ডুবলেও গাছের গোড়ায় পানি জমে গাছ পচে যাচ্ছে। তিনি বলেন, বছরের এ সময় শীতের কিছু সবজি আগাম বাজারে আসে। যেমন- ফুলকপি, বাঁধাকপি ও শিম। এসব সবজি উত্তরবঙ্গ, নোয়াখালী, কুমিল্লা, কুষ্টিয়া ও খুলনা অঞ্চলে বেশি হয়। কিন্তু সেসব এলাকায় পানির কারণে বীজ লাগানো যাচ্ছে না। সার্বিকভাবে সবজির সরবরাহ কমছে। তা ছাড়া এ সময় শ্রমিকদের মজুরিও বেশি দিতে হয়। সে জন্য উৎপাদন এলাকায় কৃষকরাও এখন তুলনামূলক দাম বেশি নিচ্ছেন। বগুড়ার মহাস্থানহাটের পাইকাররা ঢাকাসহ বিভিন্ন জেলায় প্রতিদিন ২৫-৩০ ট্রাক সবজি নিয়ে গেলেও উৎপাদন কম থাকায় এখন পাঁচ-ছয় ট্রাকের বেশি নিতে পারেন না। এখানকার পাইকারি ব্যবসায়ী বলেন, প্রতিদিন কমপক্ষে তিন ট্রাক সবজি নিয়ে যান ঢাকা কারওয়ান বাজারে।
এখন মাত্র এক ট্রাক নিচ্ছেন। বগুড়া সদরের শেখেরকোলা এলাকার সবজি চাষি বলেন, তিনি পটোল ও বেগুন চাষাবাদ করেন দুই বিঘা জমিতে। লাগাতার বৃষ্টিতে সবজি গাছের ফুল পচে গেছে, তাতে উৎপাদন কমে গেছে। এখন যা উৎপাদন হচ্ছে, তা দিয়ে খরচ উঠছে না। তবে আমদানির উদ্যোগ ও শুল্ক কমানোর খবরে গত তিন দিনে ডিমের ডজনে ২০ টাকার মতো কমে বিক্রি হচ্ছে ১৫৫ থেকে ১৬০ টাকায়। যদিও পাড়া-মহল্লায় কোনো কোনো ব্যবসায়ী এর চেয়েও বেশি দর নিচ্ছেন। ব্রয়লার মুরগির দর কমেনি। এখনো ব্রয়লারের কেজি বিক্রি হচ্ছে ১৮০-২০০ টাকা দরে। তবে অপরিবর্তিত সোনালি জাতের মুরগি।
প্রতি কেজি বিক্রি হচ্ছে ২৬০ থেকে ২৭০ টাকায়। মাসদেড়েক আগে ডিমের ডজন ১৪০ থেকে ১৪৫ এবং ব্রয়লারের কেজি ছিল ১৫০ থেকে ১৬০ টাকা। তবে স্বস্তির খবর আছে গরুর মাংসের বাজারে। প্রতি কেজি বিক্রি হচ্ছে ৭০০ থেকে ৭৩০ টাকা দরে। দুই মাস আগে মাংসের কেজি ৭৫০ টাকার বেশি ছিল। দুই মাসের বেশি সময় ধরে চালের বাজার বাড়তি। বিআর-২৮ ও পায়জাম জাতের বা মাঝারি আকারের চালের কেজি খুচরায় বিক্রি হচ্ছে ৫৮ থেকে ৬৪ টাকায়। মোটা চালের (গুটি স্বর্ণা ও চায়না ইরি) কেজি বিক্রি হচ্ছে ৫০ থেকে ৫৫ টাকায়। এ ছাড়া চিকন চাল (মিনিকেট) বিক্রি হচ্ছে কেজি ৭০ থেকে ৭৫ টাকা দরে। দুই মাস আগে প্রতি কেজি মোটা চাল ৪৮ থেকে ৫০, মাঝারি চাল ৫৪ থেকে ৫৮ এবং চিকন চাল ৬৮ থেকে ৭০ টাকায় বিক্রি হয়েছে।
সম্প্রতি ভারত চাল রপ্তানিতে শর্ত শিথিল করেছে। শুল্ক কমানোর সুপারিশও করেছে ট্যারিফ কমিশন। যদিও শুল্ক এখনো কমানো হয়নি। আমদানির খবরও পাওয়া যায়নি। তবে ব্যবসায়ীরা বলছেন, আমদানি হলে দর কমে যাবে। তবে শুল্ক কমানোর কারণে চিনির কেজিতে তিন টাকা কমে বিক্রি হচ্ছে ১২৫-১৩৫ টাকায়। কিছুটা কমতির দিকে রয়েছে ভোজ্যতেলের দরও। রপ্তানির শর্ত শিথিল করায় ভারত থেকে পেঁয়াজ আসা শুরু হয়েছে। কিন্তু দর কমেনি। বরং বেড়েছে কিছুটা। এখনো দেশি পেঁয়াজের কেজি ১১৫ থেকে ১২০ এবং ভারতীয় পেঁয়াজের কেজি ১০০ থেকে ১১০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে।
নিত্যপণ্যের এমন আগুন দরে দুর্ভোগে পড়েছেন ভোক্তারা। নতুন সরকারের কাছে মানুষ যে আশা করেছিল, তা দেখা যাচ্ছে না। এমন কোনো জিনিসি নেই, যার দর বাড়েনি। মানুষের এখন দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে। দাম নাগালে রাখতে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও ভোক্তা অধিদপ্তরের একাধিক টিম বাজার তদারকি করেছ। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের উপসচিব ব্যবসায়ীদের উদ্দেশে বলেন, পণ্যের ক্রয় রসিদ রাখতে হবে। অযৌক্তিক দরে বিক্রি করলে জরিমানা করা হবে। এ সময় তিনি বলেন, গত কয়েক দিনের তুলনায় ডিম, পেঁয়াজ ও আলুর দাম কিছুটা কমেছে। আরও কমে আসবে। সারা দেশে নিত্যপণ্যের বাজারে অভিযান চালিয়ে ভোক্তা অধিদপ্তর ৩৯টি প্রতিষ্ঠানকে বিভিন্ন অপরাধের দায়ে ৩ লাখ ১৩ হাজার টাকা জরিমানা করেছে। এখন দেখা যাক, পরিস্থিতি উন্নতি হলে সাধারণ ভোক্তার মনে কিছুটা হলেও স্বতি ফিরে আসবে এই প্রত্যাশা রইল।
লেখক: গবেষক ও অর্থনীতিবিদ

বিদ্যে বোঝাই বাবু মশাই চড়ি শখের বোটে/ মাঝিরে কন বল তো দেখি, সূর্য কেন ওঠে?/ চাঁদটা কেন বাড়ে-কমে/ জোয়ার কেন আসে/ বৃদ্ধ মাঝি অবাক হয়ে ফ্যালফেলিয়ে হাসে- আজ আমাদের দেশটা বিদ্যে বোঝাই বাবু মশাইয়ের ভিড় লেগেছে। এসব বিদ্যে জোগাড় হয়েছে সার্টিফিকেটের দৌলতে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন, বিদ্যা সহজ শিক্ষা কঠিন, বিদ্যা আবরণে, শিক্ষা আচরণে। কবিগুরুর এই সহজ অথচ গভীর কথা মর্ম উপলদ্ধি করা আজকের সমাজের কাছে প্রায় অসাধ্য। কারণ এরা গুলিয়ে ফেলতে অভ্যস্ত। আবার এত গভীরে গিয়ে কোনো অর্থ বের করার মতো সময়টাও নেই।
আবার কবিগুরুকে নিয়েও সভ্য সমাজের বিদ্যে বোঝাই বহু বাবুমশাইয়ের সন্দেহ রয়েছে। বিদ্যা অর্জন করা বেশ সহজ। বলা যায় একেবারেই সহজ কাজ। বিদ্যে মানুষকে খুব বেশি মানুষ হিসেবে পরিচিত করতে পারে না। যা মানুষকে মানুষের স্বীকৃতি দিতে পারে সেটি হলো শিক্ষা। শিক্ষা হলো একটি পদ্ধতি যা আনুষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিক হতে পারে তবে মানুষের আচরণকে একটি স্থায়ী পরিবর্তনের দিকে নিয়ে যায়। এবার উদাহরণ দিয়ে বিদ্যা ও শিক্ষার পার্থক্য বুঝিয়ে দিই। খুব ছোটবেলা থেকেই আমাদের বইয়ে এবং পরিবার ও সমাজ আমাদের মিথ্যা না বলার শিক্ষা দেয়। আসলে কিন্তু এটা শিক্ষা না বিদ্যা। এই বিদ্যা পুঁথিগত বা অপুঁথিগত হতে পারে। এটি যদি কোনো পরিবার বা সমাজে চর্চা করা হয় তাহলে এটি পরিণত হয় শিক্ষায়। রবীন্দ্রনাথের কথায় আবরণ এবং আচরণ এই দুইয়ের পার্থক্য এখানেই।
সত্য বলার অভ্যাস পরিবারে হচ্ছে না। স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের সঙ্গে মিথ্যা বলছে, সন্তান মা-বাবার সঙ্গে মিথ্যা বলছে, সমাজে একে অপরের সঙ্গে মিথ্যা বলছে। নেতারা মিথ্যা আশ্বাস দিচ্ছেন। এই দেখে দেখে একটি শিশু বড় হচ্ছে। সে বইয়ে শিখল এক আর সমাজে চর্চা হচ্ছে আরেক। অর্থাৎ সমাজ চলছে উল্টোপথে। এখন শিশুটি দেখছে সমাজে মিথ্যা বলার লাভ বেশি। সে সেটাই করছে। যদি এর উল্টোটা অর্থাৎ বইয়ে যাই থাক চর্চা হতো সত্য বলার তাহলে কিন্তু শিশু সত্য বলাই শিখত।
আবরণ মানে আমাদের পোশাক-আশাক এবং আচরণ হলো ব্যবহার যা আমরা অন্যের সামনে দেখাই। অবস্থা এমন হয়েছে যে আমি-আপনি যে শিক্ষিত সেটা প্রমাণ করতে সার্টিফিকেট ঝুলিয়ে রাখতে হবে! কারণ মানুষ যত বিদ্বান হচ্ছে, সমাজ তত অসভ্য হচ্ছে। আমরা বিদ্বান হচ্ছি বড়জোর, শিক্ষিত নয়! যারা এই পার্থক্য বুঝতে অক্ষম তিনি ওই বিদ্বান। ফেসবুকে ঢুকলেই দেখা যায় নীতিবাক্যের ছড়াছড়ি। যদি এটা সত্য বলে ধরে নেন মানে সেই ব্যক্তিদের কথা এবং তাদের জীবনযাপন পদ্ধতি সত্য বলে বিচার করেন তাহলেই আপনি ঠকেছেন। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এসব নীতিবাক্য আওড়ানো মানুষের সঙ্গে তাদের ব্যক্তিক আচরণ এবং দর্শনের বিস্তর ফারাক রয়েছে। ঘরে ঘরে খুঁজলে সার্টিফিকেটধারী মানুষের কোনো অভাব নেই। বড় বড় ডিগ্রি, বড় বড় কথা অথচ কাজকর্ম নিতান্তই অবিবেচকের মতো।
তারা যে শিক্ষিত হতে পারেননি, আমরা যে মানুষ পাচ্ছি না সেটি কিন্তু শিক্ষার দোষ না, সেটি হলো চর্চার দোষ। এই তো গণমাধ্যমে দেখলাম কারিগরি বোর্ডের সার্টিফিকেটের কেলেঙ্কারি। কতজন পকেটের টাকা খরচ করে সার্টিফিকেট কিনে সমাজে দামি চাকরি করছেন, এখন যদি তাদের আপনি শিক্ষিতভাবে তাহলেই সর্বনাশ! তারা অবশ্য বিদ্বানও না। চুরি করে আর যাই হোক বিদ্বান হওয়া যায় না। কথায় বলে, গুরু মারা বিদ্যা! এই বিদ্যা অর্জন করে শিষ্য গুরুকে মারার ক্ষমতা অর্জন করে। যদিও এই বিদ্যা ভুল এবং অন্যায্য তবুও আছে। শিক্ষককে তো আজ অনেকেই মারছে। গায়ে হাত তুলছে, জোর করে পদত্যাগ করাচ্ছে, লাঞ্ছিত করছে খোলা রাস্তায়। এই বিদ্যা অর্জন তো সেই সব শিক্ষকের বা গুরুর কাছ থেকেই শেখা।
এমন বিদ্যাই শিখেছে যে গুরুকে মারতে দ্বিধাবোধ করছে না। এখন এদেরও যদি শিক্ষিতদের কাতারে ফেলেন তাহলে তো এক দিন সমগ্র সমাজটাই অচল হয়ে যাবে। অথচ দেশ ভরে যাচ্ছে বিদ্বান মানুষে। সার্টিফিকেটধারীদের পদভারে রাজপথ ভারী হচ্ছে। মানুষ তো পাচ্ছি না। মানুষ হলে দেশটা অনেক আগেই আরও সুন্দর হয়ে উঠতে পারত। দেশকে নিয়ে আজ স্বপ্ন দেখা মানুষের সংখ্যা হাতেগোনা। অথচ নিজেকে নিয়ে স্বপ্ন দেখা মানুষের সংখ্যা ভুরি ভুরি। নিজেকে মহাজ্ঞানী ভাবা এবং অন্যকে বোকা ভাবা খুব সহজ কাজ। আমাদের বিদ্বান দরকার না, শিক্ষিত মানুষ দরকার। চর্চায় শিক্ষিত দরকার, স্যুট, টাই পরা ভদ্রলোকের দরকার নেই। তা না হলে সেই বিদ্যে বোঝাই বাবু মশাইয়ের চাপে দেশের মাটি ধসে পড়তে পারে!
লেখক: প্রাবন্ধিক ও কলামিস্ট