
শায়রুল কবির খান
নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে চলছে। এসব পণ্যের দাম বেশ আগেই দরিদ্র ও নিম্ন মধ্যবিত্ত মানুষের নাগালের বাইরে চলে গেছে। মধ্যবিত্তরা এখন হাঁসফাঁস করছেন, উচ্চ মধ্যবিত্তদের কপালেও চিন্তার রেখা। সরকারের দুর্বল বাজার ব্যবস্থাপনার কারণে এমনটা ঘটছে। অতিমাত্রায় আমলানির্ভর হওয়ায় বর্তমান সরকার রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক- কোনো কাজেই দক্ষতা দেখাতে পারছে না। পারছে না সঠিক সময়ে সঠিক পদক্ষেপ নিতে।
কোভিড-পরবর্তী অর্থনৈতিক মন্দার এবং সর্বশেষ রাশিয়া ও ইউক্রেনের যুদ্ধের ধাক্কা সামলানোর বিষয়ে সরকারের আগাম কোনো পরিকল্পনা লক্ষ করা যায়নি। এ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের নাগরিকের স্বার্থরক্ষা করে উৎপাদন ও সরবরাহব্যবস্থাকে জোরদার করার বিষয়ে শুরু থেকেই জোরালো প্রচেষ্টার অভাব ছিল।
আধুনিক বিশ্বে প্রতিযোগিতামূলক বাজার ব্যবস্থাপনায় পণ্যের দাম নির্ধারিত হয়ে থাকে পণ্যের মোট সরবরাহ ও মোট চাহিদার ভিত্তিতে। চাহিদার চেয়ে পণ্য সরবরাহ কম হলে মূল্যবৃদ্ধি ঘটে। যতক্ষণ না চাহিদা ও সরবরাহের মধ্যে একটা সমতা না আসে ততক্ষণ পর্যন্ত বাড়তেই থাকে। বর্তমান সরকারের সময়ে পণ্যের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির কারণগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো উৎপাদন উপকরণ সহজলভ্য না করা। উল্টো দফায় দফায় মূল্যবৃদ্ধি করা হয়েছে সার, বীজ, তেল, বিদ্যুৎ, পানি, কীটনাশক ইত্যাদির। অন্যদিকে সংরক্ষণ করা যায় এমন সব পণ্যের দাম অস্বাভাবিকভাবে ওঠানামা করার বিষয়টিও বাজারকে অস্থিতিশীল করার ক্ষেত্রে ভূমিকা রেখেছে। সংরক্ষণযোগ্য পণ্যের গুদামে আকস্মিক তল্লাশি, কোনো কোনো ক্ষেত্রে সিলগালা করা কিংবা বাজারে বিক্রির জন্য চাপ সৃষ্টি করা ইত্যাদি বিষয়ও পণ্যের মূল্যবৃদ্ধিতে সহায়তা করেছে।
যেকোনো পণ্য উৎপাদনের পর সংরক্ষণ করেই চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহের মধ্য দিয়ে সম্পূর্ণ হয় বাজার ব্যবস্থাপনা। মৌসুমভিত্তিক উৎপাদিত পণ্যের ক্ষেত্রে তা আরও গুরুত্বপূর্ণ। সংরক্ষণের ব্যবস্থা না থাকলে মৌসুম শেষে চাল, ডাল, পেঁয়াজ, রসুনসহ আরও অনেক পণ্যের দেখা পাওয়া যেত না। তাতে দেখা যেত, মৌসুমে ওই সব পণ্য পানির দরে বিক্রি হচ্ছে। সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাত করার সুবিধার কারণেই বছরব্যাপী পণ্য সরবরাহ করা সম্ভব হয় এবং বাজারকে স্থিতিশীল রাখা যায়। যথেষ্ট প্রতিযোগিতা থাকলে সংরক্ষণকারী পণ্য অতিরিক্ত সময়ের বেশি এক দিনও ধরে রাখবে না।
অথচ বর্তমান সরকার পণ্যের সরবরাহ ও চাহিদার অব্যবস্থাপনার দিকে মনোযোগ দেয়নি। উল্টো তারা প্রথমেই আঘাত করেছে সংরক্ষণকারীদের ওপর। অবশ্য কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই বাজারে এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া লক্ষ করা গেছে। সংরক্ষণকারীদের গুদামে হানা দেয়া থেকে বিরত হয় সরকার। কিন্তু ততদিনে সরবরাহব্যবস্থার সংকটে সর্বনাশ যা হওয়ার তা হয়ে গেছে। বিষয়টি নিয়ে খোদ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও বিরক্তি প্রকাশ করেছেন। পণ্যের দাম সাধারণের নাগালে রাখতে কঠোর নির্দেশ দিতে বাধ্য হয়েছিলেন।
পণ্য আমদানিকারক সিন্ডিকেট কিংবা বাজার ব্যবস্থাপনায় যেকোনো পর্যায়ে সিন্ডিকেটকে পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের সুযোগ দেয়া হলে তার চরম খেসারত গুনতে হয় ভোক্তাদের। এ ধরনের পরিস্থিতিতে ধরপাকড় ও হুমকি বরং বাজারে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ভীতি তৈরি করে। এতে পণ্যের সরবরাহব্যবস্থায় আরও বাধাবিপত্তি তৈরি হয়। অথচ সরকার বারবার সেই কাজটিই করেছে। ব্যবসায়ীদের ধরপাকড় করেছে।
আমদানিকারক কিংবা বাজারে যেকোনো পর্যায়ে ব্যবসায়ীদের সিন্ডিকেট তৈরি হয় ক্ষমতাসীন দলের নেতাদের পরোক্ষ অথবা প্রত্যক্ষ ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত থাকার কারণে। বাংলাদেশে যেখানে পূজা-পার্বণ ও ঈদ ছাড়া পণ্য চাহিদার আকস্মিক বৃদ্ধি ঘটে না, সেখানে সাধারণ সময়ে চাহিদার সঙ্গে সরবরাহের ঘাটতির কারণ কী? এর সহজ উত্তর, এ সরকার নৈতিকভাবে যতটা দুর্বল ঠিক ততটাই দুর্বল বাজার ব্যবস্থাপনায়। এ ধরনের পরিস্থিতিতে শুধু আমলাদের ওপর নির্ভর করে জনগণের স্বার্থ রক্ষা করা যায় না।
এই সরকার এ রকম একটা ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে টিকে আছে, যেখানে তারা অতিরিক্ত ব্যয় মেটানোর জন্য ব্যাংক খাত থেকে ঋণ নিচ্ছে, অন্যদিকে ব্যাংক পরিচালকরা সুবিধামতো লুটপাট করে অর্থ পাচার করছে। সরকার কুইক রেন্টাল বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের চুক্তি দফায় দফায় বৃদ্ধির নামে জনগণের টাকা ভর্তুকি হিসেবে দিয়ে যাচ্ছে। পরিবহন সেক্টরের কথা আর না-ই বললাম। তারা কথায় কথায় ধর্মঘটের ডাক দিয়ে থাকে কাউকে তোয়াক্কা না করেই। এসব অব্যবস্থাপনায় দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির লাগাম টেনে ধরা অনেকটাই অসম্ভব। আসলে পাগলা ঘোড়া একবার ছুটতে শুরু করলে তাকে অত সহজে থামানো সম্ভব হয় না।
এভাবেই সবকিছু একসময়ে সহনীয় হয়ে যায়। আজ যে পণ্যের দাম নাগালের বাইরে, কিছুদিন পর তা সহনীয় মনে হবে। এরপর বাড়বে অন্য পণ্যের দাম, সেটির দামও একসময় সহনীয় মনে হবে। কিন্তু এ ধরনের পরিস্থিতি অনন্তকাল ধরে চলতে পারে না। একসময় বিস্ফোরণ ঘটবেই, জনগণের বিস্ফোরণ।
লেখক: সদস্য, বিএনপি চেয়ারপারসন প্রেস উইং ও বিএনপির মিডিয়া সেল

আমরা এ রকম গল্প প্রায়ই শুনি যে, কোনো পরিবারের বড় ভাই বা বোন বাবার অক্ষমতায় বা অবর্তমানে পারিবারিক অসচ্ছলতায় নিজের কাঁধে পরিবারের সব দায়িত্ব তুলে নেন। নিজে পড়াশোনা না করে ছোট ভাইবোনদের পড়াশোনা করিয়ে তাদের প্রতিষ্ঠিত করার জন্য নিজের জীবনের সব সাধ-আহ্লাদ জলাঞ্জলি দিয়ে দেয়। নিজেকে বঞ্চিত করে নিজ জীবনের সব চাওয়া থেকে। অতঃপর যখন ভাইবোনরা বড় হয়ে যায়, যার যার মতো প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় এবং যার যার মতো সংসার গড়ে তোলে তখন বড় ভাই বা বোনটি সবার দ্বারা লাঞ্ছিত হতে থাকে। এমন খুব কম উদাহরণ আছে যে, ওই ভাই বা বোনটি যথাযথ সম্মান, ভালোবাসা পায় তাদের আজীবন আত্মত্যাগের জন্য।
এখন প্রশ্ন হলো, যে ভাই বা বোনটি নিজের জীবনের সব কিছু আত্মত্যাগ করল তা কতটা যুক্তিযুক্ত? মানুষ যেহেতু সামাজিক জীব, সেহেতু সমাজ সভ্যতার প্রথম পরিচয়ের দিক হলো পরিবার। পরিবারে যারা যারা বাস করেন পরস্পরের প্রতি অবশ্যই দায়িত্ব ও কর্তব্য থাকবেই। তবে কেউ কেউ আছেন, যারা নিজেকে উজাড় করে দিয়ে, পৃথিবীর সব ভুলে পরিবারের দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নেন খুশি মনে। আমি মনে করি, বড় হিসেবে সংসারের অবশ্যই দায়িত্ব নিতে হবে, তবে তা কখনো নিজেকে ঠকিয়ে নয়।
সময়ের সঙ্গে প্রতিটি মানুষের মানসিক পরিবর্তন হতে থাকে। আজ যারা সংসারে দায়িত্বরত ভাই বা বোনটিকে বটবৃক্ষ ভাবছে সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং ভুল শিক্ষার প্রভাবে প্রতিটি মানুষের মন-মানসিকতা পরিবর্তন স্বাভাবিক। দিন দিন ভাইয়ে-ভাইয়ে, বোনে-ভাইয়ে, এমনকি পরিবারের নতুন সদস্য যুক্ত হলে আত্মত্যাগ করা ভাই বা বোনটি তার প্রাপ্য সম্মান ও ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত হন। কারণ নতুন সদস্যটি আত্মত্যাগ করা ভাই বা বোনটির গুরুত্ব বুঝতে পারে না বা বুঝেও নিজের বিবেকবোধহীনতায় সংসারে সমস্যা সৃষ্টি করে। সারাজীবন কষ্ট করার পরও সব আত্মত্যাগ এক মুহূর্তে ধূলিসাৎ হয়ে যায়। তখন হাহাকার আর নিভৃত কান্না ছাড়া কিছুই করার থাকে না।
আবার অনেক সময় দেখা যায়, সামান্য যা পরিমাণ পৈতৃক সম্পত্তি আছে তাই নিয়ে ভাই-বোন দ্বন্দ্বে জড়ায়। সারাজীবন যে বোনটি অন্যের সংসারে থেকেও তাদের জন্য ভেবেছে, তাদের আশ্রয়, প্রশ্রয় দিয়ে মানুষ করেছে তারাও সম্পত্তির ভাগ-বাটোয়ারা করতে হবে বুঝতে পেলেই দূরত্ব বাড়ে মায়াময়, ভালোবাসাময় সম্পর্কগুলোতে। বাবা-মার বাড়িতে হাসি-আনন্দে বেড়ে ওঠা বোনটি বিয়ের পর বাবার বাড়িতে আর সেরকম মায়াময় জীবন পায় না। মা-বাবার কাছে, ভাইদের কাছে বোন আগের অধিকার যেন হারিয়ে ফেলে। আরও বেশি সমস্যা হয় যখন বোনরা বাবার সম্পত্তির ভাগ চায়। ভাইদের তখন আসল চেহেরা ফুটে উঠে এবং দুঃখজনক পরিস্থিতির শিকার হতে হয়। ভাইয়েরা শুরু করে বোনকে বঞ্চিত করার নানা কৌশল। দুই বা ততোধিক ভাইয়ের মধ্যে শুরু হয় দ্বন্দ্ব এবং পরস্পরের মুখ দেখাদেখিও বন্ধ হয়ে যায়।
এবার ফিরে যাই প্রথম প্রসঙ্গে, অতঃপর সব দায়-দায়িত্ব থেকে অবসর পাওয়ার পর সেই ভাই বা বোনটি যখন নিজের দিকে তাকায় তখন নিজেকে নিজে করুণা করারও সময় থাকে না। তাই প্রত্যেক মানুষের উচিত, সমাজ-সংসারের সব দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি নিজের জীবনকেও প্রাধান্য দেওয়া। সময়কে গুরুত্ব দিয়ে নিজের প্রয়োজন, ইচ্ছাগুলোকে ডানা মেলতে দেওয়া। প্রত্যেক মানুষের উচিত নিজেকে গড়ে তোলা, নিজের জীবনের প্রতি যত্নশীল হওয়া। এককথায় এভাবে বলা যায়, তা হলো উদার হও, তবে উজাড় হইয়ো না।
লেখক: কবি ও প্রাবন্ধিক

ধান বাংলাদেশের একটি প্রধান ফসল। এ ফসলটি শুধু বাংলাদেশে নয়- এশিয়া তথা দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর অন্যতম একটি প্রধান ফসল। আমরা জানি, আমাদের বাংলাদেশের মোট উৎপাদিত কৃষি ফসলের শতকরা আশিভাগেরও বেশি হলো ধান ফসল। তার মধ্যে অবার শতকরা ৬৭ শতাংশ হলো বোরো ধান। কাজেই তিন মৌসুমে ধান হওয়ার কারণে ধান ফসলটি সুষ্ঠুভাবে ফলানোর জন্য সেচ একটি অন্যতম অনুষঙ্গ।
পানি ছাড়া ধান আবাদ কল্পনাই করা যায় না। ধান আবাদে যেসব উপকরণ প্রয়োজন তার মধ্যে প্রধানতম হলো সেচ। আউশ, আমন ও বোরো- এ তিন মৌসুমের মধ্যে আমন এবং আউশ বৃষ্টিনির্ভর হলেও বোরোতে একেবারে প্রায় শতভাগই সেচনির্ভর। আর বৃষ্টির পানির প্রাকৃতিক বণ্টনটা এমন, দেখা গেছে একদিকে মৌসুমের শুরুতে পানির অভাবে ধান রোপণ করা যাচ্ছে না, অথচ ধান কাটার সময় আগাম বন্যা, পাহাড়ি ঢল কিংবা অতিবৃষ্টি, শিলাবৃষ্টিতে ফসল ঘরে তুলতে পারছেন না কৃষক।
আশির দশক থেকে দেশে সেচ বিপ্লব ঘটতে থাকে। আর সেই সেচ বিপ্লবের কারণেই বোরো ধান এখন দেশের একটি প্রধান ফসল হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। বোরো ধান আবাদেই যেহেতু সবচেয়ে বেশি পানি সেচের প্রয়োজন হয়, সে জন্য এ বিষয়ে বিজ্ঞানীরা এখন বেশি নজর দেওয়া শুরু করেছেন। বোরো চাষের সময়টা মূলত শীতকালে এবং শুষ্ক মৌসুমে। সেটা ডিসেম্বর থেকে এপ্রিল-মে পর্যন্ত চলে। তখন বৃষ্টিপাত খুবই কম হয়। আবার পুরো মৌসুমে বৃষ্টিপাত হয় না বললেই চলে। তা ছাড়া সে শুষ্ক সময়ে নদী-নালা, খাল-বিল ইত্যাদি মুক্ত জলাশয়ও শুকিয়ে যায়। সে জন্য পুরো বোরো মৌসুমের সেচের জন্য ভূ-গর্ভস্থ পানির ওপর নির্ভর করতে হয়।
গবেষণায় দেখা গেছে, প্রচলিত কাদা পদ্ধতিতে মাটির প্রকারভেদে পুরো বোরো মৌসুমে ১৫-৩০ বার পর্যন্ত সেচ প্রদান করতে হয়। বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (বাকৃবি), বাংলাদেশে ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি), আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ইরি), বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন করপোরেশন (বিএডিসি), রুরাল ডেভেলপমেন্ট একাডেমি (আরডিএ) ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত গবেষণা ও ধারাবাহিক উন্নয়নের মাধ্যমে কীভাবে বোরো ধান আবাদে সেচের পানি সাশ্রয় করা যায়, বহুদিন থেকে সেই গবেষণা ও পর্যবেক্ষণ প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।
সেসব গবেষণায় পাওয়া তথ্যানুযায়ী, প্রতি কেজি ধান উৎপাদনে প্রায় ৩ থেকে ৫ হাজার লিটার সেচের পানির প্রয়োজন হয়। গত কিছুদিন আগে একাধিক সেমিনারে প্রদত্ত বক্তব্যের তথ্যানুযায়ী, এক কেজি ধান উৎপাদনের জন্য ভূ-গর্ভস্থ ৩২০০ লিটার সেচের পানির প্রয়োজন হওয়ার কথা জানা গেছে। সেসব প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে ধান আবাদে ‘অলটারনেট ওয়েটিং অ্যান্ড ড্রাইং (এডব্লিউডি)’ পদ্ধতিতেও সেচের পানি সাশ্রয়ের চেষ্টা চালানো হচ্ছে বেশকিছু দিন ধরে।
ধারাবাহিকভাবে ভেজানো এবং শুকানোর এ পদ্ধতির মাধ্যমে ধানের জমিতে তা প্রয়োগ করা হচ্ছে। এর জন্য খুবই কম খরচে এবং সহজে ব্যবহারযোগ্য একটি যন্ত্র আবিষ্কার করেছেন কৃষি বিজ্ঞানীরা। এর জন্য প্রয়োজন হয় এক থেকে দেড় ফুট লম্বা প্লাস্টিক কিংবা স্টিলের এক টুকরা পাইপের। চারপাশে ছোট ছোট ছিদ্রযুক্ত সেই প্লাস্টিক কিংবা স্টিলের পাইপটি নির্ধারিত দূরত্বে পুরো জমিতে পুঁতে রাখতে হয়। জমির অতিরিক্ত পানি শুকিয়ে ফেলার সময় সেই পাইপের ভিতরে পর্যবেক্ষণ করতে হয়, সেখানে পানি কতটুকু পরিমাণ আছে, কী নেই। তার ওপর ভিত্তি করেই সেই জমিতে সেচের সময় ও পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। এতে অপ্রয়োজনীয় পরিমাণ পানির পরিবহন বন্ধ করে সেচ নিয়ন্ত্রণ করা হয়ে থাকে।
অন্যভাবেও সেচের পানি হ্রাস করে লাভজনকভাবে বোরোধান আবাদ করার বিষয়ে বেশ কয়েকটি পত্রিকায় এ সম্পর্কিত একটি রিপোর্ট বেশ গুরুত্ব দিয়ে ছাপানো হয়েছে। দেশবাসীর জন্য এটি নিঃসন্দেহে একটি সুখবর। প্রচলিত বোরো চাষ পদ্ধতিতে একটু পরিবর্তন এনে তা করা হচ্ছে। সেখানে প্রচলিত ধারার বীজতলা তৈরি ও সেখান থেকে ধানের চারা রোপণের পরিবর্তে অঙ্কুরিত ধানের বীজ প্রস্তুতকৃত অর্ধ-কর্দমাক্ত জমিতে সরাসরি রোপণ করে দেওয়া হয়। আর এ পদ্ধতিতে পুরো মৌসুমে ১৫-৩০ বারের পরিবর্তে মাত্র ৪-৮ বার সেচ দিলেই আরও বেশি ফলন পাওয়া যায়।
বাকৃবিতে কৃষিতত্ত্ব বিভাগের প্রফেসর ড. মো. মশিউর রহমান, বিভিন্ন সময়ে তার বেশকিছু গবেষণা সহযোগী এবং রিসার্চ ফেলোকে নিয়ে গঠিত গবেষক টিম দীর্ঘদিন গবেষণা শেষে একটি গণমুখী ফলাফল সুপারিশ করতে পেরেছেন। এ পদ্ধতিতে বোরো ধান আবাদের সুবিধাগুলো হলো- (১) প্রচলিত পদ্ধতির তুলনায় ৫০-৬০ ভাগ পানি, ডিজেল ও বিদ্যুৎ সাশ্রয় হয়। (২) ফেব্রুয়ারি মাসের মাঝামাঝি সময়ে কোনো বীজতলা তৈরি করা ছাড়াই অঙ্কুরিত ধানের চারা সরাসরি অর্ধ-কর্দমাক্ত জমিতে লাগিয়ে দিতে হয়।
বীজতলার অন্তর্বর্তীকালীন সময়টা না লাগার কারণে ধানের জীবনকাল কমপক্ষে ১৫ দিন কমে আসে। (৩) রংপুর, দিনাজপুর, রাজশাহী, নেত্রকোনা, ময়মনসিংহ ইত্যাদি অঞ্চলে এ পদ্ধতির ব্যাপক সাড়া পাওয়া গেছে। (৪) ব্রি-ধান ২৮ এবং ব্রি-ধান ৫৮ জাতগুলো ময়মনসিংহসহ দেশের উত্তরাঞ্চলে আবাদের জন্য এ গবেষণা চালানো হচ্ছে দীর্ঘদিন ধরে। (৫) উত্তরাঞ্চল বিশেষত রাজশাহীর বরেন্দ্র অঞ্চলে কৃষিজমির উপরিভাগ সর্বত্র সমানভাবে সমতল না হওয়ার কারণে সেখানে প্রচলিত পদ্ধতিতে সেচ দেওয়া খুবই অসুবিধাজনক। তা ছাড়া উত্তরাঞ্চলের যেসব স্থানে পানির স্তর দিন দিন নিচে নেমে যাচ্ছে সেসব অঞ্চলের জন্য এ পদ্ধতি খুবই কার্যকর।
(৬) এ পদ্ধতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে আগাছা দমন একটি বড় সমস্যা ছিল; কিন্তু বর্তমানে অনেকাংশেই তা কাটিয়ে তোলা সম্ভব হয়েছে। (৭) আমরা জানি, সবুজ বনানী থেকেও প্রতিনিয়ত পরিবেশ ধ্বংসকারী মিথেনসহ অন্য গ্রিন হাউস গ্যাস নিঃসৃত হয়ে থাকে অনবরত। সেখানে ধানগাছও এর বাইরে নয়। যত বেশিদিন তা মাঠে থাকবে ততদিনই এসব গ্যাস নিঃসরণ করবে। সে জন্য সময় কম এবং পানির পরিমাণ কম লাগার কারণে ধান গাছ থেকে পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর গ্রিন হাউস গ্যাস কম নিঃসৃত হয়। (৮) অন্যদিকে বোরো আবাদে যেহেতু প্রায় শতভাগ সেচের পানির জন্যই ভূ-গর্ভস্থ পানির ওপর নির্ভর করতে হয়।
সে জন্য পরিবেশ বিশেষজ্ঞদের মতে ভূ-গর্ভস্থ পানির এ ক্রমাগত উত্তোলন পরিবেশের জন্য মারাত্মক হুমকি হিসেবে প্রতিভাত। (৯) ফেব্রুয়ারিতে বপন করতে হয় বিধায় বোরো ধান লাগানোর আগে আমন ধান কাটার পর সরিষা, আলু ও অন্যান্য রবি ফসল এর ফাঁকে উৎপাদন করে নেওয়া সম্ভব। এতে বর্তমানে ফসলক্রমের সঙ্গে আরেকটি ফসল যুক্ত হয়ে ফসলের নিবিড়তা বাড়ে। (১০) এভাবে সেচ সহজলভ্য হবে এবং সেচের জন্য বাড়তি খরচ বেঁচে যাবে। ফলে উৎপাদন খরচ কমে গিয়ে কৃষক লাভবান হবে। কাজেই এসব পদ্ধতি সারা দেশে কার্যকরভাবে সম্প্রসারণ করতে পারলে কৃষি ও কৃষক তো উপকৃত হবেই, সেই সঙ্গে বাঁচবে পরিবেশও।
জলবায়ু পরিবর্তন এখন একটি উল্লেখ করার মতো বিষয়। আর জলবায়ু পরিবর্তনের ফলেই অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, তাপমাত্রা বৃদ্ধি ইত্যাদি তার কুফল হিসেবে পরিগণিত। কাজেই জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় কৃষির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অবদান অনস্বীকার্য। আর সেই অবদান সৃষ্টির অংশ হিসেবে বোরো আবাদের এ পরিবেশবান্ধব পদ্ধতি খুবই কার্যকরভাবে অনুসরণ করতে হবে। বোরোর মতো একটি প্রধান ধান ফসলে এগুলো করতে পারলেই একদিকে যেমন কৃষি লাভজনক হবে অন্যদিকে জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত হতে মুক্তি পাওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হবে।
লেখক: কৃষিবিদ ও রেজিস্ট্রার, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়

মহান মে মাস। বিশ্বব্যাপী শ্রমজীবী মানুষের আন্দোলন-সংগ্রামের স্বীকৃতির মাস। শ্রমিকদের দাবির প্রতি সম্মান জানিয়ে প্রতি বছর ১ মে সারা বিশ্বে দিবসটি পালন করা হয়। বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও গুরুত্বের সঙ্গে দিবসটি পালন করা হয়। এবারের মে দিবসের প্রতিপাদ্য-‘শ্রমিক-মালিক গড়ব দেশ, স্মার্ট হবে বাংলাদেশ।’
মহান মে দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশসহ বিশ্বের সব শ্রমজীবী মানুষকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়ে মহামান্য রাষ্ট্রপতি বলেন, আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বিশ্বব্যাপী শ্রমজীবী মানুষের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিল্প ও শ্রমবান্ধব বর্তমান সরকার শ্রমিকের সার্বিক কল্যাণসাধন ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে। তিনি বলেন, ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত ও স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে উন্নত কর্মপরিবেশ, শ্রমিক-মালিক সুসম্পর্ক, শ্রমিকের পেশাগত নিরাপত্তা, সুস্থতাসহ সার্বিক অধিকার নিশ্চিতকরণের কোনো বিকল্প নেই। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, মালিক-শ্রমিকের মধ্যে সৌহার্দ ও সুসম্পর্ক বজায় রাখার মাধ্যমে নিরাপদ কর্মপরিবেশ, সামাজিক নিরাপত্তা ও শ্রমিক কল্যাণ নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ শ্রম আইন যুগোপযোগী ও আধুনিকায়ন করা হয়েছে। দেশের বিভিন্ন খাতে কর্মরত শ্রমিকদের কল্যাণ নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন গঠন করা হয়েছে। আমরা রপ্তানিমুখী গার্মেন্টশিল্পের শ্রমিক-কর্মচারীদের আর্থিক সহায়তা প্রদানে একটি কেন্দ্রীয় তহবিল গঠন করেছি এবং সহযোগিতা অব্যাহত রেখেছি। সব সেক্টরে শ্রমিকদের বেতন-ভাতা বাড়ানো হয়েছে।
১৮৮৬ সালের এই দিনে যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো শহরের হে মার্কেটের শ্রমিকরা ৮ ঘণ্টা কাজের দাবিতে জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। ওই সময়ে আন্দোলনরত শ্রমিকদের ঘিরে থাকা পুলিশের প্রতি অজ্ঞাতনামা কেউ বোমা নিক্ষেপ করলে পুলিশ শ্রমিকদের ওপর গুলি চালায়। এতে ১০-১২ জন শ্রমিক ও পুলিশ নিহত হন। ওই দিন তাদের আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে বিশ্বে শ্রমিক শ্রেণির অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। অর্থাৎ শিকাগোর হে মার্কেটে দিনে ৮ ঘণ্টা কাজের দাবিতে অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন করতে গিয়ে কয়েকজন শ্রমিককে জীবন দিতে হয়। তবে দিবস পালনের সিদ্ধান্ত হয় আরও পরে। ১৮৮৯ সালে ফরাসি বিপ্লবের শতবার্ষিকীতে প্যারিসে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে ১৮৯০ সাল থেকে শিকাগো প্রতিবাদের বার্ষিকী আন্তর্জাতিকভাবে বিভিন্ন দেশে পালনের প্রস্তাব করেন রেমন্ড লাভিনে। ১৮৯১ সালে আন্তর্জাতিক কংগ্রেসে এ প্রস্তাব গৃহীত হয়। এরপর ১৮৯৪ সালে মে দিবসের দাঙ্গার ঘটনা ঘটে। এই ধারাবাহিকতায় ১০০ বছর পর ১৯০৪ সালে আর্মস্টারডাম শহরে অনুষ্ঠিত সমাজতন্ত্রীদের আন্তর্জাতিক সম্মেলনে এ উপলক্ষে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। ওই প্রস্তাবে বিশ্বজুড়ে সব শ্রমিক সংগঠন ১ মে ‘বাধ্যতামূলকভাবে কাজ না করার’ সিদ্ধান্ত নেন। এরপর থেকে সারা বিশ্বে দিনটি ‘মে দিবস’ হিসেবে পালিত হয়ে আসছে।
শ্রমিক মজুরি, মূল্যস্ফীতির হার ও জীবনের গল্প:
বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) সর্বশেষ তথ্যমতে, গত মার্চে দেশে সার্বিক মূল্যস্ফীতির হার ছিল ৯ দশমিক ৮১ শতাংশ। আগের বছরের একই মাসে যা ছিল ৯ দশমিক ৩৩ শতাংশ। চলতি বছরের মার্চে খাদ্য মূল্যস্ফীতি ছিল আরও বেশি, ৯ দশমিক ৮৭ শতাংশ। আর ১২ মাস ধরে গড় মূল্যস্ফীতির হার ৯ দশমিক ৬৯ শতাংশ। কিন্তু সে অনুযায়ী বাড়েনি শ্রমজীবীদের মজুরি। বিষয়টি বিবিএসের তথ্যেও উঠে এসেছে। গত মার্চে সাধারণ মজুরি বৃদ্ধির হার ছিল ৭ দশমিক ৮০ শতাংশ। সে হিসাবে মূল্যস্ফীতির তুলনায় তা কম ছিল ২ দশমিক শূন্য ১ শতাংশ। আর খাদ্য মূল্যস্ফীতি প্রায়ই সার্বিক মূল্যস্ফীতিকেও ছাড়িয়ে যাচ্ছে। এমন পরিস্থিতিতে দেশের শ্রমজীবীসহ নিম্ন আয়ের মানুষ প্রয়োজনের তুলনায় কম খাদ্য গ্রহণ এবং চাহিদা ছেঁটে জীবনযাপনের ব্যয় সংকুলান করছেন। জীবিকা নির্বাহ কঠিন হওয়ায় অনেকে আবার শহর ছাড়ারও চিন্তা করছেন। তাদেরই একজন পিরোজপুরের মঠবাড়িয়ার ইউনুস আলী। আগে দৈনিক মজুরি ভিত্তিতে অন্যের কৃষিজমিতে কাজ করতেন। সেই আয় দিয়ে সংসার চালাতে কষ্ট হওয়ায় পাড়ি জমান ঢাকায়। কারওয়ান বাজারে এখন কুলির কাজ করছেন। থাকেন একটি মেসে। তবে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির এ সময়ে নিজের খাবার খরচ ও মেস ভাড়া মিটিয়ে বাড়িতে তেমন টাকা পাঠাতে পারছেন না বলে জানান। তাই আবার গ্রামে পরিবারের কাছেই ফিরে যাওয়ার চিন্তা করছেন ইউসুফ।
অর্থনীতিবিদরা বলছেন, প্রকৃত আয় না বাড়ায় শ্রমিকদের ভোগ কমছে। দীর্ঘমেয়াদে জীবনযাত্রার মান কমে গিয়ে তারা চরম দারিদ্র্যসীমায় নেমে যেতে পারেন। আর ভোগ কমলে বিনিয়োগও কমবে। ফলে কমে আসতে পারে প্রবৃদ্ধিও। টিকতে না পেরে ২০২৩ সালে প্রতি হাজারে প্রায় ১৪ জন শহর ছেড়ে গ্রামে ফিরে যান। পাঁচ বছর আগে এ হার ছিল একজনেরও কম। বাংলাদেশ স্যাম্পল ভাইটাল স্ট্যাটিসটিকস-২০২৩ শীর্ষক এক প্রতিবেদনে এ তথ্য উঠে এসেছে। তাতে উল্লেখ করা হয়েছে, গত বছর প্রতি হাজারে শহর ছেড়ে গ্রামে গেছে ১৩ দশমিক ৮ জন। আগের বছর এ হার ছিল ১০ দশমিক ৯ জন। ২০২১ সালে প্রতি হাজারে ৫ দশমিক ৯ জন শহর ছেড়ে গ্রামে পাড়ি দেন। ২০২০ সালে এ হার ছিল ৮ দশমিক ৪ জনে। ২০১৯ সালে প্রতি হাজারে শহর ছেড়ে গ্রামে গেছেন একজনেরও কম বা দশমিক ৭ জন। অর্থাৎ আগের চেয়ে বেশি মানুষ এখন শহর ছেড়ে গ্রামে যাচ্ছেন।
তীব্র তাপপ্রবাহের প্রভাব জীবনমানে:
চলমান তীব্র তাপপ্রবাহের কারণে ঠিকমতো বাইরে কাজ করতে পারছেন না শ্রমিকরা। এতে তাদের আয় কমে গেছে। সংসার চালাতে অনেককে বেশ হিমশিম খেতে হচ্ছে। বরগুনা থেকে ঢাকায় এসেছেন নজরুল ইসলাম। জীবিকা নির্বাহ করছেন রিকশা চালিয়ে। এফডিসি মোড়ে তার সঙ্গে কথা হলে জানান, রোদের প্রখরতায় ঠিকমতো কাজ করতে পারছেন না। কিছু সময় পরপর পানি বা শরবত পান করতে হচ্ছে, তাতে বাড়তি ব্যয়ও গুনতে হচ্ছে। অথচ সে অনুযায়ী আয় নেই তার। নিম্ন আয়ের মানুষকে মজুরির একটি বড় অংশই ব্যয় করতে হচ্ছে খাদ্যদ্রব্য ও প্রয়োজনীয় সামগ্রী কিনতেই। অথচ মূল্যস্ফীতির তুলনায় তাদের আয় বৃদ্ধির হার সেভাবে বাড়েনি। আর খাদ্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি ভারী বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে। রংপুর থেকে ঢাকায় এসে রিকশাভ্যান চালান আলম মিয়া। তিনি জানান, আগে গাড়ির জমা হিসেবে দিনপ্রতি মালিককে দিতে হতো ১৫০ টাকা করে। এখন সেটি বাড়িয়ে দিতে হয় ২০০ টাকা। এভাবে প্রতিটি ক্ষেত্রেই দাম বেড়ে গেছে। বিবিএসের তথ্য অনুযায়ী, সবচেয়ে কম মজুরি বাড়ছে শিল্প খাতের শ্রমিকদের। গত মার্চে এ খাতের মজুরি বৃদ্ধির হার ছিল ৭ দশমিক ৩২ শতাংশ। অর্থাৎ সাধারণ মজুরির তুলনায় তাদের মজুরি বৃদ্ধির হার আরও কম। যদিও কৃষি ও সেবা খাতের শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধির হার ছিল ৮ শতাংশের বেশি। দেশে ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারির আগেও মূল্যস্ফীতির তুলনায় শ্রমিকের মজুরি হার ছিল বেশি। পণ্যের দামের চেয়ে মজুরি বেশি পাওয়ায় শ্রমিকের প্রকৃত আয় বা ক্রয়ক্ষমতাও বেশি ছিল তখন; কিন্তু ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে চলতি বছরের মার্চ পর্যন্ত টানা ২৬ মাস ধরে মূল্যস্ফীতির চেয়ে শ্রমের মূল্য কম, যা দারিদ্র্যসীমার হারকে উসকে দিচ্ছে বলে মনে করছেন অর্থনীতিবিদরা। এ বিষয়ে বেসরকারি গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) বক্তব্য, ‘প্রকৃত আয় না বাড়ায় শ্রমিকদের প্রকৃত মজুরি বাড়ছে না। ফলে তাদের জীবনমান কমছে। দীর্ঘমেয়াদে তারা দারিদ্র্যসীমার নিচে চলে যাবে। আর ভোগ কমায় বিনিয়োগ কম হবে। এতে প্রবৃদ্ধিও কমে আসবে। এটার প্রভাব থাকবে খানা ও জাতীয়পর্যায়েও। সামাজিক অসন্তোষ ও বিচ্ছিন্নতাবোধও বাড়তে পারে এ কারণে।’ বিভাগভিত্তিক হিসাবে দেখা গেছে, চট্টগ্রাম, বরিশাল ও সিলেট বিভাগে মজুরি বৃদ্ধির হার ৭ শতাংশের কম। অর্থাৎ এসব এলাকায় মূল্যস্ফীতির চাপ আরও বেশি। সিলেটে মজুরি বৃদ্ধির হার ৬ দশমিক ৪৬ শতাংশ, চট্টগ্রামে ৬ দশমিক ৫৩ আর বরিশালে ৬ দশমিক ৮৭ শতাংশ। দেশের ৬৩ খাতের তথ্য সংগ্রহ করে মজুরি বৃদ্ধির পরিসংখ্যান প্রকাশ করে বিবিএস। এর মধ্যে ১৭টি খাত কৃষিসংক্রান্ত, শিল্পসংশ্লিষ্ট ৬৩টি ও সেবাসংক্রান্ত খাত রয়েছে ১৬টি।
মূল্যস্ফীতি বাড়লে দরিদ্ররা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়, মানুষের ক্রয়ক্ষমতা কমে যায়, যারা দারিদ্র্যসীমার কাছাকাছি ছিল চলমান পরিস্থিতির কারণে তারা সীমার নিচে নেমে যাবে। আর এটা চলতে থাকলে চরম দারিদ্র্য ও বৈষম্যও বেড়ে যাবে।’ বিবিএস মূলত ১২টি খাতের সমন্বয়ে মূল্যস্ফীতির হিসাব প্রকাশ করে। মূল্যস্ফীতির খাতভিত্তিক তথ্যমতে, খাদ্যের পাশাপাশি বাসা ভাড়া, পানি, বিদ্যুৎ, গ্যাস ও অন্যান্য জ্বালানির বিল বাবদ ব্যয় আগের চেয়ে বেড়েছে। মার্চে এ খাতে মূল্যস্ফীতির হার ছিল ১১ দশমিক ৯৩ শতাংশ। বাড়ির আসবাব খাতে এ হার ছিল ১৩ দশমিক ৬১ শতাংশ। বিনোদন খাতে মূল্যস্ফীতির হার ছিল ১৭ শতাংশের বেশি।
এ ব্যাপারে সাবেক পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী বলেন ‘মূল্যস্ফীতি যে হারে বাড়ছে সেভাবে মজুরি বাড়েনি। তার বড় কারণ শ্রমিকের চাহিদা না বাড়া। উচ্চ মূল্যস্ফীতি এবং ডলার সংকটসহ আমদানি নিয়ন্ত্রণের প্রভাবে বিনিয়োগ কম হচ্ছে। ফলে শ্রমের চাহিদাও কম। তবে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে এলে এবং অর্থনীতি চাঙ্গা হলে শ্রমিকের মজুরি আবার বেড়ে যাবে। এটা সাময়িক সমস্যা, দুই-তিন মাসের মধ্যে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে চলে আসতে পারে। মূল্যস্ফীতির প্রভাব মোকাবিলায় করণীয় সম্পর্কে তার বক্তব্য হলো- উন্নয়ন প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নে ভালোভাবে নজর দিতে হবে। সরকার অবশ্য সামাজিক সুরক্ষা জোরদারে চেষ্টা করছে। আগামী বাজেটে এ খাতে বরাদ্দ ও সেবার পরিধি বাড়বে বলে আশা করছি আমরা। টিসিবির মাধ্যমে পণ্য বিক্রি করা হচ্ছে। সরকার এ বিষয়ে সজাক রয়েছে।
কৃষি শ্রমিক ও মে দিবস:
কৃষিতে শ্রম দিয়ে যারা জীবিকা অর্জন করে তাদের কৃষি শ্রমিক বলা হয়। নানা কারণে কৃষিতে শ্রমশক্তি ক্রমহ্রাসমান। ২০০০ সালে দেশের মোট শ্রমশক্তির মধ্যে ৬০ শতাংশ ছিল কৃষি শ্রমিক। সেটি কমে বর্তমানে ৩৭ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। ২০৫০ সাল নাগাদ তা ২০ শতাংশে ঠেকতে পারে। মূলত কৃষি শ্রম খাতে অবহেলার কারণে দেশে কৃষি শ্রমিকের হার দিনে দিনে কমে যাচ্ছে। কৃষি খাতে ভর্তুকি, প্রাকৃতিক দুর্যোগে প্রণোদনা, কৃষি ঋণ, বিনামূল্যে এবং ভর্তুকি মূল্যে উচ্চফলনশীল বীজ সরবরাহ, সারসহ কৃষি উপকরণে উন্নয়ন সহায়তা প্রদান ইত্যাদির প্রচলন থাকলেও কৃষক যখন মাঠে কাজ করবেন তখন তার স্বাস্থ্য ও সামাজিক সুরক্ষা তথা মানসিক প্রশান্তির জন্য কোনো অবকাঠামোগত সুবিধা নেই। প্রখর রোধে তারা কাজ করলেও বিশ্রাম নেওয়ার কোনো জায়গা নেই। কৃষককে মাঠে-ঘাটের নোংরা কাদামাটির ওপর বসেই খাবার খেতে হয়। কাছাকাছি কোনো নিরাপদ পানির উৎস না থাকায় অনিরাপদ পানি খেতে হয়।
প্রতি বছর মে দিবস এলেই শ্রমিকদের অধিকার নিয়ে নানা রকম সভা-সমাবেশ, বক্তৃতা-বিবৃতি, সেমিনার-সিম্পোজিয়াম ও শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়। সংবাদপত্রে বের করা হয় বিশেষ ক্রোড়পত্র। ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় সম্প্রচার করা হয় আলোচনা অনুষ্ঠান, প্রামাণ্য অনুষ্ঠান ও টক শো। মে দিবস আসে আবার চলেও যায়। কিন্তু দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রমিকশ্রেণি তথা কৃষিশ্রমিকদের কথা থাকে উপেক্ষিত। অথচ কৃষিভিত্তিক আমাদের এ দেশ বাংলাদেশ। মোট জনশক্তির প্রায় ৫০ ভাগ এখনো প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কৃষিকাজে নিয়োজিত; কিন্তু শ্রমিকশ্রেণির সর্বাধিক এ খাতটি নিয়ে তেমন কোনো আলোচনা দেখা যায় না। উপরন্তু কৃষিশ্রমিকদের নেই কোনো সংগঠন, সমিতি বা কারখানার শ্রমিকদের মতো ট্রেড ইউনিয়ন। আর তাই তাদের মৌলিক মানবিক ও সামাজিক অধিকার, সুযোগ-সুবিধা এবং নানা সমস্যা থেকে যায় অতল অন্ধকারে।
কৃষিশ্রমিকদের অর্ধেকই হলো আবার নারী কৃষিশ্রমিক। যেখানে কৃষিশ্রমিকদের শ্রমিকশ্রেণির অংশই মনে করা হয় না সেখানে নারী কৃষিশ্রমিক যারা ফসল রোপণ-বপন, পরিচর্যা এবং ফসল সংগ্রহোত্তর কার্যক্রমের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত তাদের অবস্থান কোথায় তা সহজেই বোধগম্য। বিগত জাতীয় কৃষি শুমারিগুলোর রিপোর্টে দেখা যায়, দেশে কৃষি খামারের সংখ্যা ও আয়তন উল্লেখযোগ্য হারে কমেছে। বেড়েছে ভূমিহীন ও বর্গাচাষির সংখ্যা। গ্রামে বর্গাচাষির সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় কৃষি খামারের আয়তন কমে যাওয়ায় কৃষি অর্থনীতির জন্য ইতিবাচক কিছু নয়। দ্রুত নগরায়ণ ও গ্রামে ভূমিহীনের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় শহরেও ভূমিহীন মানুষের সংখ্যা বাড়ছে। উচ্চমূল্যের কৃষি উপকরণ, কৃষিপণ্যের ন্যায্যমূল্য না পাওয়া, কৃষিতে মধ্যস্বত্বভোগী ও মহাজনের দৌরাত্ম্য, কৃষিতে জলবাযু পরিবর্তনের প্রভাব, নতুন প্রযুক্তির সঙ্গে কৃষকরা খাপ খাওয়াতে না পারা প্রভৃতি কারণে স্বাধীনতা-উত্তর ক্রমান্বয প্রান্তিক কৃষকরা ভূমিহীন জনগোষ্ঠীতে পরিণত হচ্ছে। বর্তমানে এদের অবস্থা হয় বর্গাচাষি বা কৃষি দিনমজুর কিংবা নগরশ্রমিক। খুলনা বিভাগে জমিতে লবণাক্ততা ও রাজশাহী বিভাগে খরা এবং পানি স্বল্পতার কারণে অনেক জমি কৃষিকাজের অনুপযোগী হয়ে উঠছে। ফলে বেকার হয়ে পড়ছে কৃষিশ্রমিক। এ ছাড়া দেশে কৃষিশ্রমিকদের সারা বছর নিরবচ্ছিন্ন কাজ থাকে না। তাই তারা অন্য পেশায় চলে যাচ্ছেন। এ জন্য আমরা লক্ষ্য করি ধান কাটার মৌসুমে পর্যাপ্ত কৃষিশ্রমিক পাওয়া যায় না।
উপসংহার:
সরকার শ্রমিকদের স্বার্থ সংরক্ষণে সজাগ রয়েছে এবং স্মার্ট বাংলাদেশ বির্নিমাণে শ্রমিকদের সঙ্গে করে দেশকে গড়বে । মে দিবস বিশ্বের শ্রমজীবী মানুষের অধিকার আদায়ের দিন। দেশে দ্রব্যমূল্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে অন্য পেশাজীবীদের বেতন-ভাতা বাড়লেও অনেকেই পিছিয়ে রয়েছেন। এ ছাড়া অনেক প্রতিষ্ঠানে বেতন অনিয়মিত। এ বিষয়ে রাষ্ট্রকে আরও দায়িত্বশীল হতে হবে। জয় হোক মেহনতি মানুষের।
লেখক: অধ্যাপক (অর্থনীতি), সাবেক ডিন, ব্যবসায় প্রশাসন অনুষদ, সিটি ইউনিভার্সিটি, ঢাকা।
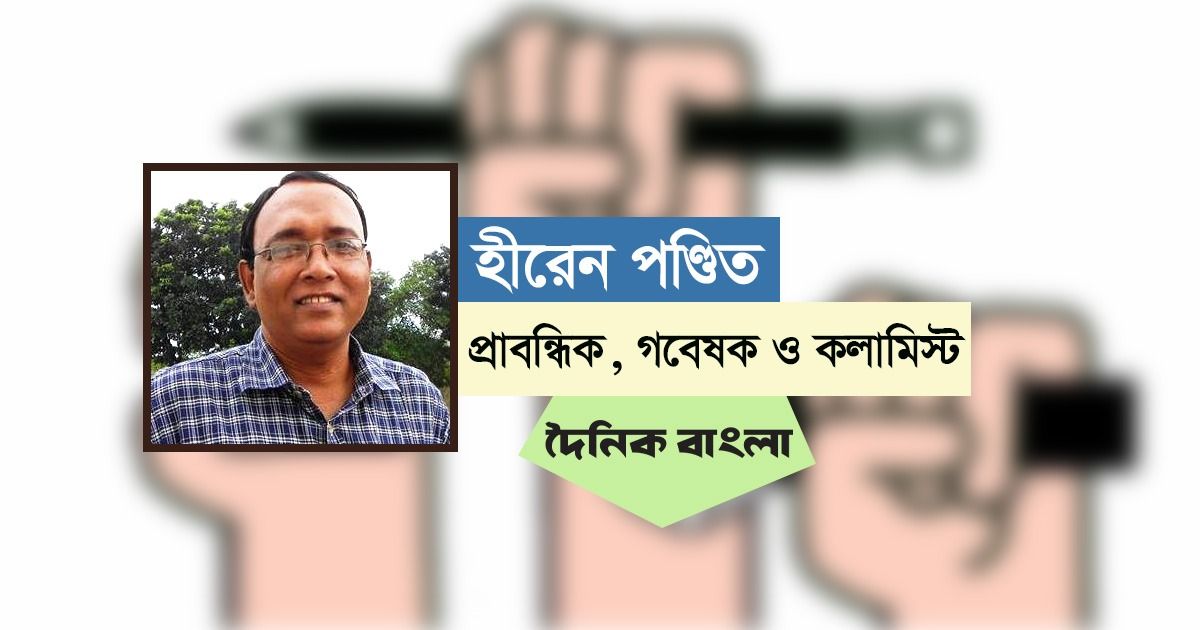
অপরের অধিকারে হস্তক্ষেপ না করে নিজের ইচ্ছামতো চলাই স্বাধীনতা, হার্বার্ট স্পেন্সার তাই বলেছেন। গণমাধ্যমের স্বাধীনতার পাশাপাশি তথ্যভিত্তিক সংবাদও সমান গুরুত্বপূর্ণ। সরকারের কার্যক্রম নিয়ে যেকোনো সমালোচনা যে কেউ করতে পারে। কিন্তু উদ্দেশ্যমূলকভাবে যখন ধারাবাহিক মিথ্যাচার করা হয়, তখন প্রশ্ন ওঠে। সেসব সংবাদ নিয়েও জনগণের মনে নানা প্রশ্ন থাকতে পারে।
১৯৯১ সালে ইউনেস্কোর ২৬তম সাধারণ অধিবেশনের সুপারিশ মোতাবেক ১৯৯৩ সালে জাতিসংঘের সাধারণ সভায় ৩ মে তারিখটিকে ওয়ার্ল্ড প্রেস ফ্রিডম ডে অথবা বিশ্ব মুক্ত গণমাধ্যম দিবসের স্বীকৃতি দেওয়া হয়। সাংবাদিকতার স্বাধীনতা ও মুক্ত গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠার মৌলিক নীতিমালা অনুসরণ, বিশ্বব্যাপী গণমাধ্যমের স্বাধীনতার মূল্যায়ন, স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ প্রতিহত করার শপথগ্রহণ এবং পেশাগত দায়িত্ব পালনকালে ক্ষতিগ্রস্ত ও জীবনদানকারী সাংবাদিকদের স্মরণ ও তাদের স্মৃতির প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয় এই দিবসে।
মত প্রকাশের স্বাধীনতা পর্যবেক্ষণ করে এমন কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের জরিপ ও মূল্যায়নে দেখা যাচ্ছে, সারা বিশ্বেই গণমাধ্যমের ঝুঁকি বেড়ে চলেছে। বিশ্বের গণতান্ত্রিক দেশগুলোতে আইন কমিশন ও বিচার বিভাগীয় প্রতিষ্ঠানগুলো ঐতিহ্যগতভাবে সংবাদপত্রের স্বাধীনতাকে সুদৃঢ় করতেই ভূমিকা পালন করে থাকে।
এটি অনস্বীকার্য যে বাক্-স্বাধীনতা অধিকারের রক্ষাকবচ অবশ্যই যুক্তিসংগত বাধা-নিষেধ সাপেক্ষেই নাগরিক ও সাংবাদিকরা ভোগ করে থাকেন। কেউ সেই বিধি-নিষেধ না মানলে তার বিরুদ্ধে দেশের প্রচলিত আইনেই ব্যবস্থা নেওয়া যায়। গণমাধ্যমের জবাবদিহি নিশ্চিত করতে প্রেস কাউন্সিলকে অধিকতর শক্তিশালী করা হয়েছে। তথ্য মন্ত্রণালয়ের হিসাব বলছে, সার্বিকভাবে গত এক যুগে তথ্য মন্ত্রণালয়ের সুবিশাল কর্মযজ্ঞে দেশে গণমাধ্যমের অভূতপূর্ব বিকাশ ঘটেছে এবং অবাধ তথ্যপ্রবাহের নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে।
পিআইডির তথ্য থেকে জানা যায়, গণমাধ্যমের উন্নয়নে এ সময়ে নতুন দুই হাজারের বেশি পত্রিকা নিবন্ধিত হয়েছে; বেসরকারি খাতে নতুন ৪৪টি স্যাটেলাইট টেলিভিশন চ্যানেলের অনুমোদনসহ ২৮টি এফএম রেডিও এবং ৩২টি কমিউনিটি রেডিওকে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক ও ষান্মাসিক মিলিয়ে মোট পত্রিকার সংখ্যা দুই হাজার ৮৫৫। বাংলাদেশ টেলিভিশন, বিটিভি ওয়ার্ল্ড, সংসদ বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বাংলাদেশ টেলিভিশন চট্টগ্রাম কেন্দ্র নিয়ে সরকারি চারটি ও অনুমোদনপ্রাপ্ত ৪৪টি বেসরকারি স্যাটেলাইট টেলিভিশন। পিআইডির প্রতিবেদনের মাধ্যমে জানানো হয়েছে, ‘দেশের উন্নয়নকে টেকসই, গতিশীল ও অংশগ্রহণমূলক করতে অবাধ তথ্যপ্রবাহের কোনো বিকল্প নেই।
বর্তমান সরকারের এই অন্যতম মূলমন্ত্র বাস্তবায়নে কাজ করছে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়। উন্নয়নে জনগণের অংশগ্রহণ এবং প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়ার অধিকার নিশ্চিত করার পাশাপাশি দেশের গণমাধ্যমকে শক্তিশালী করার দৃঢ় প্রত্যয় সেই কাজেরই অংশ।
গণমাধ্যমের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করার ইচ্ছে নেই। তবে যারা সরকারের উন্নয়নের অপপ্রচার করবে, তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী আরাফাত। তিনি বলেন, ‘রামপাল নিয়ে অনেক মিথ্যাচার হয়েছে। এর মধ্যে সবচেয়ে বড় মিথ্যা হচ্ছে, ভারত নিয়ে মিথ্যাচার। রিপোর্টিংয়ের সততা থাকতে হবে। যেকোনো ধরনের সমালোচনাকে আমরা স্বাগত জানাই, তবে মিথ্যাচারকে নয়।’
ইউনেস্কো, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের (টিআইবি) ও আর্টিকেল ১৯ আয়োজিত ‘বিশ্ব মুক্ত গণমাধ্যম দিবস ২০২৪’ উপলক্ষে ‘বর্তমান বৈশ্বিক পরিবেশগত সংকটের প্রেক্ষাপটে মুক্ত গণমাধ্যম এবং মতপ্রকাশের স্বাধীনতা’ শীর্ষক আলোচনা সভায় তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী এসব কথা বলেন।
তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী বলেন, ‘গণমাধ্যমের স্বাধীনতার নামে যখন এর অপব্যবহার হয়, তখন এটার পরিণাম হয় খুবই ভয়াবহ, এ ক্ষেত্রে সতর্ক থাকতে হবে। গত ১৫ বছরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণমাধ্যমের প্রসার ও এর স্বাধীনতার জন্য ব্যাপক ভূমিকা পালন করেছেন। সরকার অঙ্গীকারবদ্ধ গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে। আমরা প্রকৃতি ও পরিবেশ রক্ষায় অঙ্গীকারবদ্ধ। এ ক্ষেত্রে সবাইকে আমরা স্বাগত জানাই, যারা বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত দিয়ে সহযোগিতা করতে চায়। আমরা শুধু উন্নয়নই করতে চাই না, আমরা টেকসই উন্নয়ন করতে চাই, যেটা আমাদের পরিবেশকে সুরক্ষা দেবে।’
বাংলাদেশ বৈশ্বিক উষ্ণায়ন মোকাবিলায় প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করেছে। ক্রমবর্ধমান ভূমি দস্যুতা, উন্নয়নের নামে জীববৈচিত্র্য ধ্বংস করা, নগরায়ণের নামে জবর দখল এখন স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় পরিণত হয়েছে। পরিবেশের ওপর এমন আগ্রাসনে ক্ষমতাসীনদের একাংশ লাভবান হচ্ছে বিধায় এ দের সুরক্ষা দিচ্ছে তারা। এসব নিয়ে যারা কাজ করবে গণমাধ্যমসহ সুশীল সমাজ, সেই পরিবেশ দিন দিন সংকুচিত হচ্ছে। আইনের মধ্যেও দুর্বলতা রয়েছে। যাদের আইন প্রয়োগ করার কথা, জবাবদিহি নিশ্চিত করার কথা, তাদেরও যোগসাজশ রয়েছে বলে টিআইবি উল্লেখ করে।
সাংবাদিকতা সারা বিশ্বেই চ্যালেঞ্জের মুখে। পরিবেশ বিষয়ক সাংবাদিকতা একটু বেশি চ্যালেঞ্জিং। বালুমহাল, পাহাড় কেটে লেক তৈরি, এসবের পেছনে অনেক ক্ষমতাধর ব্যক্তিরা জড়িত। তাদের বাধার মুখে পড়তে হয়। টিভি সাংবাদিকদের দেখার কেউ নেই। ঝুঁকি নিয়ে সাংবাদিকরা কোনো একটা কাজ করতে গেলে, বিপদে পড়লে কেউ পাশে থাকে না।
তথ্যপ্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী আরাফাত উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলেন, ‘দেশের গণমাধ্যম শুধু মুক্ত নয়, উন্মুক্ত। তবে যারা রাষ্ট্রের বিরোধিতা করছে, তাদেরকে সরকার নজরদারিতে আনতে চায়।’ তিনি বলেন, ‘গণমাধ্যমের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করার কোনো ইচ্ছে সরকারের নেই। তবে যারা দেশের উন্নয়নের অপপ্রচার করবে, তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। গণমাধ্যমের স্বাধীনতা রক্ষায় সরকার কমিটেড। গণমাধ্যম শুধু মুক্ত নয়, উন্মুক্ত। বরং সরকারকেই অনেক সাংবাদিক নিবন্ধনহীন অনলাইন বন্ধ করার কথা বলেন। গণমাধ্যম কর্মীদের তালিকা করতে বলে, কে কোথায় কাজ করে। আমরা কিন্তু সেটা করছি না। আমরা চাই একটা নিয়মতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মধ্যে সবাই আসুক। সুস্থ ধারার সাংবাদিকতায় কোনো বাধা নেই।
তবে গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ব্যবহার করে যাতে আইনের অপব্যবহার না হয়, সে ব্যাপারে সচেতন হওয়া প্রয়োজন। সঠিক তথ্য-উপাত্তের বিপরীতে ডকুমেন্টস থাকে, তার বিরুদ্ধে কথা বলার সুযোগ নেই। গণমাধ্যমের স্বাধীনতা মানে কোনো নিজস্ব পারপাস সার্ভ করা নয়। গণমাধ্যমের স্বাধীনতার নামে যখন এর অপব্যবহার হয়, তখন এর পরিণাম হয় খুবই ভয়াবহ। এ ক্ষেত্রে সতর্ক থাকতে হবে। গত ১৫ বছরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণমাধ্যমের প্রসার ও এর স্বাধীনতার জন্য ব্যাপক ভূমিকা পালন করেছেন। গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে সরকার অঙ্গিকারবদ্ধ। আমরা প্রকৃতি ও পরিবেশ রক্ষায় অঙ্গীকারবদ্ধ। পরিবেশকে সুরক্ষিত করতে চাই।
রামপাল ও আদানি গ্রুপ নিয়ে দিনের পর দিন মিথ্যাচার হয়েছে। এটা যে ক্ষতিকর সেটা সত্যি নয়। আমরা আমাদের স্বার্থে এনটিএমসিকে বাংলাদেশে এনেছি। তাদের ৭০ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ প্রকল্প করার অভিজ্ঞতা আছে। আমরা এক্সিম ব্যাংকের বিনিয়োগ এনেছি। আমরা চেয়েছি পার্টনারশিপের মাধ্যমে বিদ্যুতের উন্নয়ন। পুরোটাই বাংলাদেশের স্বার্থ। ওখানে ৫০-৫০ পার্টনারশিপ, লাভ যা হবে তাও ভাগ হবে।’
তিনি বলেন, ‘আমাদের গার্মেন্টন্স ও পাহাড়ি এলাকা নিয়ে আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র হয়। এটা সত্যি। সরকার সব সময় সমালোচনাকে স্বাগত জানায়। কিন্তু যখন সিস্টেমেটিক এজেন্ডা বাস্তবায়ন হয়, আমরা সেটার বিরুদ্ধে। পরিবেশ বিপর্যয় কিংবা দুর্নীতি নিয়ে যেকোনো প্রতিবেদনকে স্বাগত জানাই। আমি এখনো বলে যাচ্ছি, এই ধরনের সাংবাদিকতা রক্ষায় সঙ্গে আছি।’
বিশ্ব মুক্ত গণমাধ্যম সুচকে পিছিয়ে বাংলাদেশ প্রসঙ্গে প্রতিমন্ত্রী বলেন, ‘রিপোর্টার্স উইদাউট বর্ডারস (আরএসএফ) ২০২৩ সালের মে মাসে যে প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে তাতে ভুল তথ্য আছে এবং সেখানে বাস্তবতার প্রতিফলন ছিল না। ওয়েবসাইটে ভুল, অর্ধসত্য ও অপর্যাপ্ত তথ্যের ওপর ভিত্তি করে বিশ্ব মুক্ত গণমাধ্যম সূচকে বিশ্বের ১৮০টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশকে ১৬৩তম দেখানো হয়েছে। এটা নিয়ে আমরা চিঠি লিখেছি, তারা ভুল তথ্য ডিলিট করেছে। কিন্তু র্যাংকিং ঠিক করা হয়নি।
সংবাদ প্রকাশের জেরে গণমাধ্যমকর্মীদের ওপর হামলা, মামলা বা হয়রানির ঘটনা অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় অনেক সময় শুধু সংবাদ সংগ্রহ বা সংবাদের জন্য সাংবাদিক নিগৃহীত হয়েছেন এর সংখ্যা খুব বেশি নয় তবে তথ্য বা সংবাদ প্রচারের চেয়ে ব্যক্তিগত শত্রুতার সংখ্যা অনেক বেশি। পাশাপাশি সাংবাদিকদের তথ্য পাওয়ার সুযোগও দিন দিন সংকুচিত হচ্ছে এই অভিযোগও ঠিক নয় সরকারের সব তথ্য এখন ওয়েবসাইটে দেওয়া অছে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে সাংবাদিকদের প্রবেশ আটকাতে এবং তথ্য সংগ্রহে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করতে চলছে নানা তৎপরতা এই অভিযোগ সঠিক নয়। বাংলাদেশ ব্যাংকে সাংবাদিক প্রবেশে অলিখিত নিষেধাজ্ঞার বিষয়টি নিয়ে গণমাধ্যমকর্মীদের মধ্যে উদ্বেগের সৃষ্টি হয়েছে, তবে এটাও সত্য বাংলাদেশ ব্যাংক একটি সংবেদনশীল জায়গা। ২০০৯ সালের তথ্য অধিকার আইনে স্পষ্ট বলা আছে কোন তথ্য দেওয়া যাবে কোনটা যাবে না।
তথ্য প্রদানের জন্য সব সরকারী, স্বায়ত্তশাসিত ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে একজন তথ্যপ্রদানকারী কর্মকর্তা রয়েছে। যে কারণে তথ্য অধিকার আইন করে অনেক বেশি লাভ হয়েছে। তথ্য পাওয়া নাগরিক অধিকার। জনগণের কাছে সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর জবাবদিহি আছে। এটি নিশ্চিতে সাংবাদিক প্রবেশে কোথাও নিষেধাজ্ঞা নেই। তবে সংবেদনশীল অফিস ও তথ্যগুলো সবাইকে সেদিক থেকেই ভাবতে হবে।
সরকারি, আধা সরকারি বা স্বায়ত্তশাসিত দপ্তর এমনকি জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত কোনো কোনো প্রতিষ্ঠানেও পেশাগত কাজে প্রবেশ করতে কোনো বাধা নেই। সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলোতে সাংবাদিকদের প্রবেশ একটি শৃঙ্খলার মধ্যে আনা যেতে পারে। সে ক্ষেত্রে কেউ যখন তথ্য চাইবেন, তা পাওয়ার ব্যবস্থা থাকতে হবে। তথ্য পাওয়া নাগরিক অধিকার। জনগণের কাছে সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর জবাবদিহি আছে, সেভাবেই সবাইকে কাজ করতে হবে।
নানা সীমাবদ্ধতার পরও এগোচ্ছে, মুক্ত গণমাধ্যমও এগোচ্ছে, এগোবে। আরও এগোতে হবে। গণমাধ্যমকে গণতন্ত্র ও উন্নয়নের সোপান হিসেবে ব্যবহার করতে হবে। তবে গণমাধ্যমকে শক্তিশালী করতে আমাদের আরও কাজ করতে হবে। গণমাধ্যম মানুষের জন্য তথ্যের বৃহত্তর স্বার্থ রক্ষা করে। তবে অনেক সময় গণমাধ্যমকেও পক্ষপাতিত্ব করতে দেখা যায়। নানা মতাদর্শের ভিন্ন আঙ্গিকের সংবাদ জনসাধারণের কাছে তুলে ধরা হয়। এর মাধ্যমে গণমাধ্যম অগণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থাকে উৎসাহিত করে।
ইন্টারনেটভিত্তিক সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম জনসাধারণ সরাসরি মত প্রকাশ করতে পারছেন। এখন আর মত প্রকাশের স্বাধীনতা শুধু সংবাদপত্রের ওপরই নির্ভর করে না। এতে যুক্ত হয়েছে সামাজিক মাধ্যম ফেসবুক, ইউটিউব, টুইটার ও ব্লগ। তবে এসব মাধ্যমের সুযোগ নিয়ে রাজনৈতিক কিংবা ব্যক্তি স্বার্থ রক্ষায় অনেক সময় ভুল সংবাদ প্রচারের মাধ্যমে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করা হয়, এর ফলে গণতন্ত্রের মূলমন্ত্র বাধাগ্রস্ত হয়। মালিক ও বিজ্ঞাপনদাতাদের প্রভাবও স্বাধীন সাংবাদিকতাকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে।
গণমাধ্যমের কাজ হলো এই জনগণের বার্তা নিরপেক্ষ ও নির্ভুলভাবে সরকারের কাছে তুলে ধরা। একটি দেশে গণমাধ্যমের স্বাধীনতা আছে কি নেই এবং নাগরিকের চিন্তার স্বাধীনতা আছে কি নেই, তা দিয়ে সহজেই গণতান্ত্রিক পরিস্থিতি পরিমাপ করা সম্ভব। গণমাধ্যমের সমন্বয়হীনতা রোধ করা জরুরি। দেশ, জাতি, গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, মানবাধিকার, গণমাধ্যমের স্বাধীনতা এবং আইনের শাসনের বিষয়টি বরাবরই সমুন্নত ইন্টারনেটের কল্যাণে মূলধারার গণমাধ্যমের পাশাপাশি অনলাইন সংবাদমাধ্যমসহ ব্যক্তি পর্যায়ে বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মের মধ্যে সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমগুলো বড় ধরনের তথ্যপ্রযুক্তিনির্ভর বিপ্লব ঘটিয়েছে বলা যায়।
সব সময় দেশের স্বাধীনতা, মানবাধিকার, সুশাসন, মত প্রকাশের স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রকে সুসংহত করার জন্য নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে মিডিয়া। একটি স্থিতিশীল ও শান্তিপূর্ণ বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মত প্রকাশের স্বাধীনতা, নাগরিক অধিকার, আইনের শাসন এবং মানবাধিকারের মতো বিষয়গুলোর ওপর জোর দিয়ে বাংলাদেশের অদম্য যাত্রা অব্যাহত রাখবে মিডিয়া।
লেখক: হীরেন পণ্ডিত: প্রাবন্ধিক, গবেষক ও কলামিস্ট

প্রযুক্তি দখল করছে প্রজন্মের মনন! কিন্তু এর পাশাপাশি মানুষ কতটা ভালোবাসছে প্রকৃতিকে! কতটা নিজের জন্য সঞ্চয় করে রাখছে এতটুকু সবুজ! সভ্যতার শক্তিটিই প্রকৃত শক্তি। মানুষ সেই সভ্য সমাজের সদস্য। একই সঙ্গে প্রকৃতিরও একটি অধিকার আছে। সেই অধিকার মানুষের কাছে। মানুষ যে আজ প্রকৃতি খুন করছে, তা সেই অধিকারকে হত্যা করার শামিল। আজ ফ্ল্যাট সভ্যতা দখল করে নিচ্ছে আমাদের বনাঞ্চল।
আমাদের চারপাশে আরও খোলা বাতাস ছিল। ছিল প্রকৃতির অবারিত কৃপা। তা এখন ক্রমশই সঙ্কুচিত হয়ে আসছে। দেশে-বিদেশে, সবখানেই। মানুষের ব্যস্ততা বাড়ছে। বাড়ছে তাড়না। ধনীরা আরও ধনকুবের হওয়ার সুযোগ পেলেও দরিদ্র শ্রেণি, সীমা অতিক্রম করে ওঠে আসতে পারছে না। কেউ কেউ কিছুটা সমিল খুঁজে নিজে নিজে ধন্য হতে চাইছে। কারও হাতে ব্ল্যাকবেরি, আইফোন, সনি এরিকসন। কারও হাতে নেহায়েত একটি ‘নকিয়া’। মোবাইল তো আমার হাতেও আছে, তা-ই এখন পরম সান্ত্বনা! এক ধরনের আত্মতৃপ্তি।
বিদেশের সিংহভাগ মানুষ মোবাইলবিহীন জীবন ভাবতেও পারছে না এখন। পাশ দিয়ে যখন কেউ একা একা কথা বলে রাস্তায় চলে, তখন মনে করার কোনো সুযোগ নেই, লোকটি প্রলাপ বকছে। কারণ হ্যান্ডসেট ফ্রি, আনমনে হেঁটে হেঁটে কথা বলছে। ব্রাউজ করে দেখে নিচ্ছে দূরান্তের ছবিও।
এটা বর্তমান সভ্যতার স্বরূপ। কিন্তু এই স্বরূপের বাস্তবতাকে প্রকৃতি কতটা সাহায্য করছে? এই সাহায্য পেতে মানুষের করণীয় কী? এই প্রশ্নটি গোটা বিশ্বে আবারও উত্থাপিত হচ্ছে। আবারও ভাবতে হচ্ছে, মানুষ প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করে কিভাবে টিকে থাকবে। কিভাবে এগিয়ে নেবে প্রজন্মের পথ।
নীতিবানদের আয়োজনে বিশ্ব পরিবেশ সম্মেলন শেষ হয় প্রতিবারই। নানা আশা-দূরাশার দোলাচলের মধ্য দিয়ে কথা হয়। তা নিয়ে যুক্তি ওঠে পক্ষে-বিপক্ষে। তারপরও বিশ্বে ঘটে ইতিহাসের নির্মমতম ভূমিকম্প। এসব ভূমিকম্পে কখনো লাখ প্রাণহানির আশঙ্কা করা হচ্ছে। উদ্ধারকাজ শেষ হতে কয়েক মাস সময় লাগে। আর যে দেশে তা ঘটে, সেই দেশটির পুনর্নির্মাণে লাগতে পারে কয়েক বছর।
মানুষের প্রতি প্রকৃতির এই বৈরী আচরণ অত্যন্তই বেদনাদায়ক। কারণ নির্বোধ শিশু থেকে নির্বাক বৃদ্ধ- সবাইকেই হরণ করেছে এই ভূমিকম্প। এ থেকে মানুষ কী শিখতে পারে? কী করণীয় আছে তাদের?
সে প্রসঙ্গে যাওয়ার আগে একটি ঘটনা বলি। আমাদের মনে আছে, হাইতিতে এই ভয়াবহ ভূমিকম্পের ঘটনাকে পুঁজি করে রীতিমতো অমানবিক বাণিজ্যে উঠেপড়ে লেগেছিল একটি মহল। এরা মানুষের সঙ্গে প্রতারণা করে হাতিয়ে নিয়েছিল লাখ লাখ ডলার। পত্র-পত্রিকায় ভুয়া বিজ্ঞাপন, ওয়েবসাইটে প্রচারণা, ব্যক্তিগত ফোনকল কিছুই তারা বাকি রাখেনি। এমনটি বাংলাদেশে বন্যা এলেও হয়। ত্রাণ ওঠে। গণমানুষের হাতে পৌঁছে না।
আমরা প্রায়ই দেখি, যুক্তরাষ্ট্রে এসব প্রতারক চক্র গড়ে ওঠে রাতারাতি। ইউরোপের অন্যান্য দেশেও এমন চক্র বেড়ে ওঠার খবর প্রকাশিত হয় প্রায়ই। যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবশালী টিভি চ্যানেলগুলো তা নিয়ে সচিত্র প্রতিবেদন প্রচার করে অনেক সময়।
এরকম ঘটনা ঘটলে আমি প্রায়ই দশ-বারোটির মতো ফোনকল পাই। একবার ‘চ্যারিটি গিল্ড অফ আমেরিকা’ নামধারী একটি সংস্থার পক্ষ থেকে আমাকে ফোন করার পর আমি বললাম, ‘আমি কি তোমাদের ট্যাক্স আইডি নম্বরটি পেতে পারি?’ অপর প্রান্ত থেকে মহিলা হেসে দিলেন। বললেন- ‘তুমি বেশি জানো’ (ইউ নো টু মাচ)। বলেই আমার মুখের ওপর ফোন লাইনটা কেটে দিলেন। কিছুটা রাগ হলো আমার। কলার আইডি দেখে ফোন করলাম। মেশিনে বেজে উঠল ‘ইওর কল ক্যান নট বি রিচড’।
এরা সবই প্রতারক। প্রতারকদের চিনতে ‘টু মাচ’ জানতে হয় না। যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিটি নন প্রফিট অর্গানাইজেশন, আয়কর বিভাগ, সিটি সরকারের কাছে নিবন্ধনকৃত। রয়েছে ফেডারেল সরকারের তদারকিও। তাই ভুয়া চাঁদা কিংবা ডোনেশন আদায় সহজ কাজ নয়। তারপরও যে চুরি-চামারি হচ্ছে না, তা আমি বলছি না। হচ্ছে। তবে সরকারি সংস্থাগুলোও এদের ধরতে চালিয়ে যাচ্ছে নানা তৎপরতা। সাঁড়াশি অভিযান। ফলে সেসব অবৈধ কর্মতৎপরতা সরকারি মদত পাচ্ছে না। আর সচেতন মানুষজন তো রয়েছেই। যারা এর প্রতিবাদ করছে। প্রয়োজনে প্রতিরোধ গড়ে তুলছে। রয়েছে মিডিয়াগুলোর সাহসী ভূমিকা।
প্রাকৃতিক দুর্যোগ, পরিবেশ বিপন্নতা বর্তমান বিশ্বের একটি চরম সংকট। যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া, সাউথ ক্যারোলিনা, নর্থ ক্যারোলিনা, আরিজোনা, লুইজিয়ানা, ফ্লোরিডা প্রভৃতি অঙ্গরাজ্যে বিভিন্ন সময়ে ভয়াবহ দুর্যোগের ঘটনা আমরা দেখেছি। আগ্নেয়গিরির লেলিহান শিখা প্রায়ই পুড়িয়ে দেয় ক্যালিফোর্নিয়ার জমি-বৃক্ষ-গাছগাছালি। তা রোধের উপায় যে যুক্তরাষ্ট্র সরকার খুঁজছে না, তা নয়। তারা চেষ্টা করেই যাচ্ছে। চলছে নানা গবেষণা। মোট কথা মানুষকে প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করেই বাঁচতে হবে। রক্ষা করতে হবে প্রাকৃতিক ভারসাম্য।
এই যে, প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রাম, তা করার জন্য বাংলাদেশ কতটা প্রস্তুত? এই প্রশ্নটি আসছে খুব সঙ্গত কারণে। কোপেনহেগেন পরিবেশ সামিটে বাংলাদেশ আগেও বলেছে, আমরা ভুক্তভোগী-ক্ষতিগ্রস্ত দেশ। কিন্তু এটাই তো শেষ কথা নয়।
ভূমিকম্পের দিক দিয়ে বাংলাদেশ একটি ঝুঁকিপূর্ণ দেশ। একথা সব বিশেষজ্ঞই বলছেন সমস্বরে। কিন্তু বাংলাদেশ, এই ২০২৪ সালে তা মোকাবেলার জন্য কতটা প্রস্তুত? বাংলাদেশে প্রথম ও প্রধান সমস্যাটি হচ্ছে, অপরিকল্পিত নগরায়ণ। এর কারণে যত্রতত্র গড়ে উঠছে ইমারত। বৃক্ষনিধনও হচ্ছে বিভিন্ন প্রভাবশালী মহলের ছত্রছায়ায়। একটি বড় ধরনের বহুতল ভবন হবে, আর তাতে পর্যাপ্ত পরিমাণ অগ্নিপ্রতিরোধক ব্যবস্থা থাকবে না- তা কি মানা যায়? রানা প্লাজার ঘটনা আমরা ভুলে যাইনি।
লেখার শুরুতেই আমি ফ্ল্যাট প্রজন্মের কথা বলেছি। এই প্রজন্ম বড় হচ্ছে, তারা কী তাদের প্রাপ্য প্রাকৃতিক বিনোদনটুকু পাচ্ছে? না, পাচ্ছে না। বরং মাথা গোঁজার ঠিকানাই হয়ে উঠছে এখন আরাধ্য বিষয়। যারা ধনকুবের, যারা বহু রঙবিশিষ্ট বাংলা বাড়ি বানাবার জন্য বিভোর, তারাও নিরাপদ নয়। কারণ তার প্রতিবেশ দূষিত হচ্ছে আবর্জনায়। ‘পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ইমানের অঙ্গ’- এমন আপ্তবাক্যটিকেও চরমভাবে অপমান করছে একশ্রেণির মানুষ।
সংবাদমাধ্যমে, বাংলাদেশের এখন একটি অন্যতম খবর ‘ভূমিখেকোদের দৌরাত্ম্য’। এরা কারা, কী তাদের পরিচয়? দেশের ভূমিমন্ত্রী যখন বলেন, ভূমিখেকোদের শিকড় বড় বেশি শক্ত, তখন সাধারণ মানুষের আর কোনো ভরসাই থাকে না।
দেশের বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের সচিব যখন বলেন, সরকারি বনাঞ্চল দখলদাররা দখল করে নিয়েছে, তখন আমাদের লজ্জায় মুখ ঢাকতে হয়। এসব তো প্রকৃতির পরিহাস নয়। এগুলো হচ্ছে মানব-শক্তি নির্মিত অপপ্রয়াস। সমাজ, প্রজন্মকে ধ্বংস করে দেওয়ার অপচেষ্টা।
বাংলাদেশের বিভিন্ন স্যাটেলাইট চ্যানেল, নদী দখলের ওপর ইতোমধ্যে সচিত্র প্রতিবেদন দেখাচ্ছে। বিস্তর লেখালেখি হচ্ছে নানা মিডিয়ায়। তারপরও এসব ভূমিখেকো দখলদার, বৃক্ষনিধনকারী, দুষ্টচক্র নানাভাবে সরকারি মদত পাওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।
বাংলাদেশে যেসব নতুন বহুতল ভবন নির্মাণ করা হচ্ছে, তারা রাষ্ট্রীয় ধারা অনুযায়ী ‘বিল্ডিং কোড’ মানছে কি না, সে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে। এরা একটিবারও ভাবছে না, এই অপরিকল্পিত নির্মাণ স্থাপনা একদিন তাদের মাথার ওপরই ভেঙে পড়তে পারে। এরা তাৎক্ষণিক সুবিধাদিকে, মুনাফার লুটপাটতন্ত্রকে ধারণ করছে। স্থায়ী পরিশুদ্ধ পরিকল্পনাকে ধারণ করছে না।
ভূমিকম্পসহ সব প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় সরকার ও জনগণ প্রতিটি শক্তিকেই সচেতন হতে হবে। কয়েক কোটি মানুষের জীবন ধারণকারী শহর ঢাকায় পর্যাপ্ত পরিমাণ ফায়ার ব্রিগেড স্টেশন এবং ফায়ার ফোর্স নেই- তা ভাবতেও কষ্ট হয়। এই মানসিকতা নিয়ে তো ‘ডিজিটাল বাংলাদেশ’-এর স্বপ্ন আমরা দেখতে পারি না।
গ্লোবাল ওয়ার্মিং থেকে কারোরই সহজে রক্ষা পাওয়ার কোনো সুযোগ নেই। তাই শক্ত প্রস্তুতি নিতে হবে। বাংলাদেশের প্রতিটি উপজেলা পর্যায়ে শক্তিশালী ফায়ার ব্রিগেড স্টেশন স্থাপনে সরকারকে গুরুত্ব দেওয়া উচিত। বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনীর যে সুনাম রয়েছে, তাকে আরও পরিপূর্ণ করতে ‘তাৎক্ষণিক সাহায্য টিম’ গড়ে তুলতে হবে তাদের মধ্য থেকেই। যেভাবে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে স্পেশাল উদ্ধারকারী টিম থাকে। পৃথিবী কাঁপছে। আমরা এর মুখোমুখি দাঁড়িয়েই করছি সব জৈবিক লেনাদেনা। তাই সব প্রতিকূলতাকে ডিঙিয়ে যাওয়ার প্রস্তুতি আমাদের থাকতেই হবে।
আমরা জানি মানুষের পাঁজর একসময় সম্প্রীতিতে ভরপুর ছিল। এখন সেই পাঁজরের ওপরই গুলি চালাচ্ছে কেউ কেউ। কুড়াল দিয়ে গাছ কাটছে। আর হত্যা করে মানুষ ভাসিয়ে দিচ্ছে নদীতে। এর সুবিচার হচ্ছে না। অথচ আমরা মুক্তিযুদ্ধের মানচিত্র দেখে যে বাংলাদেশ চেয়েছিলাম, সেই বাংলাদেশ আজ কোথায়? এ দেশে কি কোনো শাসনতন্ত্র নেই? সংবিধান নেই? শাসকগোষ্ঠী নেই? এভাবে কি একটি দেশ চলতে পারে? না পারে না। রক্ষক যখন ভক্ষকের চরিত্রে অবতীর্ণ, তখন রাষ্ট্রে ভৌতিক দখলদাররা মাথাচাড়া দেয়। বাংলাদেশ কি এই রাহুগ্রাস থেকে আদৌ মুক্তি পাবে না?
‘তোমার দিকে আমার তাকাবার সময় না-ও হতে পারে/ ধূসর পৃথিবীর দিকে তাকালে কেবলই দেখবো মৃত আকাশ/ দেখবো- নক্ষত্রগুলো ছাই হয়ে আছে/ এর পাশে/ পড়ে আছে কিছু পাঁজর/ যা একসময় মানুষের ছিল’। আজ থেকে প্রায় আড়াই দশকের বেশি সময় আগে এই পঙ্ক্তিগুলো যখন লিখি, তখনো এভাবে ফ্ল্যাট প্রজন্ম গড়ে ওঠেনি। গড়ে ওঠেনি প্লট বাণিজ্যের অবিন্যস্ত পসরা। ছিল না মোবাইল ফোনের দাপট, কম্পিউটারের সহজলভ্যতা। কিন্তু এই প্রযুক্তি সভ্যতা আমাদের কতটা কাজে আসছে মানবিক জীবনে- তা ভাববে কে!
লেখক: কবি ও কলামিস্ট

আজকাল গণমাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনায় দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যদের যোগ্যতা-অযোগ্যতা, অনিয়ম, দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি প্রভৃতি নিয়ে প্রায়শ খবর প্রকাশিত হতে দেখছি। আমিও একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। কোনো কোনো গণমাধ্যমের খবরে আমার নামটিও রয়েছে। সে পরিপ্রেক্ষিতে এই লেখা। লেখাটির শিরোনাম কী দেব বুঝতে পারছি না। অগত্যা ‘একজন উপাচার্যের কৈফিয়ত’ এই নাম দিয়েই লেখাটি শুরু করলাম।
আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা থেকে অবসর নেওয়ার পরপরই ২০২০ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের দায়িত্ব পালন করে আসছি। আমার দায়িত্ব পালনের প্রথম দিকে প্রায় এক থেকে দেড় বছর ছিল করোনাকাল। সে সময় আমি ও আমার স্ত্রী দুজনই দুইবার করোনায় আক্রান্ত হয়েছিলাম। করোনা চলার সময় অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মতো এই বিশ্ববিদ্যালয়েও কম-বেশি সব কার্যক্রম বন্ধ থাকলেও উপাচার্যের অফিস চলত প্রায় স্বাভাবিক সময়ের মতো। এ সময়ে আমাদের প্রধান চেষ্টা ছিল অনলাইন এবং পরবর্তী সময় অনলাইন-অফলাইন সমন্বিত মোডে কী করে ক্লাস-পরীক্ষা চালু রাখা যায়। আমার একটি তৃপ্তির অনুভূতি যে, তখন থেকে এ পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম ধারাবাহিকভাবে অব্যাহত রয়েছে; নানারকম প্রতিকূলতা সত্ত্বেও ক্লাস-পরীক্ষা এক দিনের জন্যও বন্ধ থাকেনি কিংবা তেমন কোনো অস্থিরতাও তৈরি হয়নি।
গত এক থেকে দেড় বছর ধরে বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার ক্ষেত্রে দৃশ্যপট পাল্টাতে শুরু করেছে। এখানে বিশেষ করে কিছু সংখ্যক শিক্ষক রয়েছেন যারা কম-বেশি সব আমলে উপাচার্যের প্রীতিভাজন হয়ে প্রশাসনকে কবজায় নিয়ে নিজেদের মতো করে বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা করতে চান। এমনটি না হলে সাধারণত কোনো উপাচার্যই তাদের মেয়াদ পূর্ণ করতে সক্ষম হন না। জন্মকাল থেকে ১৩ জনের মধ্যে এ পর্যন্ত এক-দুজন উপাচার্য কেবল মেয়াদ শেষ করতে পেরেছেন। যাই হোক এই শিক্ষকদের কেউ কেউ সুবিধা করতে না পেরে অন্তত দু-একজন শিক্ষক আমাকে এমনও বলেছেন যে, পূর্বে কম-বেশি সব উপাচার্য তাদের নিয়ে চলেছেন, অথচ আমার সময়ে তিনি/তারা একটু ঝাড়ুদারের দায়িত্বও পাচ্ছেন না। এরপর থেকে দিনে দিনে শুরু হয়েছে অনলাইন ও বিভিন্ন ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে আমার বিরুদ্ধে মিথ্যাচার আর অপপ্রচারের প্লাবন। একটি একটি করে তা পাঠকের জন্য তুলে ধরতে চাই।
প্রায় দেড় বছর পূর্বে হঠাৎ করে একদিন বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে ভ্যানে মাইক লাগিয়ে আমার কণ্ঠ-সাদৃশ্য বাক্যাংশের একটি অডিও বাজিয়ে কে বা কারা প্রচার করতে থাকে যে, উপাচার্য হিসেবে আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগ-বাণিজ্য করছি। মূলত ঘটনাটি ছিল এমন যে, ওই সময়ে শিক্ষকশূন্য একটি বিভাগে শিক্ষক নিয়োগের জন্য একটি বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছিল। সেখানে মাত্র তিনটি আবেদনপত্র জমা পড়েছিল এবং নিয়োগ পরীক্ষায় দুজন প্রার্থী উপস্থিত হয়েছিলেন। আমরা প্রার্থী স্বল্পতার জন্য ওই পরীক্ষা বাতিল করে পুনঃবিজ্ঞাপনের সিদ্ধান্ত নিই। এর কয়েক দিন পর আমি আমার এক ছাত্রকে (যিনি একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকও বটে) অনুরোধ করি যে, তোমরা ঢাকায় থাক, আমাদের শিক্ষক দরকার। তুমি আমাদের একটু সাহায্য কর- তোমার বন্ধুবান্ধব বা পরিচিতজনদের বল তারা যেন এখানে দরখাস্ত করে। উত্তরে সে জানায় যে, স্যার ওখানে কেউ যেতে চায় না। তা ছাড়া একটা দরখাস্ত করতে গেলে ৫ থেকে ৬ হাজার টাকা ব্যয় হয়, তাই কেউ দরখাস্ত করতেও উৎসাহী হয় না। আমি তখন জবাবে বলি- ওরা তোমাদেরই বন্ধুবান্ধব, প্রয়োজনে টাকা-পয়সা দিয়ে সহায়তা করে তাদের দরখাস্ত করতে একটু উদ্বুদ্ধ কর। এই কথোপকথনের ‘টাকা-পয়সা দিয়ে’ এই বাক্যাংশটুকু নিয়ে কীভাবে তারা একটি অডিও বানিয়ে প্রচার আরম্ভ করে যে, উপাচার্য নিয়োগ-বাণিজ্য করছেন। শুনেছি এভাবে তারা একাধিক অডিও [যা শুধু একজন অর্থাৎ আমার কণ্ঠ সাদৃশ্য এবং তা’ মিথ্যা, বানোয়াট, খণ্ডিত, এক পক্ষীয় (অন্য প্রান্তে কে কী বলছেন তার কোনো হদিস নেই) এবং হয়তো বা সুপার এডিটেড] বানিয়ে বিভিন্ন জায়গায় পাঠিয়ে উপাচার্যকে কীভাবে হেনস্তা করে তাদের অপ-ইচ্ছার কাছে নতি স্বীকার করানো যায় সে চেষ্টাই তারা অনবরত করে যাচ্ছে।
আমি আমার কণ্ঠ সদৃশ আরও একটি অডিওর বক্তব্য শুনেছি। এটিও ছিল এক পক্ষীয় এবং খণ্ডিত। আমার আলাপন সেখানে পূর্ণাঙ্গ নেই। অন্যপ্রান্তে কে কথা বলছেন তারও কোনো অস্তিত্ব নেই। অডিওর বিষয়টি হলো- আমি কোনো একজনকে বলছি যে, ‘আপনার নির্দিষ্ট প্রার্থীকে আমার কাছে পাঠিয়ে দেবেন... আমি দেখব।’
সাধারণত কোনো নিয়োগের আগে অনেকেই অনুরোধ করেন যাতে তার প্রার্থীকে যেন একটা চাকরি দেওয়া হয়। বিশেষ করে জনপ্রতিনিধিরা অথবা কোনো রাজনৈতিক/সামাজিক ব্যক্তিত্ব ১টি পদের জন্য কখনো কখনো ৩ থেকে ৪ জন প্রার্থীর রোল নম্বর পাঠিয়েও এ ধরনের অনুরোধ করেন। ধরা যাক, এদের মধ্যে একজনেরই চাকরিটি হয়েছে। অধিকাংশ সময়ে সে ফিরে গিয়ে তার জন্য অনুরোধকারীকে সুখবরটি জানায় কি না, তা আমার জানা নেই। কিন্তু প্রায়শ এমনটি ঘটে যে, বাকি যাদের চাকরি হয় না তারা গিয়ে তাদের স্ব-স্ব নেতা বা অনুরোধকারীকে এই বলে বিষিয়ে তোলে যে, উপাচার্য আপনার অনুরোধের কোনো দামই দিলেন না। এমন পরিস্থিতিতে মন খারাপ করে জনপ্রতিনিধিরা বা রাজনৈতিক/সামাজিক নেতারা টেলিফোন করে আমাকে হয়তো বলে থাকেন- আপনি আমার একটা অনুরোধ রাখলেন না। এমন পরিস্থিতিতে আমাকে জবাব দিতে হয় যে, এরপর তাহলে আপনার সুনির্দিষ্ট প্রার্থীকে আমার সঙ্গে দেখা করতে বলবেন ... আমি দেখব। এই ‘দেখা করতে বলা’ কি নিয়োগ-বাণিজ্যের সঙ্গে যায়? এভাবে একটি গোষ্ঠী কেবলই মিথ্যাচার করে উপাচার্য হিসেবে আমাকে নাজেহাল করার অনবরত চেষ্টা করে যাচ্ছে, যাতে আমি নতি স্বীকার করে তাদের হাতের পুতুল হয়ে কাজ করি। মিথ্যার কাছে নতি স্বীকার করে বেঁচে থাকার ইচ্ছে বা অভিপ্রায় আমার নেই।
আমার বিরুদ্ধে নাকি অভিযোগ রয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের চলমান উন্নয়ন প্রকল্পের নির্মাণকাজে আমি অতিরিক্ত কাজ দেখিয়ে ৬ থেকে ৮ কোটি টাকার বিল বানিয়ে অর্থ-আত্মসাৎ করেছি বা করার চেষ্টা করেছি। রুচিহীন এবং উদ্ভট এসব অভিযোগের জবাব দিতেও আমি ইতস্তত বোধ করছি। উল্লেখ্য, নির্মাণকাজের বাস্তব অগ্রগতি পরিমাপ করে ৩ থেকে ৪ মাস অন্তর পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর বিল ঠিকাদারের প্রদান করা হয়। এই কাজে বিভিন্ন পর্যায়ে সাইট ইঞ্জিনিয়ার-সহকারী ইঞ্জিনিয়ার-নির্বাহী বা তত্ত্বাবধায়ক ইঞ্জিনিয়ার-প্রধান প্রকৌশলী ও প্রকল্প পরিচালক প্রমুখ কর্তৃক পরীক্ষিত ও নিরীক্ষিত কাজের পরিমাপ এবং প্রস্তাবিত বিল ঠিক থাকলে তা চলে যায় ট্রেজারার মহোদয়ের কাছে। তখন তার নেতৃত্বে গঠিত ভিজিলেন্স টিম সরেজমিনে সাইট পরিদর্শন করে সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে তা উপাচার্যের নিকট অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হয়। বর্ণিত ক্ষেত্রে আমার নিকট ফেবরিকেটেড ওই বিল অনুমোদনের জন্য কোনো ফাইলই উপস্থাপিত হয়নি। বরং ৪ থেকে ৫ মাস পূর্বে আমার দপ্তরে একটি বেনামি চিঠি আসে, নির্মাণকাজ বেশি দেখিয়ে আট কোটি টাকার একটি বিল প্রদত্ত করে তা প্রক্রিয়া করা হয়েছে। এই চিঠির সঙ্গে ফটোকপিকৃত কিছু ডকুমেন্ট ছিল, যা দেখে অভিযোগের সত্যতা থাকতে পারে বলে আমার কাছে মনে হয়েছিল। আমি তাৎক্ষণিকভাবে এই চিঠির ভিত্তিতে একজন সিন্ডিকেট সদস্যকে আহ্বায়ক এবং খুলনা প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপককে সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করি। ইতোমধ্যে কমিটি তাদের রিপোর্ট প্রদান করেছে। পরবর্তী সিন্ডিকেট সভায় তা উপস্থাপিত হবে এবং সিন্ডিকেট সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এখানে উপাচার্য হিসেবে আমি কি দুর্নীতি করেছি, আশা করি পাঠকরা তা উপলব্ধি করতে পারছেন।
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে চলমান উন্নয়ন প্রকল্পের ব্যাপারে দু-একটি অনলাইন পত্রিকায় নিউজ করানো হচ্ছে যে, প্রকল্প সাইটে মাটির নিচে পাইলিংয়ের জন্য যে রড ব্যবহার করা হয়েছে সেখানেও নাকি উপাচার্য হিসেবে আমি দুর্নীতি বা অনিয়ম করেছি। যেকোনো নির্মাণে পাইলিংয়ের জন্য মাটির নিচে রড কতটুকু ব্যবহার করা হবে তা নির্ভর করে সয়েল টেস্ট রিপোর্টের ওপর। আমি উপাচার্য হিসেবে যোগদানের বহু পূর্বে প্রকল্পটি অনুমোদনের প্রক্রিয়ায় সয়েল টেস্ট করে প্রকল্প দলিল প্রণীত ও অনুমোদিত হয়েছিল। আমার সময়ে এসে প্রকল্পের কাজ শুরুর পর যখন পাইলিং আরম্ভ হয় তখন সংবাদকর্মীদের মাধ্যমে আমি জানতে পারি যে, প্রকল্প দলিল অনুযায়ী মাটির নিচে যে পর্যন্ত রড ব্যবহারের কথা (ধরা যাক ৫০ ফুট) তার চেয়ে কম গভীরতায় রড ব্যবহারে পাইলিংয়ের পদতি নেওয়া হচ্ছে। আমি সঙ্গে সঙ্গে প্রধান প্রকৌশলীকে বিষয়টি দেখতে বলি এবং ভিজিলেন্স টিম পাঠিয়ে তাদের ব্যবস্থা নিতে বলি। ভিজিলেন্স টিমের সদস্য এবং ইঞ্জিনিয়ারিং অফিসের কর্মকর্তারা আমাকে এসে রিপোর্ট করেন যে, সয়েল টেস্টিংয়ের ভিত্তিতে যেভাবে পাইলিংয়ের রড প্রকল্প অনুযায়ী মাটির নিচে ব্যবহারের কথা বাস্তবে তা ব্যবহার করা যাচ্ছে না। রড ঢুকছে তার কম (কম-বেশি ৪০ ফুট)। এ পর্যায়ে সবাই মিলে সিদ্ধান্ত নিয়ে পুনরায় সয়েল টেস্ট ও তা ভেটিং করিয়ে টেস্টের রিপোর্ট অনুযায়ী সেই গভীরতায় রড ব্যবহার করে পাইলিংয়ের কাজ করা হয়েছে। এ বিষয়টি প্রজেক্ট ইমপ্লিমেন্টেশন কমিটির (যেখানে শিক্ষা মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা কমিশন, আইএমইডি, ইউজিসির প্রতিনিধিরা থাকেন) সভায় অবহিত করা হয়েছে। এখানে উপাচার্য কীভাবে রড কম গভীরতায় ঢুকিয়ে দুর্নীতি বা অনিয়মের আশ্রয় নিয়েছেন সে বিবেচনার ভার পাঠকদের ওপর ছেড়ে দিলাম।
আমি প্রায়ই শুনি, আমার বিরুদ্ধে নাকি আরও একটি অভিযোগ, আমি অবৈধভাবে কর্মকর্তাদের উচ্চতর বেতন স্কেল প্রদান করেছি। বিষয়টি আমি নিচে ব্যাখ্যা করছি। তার আগে বলে রাখা দরকার যে, এটি ডেপুটি এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট রেজিস্ট্রার পর্যায়ের সব কর্মকর্তার জন্য একটি আর্থিক সুবিধা প্রদানের বিষয়। এটি প্রদানের ক্ষেত্রে আর্থিক নিয়মের কোনো ব্যত্যয় ঘটলে ইউজিসি অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ে যারা বছরে একাধিকবার অডিট করেন তারা আপত্তি উত্থাপন করতে পারেন। কিন্তু উপাচার্যের দুর্নীতির উপাদান এখানে কী থাকতে পারে তা আমার বোধগম্য নয়।
ঘটনাটি ছিল এমন যে, ২০১৫ সালের জাতীয় বেতন স্কেল কার্যকর হওয়ার পূর্বে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেপুটি এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট রেজিস্ট্রার পর্যায়ের কর্মকর্তাদের একটি নির্দিষ্ট সময় পরে একধাপ উচ্চতর স্কেলে বেতন উন্নীত করে তা প্রদান করা হতো। ২০১৫ সালের বেতন স্কেল কার্যকর হওয়ার পর এই সুযোগ রহিত করা হয়। আমি ২০২০ সালের শেষ দিকে করোনাকালে যখন এখানে উপাচার্য হিসেবে যোগদান করি তার কয়েক দিনের মধ্যে ওই পর্যায়ের কর্মকর্তাদের একটি অংশ এসে আমার সঙ্গে দেখা করে দাবি জানায় যে, এই স্কেল উন্নীতকরণ ঘটবে উপ-রেজিস্ট্রার ও সহকারী রেজিস্ট্রার পর্যায়ের সব কর্মকর্তার ক্ষেত্রে। কিন্তু পূর্বের প্রশাসন ২০১৯ সালে বেছে বেছে তাদের অনুগত কর্মকর্তাদের এই সুযোগ প্রদান করেছে- কাজেই অবশিষ্টদেরও এটি দিতে হবে। বিষয়টি নিয়ে ২০২২ সালের দিকে তারা একটি বড় আন্দোলন গড়ে তোলে এবং প্রায় ২ মাস ধরে কর্মবিরতি পালন করে। একপর্যায়ে গিয়ে এ বিষয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি দেখতে পায় এই সুবিধাটি ২০১৫ সালের পে-স্কেলের সময় রহিত করা হলেও ঢাকাসহ রাজশাহী, চট্টগ্রাম, জাহাঙ্গীর নগর, মওলানা ভাসানী বিশ্ববিদ্যালয় বেশ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে এটি তখনো চালু রয়েছে। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে এই সুবিধা পূর্বে অলরেডি কর্মকর্তাদের একটি অংশকে দেওয়া হয়েছে এবং কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে তখনো এই সুবিধা প্রদান বহাল রয়েছে। এই বিবেচনায় কর্মকর্তাদের আরেকটি অংশ যাতে বঞ্চিত না হয় (অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে তখনকার পরিস্থিতি) সেসব বিবেচনায় নিয়ে কমিটি বঞ্চিতদের জন্য স্কেল উন্নীত করণের সুপারিশ করে। এই সুপারিশ ফিন্যান্স কমিটি এবং সিন্ডিকেটে এই শর্তে অনুমোদন দেওয়া হয় যে, এ ব্যাপারে ভবিষ্যতে কখনো যদি অডিট আপত্তি উত্থাপিত হয় তাহলে এই উন্নীতকরণ বাতিল হবে এবং কর্মকর্তাদের দেওয়া অর্থ ফেরত দিতে হবে। বিষয়টি সে সময় এভাবে ফয়সালা করা হয়েছে। এখানে উপাচার্য হিসেবে আমার দুর্নীতির জায়গাটি কোথায় তা আমার বোধগম্য নয়। আমি মনে করি, এটি বড়জোর একটি অডিট আপত্তি/অনাপত্তির বিষয়। ব্যক্তি বা সামষ্টিক দুর্নীতির সজ্ঞার সঙ্গে এটি যায় কি?
উপাচার্য হিসেবে আমার বিরুদ্ধে আরও একটি অভিযোগ সম্পর্কে দু-একটি অনলাইন পত্রিকা এবং নষ্ট-ভ্রষ্ট ওই গোষ্ঠীর প্রচার-প্রোপাগান্ডা থেকে জেনেছি যে, আমি আমার ঢাকার বাসার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের টাকায় সিকিউরিটি নিয়োগ দিয়েছি। এটি সর্বৈব মিথ্যা রটনা। ঢাকায় ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি রেস্ট হাউস রয়েছে। সেখানে মাত্র ২ জন কর্মী (একজন কুক, একজন সাধারণ) কাজ করে। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রতিদিন গড়ে ১৫-২০ জন শিক্ষক-কর্মকর্তা (কখনো কখনো তাদের পরিবার- বিশেষ করে চিকিৎসার জন্য) ঢাকায় গিয়ে রেস্ট হাউসে অবস্থান করেন। উল্লেখ্য, এ সময়ে বেশ কয়েক মাস ধরে রেস্ট হাউস ভবনের সংস্কার কাজ চলছিল। রেস্ট হাউসে ইবি পরিবারের সদস্যগণ দিনে-রাতে (কোনো ধরাবাঁধা সময় নেই) যাতায়াত করেন। তাদের জন্য বারবার গেট খোলা এবং লাগানোর মতো কোনো জনবলই সেখানে ছিল না। অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী স্থায়ী জনবল নিয়োগেরও তেমন কোনো সুযোগ ছিল না। সে সময় এস্টেট অফিস থেকে আমাকে জানানো হয় যে, ঢাকা রেস্ট হাউসে কিছু সিকিউরিটি ডেপুট (নিয়োগ নয়) করা দরকার। ইবি ক্যাম্পাসের কয়েকজন আনসার দিয়ে সেটা করা যায় কি-না সে ব্যাপারে এস্টেট অফিস আমাকে অবহিত করে যে, আনসার ডেপুট করা অনেক খরচের ব্যাপার এবং বারো জনের নিচেয় আনসার কর্তৃপক্ষ জনবল দেবে না। বিকল্প হিসেবে স্বল্প সংখ্যক (৫-৬ জন) জনবল বরং সিকিউরিটি সংস্থা থেকে ডেপুট করা যায়। সে অনুযায়ী যথাযথ বিধি বিধান প্রতিপালন করে ফিন্যান্স কমিটি এবং সিন্ডিকেটের অনুমোদন নিয়ে ঢাকা রেস্ট হাউসের জন্য ছয়জন সিকিউরিটির সেবা হায়ার করা হয়েছে। উপাচার্য হিসেবে প্রায়শ আমাকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ইউজিসি, ধর্ম মন্ত্রণালয় (ইসলামী ফাউন্ডেশন), এ ইউ বির সভা এবং গুচ্ছের সভাসমূহে যোগাযোগসহ প্রভৃতি কারণে ঢাকায় যেতে হয়। সে কারণে শিফট অনুযায়ী সিকিউরিটি সদস্য যারা রেস্ট হাউসে ডিউটি করে তাদের একজন রেস্ট হাউসে এবং একজনকে উপাচার্যের বাসায় ডিউটি বণ্টন করা হয়েছে মাত্র। উপাচার্যের বাসার জন্য কোনো সিকিউরিটি সদস্য নিয়োগ দেওয়া হয়নি। উপাচার্যের বাসার জন্য সিকিউরিটি নিয়োগ দেওয়া হয়েছে এটাও একটি মিথ্যা প্রচারণা।
প্রকৃতপক্ষে আমি জানি না উপাচার্য হিসেবে আমার বিরুদ্ধে আর কী কী অভিযোগ রয়েছে? অভিযোগগুলো কিসের ভিত্তিতে করা হয়েছে? অভিযোগগুলো কারা করেছে তা-ও আমার জানা নেই। যাহোক একটি স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর প্রচার প্রোপাগান্ডার কারণে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এ ব্যাপারে ইউজিসিকে দিয়ে একটি তদন্ত কমিটি করিয়েছে। কমিটির সদস্যবৃন্দ আমাকে সুনির্দিষ্ট কয়েকটি বিষয়ে লিখিত মতামত/বক্তব্য দিতে বলেছিলেন। আমি তাদের নিকট লিখিতভাবে (ডকুমেন্টসহ) আমার বক্তব্য প্রেরণ করেছি।
আশা করি পাঠকবৃন্দ বিষয়সমূহ অবহিত হয়ে একজন উপাচার্যকে কীভাবে কেবল রসালো, মিথ্যা, বানোয়াট এবং বস্তনিষ্ঠহীন অভিযোগ তুলে তাকে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করানোর চেষ্টা করা হচ্ছে তা উপলব্ধি করতে সক্ষম হবেন। উপাচার্য এবং ব্যক্তি মানুষ হিসেবে আমি শুধু এতটুকুই বলব- আমি কোনো দুর্নীতি করে উপাচার্যের এই চেয়ারকে কলুষিত করিনি; আমি স্বার্থান্বেষী নষ্ট-ভ্রষ্ট কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর কাছে মাথা নত করব না।
লেখক: উপাচার্য, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া

রাজনীতিতে তাৎক্ষণিক সুবিধা বা লাভের জন্য কিছু করাটা বিরল ব্যতিক্রম ছাড়া সব সময়েই প্রধান হয়ে দাঁড়ায়। তাতে আপাত সুবিধা হলেও তা কখনো বা বিপদের কারণ হতে পারে। ২০২৪ সালের জানুয়ারির জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সময় প্রধান বিরোধী দল বিএনপি বয়কট করলে ভোটার আনতে ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগ দলের বিদ্রোহী প্রার্থীদের নির্বাচন করার সুযোগ দিয়েছিল। তাতে ৩০০ আসনের মধ্যে বিদ্রোহী প্রার্থীদের ৬২ জন বিজয়ী হন। সংখ্যাটা নেহাত কম নয়।
এ থেকে দলের ভেতরের পাল্টাপাল্টি অবস্থার আঁচ করা যায়। নির্বাচনের পর আওয়ামী লীগ হয়েও তারা দলের সিদ্ধান্ত মোতাবেক আলাদা গ্রুপ করে রয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকারের গঠনমূলক সমালোচনা করার জন্য স্বতন্ত্র সদস্যদের আহ্বান জানিয়ে বলেছেন, বাড়ি একটা, ঘর হয়েছে দুটো। দুই হাতই আমার। দেশের রাজনীতির ইতিহাসে এমন অবস্থা অভিনব।
এদিক বিবেচনায় এখনো পর্যন্ত লাভ বা সুবিধার মধ্যেই রয়েছে আওয়ামী লীগ। কিন্তু উপজেলা নির্বাচন ঘিরে তৃণমূলে যে দ্বন্দ্ব-বিরোধ-পাল্টাপাল্টি সৃষ্টি হয়েছে তা থেকে অনুধাবন করা যাচ্ছে, সংসদ নির্বাচনের পর দলে দলাদলি চরমে পৌঁছেছে। অতীত থেকেই ব্যতিক্রম বাদে জেলায়-তৃণমূলে আওয়ামী লীগে গ্রুপ বিভক্তি চলে এসেছে। সব সময়েই তা কম-বেশি চলতে থাকে এবং দৈনন্দিন কাজে কখনো বিঘ্ন ঘটায়। বিশেষভাবে সম্মেলন ও নির্বাচন এলে বিভক্তি- পাল্টাপাল্টি কোথাও কোথাও তীব্র ও প্রকাশ্য রূপ নেয়। এমনটাও দেখা যায়, ক্ষমতায় থাকলে বিরোধ যতটা বাড়ে, বিরোধী দলে থাকলে বিরোধ ততটা কমে। গঠনতান্ত্রিকভাবে সমস্যার সমাধান সাধারণভাবে হয় না।
এমনও দেখা গেছে, দলীয় সিদ্ধান্ত অমান্য করে বিদ্রোহী হয়ে জিতে কিছুদিন শোকজ কিংবা বহিষ্কারের টানাপড়েনের পর আবার সব ঠিক হয়ে যায়। এ বিষয়ে কথা উঠলে আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের বলতে শোনা যায়, বড় দলে গ্রুপ দ্বন্দ্ব-পাল্টাপাল্টি থাকবেই। নিয়ম-কানুন বড় নয়, জনগণের সমর্থনই বড়। ওপরে নেত্রী আর নিচে গণসমর্থন- এটাই হচ্ছে আওয়ামী লীগ। যতটুকু মনে হচ্ছে, সাম্প্রতিক অতীতে ১/১১-এর জরুরি আইনের সরকারের সময় ‘ মাইনাস টু’ কার্যকর করতে যাওয়ার সময় ছাড়া কেন্দ্রীয় কার্যকর কমিটিতে এবারের মতো আর ভিন্নমত বা বিদ্রোহের প্রকাশ্য বহির্প্রকাশের আগে তেমনভাবে হয়নি।
কিন্তু আসন্ন উপজেলা নির্বাচনকে সামনে রেখে আওয়ামী লীগে গ্রুপ দ্বন্দ্ব- পাল্টাপাল্টি এমন চরমে উঠেছে, যাতে কেন্দ্রীয় কার্যকর কমিটিকেও স্পর্শ করেছে। গ্রুপ দ্বন্দ্ব সামাল দেওয়া সম্ভব নয় বিবেচনায় নিয়েই হোক কিংবা বিরোধী দল বিএনপিসহ কতক দল ভোট বয়কট করবে বলেই হোক, উপজেলা নির্বাচনে দলীয় প্রতীক ব্যবহার না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে আওয়ামী লীগ। বাস্তবে দলীয় প্রতীক নিয়ে নির্বাচন পদ্ধতি চালুর আগে স্থানীয় নির্বাচনে আওয়ামী লীগ দলের বহু প্রার্থী তো থাকতই। আওয়ামী লীগের কাছে তাই স্থানীয় নির্বাচনে বহু প্রার্থী এবং প্রার্থীদের পক্ষ-বিপক্ষ নিয়ে ভাগাভাগি-পাল্টাপাল্টি কোনো নতুন বিষয় নয়।
কিন্তু বাদসাধে যখন আওয়ামী লীগ দলীয় মন্ত্রী-এমপিদের আত্মীয়-স্বজনই প্রার্থী হয়ে যায়। অতীতেও এমন হয়েছে এবং তাতে এমপি-মন্ত্রী-নেতারাই এলাকা সম্পূর্ণভাবে নিজেদের করায়ত্ব করে নিয়েছেন। এবারেও বেশ কতক এলাকায় আর্থিক সিন্ডিকেটের মতোই আত্মীয়-স্বজন নিয়ে রাজনৈতিক সিন্ডিকেট গড়ে ওঠে। তাতে আওয়ামী লীগ আত্মীয়-স্বজন প্রার্থীদের পদত্যাগপত্র প্রত্যাহারের নির্দেশ দেয়। কিন্তু তা কার্যকর করা সম্ভব হয় না। নাটোরে অপহরণ- মারধরের মতো ঘটনা ঘটে। অনভিপ্রেত ঘটনার পর প্রতিমন্ত্রী জুনায়েদ আহমেদ পলকের শ্যালক নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানোর পর সংকটের অবসান হয়েছে।
কিন্তু গোল বাধে মাদারিপুরে। দলীয় নির্দেশ উপেক্ষা করে শাজাহান খানের ছেলে চেয়ারম্যান পদে দাঁড়িয়ে যান। এ নিয়ে বিগত ২৪ এপ্রিল সন্ধ্যায় প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক কার্যালয়ে প্রকাশ্যে বিতর্কে জড়ান সাধারণ সম্পাদক ও সেতুমন্ত্রী ওবায়েদুল কাদের এবং সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য শাজাহান খান। সভানেত্রী ও প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ সামনে এনে সাধারণ সম্পাদক কথা বললেও বিতর্ক থামে না। সম্পাদকের সঙ্গে প্রকাশ্য বিতর্ক আওয়ামী লীগে বিরল ঘটনা বৈকি! নিঃসন্দেহে তা দলের জন্য শুভ নয়। পরিবারের সংজ্ঞা কি হবে, পরিষ্কার না থাকায় তা নিয়েও বিতর্ক রয়েছে।
প্রসঙ্গত, বিগত ২৭ এপ্রিল রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন ভবনে নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে প্রশাসনের আলোচনার সময় ডিসি ও এসপিরা মন্ত্রী-এমপি ও প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতাদের প্রভাব ও হস্তক্ষেপ নিয়ে গভীর শঙ্কা প্রকাশ করেন। প্রধান নির্বাচন কমিশনার যেকোনো মূল্যে নির্বাচন সুষ্ঠু করতে হবে বলে বক্তব্য দেন। এদিকে এমপি-মন্ত্রীর স্বজনদের প্রার্থিতা প্রত্যাহারে কঠোর নির্দেশ এবং দল থেকে সাংগঠনিক ব্যবস্থা গ্রহণের হুঁশিয়ারি দিলেও কাজ না হওয়ায় ৩০ এপ্রিল কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সভা আহ্বান করা হয়েছে। সভায় উদ্ভূত পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে বলে জানা গেছে।
দলীয় সভা সামনে থাকলেও বিতর্ক থামেনি। সভা ২৮ এপ্রিল সমকাল পাঠে জানা গেল সাবেক মন্ত্রী শাজাহান খান প্রশ্ন তুলেছেন, ‘স্বজন রাজনীতি করলে ভোটে কেন নয়?’ তিনি বলেন, ‘স্থানীয় সরকার নির্বাচনে দলীয় মনোনয়নের সিদ্ধান্তের সঙ্গে একমত’ নন এবং কার্যনির্বাহী সংসদের বৈঠকে এ ব্যাপারে ভিন্নমত তুলে ধরেছিলেন। ‘আমি নির্বাচন করছি না’ মন্তব্য করে তিনি বলেন, ‘ছেলে নির্বাচন থেকে সরবে কি না, সেটা তার সিদ্ধান্ত।’ তিনি বলেছেন ৩০ এপ্রিল সভায় প্রধানমন্ত্রীর সামনে তিনি মন্ত্রী-এমপির স্বজনদের উপজেলা নির্বাচনে অংশ নেওয়ার পক্ষে বক্তব্য তুলে ধরবেন। দলীয় সিদ্ধান্তে ‘গণতান্ত্রিক অধিকার নষ্ট হচ্ছে কি না’, নাগরিক অধিকার ক্ষুণ্ন হচ্ছে কি না’ এসব নিয়েও কথা বলবেন। এদিকে প্রচার চলছে ওই সভায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দলীয় সিদ্ধান্তের ব্যাপারে শক্ত অবস্থান নেবেন।
ব্যবসার মতো দলীয় রাজনীতিতে পারিবারিক সিন্ডিকেট, কোটারি বা একচেটিয়াত্ত অবস্থা সৃষ্টি হোক, তা গণতান্ত্রিক মতের মানুষ কেউ-ই চাইতে পারেন না। ঐতিহ্যবাহী দল আওয়ামী লীগে তো নয়ই। তবে কর্মজীবনের প্রথম থেকে রাজনৈতিক দল করার অভিজ্ঞতা থেকে জানি, আত্মীয়-স্বজনরা দল করলে দলীয় পদ বা সুযোগ লাভ তারা করতে পারবেন না কেন- এই প্রশ্ন বড় দলে যেমন উঠেছে, তেমনি ছোট দলেও থাকে। ‘গণতান্ত্রিক অধিকার’ ও ‘ নাগরিক অধিকার’, ছেলে ও বাবা ‘দুই ব্যক্তি’ প্রভৃতির পক্ষে যেমন যুক্তি আছে, তেমনি দল করলে দলীয় সিদ্ধান্ত মানার বিষয়টিও একেবারেই উপেক্ষা করার মতো নয়।
অতীত থেকে আওয়ামী লীগ বিদ্রোহী প্রার্থী বিজয়ী এবং এমনকি পরাজিত হলেও শৃঙ্খলা ভঙ্গের জন্য কোনো শাস্তি দেয়নি। দলীয় মন্ত্রী-এমপি-নেতা কারও মৃত্যু হলে দল না করলেও বা দলে সক্রিয় না থাকলেও স্ত্রী-পুত্র-আত্মীয়দের নির্বাচনে প্রার্থী করেছে। জেলাসহ তৃণমূলের কমিটিগুলো যখন নেতা-মন্ত্রী-এমপিদের আত্মীয়-স্বজন দিয়ে করা হয়েছে, তখনো কোনো উচ্চবাচ্য করে নাই। ফলে দেশের বৃহত্তম ও ঐতিহ্যবাহী গণআস্থাসম্পন্ন দল, যে দল মুসলিম লীগের জমিদার-মহাজন তথা উচ্চবংশীদের কোটারি ভাঙতে না পেরে আলাদাভাবে গণতান্ত্রিক পার্টি হিসেবে জন্ম নিয়েছে, সেই দল আওয়ামী লীগে তৃণমূলে আজ কোটারি হচ্ছে।
বঙ্গবন্ধু দলে গণতন্ত্র ও গঠনতন্ত্র সুরক্ষার স্বার্থে ১৯৫৭ সালে মন্ত্রীপদ ছেড়ে দিয়েছিলেন। ১৯৫৭ সালের কাউন্সিলে পররাষ্ট্রনীতি নিয়ে ভোট হয়। প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী পান ৫০০ ভোট আর সভাপতি মওলানা ভাসানী পান ৩৫ ভোট। ভোটেই আওয়ামী লীগের ভাগ্য নির্ধারিত হতো। স্বাধীনতার পর বাকশাল গঠনের আগে দলীয় গণতন্ত্রকে অবারিত করার জন্য ১৯৭৪ সালে বঙ্গবন্ধু সভাপতির পদ ছেড়ে দেন। আওয়ামী লীগ দলের রয়েছে গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য। বর্তমানে দলীয় পাল্টাপাল্টির যা অবস্থা, তাতে আদেশ-নির্দেশ কাজ দিলে ভালো। তবে অভিজ্ঞতা বলে, রাজনৈতিক দলে ‘কমান্ড মেথড’ তাৎক্ষণিক ফল দিলেও ভবিষ্যতে ক্ষতির কারণ হয়। রাজনৈতিক দলে কমান্ড রাখতে হয়, গণতন্ত্রকে সংকুচিত করার জন্য নয়, ক্রমে প্রসারিত করার জন্য।
বর্তমানে প্রধান বিরোধী দল বিএনপি রয়েছে লেজেগোবরে অবস্থায়। পত্র-পত্রিকার খবরে জানা যাচ্ছে, দায়িত্বশীল নেতাদের অকার্যকর ভূমিকা, কর্মীদের পাশে না দাঁড়ানো ও সমন্বয়হীনতা এবং সর্বোপরি লন্ডন থেকে ‘ডিসিশন’ আসার কারণে বিএনপি রয়েছে তালগোল পাকানো অবস্থায়। দলীয় সিদ্ধান্ত ভেঙে উপজেলা নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ায় সর্বশেষ ৭৩ জন নেতাকে বিএনপি বহিষ্কার করেছে। বয়কট-বর্জনের ভেতর দিয়ে দলটি রয়েছে জনগণ ও কর্মীদের থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায়। প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী দল বিএনপির এই অবস্থা আওয়ামী লীগকে দিচ্ছে ফাঁকা মাঠ। আওয়ামী লীগ পাচ্ছে সময়ও।
এই সুযোগ ও সময় প্রাপ্তির মধ্যে আওয়ামী লীগ যদি দলের ভেতরে গণতন্ত্রের চর্চা ও সংস্কৃতি সম্প্রসারণ করতে পারে, তবে কেবল দল নয়, দেশের গণতন্ত্রের জন্যও তা ইতিবাচক ফলাফল বয়ে আনবে বলে মনে করার যথেষ্ট যুক্তি রয়েছে। এটা তো অস্বীকার করার উপায় নেই, বঙ্গবন্ধুর সময় দেশের রাজনীতি ছিল এগিয়ে আর অর্থনীতি ছিল পিছিয়ে। আর এখন অর্থনীতি গেছে অনেক এগিয়ে রাজনীতি আছে পিছিয়ে। রাজনীতি-অর্থনীতির অসামঞ্জস্যতা থেকেই অস্থিরতা-অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি হয় এবং বিয়োগান্তক সব ঘটনা ঘটে।
বর্তমানে সৃষ্ট অসামঞ্জস্যতা আওয়ামী লীগের দূর করা ভিন্ন বিকল্প আর কিছু নেই। সময়ের দাবি এটাই। প্রয়াত আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আশরাফুল ইসলামের একটি কথা এ ক্ষেত্রে স্মরণযোগ্য: আওয়ামী লীগ পাল্টালে দেশ পাল্টাবে। দেশ রাজনীতি-অর্থনীতি দুদিক থেকেই এগিয়ে যাক, এটাই আজকের দিনের একান্ত কামনা।
লেখক: রাজনীতিক

স্কুলজীবন শুরু হয় আমার ১৯৫৮ সাল থেকে- সেই সময়ে স্কুলে নিয়ে যেতাম দোয়াত -কলম। দোয়াত-কলম নিয়ে গিয়েছি ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত। স্কুলের লেখালেখি, বাসায় বসে লেখালেখি কিংবা স্কুলের পরীক্ষায় দোয়াত-কলম নিয়ে যেতে হতো। কিছুক্ষণ পর পর কলমের লেখার অংশটা বারবার কালির মধ্যে ডুবিয়ে নিতাম। দোয়াত-কলমের পরে এলো ফাউন্টেন পেনের যুগ- কলমের নিচের দিকের অংশে কালি ভরে নিতে হতো তখন।
কালি শেষ হলে অবশেষে আবার কালি ভরে নিতে হতো। তবে ফাউন্টেন পেনের ভরা কালি দিয়ে পরীক্ষার খাতায় কমপক্ষে ২৫ পৃষ্ঠার মতো লেখা যেত। স্কুলের শেষদিকে, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের লেখাপড়া শেষ করেছিলাম ফাউন্টেন পেন দিয়েই।
তবে দোয়াত-কলম নিয়ে অনেক স্মৃতি জেগে রইল মনের গহিন কোণে- কোথায় গেল দোয়াত-কলমের সেই দিনগুলো। লেখালেখির আদি যুগ বা তার পরে মধ্যযুগে ওস্তাদ কলমবাজদের বলা হতো ক্যালিগ্রাফিস্ট বা লিপিকুশলী।
রাজা-রাজরা, নবাব-বাদশাদের দরবারে এক দিন তাদের কত না খাতির ছিল। আমাদের বাংলাদেশে বা বাংলা মুলুকেও রাজা আর জমিদাররা লিপিকুশলীদের গুণী হিসেবে সম্মান করতেন। তাদের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করতেন। সাধারণ গেরস্থরাও এসব গুণী লিপিকরদের ডেকে পুঁথি নকল করাতেন। এখনো সেসব পুঁথি দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। সব অক্ষরের মাপ সমান, বাক্যের একটা পদ থেকে অন্য পদের দূরত্ব সমান, প্রত্যেকটা ছত্র সুশৃঙ্খল, পরিচ্ছন্ন, যাকে বলে মুক্তোর দানার মতো হস্তাক্ষর। অথচ এদের রোজগার ছিল যৎসামান্য। রাজা বা নবাব-বাদশাদের দরবারে যেসব লিপিকরদের ঠাঁই হতো, তাদের কথা অবশ্য আলাদা। ৪ খণ্ডের রামায়ণ কপি করে আঠারো শতকের একজন সুদক্ষ লিপিকর পেয়েছিলেন মাত্র ৭ তঙ্কা, কিছু কাপড় আর মিঠাই।
১৯ শতকে ১২ আনায় অর্থাৎ ৭৫ পয়সায় ৩২ হাজার অক্ষর লেখানো যেত। তবু সেসব হাতের লেখার পুঁথির সামাজিক মর্যাদা আর মাহাত্ম্য ছিল আকাশছোঁয়া।
বলা যায়, কলম তোমার দিন গিয়েছে। কম্পিউটার এসে যেন কালি, কলম আর হাতের লেখাকে জাদুঘরে পাঠিয়ে দিয়েছে সে কবে!
আদিকালে যেসব পেন ছিল তা হলো- বিউরিন পেন, স্টাইলাস বা রিড পেন। পাথর খোদাই শিলালিপির জন্য নির্দিষ্ট ছিল বিউরিন নামের লৌহশলাকা। আর মোমের ট্যাবলেটে লেখা হতো স্টাইলাস পেন দিয়ে। স্টাইলাস পেন ছিল ব্রঞ্জের দ্বারা তৈরি। নীলনদ, টাইগ্রিস আর ইউফ্রেটিস উপত্যকার লোকরা রিড পেন ব্যবহার করতেন। আজকের ক্যালিগ্রাফাররা অনেক উন্নত মানের রিড পেন ব্যবহার করেন। সত্যজিৎ রায় তো নিবের কলমের মান-মর্যাদা বাঁচিয়ে রেখেছিলেন। তার অননুকরণীয় লিপিশিল্প বা চলচ্চিত্রের আগাম স্কেচ এই নিবের কলমেই করে গেছেন।
এরপর ধীরে ধীরে রিড পেনের জায়গা দখল করে নিল কুইল পেন। রাজহাঁস, পেলিক্যান, ঈগল কিংবা কাকের পালক থেকে কুইল পেন তৈরি হতো। এই ধরনের কলমে যারা লিখতেন, তারা সঙ্গে রাখতেন পেন-নাইফ। এই কলম দিয়ে লিখতে লিখতে ভোঁতা হয়ে গেলে পেন-নাইফ দিয়ে তাকে লেখার উপযোগী করে নেওয়া হতো। অভিজাতদের এসব পেন-নাইফ ছিল সোনা আর মণিমানিক্য খচিত।
প্রাচীন বাংলা পুঁথি, দলিল-দস্তাবেজ আর সনদের সব লেখাতেই ব্যবহার করা হয়েছে পাখির পালকের কুইল পেনের। কালির দোয়াতে সেই কলম চুবিয়ে লেখা হতো।
এক সময় এল হোল্ডার পেন- এটি ছিল লম্বাটে হ্যান্ডেলের মাথায় লোহার নিব লাগানো কলম। সরু- মোটা অনুযায়ী সেসব নিবের রকমফের হতো। এসব হোল্ডার কলমও অনেক আগে থেকেই বাঁশ নলখাগড়া পাখির পালক বা ব্রঞ্জ শলাকা গড়া কলমের মতো ইতিহাসের তাকে উঠে গেছে। কঞ্চির কলম, খাগের কলম আর পালকের কলমের কথা আজ খুব করে মনে পড়ে।
পরে এল ফাউন্টেন পেনের যুগ- এ কলম দিয়ে হাতের লেখার দুনিয়ায় বিপ্লব ঘটে গেল। এই কলমকে আমরা ঝরনা কলমও বলতাম।
কালির দোয়াত থাকত তখন পোড়ামাটি দিয়ে তৈরি। আর এতে যেসব কালি রাখা হতো তার নাম ছিল কত বাহারি- কাজল কালি, সুলেখা কালি। কুইঙ্ক, পারকার কালি ছিল ফাউন্টেন পেনের ব্যবহারের জন্য।
হারিয়ে যাচ্ছে হাতের লেখা
হাতের লেখা নিয়ে এক সময় প্রতিযোগিতা হতো স্কুল-কলেজে। তা আর দেখা যায় না- হারিয়ে গেছে হাতের লেখা এবং এর প্রতিযোগিতা। হাতের লেখা নিয়ে আমাদের কালে এবং তারও আগে বাঙালির উৎসাহের অন্ত ছিল না। পরিষ্কার হাতের লেখার কদর ছাড়াও অনুসারী হাতের লেখাও আমরা দেখেছি। রবীন্দ্রানুসারী, নজরুলানুসারী, মাইকেল মধুসূদনানুসারী, সত্যজিৎ- অধিকাংশ জায়গায় অফলাইনে পরীক্ষা বন্ধ করে এখন চলছে অনলাইনে সব পরীক্ষা। হাতে লেখার মেহনত আর কোনো পড়ুয়া নিতে চাইছে না। কম্পিউটারে অনলাইনে পড়াশোনা করতে করতে ছেলেবেলা থেকেই মস্তিষ্ক এমনভাবে তৈরি হয়ে যাচ্ছে যে কম্পিউটার ছাড়া মস্তিষ্ক কাজ করে না এখনকার ছেলেমেয়েদের।
লেখক: পরিবেশবিদ ও চিঠি বিশেষজ্ঞ

‘কিশোরদের জীবন সম্পর্কে জ্ঞান দেওয়া আর মাছকে গোসলের কথা বলা একই বিষয়।’ কথাটি আরনল্ড এইচ গ্ল্যাসোর। আবার কিশোরদের সম্পর্কে ছুটি গল্পে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন, ‘----পৃথিবীতে এমন বালাই আর নাই’। ১৩ থেকে ১৮ বছর বয়সসীমার হিসাবটি এত সহজ নয়। এ সময় ছেলেমেয়েদের মধ্যে নানা শারীরিক পরিবর্তন ঘটে- যাকে বলা হয় বয়ঃসন্ধিকাল। শারীরিক পরিবর্তনের পাশাপাশি তাদের মনেও চলে নানা আলো-আঁধারির খেলা। গ্যাং শব্দটি অপরাধ কিংবা নেতিবাচক কর্মের সঙ্গে সম্পৃক্ত শব্দ-তাতে কোনো সন্দেহ নেই। সেই পর্যবেক্ষণে অপরাধে জড়িত কিশোরদের প্রত্যেকটি দলই কিশোর গ্যাং।
২০১২ সাল থেকে কিশোরদের নিয়ে গড়ে উঠেছে অপরাধের সাম্রাজ্য। যারা ‘কিশোর গ্যাং’ নামে পরিচিত। সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায়ে অবস্থানরত ব্যক্তি স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত ৮ এপ্রিল এ বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করেছেন।
১০ এপ্রিল ছেলের ওপর প্রতিশোধ নিতে আসা কিশোর গ্যাংয়ের হামলায় দন্ত চিকিৎসক কোরবান আলী চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছেন। ৯ ফেব্রুয়ারি মুন্সীগঞ্জের শ্রীনগরে একটি খুনের ঘটনায় কিশোর গ্যাং নতুন করে আলোচনায় এসেছে। ছাত্রীদের উত্ত্যক্ত করার প্রতিবাদে নীরব হোসেন নামের একজন এসএসসি পরীক্ষার্থীকে কিশোর গ্যাংয়ের সদস্যরা ছুরিকাঘাত করে খুন করেছে। রাজধানীর উত্তরায় ২০১৭ সালের ৬ জানুয়ারি অষ্টম শ্রেণির ছাত্র আদনান কবির ১৩ নম্বর সেক্টরের ১৭ নম্বর সড়কের খেলার মাঠে নিহত হয়। ‘নাইন স্টার’ এবং ‘ডিসকো বয়েজ’-এর সংঘাতে কিশোর গ্যাং তাকে পিটিকে হত্যা করে। এর পরই কিশোর গ্যাংয়ের বিষয়টি আলোচনায় আসে। ‘বন্ড ০০৭’ নামের একটি গ্রুপ ২০১৯ সালে বরগুনায় রিফাত শরীফ নামের এক যুবককে প্রকাশ্যে কুপিয়ে হত্যা করে।
পূর্বে যাদের বখাটে বলা হতো- তারাই তথ্যপ্রযুক্তির বিস্ফোরণের যুগে অ্যাপভিত্তিক ও সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ গড়ে তুলেছে। প্রতিটি গ্যাংয়ের একজন দলনেতা এবং একজন পৃষ্ঠপোষক থাকে। আধিপত্য বিস্তার এবং সিনিয়র-জুনিয়র দ্বন্দ্বে কিশোর গ্যাং-এ জড়িত কিশোররা পর্যায়ক্রমে আলাদা আলাদা গ্রুপ তৈরি করে। এদের ড্রেস কোড, হেয়ার স্টাইল এবং চালচলন আলাদা। অস্তিত্ব জানান দিতে পাড়া-মহল্লার দেয়ালে তারা নিজেদের গ্রুপের নাম লেখে, গ্রাফিতি আঁকে। কিশোর গ্যাংয়ের সদস্যরা বিভিন্ন পার্ক, খোলা জায়গা, ফুটপাত, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সামনে একত্রিত হয়ে অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি, ইভ টিজিং, পথচারীদের গতিরোধ, বাইক মহড়াসহ বিভিন্ন অসৌজন্যমূলক আচরণ করে এবং ভিডিও কন্টেন্ট তৈরি করে। কিশোর গ্যাং মূলত ছিনতাই, চাঁদাবাজি, অস্ত্রবাজি, বোমাবাজি, মাদক ব্যবসা, জমি দখলে ভাড়া খাটা, হামলা, মারধর, উত্ত্যক্ত করা এবং খুনের মতো অপরাধের সঙ্গে সরাসরি জড়িত। একাধিক গোয়েন্দা সূত্রে জানা গেছে, কিশোর অপরাধের সঙ্গে জড়িত একটা বড় অংশ রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় ভাসমান জীবনযাপন করে। রেললাইন ও বস্তি এলাকায় নানা অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে তাদের রয়েছে যোগাযোগ। আবার বিত্তশালী পরিবারের সন্তানরা সব পেয়ে যাওয়ার দুঃখ বিলাস লাঘব করার জন্য মাদক ও অনিয়ন্ত্রিত জীবনযাপন বেছে নেয়।
ঢাকায় কিশোর গ্যাংয়ের সংখ্যা কমপক্ষে ৮০। গ্যাংয়ের সদস্য সংখ্যা অধিকাংশ ক্ষেত্রে ১০-৫০ জন। ২০২২ সালের শেষে পুলিশের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, পুরো দেশে অন্তত ১৭৩টি কিশোর গ্যাং রয়েছে। ২০২৩ সালে ঢাকায় সংঘটিত ২৫টি খুনের সঙ্গে কিশোর গ্যাংয়ের সংশ্লিষ্টতা রয়েছে। প্রতিটি কিশোর গ্যাংয়ের নানাবিধ নাম রয়েছে: গাংচিল, ম্যাক্স পলু, বাট্টু, লিটন বাহিনী, ভাগনে সুমন বাহিনী, রাজগ্রুপ, রকি গ্রুপ, রোমান্টিক গ্রুপ, পটেটো রুবেল গ্রুপ, ডাইল্লা গ্রুপ ইত্যাদি। উত্তরা, মিরপুর, তেজগাঁও, ধানমন্ডি, মোহাম্মদপুর, হাজারীবাগ, মহাখালী, বংশাল, মুগদা, চকবাজার এবং শ্যামপুরে কিশোর গ্যাংয়ের আধিক্য লক্ষ্যযোগ্য। প্রতিটি গ্রুপের রয়েছে নিজস্ব ফেসবুক গ্রুপ। যেখানে কিশোররা পরবর্তী সময়ে কাকে টার্গেট করা হবে, কার উপরে আক্রমণ করা হবে সে বিষয়ে পোস্ট দিয়ে থাকে।
স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন আসে- কিশোররা কেন বখে যাচ্ছে এবং তারা গ্যাং কালচার গড়ে তুলছে। এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে প্রথমই আমাদের সমাজীকরণ প্রক্রিয়ার দ্বারস্থ হতে হবে। প্রথমত, পরিবারের প্রসঙ্গ আসে। একটি শিশু যখন একটি পরিবারে বেড়ে ওঠে- সে সেই পরিবার থেকে ওই সমাজের উপযোগী আচরণের ধারা রপ্ত করে। নিম্নবিত্ত পরিবারের সদস্যদের ভেতরে নানাবিধ কারণেই সুস্থিরতা থাকে না। প্রধানত রুটি-রুজির সন্ধানে তারা এতটাই ব্যস্ত থাকেন যে, সন্তানকে সময় দিতে পারেন না। আবার ভাঙা সংসারের বিষয়টিও এখানে প্রযোজ্য। খেলার মাঠ এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানও সমাজীকরণ প্রক্রিয়ার আওতাভুক্ত। খেলাধুলা কিশোরদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। অথচ হায়! ঢাকা শহরে খেলার মাঠ কোথায়? অধিকাংশ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেও খেলার মাঠ নেই।
অন্যদিকে জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গড়ার কথা জোরেশোরে বলা হলেও আমরা জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গড়তে পারিনি। এক সময় শিক্ষকরা ছাত্রদের কাছে আদর্শ হিসেবে বিবেচিত হতেন। শিক্ষকের সেই মর্যাদা বহুদিন ধরেই নেই। অথচ কেনা জানে একটি জাতি গঠনে শিক্ষকরা কতটা ঘাম ঝরান। এখন ক্ষমতা এবং বিত্ত জ্ঞানের জায়গাটি দখল করে নিয়েছে। ক্ষমতার কাছাকাছি থাকাটাই সবার কাছে মুখ্য হয়ে উঠেছে। বর্তমানে ক্ষমতা আর বিত্ত সরলরেখায় চলে। কিশোররা তাই ক্ষমতার কাছাকাছি থেকে ক্ষমতা অনুশীলনের পাশাপাশি বিত্তের কাছেও পৌঁছতে চাইছে। বর্তমান সামাজিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতা কিশোরদের ভেতরের স্বভাবজাত হিরোইজমকে উসকে দিচ্ছে। কিশোররা অন্যের মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু হতে চাইছে। আর সত্য বচন হলো- তথ্যপ্রযুক্তির এই যুগে পিতা-মাতা সঠিক প্যারেন্টিং করছেন না। তাদের দৃষ্টিও গ্যাজেটের দিকে। অনেক ক্ষেত্রে পিতা-মাতার মধ্যে সন্তান স্বচ্ছতা দেখছে না। ফলে পিতা-মাতাও সন্তানকে শাসন করার যোগ্যতা হারাচ্ছেন।
পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ থেকে প্রতীয়মান হয়েছে, রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় এই কিশোর গ্যাং গড়ে উঠছে, প্রতিপালিত হচ্ছে এবং রকমারি অপরাধে লিপ্ত হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে টমাস মানের কথাটিই মনে পড়ে যাচ্ছে, রাজনীতি আমাদের ‘বিধিলিপি’। অতি সম্প্রতি পুলিশের প্রতিবেদনে কিশোর গ্যাংয়ের প্রশ্রয়দাতা হিসেবে ঢাকার ২১ জন কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে অভিযোগ এসেছে। স্পষ্টতই গ্যাংয়ের নিয়ন্ত্রক বা পৃষ্ঠপোষকের ভূমিকায় রয়েছেন বড় ভাই। গ্যাংয়ের বড় অংশ কিশোর হলেও নেতাদের বয়স ১৯ থেকে ৩৮ বছর।
পুলিশের নানা সংস্থা প্রায় প্রতিদিনই কিশোর গ্যাংয়ের সদস্যদের গ্রেপ্তার করছে। আদালতের নির্দেশনা অনুযায়ী এদের হেফাজতে নিতে যে নিয়ম রয়েছে তা অনুসরণ করে কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রে পাঠাচ্ছেন। এখানে থেকে যায় অনেক প্রশ্ন। শিশু আদালতের সংখ্যা; প্রচলিত আইন; বিচারিক প্রক্রিয়া এবং সংশোধনাগারের অন্তর্তল ও বহির্তলের নানাবিধ কাঠামো নিয়েও।
কিশোররা ব্যবহৃত হচ্ছে। তাদের ব্যবহার করা হচ্ছে। নিয়ন্ত্রক বা পৃষ্ঠপোষকের ভূমিকায় রয়েছে সমাজের কিছু ‘বড় ভাই’। তাদের আইনের আওতায় নিয়ে আসা প্রচলিত আইনে যথেষ্ট কঠিন। কারণ তাদের জড়িত থাকার কোনো দালিলিক প্রমাণ নেই। কিশোর গ্যাংয়ের সদস্যদের দ্বারা যখন অপরাধ সংঘটিত হয় তখন বড় ভাইয়েরা সঙ্গে থাকেন না। অর্থাৎ চাক্ষুষ প্রমাণ মিলছে না। বাকি থাকে Circumstantial evidence. Circumstantial evidence-এ অভিযুক্ত ব্যক্তির অপরাধ প্রমাণ করা অত সহজ নয়। তবে বিষয়টি মোটা দাগে কী দাঁড়াল? কিশোর অপরাধী কিশোর হিসেবে পার পেয়ে যাচ্ছে আর পৃষ্ঠপোষক পার পেয়ে যাচ্ছে যথাযথ প্রমাণের অভাবে। এখানেই তামাক আর ফিল্টার-দুজনে দুজনার।
যুক্তরাজ্যের UCL প্রেস থেকে ‘The Wild East: Criminal Political Economies in South Asia’ নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। বাংলায় বললে, ‘বুনো পূর্ব: দক্ষিণ এশিয়ার অপরাধমূলক রাজনৈতিক অর্থনীতি।’ সহজ কথায় রাজনৈতিক ঠগিতন্ত্রের অর্থনীতি। অধিক ঘনবসতিপূর্ণ, চরম বৈপরীত্যপূর্ণ, নোংরা ও অপরাধে পরিপূর্ণ নগরসমূহে ক্ষমতাবানের গড়ে তোলে নিজস্ব বাহিনী এবং রাজত্ব। এসব করতে হলে থাকতে হয় আইনের ঊর্ধ্বে। কিশোর গ্যাং-ও প্রকারান্তরে তাই-ই। এটি শুধু বাংলাদেশের সমস্যা নয়- ভারত ও পাকিস্তানেরও সমস্যা।
বাংলাদেশের অবকাঠামোগত উন্নয়নে নাগরিক হিসেবে আমরা গর্বিত। তবে এখন সময় এসেছে সমতা এবং মানবিক উন্নয়নের। বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার ৪ কোটি শিশু-কিশোর। এই সংখ্যার ১ কোটি ৩০ লাখ শিশু-কিশোর নানা ঝুঁকিপূর্ণ কর্মে নিয়োজিত। অর্থাৎ তাদের জীবনের স্থির কোনো লক্ষ্য নেই। রয়েছে অনিশ্চয়তা। এই অনিশ্চয়তাই শিশু-কিশোরদের অপরাধের পথে ঠেলে দিচ্ছে। এদের মূলধারায় ফিরিয়ে আনতে সমাজে সমতা প্রতিষ্ঠা ভীষণ জরুরি। একদিকে সুরম্য অট্টালিকা অন্যদিকে বস্তির ছড়াছড়ি বিষয়টি সতর্ক পদক্ষেপ দাবি করে।
শুরুতেই উল্লেখ করেছিলাম প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনার বিষয়টি। এই সমন্বিত উদ্যোগে তিনি অভিভাবক, শিক্ষক, স্থানীয় জনপ্রতিনিধিসহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে যুক্ত হতে বলেছেন। কিশোর গ্যাং বা কিশোর অপরাধীদের অন্য অপরাধীদের সঙ্গে মিলিয়ে ফেলতে না করেছেন। কারণ এরা ভবিষ্যতের নাগরিক। বিশেষ কাউন্সিলিং এবং কিছু প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলেছেন। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বিশেষ দৃষ্টি দিতে বলা হয়েছে। কিশোর গ্যাং বিষয়ে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প নিতে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়কে নির্দেশনা দিয়েছেন তিনি। মন্ত্রিসভার বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী এ সিদ্ধান্ত প্রদান করেন। পরে সংবাদ সম্মেলনে মন্ত্রিপরিষদ সচিব মো. মাহবুব হোসেন বৈঠকের সিদ্ধান্ত অবহিত করেন।
কিশোর গ্যাং তাবৎ দেশে যেভাবে তাণ্ডব চালাচ্ছে তাতে এখনই সরকারকে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে প্রতিটি শিশু-কিশোরের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করা; সমাজীকরণ প্রক্রিয়া যথাযথভাবে সম্পন্ন করা; রাজনৈতিক হীনস্বার্থে শিশু-কিশোরদের ব্যবহার বন্ধ করা; শিশু আইনে প্রয়োজনীয় সংশোধন আনা; কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রকে ঢেলে সাজানো এবং অস্ত্র ও মাদকের সহজলভ্যতা রোধ করা একান্ত জরুরি।
লেখক: সেক্রেটারি জেনারেল, পেন ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ ও নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক

পদ্মা সেতুতে টোল আদায় ১৫০০ কোটি টাকা ছাড়াল। ২০২২ সালের ২৫ জুন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বহুল প্রতীক্ষিত পদ্ম সেতু উদ্বোধন করেন। এ পর্যন্ত সেতুর উভয় প্রান্ত দিয়ে যানবাহন পারাপার হয়েছে ১ কোটি ১২ লাখ ৯১ হাজার ৯৫টি। এর মধ্যে মাওয়া প্রান্ত দিয়ে পারাপার হয়েছে ৫৬ লাখ ১ হাজার ২৩২ এবং জাজিরা প্রান্ত দিয়ে পারাপার হয়েছে ৫৬ লাখ ৮৯ হাজার ৮৬৩টি যানবাহন। পদ্মা সেতু দিয়ে আশানুরূপ টোল আদায় অব্যাহত রয়েছে। ২৬ জুন থেকে সেতুটি যান চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করা হয়।
৩০ হাজার ১৯৩ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত ৬ দশমিক ১৫ কিলোমিটার দীর্ঘ পদ্মা বহুমুখী সেতু উদ্বোধনের পর থেকে দক্ষিণ ও পশ্চিমাঞ্চলের ২১ জেলা ও দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে এটি। সেতু হওয়ার পর কোনো রকম ঝক্কিঝামেলা ছাড়াই দক্ষিণের জেলাগুলোর মানুষেরা ঈদসহ যেকোনো প্রয়োজনে সহজেই রাজধানীর ঢাকায় আসা-যাওয়া করতে পারছেন।
১৯৭১ সালে স্বাধীনতা অর্জনের পর থেকে সড়ক যোগাযোগের গুরুত্ব বৃদ্ধি পেতে থাকে। এক্ষেত্রেও বাধা ছিল অসংখ্য নদ-নদী। যেকোনো সড়ক তৈরি করতে গেলেই ছোট-বড় নদী অতিক্রম করতে হতো। অনেক ফেরি চালু ছিল। উত্তরাঞ্চলের মানুষ কখনও ভাবতেই পারেনি সকালে রওনা দিয়ে দুপুরে ঢাকা পৌঁছে যাবে। বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে প্রায় তিন কোটি লোক বসবাস করে, যারা পদ্মা সতু প্রকল্পটির প্রাথমিক উপকারভোগী।
বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনীতিতে পদ্মা সেতুর প্রভাব সুদূর প্রসারী। সামাজিক উন্নয়নেও এর বড় প্রভাব থাকছে প্রতিদিনই। পদ্মা সেতু দেশের দক্ষিণাঞ্চলের মানুষের জন্য অর্থনৈতিক লাইফ লাইন রূপে কাজ করছে। বাণিজ্য, আঞ্চলিক বাণিজ্য, দক্ষিণ এশিয়ায় সংযোগ, শিল্পাঞ্চল গড়ে ওঠা, কৃষি সম্প্রসারণ, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিসহ আর্থসামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখছে পদ্মা সেতু। পদ্মা সেতু বাঙালির আত্মমর্যাদা এবং আত্মনির্ভরতার প্রতীক। জাতি হিসেবে এটি আমাদের দীর্ঘদিনের লালিত স্বপ্ন ছিলো। পদ্মা সেতু বাংলাদেশের বহুমাত্রিক ক্ষেত্র সৃষ্টি করেছে। পদ্মা সেতুকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশে শিল্প এখন নতুন শিল্পাঞ্চল গড়ে উঠছে, অর্থনৈতিক উন্নয়ন হচ্ছে।
গত দিনগুলোতে পদ্মা সেতু দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ২১ জেলার তিন কোটি মানুষের জীবনমান পাল্টে দিয়েছে। নিজের টাকায় নিজেদের পদ্মা সেতু আজ মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে পদ্মার বুক চিরে। স্বপ্নের পদ্মা সেতুর প্রভাবে বদলে গেছে এ অঞ্চলের অর্থনীতির চালচিত্র। খুলনা রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর হিসাব অনুযায়ী, ২০২২-২৩ অর্থবছরে এ অঞ্চল থেকে বিদেশে রপ্তানিকৃত পণ্য থেকে আয় বেড়েছে প্রায় ১ হাজার কোটি টাকা।
পদ্মা বহুমুখী সেতুর কারণে এ অঞ্চলে যেমন যোগাযোগ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন হয়েছে, তেমনি অর্থনীতিও ব্যাপকভাবে চাঙা হয়েছে। সেইসঙ্গে মৃতপ্রায় মোংলা বন্দর এখন কর্মচাঞ্চল্যে মুখর। এছাড়া পদ্মা সেতু ঘিরে মোংলা বন্দরের সঙ্গে সরাসরি সংযোগ ও উত্তরাঞ্চলের সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে ১৮টি প্রকল্পের আওতায় আনা হয়েছে। যশোর-খুলনা মোংলা মহাসড়ক ছয় লেনে উন্নীত করাসহ আরো সাতটি প্রকল্পের কাজ চলছে।
এ সেতু শুধু যোগাযোগের মাধ্যম নয়, উন্নয়নের প্রবেশদ্বারও। শিল্প, সংস্কৃতি, কৃষি, পর্যটন, শিল্পসহ নানা ব্যবসার প্রসার ঘটেছে এই সেতুর মাধ্যমে। এ সেতুর ফলে বদলে গেছে দক্ষিণের ২১ জেলার কৃষি ভিত্তিক অর্থনিতির চিত্র। দেশের গন্ডি পেরিয়ে প্রথমবারের মতো দক্ষিণাঞ্চলের সবজি রপ্তানি হচ্ছে ইউরোপে। যোগাযোগ সহজ হওয়ায় রাজধানী থেকে মাত্র ৫০ কিলোমিটার দূরের পদ্মা পাড়ের সবজির সবজির চাহিদা। শুধু তাই নয়, কন্ট্রাক্ট ফার্মিংয়ের মাধ্যমে গত কয়েক মাসে ইউরোপের বাজারে প্রচুর সবজি রপ্তানি করার সুযোগ এসেছে। তাই মান সম্মত সবজি উৎপাদনে প্রশিক্ষণ ও পরামর্শ দেয়া হচ্ছে হাজার হাজার কৃষককে। ন্যায্য মূল্যে সবজি বিক্রির ফলে লাভবান হচ্ছেন কৃষক ও ব্যবসায়ীরা। কৃষকরা জানান, আগে ফেরি পার হতে সময় লাগায় উৎপাদিত কৃষি পণ্য সময় মত বাজারজাত করা যেত না। পদ্মা সেতু হওয়ার পর এখন এ অঞ্চলে উৎপাদিত কৃষিপণ্য বিদেশে রপ্তানি করা হয়। মাটির ধরণ অনুযায়ী অনাবাদী জমিতে রপ্তানিমুখী সবজি উৎপাদনে কাজ চলছে। আর রপ্তানিকে আরও সহজ করতে প্যাকেজিং ও প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্র নির্মাণের বিষয়ে কাজ হচ্ছে।
পদ্মা সেতুর কল্যাণে ওই অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক দিক দিয়ে ব্যাপক উন্নতি হচ্ছে। আগে ওইসব এলাকা থেকে কেউ ঢাকায় কোনো কাজ সারতে আসল কমপক্ষে দুই রাত ও এক দিন অবস্থান করতে হতো। অথচ এখন দিনে এসে কাজ সেরে দিনের মধ্যেই চলে যেতে পারছে। এটি যে কত বড় পাওয়া ওইসব এলাকার মানুষের সেটি বলে বোঝানো যাবে না। তা ছাড়া বাণিজ্য বেড়েছে, বাড়ছে বিনিয়োগ, পর্যটন খাতের ব্যাপক উন্নতি হয়েছে, জমির মূল্য বেড়েছে অনেক, যার সুফল পাচ্ছেন ওইসব এলাকার মানুষ। পদ্মাসেতুর নির্মাণ এর পর জমি জমার দাম কি পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে তা হিসাব করা উচিত। উৎপাদিত পণ্যের দাম বেড়েছে। যার কয়েক কাঠা জমি আছে সে এখন ৩-৪ কোটি টাকার মালিক।
পদ্মা সেতু অর্থনীতি ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে এবং কৃষি বিপ্লব ও কর্মসংস্থানের ব্যাপক অবদান রাখছে বলে উল্লেখ করেছেন বিশ্লেষকরা। পদ্মা সেতুর মাধ্যমে রাজধানী ঢাকার সঙ্গে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চল, মংলা বন্দরের সরাসরি সড়ক যোগাযোগ তৈরি হয়েছে। রাজধানী এবং দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের মধ্যে যাতায়াতের সময় এক-চতুর্থাংশ কমে এসেছে। আগে যেখানে ১০ থেকে ১২ ঘণ্টা সময় লাগত দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলোতে যেতে, সেখানে এখন যেতে সময় লাগছে আড়াই ঘণ্টা থেকে সর্বোচ্চ সাড়ে তিন ঘণ্টা। পদ্মা সেতুর কল্যাণে পর্যটন খাতেরও ব্যাপক উন্নয়ন ঘটেছে। প্রস্তাবিত এশিয়ান হাইওয়ের এবং ট্রান্স-এশিয়ান রেলওয়ে নেটওয়ার্কের অংশ হওয়ায় পদ্মা সেতু আঞ্চলিক সংযোগকে সহজতর করেছে। নির্মাণ খাতে ২৯ শতাংশ, কৃষি খাতে ৯ দশমিক ৫ শতাংশ এবং উৎপাদন ও পরিবহনে ৮ শতাংশ প্রবৃদ্ধিতে অবদান রাখছে পদ্মা সেতু।
পদ্মা সেতুর প্রভাবে এই অঞ্চলে দারিদ্র্য ১ শতাংশ কমেছে এবং জাতীয়ভাবে কমবে শূন্য দশমিক ৮ শতাংশ। দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে ১ দশমিক ২৩ শতাংশ এবং জাতীয়ভাবে শূন্য দশমিক ৫৬ শতাংশ জিডিপির প্রবৃদ্ধি হবে। পদ্মা সেতুর জন্য করা নদী শাসনের ফলে ৯ হাজার হেক্টর জমি খরা ও বন্যা থেকে রক্ষা পাচ্ছে, যার আর্থিক মূল্য ১৫৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। মাওয়া-জাজিরা রুটে ৪০০ মিলিয়ন ডলারের ফেরি সার্ভিস খরচ সাশ্রয় হচ্ছে।
কুয়াকাটা সমুদ্রসৈকতসহ এই এলাকার অন্যান্য পর্যটন এলাকায় পর্যটকের সংখ্যা অনেক বেড়েছে। এখন প্রতিদিন ১০০ থেকে ১৫০টি গাড়িতে করে কুয়াকাটায় যাচ্ছেন পর্যটকরা। ঢাকা থেকে এখন বরিশালে মাত্র আড়াই ঘণ্টায় চলে আসা যাচ্ছে। এই সুফলটি মিলছে এই পদ্মা সেতুর কল্যাণে। উদ্যোক্তারা এই এলাকায় ব্যাপক বিনিয়োগের জন্য আসছেন। তারা প্রচুর জমি কিনছেন শিল্প কারখানা গড়ার জন্য।
এতে কর্মসংস্থান বাড়ছে। সবচেয়ে বড় কথা পদ্মা সেতুর কল্যাণে বরিশাল বিভাগের কৃষি, প্রাণিসম্পদ খাতের ব্যাপক উন্নতি ঘটেছে। আগে পণ্য আনা-নেওয়া করতে লঞ্চের জন্য অপেক্ষা করতে হতো ঘণ্টার পর ঘণ্টা। এতে পথেই অনেক পণ্য নষ্ট হয়ে যেত। এখন আর এমনটি হয় না। সুতরাং পদ্মা সেতুর কল্যাণে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের মনুষের জীবনে আমূল পবির্তন এসেছে। বদলে গেছে ২১ জেলার অর্থনীতি।
পদ্মা সেতুর কারণে পণ্য আমদানি ও রপ্তানিতে গতি বেড়েছে বেনাপোল স্থলবন্দরে। কম খরচে ও অল্প সময়ে রাজধানী ঢাকাসহ বিভিন্ন স্থানে পণ্য সরবরাহ করতে পারছেন দেশের বৃহৎ স্থলবন্দর বেনাপোল বন্দরের ব্যবসায়ীরাও। পদ্মা সেতুর মাধ্যমে সহজ ও উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার সুবাদে আরও গতিশীল হয়ে উঠছে এই বন্দর।
এর আগে ফেরির সিরিয়াল পাওয়া, আবার অন্য রোড দিয়ে ঘুরে যাওয়াতে ব্যবসায়ীদের খরচ বাড়ত। এখন পদ্মা সেতুর কল্যাণে সময় আর খরচ দুটিই কমেছে। পদ্মা সেতুর উদ্বোধনের পর দেশের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ২১ জেলার অর্থনৈতিক অবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটছে। এ অঞ্চলের মানুষের ভাগ্য বদলে যাচ্ছে। মোংলা ও পায়রা বন্দরের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন হয়েছে।
পায়রা থেকে কুয়াকাটার বিস্তৃত এলাকা ঘিরে পর্যটনভিত্তিক উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি সমন্বিত মাস্টার প্ল্যান বাস্তবায়ন করছে সরকার। এই মাস্টার প্ল্যানে থাকছে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, আধুনিক পর্যটনকেন্দ্র, শিল্পভিত্তিক বন্দরনগরী, পরিকল্পিত নগরায়ন, যোগাযোগ, অর্থনীতি ও কৃষি খাতের উন্নয়ন, পরিবেশ সুরক্ষা ও দুর্যোগ ঝুঁকিসহ জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলাভিত্তিক কার্যক্রম। পদ্মা সেতু এসব ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা রাখবে। ভবিষ্যতে পদ্মা সেতু দক্ষিণ এশিয়া ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার যোগাযোগ, বাণিজ্য, পর্যটনসহ অনেক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। সড়ক ও রেলপথের মাধ্যমে পিছিয়ে পড়া অঞ্চলকে কর্মসংস্থান, বিনিয়োগ ও রপ্তানি বাড়াতে সহায়তা করছে। রেললাইন চালু হলে জিডিপিতে আরও ১ শতাংশ যুক্ত হবে।
পদ্মা সেতু শুধু মানুষের যাতায়াত আর পণ্য পরিবহনের সমাধান করেনি, দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের মানুষের ভাগ্য আমূল বদলে দিয়েছে। মৃতপ্রায় মোংলা বন্দরকে সচল করে সারা বিশ্বের কাছে বাংলাদেশকে মাথা উঁচু করে দাঁড় করিয়েছে পদ্মা সেতু। এ কথায় বলা যায় নিজস্ব অর্থায়নে স্বপ্নের পদ্মা সেতু নির্মাণ করে বিশ্বকে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন শেখ হাসিনা। চ্যালেঞ্জের মুখে এই পদ্মা সেতু নির্মাণ একমাত্র বঙ্গবন্ধুকন্যার পক্ষেই সম্ভব হয়েছে। পদ্মা সেতু চালু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মোংলা বন্দরের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ ব্যবস্থায় একটা আমূল পরিবর্তন হয়েছে। দেশের বিভিন্ন এলাকার ব্যবসায়ীরা বিদেশ থেকে গাড়ি আমদানি করছেন। তারা কম খরচের জন্য চট্টগ্রাম পোর্ট ব্যবহার না করে বর্তমানে মোংলা পোর্ট থেকে তাদের গাড়ি ছাড়িয়ে নিচ্ছেন।
এমনকি প্রতিবেশী দেশ ভারতের সঙ্গে আমাদের বাণিজ্য বেড়েছে। দেশের অন্যতম বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী খাত হিমায়িত মৎস্য ও পাট শিল্প থেকে রপ্তানির মাধ্যমে আয় অধিকাংশ খুলনা থেকে হতো। পদ্মা সেতু চালু হওয়ার পর সেই খাত তার হারানো গৌরব ফিরে পাচ্ছে, আয়ও বেড়েছে। এর পাশাপাশি কমে গেছে পণ্য পরিবহনের খরচও। পদ্মা সেতু কেবল দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের নয়, পুরো বাংলাদেশের অর্থনীতির চেহারাই বদলে দিয়েছে।
এদিকে পদ্মা সেতু হওয়ায় সবচেয়ে বেশি লাভবান হচ্ছেন এই অঞ্চলের হিমায়িত পণ্য রপ্তানিকারকরা। পদ্মা সেতুর কারণে আবারো ঘুরে দাঁড়াতে যাচ্ছে বাংলাদেশের হিমায়িত মৎস্য খাত। এই সেতু দিয়ে চট্টগ্রাম বন্দরে যথাসময়ে হিমায়িত চিংড়ি ও অন্যান্য মাছ বিদেশে রপ্তানি করতে পারছেন ব্যবসায়ীরা। এতে রপ্তানিকারকরা অনেক বেশি সুফল ভোগ করছেন।
খুলনা, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট, বরগুনা ও পটুয়াখালীর অংশবিশেষ নিয়ে বিশ্বের বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বন সুন্দরবন। ৬৫১৭ বর্গকিলোমিটার বিস্তৃত এই বনের এলাকা। দীর্ঘ সময় নষ্ট হওয়ায় ও যাতায়াত ব্যবস্থা ভালো না থাকায় একসময় সুন্দরবন ভ্রমণে দেশি-বিদেশি পর্যটকরা আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছিলেন। পদ্মা সেতু হওয়ার পরে সেই দৃশ্য পাল্টে গেছে। গত এক বছরে দেশি ও বিদেশি পর্যটকদের ব্যাপক সমাগম ঘটছে সুন্দরবনে। এতে একদিকে স্থানীয় অধিবাসীরা যেমন সুফল ভোগ করছে, তেমনি সরকার পাচ্ছে রাজস্ব।
পদ্মা সেতু দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের অর্থনীতিকে চাঙা করে তুলছে। এছাড়া কৃষিভিত্তিক শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠায় মানুষের কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে। এক বছরে সড়কপথে যোগাযোগ ব্যবস্থার আমূল পরির্বতনসহ পণ্য পরিবহনের ব্যাপক সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মাওয়ায় পদ্মা সেতু নির্মাণ করে এ অঞ্চলের মানুষের মুখে হাসি ফুটিয়েছেন।
দেশের দক্ষিণাঞ্চল ট্রান্স-এশিয়ান হাইওয়ে এবং ট্রান্স-এশিয়ান রেলওয়ের সঙ্গে সংযুক্ত হবে। ভারত, ভুটান ও নেপালের সঙ্গে বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক যোগাযোগ থাকবে। যানবাহনের সংখ্যা প্রতিবছর ৭-৮ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে এবং ২০৫০ সাল নাগাদ ৬৭ হাজার যানবাহন চলাচল করবে। পদ্মা সেতু বাস ও রেল উভয়ই চলাচলের উপযোগী করে তৈরি করা হয়েছে। এটির মাধ্যমে শুধু যাতায়াতেরই সুবিধা হবে না বরং এটি টেলিযোগাযোগ, বিদ্যুৎব্যবস্থা এবং প্রাকৃতিক গ্যাস পরিবহনের ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা পালন করবে।
লেখক: প্রাবন্ধিক, গবেষক ও কলামিস্ট

ভাটি এলাকার কৃষকের একমাত্র ফসল ধান। হবিগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোনা, সুনামগঞ্জ এই চার জেলার বিস্তীর্ণ এলাকা নিয়ে হাওর। এখানকার নব্বই ভাগ মানুষ কৃষির ওপর নির্ভরশীল। হাওর এলাকার কৃষকের প্রধান ফসল ধান। সোনালি ফসল ঘিরেই স্বপ্ন বোনেন সেখানকার বেশির ভাগ মানুষ। এই ধানচাষ হয় শীতের শেষে এবং উঠানো হয় বৈশাখ থেকে জ্যৈষ্ঠ মাসের মধ্যে। প্রকৃতির বিরূপ আচরণে প্রায় বছরই তাদের ফসল তলিয়ে যায়। বর্ষার মৌসুমে মৎস্য শিকার করে জীবিকা চলে অধিকাংশ কৃষকের। এখন জলাশয়ে সেই মাছও নেই। তারপরও তাদের জীবন থেকে নিই।
আমাদের দেশের ভৌগোলিক প্রেক্ষাপটে স্বাভাবিকভাবেই ঝড়, প্লাবন কিংবা খরার মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগের সঙ্গে সংগ্রাম করে একজন কৃষক ফসল উৎপন্ন করেন। নানা সংগ্রাম করে কৃষক নতুন উদ্যোমে চাষবাস করেন।
কৃষকরা ক্রমাগত বাম্পার ফলন উৎপাদন করেছেন। বাম্পার ফলন মানেই অধিক পরিমাণ ধান বাজারে সহজলভ্য হওয়া। তবে এর অন্য প্রভাব হলো, উৎপাদিত কৃষিপণ্যে মূল্যহ্রাস, যা কৃষকের জন্য সুখকর নয়। বৈশাখের নতুন ধানে ভরপুর কিশোরগঞ্জের ভৈরব বাজারের মোকাম। তবে বাজারে ক্রেতা কম থাকায় দুশ্চিন্তায় ধান বিক্রেতারা। খরবে জানা যায়, হবিগঞ্জের আজমিরীগঞ্জ এলাকা থেকে শাহ হোসেন মাঝি ২ হাজার ৪০০ মণ বৈশাখী ধান নিয়ে ভৈরব ঘাটে এসেছেন। এ বছর হাওরে ধানের ফলন অন্যান্য বছরের তুলনায় ভালো হয়েছে। তাই কৃষকরা পাইকারদের কাছে ধান বিক্রি করেছেন। তবে এ বছর ধানের দাম খুব কম। তাই ফসল বেশি পেলেও দাম না পাওয়ায় মন ভালো নেই কৃষকদের।
এ বছর ধানের ফলন ভালো হয়েছে। উচ্চফলনশীল ধান উৎপাদন করে কৃষকের মুখে ফুলকি দেখা যাচ্ছে; কিন্তু সোনালি ফসল ঘরে তোলার সঙ্গে সঙ্গে দুশ্চিন্তা ভর করছে প্রতিটি কৃষকের। তারা পাচ্ছেন না ন্যায্য মূল্য। উৎপাদন খরচের কম মূল্যে ধান বিক্রি করতে অনেকে বাধ্য হচ্ছেন। কৃষকের হাতে টাকা নাই। পরিবারের ভরণপোষণের জন্য ধানই একমাত্র সম্বল। ধান বিক্রি করতে গিয়ে তারা হতাশায় নিমজ্জিত হচ্ছেন।
বাড়তি খরচের চাপ সামলাতে কৃষকের চোখে-মুখে যেন বিষণ্নতার ছাপ ফুটে উঠেছে। আর উৎপাদিত কৃষিপণ্যের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত না হলে চাষাবাদে আগ্রহ হারানোর শঙ্কা রয়েছে। তাই ফসলের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করার দাবি কৃষকদের। এখন ভাটি এলাকায় ধান বিক্রি হচ্ছে ৭৬০ টাকা থেকে ৮০০ টাকা মণ দরে। অথচ তাদের উৎপাদন খরচ আছে ৮০০ টাকার ওপরে। সরকার ঘোষণা দিয়েছে ৩২ টাকা কেজি দরে অর্থাৎ ১২৮০ মণ দরে ধান কিনবে আগামী ৭ মে থেকে। দামের এত ফারাক কেন?
সরকারিভাবে প্রতি বছরই নির্ধারিত মূল্যে সরকার চাল সংগ্রহ করে। বেশির ভাগ সময়েই লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব হয় না। এর কারণ প্রধানত বিদ্যমান বাজারদরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করা সরকারের পক্ষে সম্ভব হয় না। তা চেষ্টা করা বাস্তবসম্মতও নয়। সরকারি চাল সংগ্রহনীতির প্রধান উদ্দেশ্য হলো কৃষকদের ধানের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করা।
সরকার ঘোষণা করেছে চলতি বছর বোরো মৌসুমে কৃষকের কাছ থেকে ৩২ টাকা কেজি দরে ৫ লাখ টন ধান কিনবে সরকার। গতবার ৩০ টাকা দরে কেনা হয়েছিল। সে হিসাবে এবার প্রতি কেজিতে দুই টাকা বাড়ানো হয়েছে। তা ছাড়া গতবারের চেয়ে এবার এক লাখ টন বেশি ধান কেনা হবে। আগামী ৭ মে থেকে ধান কেনা শুরু হবে ও ৩১ আগস্ট পর্যন্ত তা চলবে জানিয়ে কৃষিমন্ত্রী বলেছেন, বেশি ধান কেনা হবে হাওর থেকে। প্রয়োজনে কৃষকের কাছ থেকে ৫ লাখ টনের বেশি ধান কেনা হবে। ধানের পাশাপাশি এবার ৪৫ টাকা কেজি দরে ১১ লাখ টন সেদ্ধ চাল সংগ্রহ করা হবে। গতবার এটি ৪৪ টাকা কেজি দরে কেনা হয়েছিল। এ ছাড়া ৪৪ টাকা কেজি দরে এক লাখ টন আতপ চাল কিনবে সরকার। ৩৪ টাকা কেজি দরে ৫০ হাজার টন গমও কেনা হবে।
লেখক: সাংবাদিক, সমাজকর্মী

১৭৭৯ সালে ইংরেজরা নৌবহরে এসে আন্দামান দ্বীপে পৌঁছায়। আন্দামানের নিরিবিলি পরিবেশ, উত্তাল সমুদ্রের ঢেউ, উন্মুক্ত নীল আকাশ ইংরেজ সাহেবদের খুব পছন্দ হয়। পরে ইংরেজ লাট সাহেবরা আন্দামানে তাদের নৌ-সেনাবহর, ইংরেজ কলোনি, অফিস ঘাট তৈরি করেন।
তৎকালীন সময়ে ভারতসহ বার্মা, পোত্রগাল, মাল্লাকা, পেলাই, সিংগাপুর প্রভৃতি দেশে ইংরেজদের উপনিবেশ ছিল। আন্দামানে ইরেজরা তাদের প্রভুত্ব থাকা দেশগুলো থেকে বিভিন্ন কয়েদিকে সাজা খাটানোর জন্য নিয়ে এসে আন্দামানের রাস্তা-ঘাট ইত্যাদি নির্মাণ করেন।
ভারত ছাড়াও অন্যান্য দেশে, যেসব লোকেরা নিজেদের স্বাধীনতার স্বার্থে ইংরেজদের বিরুদ্ধে গর্জে উঠত তাদের শায়েস্তা করার জন্য সাজা দিত।
কিন্তু হলে কি হবে বিপ্লবীর রক্ত, রক্ত বীজের মতো দেশের তরুণ দিকে স্বাধীনতার স্বার্থে গর্জে ওঠার আহ্বান জানাত। এসব তরুণ বিপ্লবীরা ইংরেজের সাজার তোয়াক্কা না করে ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলে, ইংরেজদের রাজ্য শাসনের ক্ষেত্রে প্রধান বাধার কারণ হয়ে সামনে আসে।
সেই স্বাধীনতাকামী বিপ্লবীদের দেখে যাতে নতুন প্রজন্ম অনুপ্রেরণা না পায় তার জন্য, ইংরেজরা বিপ্লবীদের সঙ্গে সাধারণ মানুষের জনসংযোগ বিচ্ছিন্ন করতে চাইছিল। ১৭৯০ সালে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাইড্রোফিগার ক্যাপ্টেন ব্লেয়ার এবং সার্ভেয়ার জেনারেল ইন্ডিয়ার কর্নেল কোল বুকের পরামর্শে ইন্ডিয়ান ব্রিটিশ গভর্মেন্ট বিপ্লবী বন্দিদের আন্দামানের ছাতিম দ্বীপে এনে রাখার পরামর্শ দেন। এরপর থেকে স্বাধীনতার স্বার্থে তরুণ বিপ্লবীদের দমনের জন্য ইংরেজরা ফাঁসি না দিয়ে দ্বীপান্তর সাজা দেওয়ার প্রথা চালু করেন। ভারতের মূল ভূখণ্ড থেকে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ সমুদ্রের মাঝে থাকায় সাধারণ মানুষ থেকে বিপ্লবী বন্দিদের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।
ছাতিম দ্বীপে কয়েদিদের থাকার জন্য বস্তি নির্মাণ করা হয়; কিন্তু আন্দামানে নোনা, স্যাঁতসেঁতে প্রতিকূল জলবায়ুর কারণে কয়েদিদের মৃত্যু হতে থাকে। ১৮৫৭ সালে সিপাহি বিদ্রোহের নায়ক মঙ্গল পান্ডে কার্তুজে শুয়োরের চর্বি মেশানোকে কেন্দ্র করে সিপাহি বিদ্রোহের সূচনা করে। সেই বিদ্রোহের আগুনের ফুলকি ভারতবর্ষের আকাশে-বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে। মঙ্গল পান্ডের ছড়ানো বিদ্রোহের আগুনে সারা দেশটা জ্বলে ওঠে।
সিপাহি বিদ্রোহের আগুনকে মানুষের মন থেকে নেভানোর জন্য বিপ্লবী বিদ্রোহীদের জনসম্মুখ থেকে দূরে সরিয়ে নেওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে ইংরেজ সরকার। বিদ্রোহীদের বিদ্রোহ দমন করার জন্য ইংরেজদের দ্বারা পোর্টব্লেয়ারে স্থায়ীভাবে একটি জেল বানানোর পরিকল্পনা নেওয়া হয়। ১৮৯০ সালে ছাতিম দ্বীপে, দ্বীপান্তর করা যুদ্ধ বন্দিদের মৃত্যুর কারণ খুঁজে বের করার জন্য ইংরেজ সরকার একটি অনুসন্ধান কমিটি গঠন করে।
অনুসন্ধান কমিটি তাদের রিপোর্টে বন্দিদের মৃত্যুর কারণ হিসাবে প্রতিকূল জল আবহাওয়া, কয়েদিদের ওপর ইংরেজদের অকথনীয় মাত্রারিক্ত অত্যাচারকে দায়ী করেন। পরবর্তীকালে কমিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী অতিরিক্ত সাজার পরিবর্তে কয়েদিদের আলাদা আলাদা কুঠুরিতে রাখার নির্দেশ দেয়। কারণ ইংরেজ সরকার বুঝে গেছিল জেলবন্দিদের আলাদা আলাদা কুঠুরিতে বন্দি করে রাখলে ধীরে, ধীরে তাদের মনোবল ভেঙে পড়বে, বন্দিরা একে অপরের কাছে ভাব-বিনিময়ের সুযোগ পাবেন না।
অনুসন্ধান কমিটির এই নির্দেশ আন্দামান নতুন করে জেল বানানোর রাস্তা করে দেয়। ১৮৯৩ সালে কালাপানি সেলুলার জেলের ভিত্তি প্রস্তর রাখা হয়। ১৮৯৬ সাল থেকে কালাপানি সেলুলার জেলের নির্মাণ কাজ শুরু করা হয় এবং জেল তৈরি শেষ হয় ১৯০৬ সালে। জেল বানানো শেষ হয়ে গেলে
তারপর থেকে ব্রিটিশদের হাতে গ্রেপ্তার হওয়া বিপ্লবীদের আন্দামানের কালাপানি সাজা জেলে (Kalapani jail) পাঠিয়ে দেওয়া হতো। কালাপানি সেলুলার জেল নির্মাণে মোট ১৩ বছর সময় লাগে।
কালাপানি সেলুলার জেল নির্মাণ করা হয় স্বাধীনতা সংগ্রামীদের দ্বারা। ইংরেজরা যেসব বিপ্লবীদের বন্দি করে নিয়ে যেত তাদের ব্যবহার করত জেল নির্মাণের কাজে। বিপ্লবীদের রক্ত জল করেই ইংরেজরা লাল ইট তৈরি করে জেল নির্মাণের কাজে ব্যবহার করে।
কালাপানি সেলুলার জেলের (Kalapani jail) নকশা প্রস্তুত করা হয় তারা মাছের আদলে। তারা মাছের যেমন মধ্য বিন্দু থেকে আলাদা আলাদা ৫টি লেজ/শাখা পঞ্চভুজের মতো চারদিকে ছড়িয়ে থাকে, ঠিক তেমন সেলুলার জেলের নকশায় সেন্ট্রাল পয়েন্ট থেকে আলাদা আলাদা করে ৭ খানা বাহু তৈরি করা হয়। আর এই সেন্ট্রাল পয়েন্টে এক খানা ওয়াচ টাওয়ার বানানো হয়, এই ওয়াচ টাওয়ারের সঙ্গে জেলের ৭ খানা বাহুজুড়ে দেওয়া হয় যাতে ওয়াচ টাওয়ার থেকে জেলের ৭ খানা বাহুতে সমানভাবে নজর জমানো যায়।
সেলুলার জেলের ৭ খানা বাহু লম্বায় এক রকমের ছিল না জেলের বাহুগুলোর লম্বায় ছোট-বড় ছিল। কারণ যেখানে কালাপানি সেলুলার জেল তৈরি হয়েছে সেখানে পাহাড় ছিল। আর এই পাহাড় কেটে সেলুলার জেল নির্মাণ করা হয়েছিল। কালাপানি জেলে মোট ৩টি ফ্লোর ছিল। নিচু তলা মানে গ্রাউন্ড ফ্লোরে ছিল জেলের মধ্যে প্রবেশের প্রধান দরজা।
প্রধান দরজায় প্রবেশ করে ওয়াচ টাওয়ারে সিঁড়ি বেয়ে দ্বিতীয় তলা এবং তৃতীয় তলায় যাওয়া যেত। তৃতীয় তলায় একটি বড় ঘণ্টা বাঁধা ছিল।
জেলের মধ্যে থাকা ঘণ্টার ব্যবহার দিনের বেলা সময় জানানো এবং জেলের মধ্যে বড়লাটের মতো উচ্চ পদস্থ কর্মচারীর আগমন ঘটলে বাজানো হতো।
রাত্রিবেলা এই ঘণ্টার ব্যবহার হতো আপদকালীন পরিস্থিতিতে, জেল থেকে বন্দি পলায়ন করলে প্রহরীদের সতর্ক করার জন্য এই ঘণ্টার ব্যবহার হতো।
কালাপানি সেলুলার জেল (Kalapani jail) বানানোর জন্য ব্যয় হয়েছিল ৮ লাখ ভারতীয় মুদ্রা। ভারতীয় স্বাধীনতাকামী বিপ্লবীদের শায়েস্তা করার জন্য ৬৯৩ কুঠুরি বিশিষ্ট বিশেষ জেল নির্মাণ করা হয়েছিল এবং একসঙ্গে অনেক সেল থাকায় এই জেলের নাম দেওয়া হয় সেলুলার জেল।
সেলুলার জেলের কুঠুরিগুলো এত ছোট করে তৈরি করা হয়েছিল যাতে সেই কুঠুরির মধ্যে ১ জনের বেশি কয়েদিকে রাখার জায়গা না থাকে।
একটি কুঠুরি থেকে আর একটি কুঠুরির মধ্যে কোনো রকম জানালা রাখা হয়নি, যাতে করে একজন কয়েদি আর একজন কয়েদির সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে না পারে।
জেলের কুঠুরির মধ্যে প্রবেশ দরজা ছাড়া কুঠুরির পিছনের দেওয়ালে ৩ ফুট উঁচুতে একটি ছোট জানালা রাখা হয়েছিল তবে জানালা দিয়ে উত্তাল সমুদ্র ছাড়া আর কিছুই দেখা যেত না।
কয়েদিদের জন্য আলাদা করে কুঠুরির মধ্যে টয়লেট করার জন্য কোনো টয়লেটের ব্যবস্থা ছিল না, কয়েদিদের শরীর খারাপ, পেট খারাপের মতো সমস্যা হলে কুঠুরির মধ্যেই টয়লেট হয়ে গেলে ওই একইভাবে কয়েদিকে ময়লা নিয়েই রাত কাটাতে হতো, পরের দিন সকালবেলা ছাড়া ময়লা পরিষ্কার করার আর আলাদা করে কোনো উপায় ছিল না।
ফাঁসি সাজাপ্রাপ্ত আসামিদের জন্য জেলের ভিতর স্পেশাল কন্ডেমড সেলের ব্যবস্থা ছিল। কন্ডেমড সেলে থাকাকালে ফাঁসির আসামিদের সঙ্গে জেলকর্মীরা ভালো ব্যবহার করত, তাদের ভালো খাবার দেওয়া হতো আসামিদের ওপর শারীরিক অত্যাচার করা হতো না।
১৯৩০ সালে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুঠের পর বেশ কয়েকজন স্বাধীনতা সংগ্রামীসহ ভগৎ সিং-এর বন্ধু মহাবীর সিংকে কালাপানি সাজা খাটার জন্য সেলুলার জেল আন্দামানে পাঠানো হয়।
কিন্তু জেলের (Kalapani jail) মধ্যে চলতে থাকা ইংরেজ জেলারের অকথনীয় অত্যাচার দেখে তিনি জেলের মধ্যে অনশন ধর্মঘট শুরু করেন।
জেলার মহাবীর সিং-এর অনশন ভাঙার চেষ্টা করেন কিন্তু তাতে কোনো সুফল হয় না। এভাবে কয়েক দিন কেটে যাওয়ার পর, মহাবীর সিং-এর প্রতি জেলের
বন্দিদের প্রতিপত্তি কমানোর জন্য ইংরেজরা ষড়যন্ত্র করে মহাবীর সিংকে জোড় করে বিষ দুধ পান করিয়ে হত্যা করেন।
এরপর মহাবীর সিং-এর লাশের সঙ্গে বড় একটা পাথর বেঁধে সমুদ্রের জলে ফেলে দিয়ে আসা হয়; কিন্তু এই খবর ইংরেজরা জেলের মধ্যে ধামাচাপা দিয়ে রাখতে পারেননি জেলের অন্য কয়েদিরা মহাবীর সিংকে চক্রান্ত করে হত্যা করার প্রতিবাদে জেলের সব কয়েদি অনশনে নেমে পড়েন। কয়েদিদের অত্যাচার ভাঙার জন্য কয়েদিদের ওপর অকথ্য অত্যাচার চলতে থাকে তবুও তারা তাদের অনশন ভাঙেনি। শেষ পর্যন্ত ৪৫ দিন অনশন চলার পর কয়েদিরা গান্ধীজি ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুরোধে অনশন ভাঙেন।
লন্ডনে আইন নিয়ে পড়াশোনা করার সময় ১৯১১ সালে ভারতের বীর সাভাকর নামের একজন স্বাধীনতাকামী বিপ্লবীকে লন্ডন থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। বীর সাভাকরকে লন্ডন থেকে জলজাহাজে করে ভারতে নিয়ে আসার সময় ফ্রান্সের কাছে জাহাজ এসে পৌঁছালে বীর সাভাকর জলে ঝাঁপ দিয়ে ফ্রান্সে পালিয়ে যায়।
পরে ফ্রান্স পুলিশের হাতে সাভাকর ধরা পড়ে যায় এবং ফ্রান্স পুলিশ সভাকরকে পুনরায় ইংরেজদের হাতে তুলে দেয়। কোর্টে সাভাকরের ৫০ বছরের কারাবাসের সাজা হয়।
সাভাকরকে সেলুলার জেলে ১৯১১-১৯২১ সাল পর্যন্ত ১০ বছর বন্দি করে রাখা হয়েছিল। আপনারা জানলে অবাক হবেন কালাপানি জেলে বীর সাভাকরের ভাই
গণেশ সাভাকরকে বন্দি করে রাখা হয়েছিল; কিন্তু একই জেলে থাকা সত্ত্বেও তারা দুই ভাই-এর একে অপরের সঙ্গে দেখা হয় দুই বছর পরে।
তারা দুজনের কেউ জানত না যে তার দাদা ও ভাই একই জেলে বন্দি আছে। কালাপানি জেলে সাজা খাটার সময় বীর সাভাকরের অনুরোধে জেলের মধ্যে একটা ছোট গ্রন্থাগার খোলা হয়। কালাপানি জেলে ১০ বছর সাজা খাটার পর ১৯২১ সালে বীর সাভাকরকে মহারাষ্ট্রের রত্নগিরি জেলে ৩ বছরের সাজা খাটার জন্য স্থানান্তর করা হয়।
এভাবে ১৯২১ সাল পর্যন্ত সাভাকর রত্নগিরি জেলে সাজা খাটেন এবং বাকি ৫ বছর ইংরেজ সরকার কোনো রকম রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগাযোগ না রাখার শর্তে গৃহবন্দি হয়ে থাকার অবসর দেন। ১৯৮৬ সালে ৮৩ বছর বয়সে বীর সাভাকর মারা যান। সেলুলার জেল (Kalapani jail) বন্দিদের তালিকায় স্বাধীনতা সংগ্রামীদের আত্মত্যাগের তালিকার দীর্ঘ সূচি রয়েছে। তাদের মধ্যে-বটুকেশর দত্ত, বীর সাভাকর, মাওলানা আহমদুল্লা, এস চন্দ্র চ্যাটার্জী প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।
লেখক: ডেপুটি জেলার, ঢাকা কেন্দ্রিয় কারাগার

বাংলাদেশের এক বিশাল অংশ নিয়ে চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চলগুলো গঠিত। পুরো বাংলাদেশের দশ ভাগের এক ভাগ এলাকা এখানে অবস্থিত। চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চলগুলো এখন এক সম্ভাবনার আলো দেখাচ্ছে। চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চলগুলোর মধ্যে রামগড়, খাগড়াছড়ি, কাপ্তাই, বান্দরবান, চন্দ্রঘোনা, লামাসহ বিভিন্ন এলাকা রয়েছে। এসব এলাকাগুলোর অবস্থা এখন আর আগের মতো নেই। গত কয়েক দশক আগেও এসব এলাকার পাহাড়গুলো অনাবাদি অবস্থায় ছিল। ৮০-র দশকের পর থেকে পার্বত্য অঞ্চলগুলোকে আবাদের আওতায় আনা হয়। পাহাড়গুলো আবাদ করে প্রথমে রাবার চাষের উদ্যোগ নেওয়া হয়। রাবার চাষে সফল হওয়ায় অনেকেই রাবার চাষে এগিয়ে আসে। সরকার পাহাড়গুলো লিজের মাধ্যমে বিভিন্ন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে প্রদান করলে চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চলে রাবার একটি শিল্পে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। বর্তমানে চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চলগুলোতে কয়েক লাখ একর জমিতে রাবার চাষ করা হচ্ছে। প্রতি বছর এখানে ছয় হাজার মেট্রিক টন রাবার উৎপন্ন হচ্ছে। চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চলে উৎপাদিত প্রাকৃতিক রাবার দেশের রাবারের চাহিদা অনেকখানি মেটাচ্ছে। বর্তমানে রাবারের উৎপাদন যে হারে বাড়ছে তাতে বিদেশ থেকে রাবার আমদানির প্রয়োজন হবে না। বরং আমাদের দেশে উৎপাদিত রাবার বিদেশে রপ্তানি করা সম্ভব হবে। পার্বত্য অঞ্চলে উৎপাদিত রাবারকে সাদা স্বর্ণ হিসেবে আখ্যায়িত করা হচ্ছে। কারণ এই রাবার আমাদের জাতীয় অর্থনীতিতে বিশেষ অবদান রাখছে। ৮০-র দশকের পর থেকে এ পর্যন্ত চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চলগুলোতে যেভাবে পাহাড়ে আবাদ শুরু হয় তাতে পার্বত্যাঞ্চল অনেক এগিয়ে গেছে। এখানে গড়ে উঠেছে বিশাল বিশাল বাগান। পাহাড়ের ঝোপঝাড় পরিষ্কার করে ফলজ, বনজ বাগান গড়ে তোলা হচ্ছে। রাবার বাগানগুলোতে উন্নতজাতের আমের বাগান গড়ে তোলা হচ্ছে। বর্তমানে চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চলে ছোট-বড় প্রায় পাঁচ হাজার আমের বাগান রয়েছে। আমের মৌসুমে এখানে উন্নতজাতের আম্রপালি উৎপন্ন হচ্ছে। প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা যায় প্রতি বছর এখানে পাঁচ হাজার মেট্রিক টন আম্রপালি আম উৎপন্ন হয়। এই আম আমাদের আমের চাহিদার অনেকাংশ পূরণ করছে। এখানকার আমচাষিরা জানান আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চলগুলো আম্রপালি আম উৎপাদনে স্বয়ং সম্পূর্ণ হয়ে উঠবে। বিদেশি আমের ওপর আর নির্ভর করতে হবে না। এখানে আমের বাগানের সম্প্রসারণের ব্যাপারে উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। চট্টগ্রামের পার্বত্যাঞ্চলে আম চাষের পাশাপাশি কাঁঠাল, লিচু, মালটা, কমলা, সফেদা কাজুবাদাম ড্রাগন ফলসহ আদা, হলুদের চাষ করা হচ্ছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে অন্যান্য ফলনের মধ্যে অত্যন্ত সুস্বাদু ফল কাজুবাদাম চাষের জন্য আমাদের দেশের পার্বত্য অঞ্চলগুলো সম্ভাবনাময় স্থান হিসেবে ইতোমধ্যে চিহ্নিত হয়েছে। বিদেশি ফল কাজুবাদাম চাষের ব্যাপারে আমাদের দেশের কৃষিবিদরা দীর্ঘদিন ধরে চেষ্টা চালিয়ে আসছেন। এ ব্যাপারে তারা সফলও হয়েছেন। চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চলগুলোর মধ্যে রামগড়, খাগড়াছড়ি, রাঙামাটি, কাপ্তাই, বান্দরবান, লামাসহ বিভিন্ন এলাকায় বর্তমানে অনেক বাগানের মালিক সীমিত পর্যায়ে কাজুবাদামের চাষ করে ভালো ফলন পাচ্ছেন। প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা যায় ৮০-র দশকের দিকে সর্বপ্রথম রামগড় এলাকায় কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ কাজুবাদাম চাষের উদ্যোগ নেয়। সেই উদ্যোগ সফল হওয়ার পর অনেকেই কাজুবাদাম চাষে এগিয়ে আসে। কৃষি কর্মকর্তারা জানান চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চলের মাটি, আবহাওয়া এবং পারিপার্শিক অবস্থা কাজুবাদাম চাষের জন্য উপযুক্ত। বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন এলাকায় উৎপাদিত কাজুবাদাম বাজারে পাওয়া যাচ্ছে। পার্বত্যাঞ্চলে উৎপাদিত কাজুবাদামগুলো বিদেশি কাজুবাদামের মতো উন্নত। তবে এখানে উন্নত প্রক্রিয়াজাতকরণ ব্যবস্থা না থাকায় কাজুবাদামগুলো ক্রেতাদের সহজে আকৃষ্ট করছে না। সম্পূর্ণ হাতে বাদামের খোসা ছাড়ানোর কারণে এমনটি হচ্ছে। মেশিনে বাদামের খোসা ছাড়ানোর ব্যবস্থা নেওয়া গেলে এসব কাজুবাদামও বিদেশি কাজুবাদামের সমতুল্য হতো। এ ব্যাপারে কাজুবাদাম চাষিরা উদ্যোগ নিচ্ছেন বলে জানা গেছে। বাংলাদেশে উৎপাদিত কাজুবাদাম ঢাকা, চট্টগ্রামের বিভিন্ন ফলের দোকানে পাওয়া যাচ্ছে। বিদেশি কাজুবাদাম প্রতি কেজি ১১০০-১২০০ টাকায় বিক্রি হয় আর সেখানে আমাদের দেশে উৎপাদিত কাজুবাদাম বিক্রি হয় প্রতি কেজি ৬০০-৭০০ টাকায়। পার্বত্য চট্টগ্রামে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে কাজুবাদাম চাষের ব্যাপারে বিভিন্ন শিল্পোদ্যোক্ততা, এনজিও সংস্থা, কৃষিবিভাগ এবং সরকার বিভিন্ন প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। সাম্প্রতিক প্রাপ্ত তথ্যে জানা যায় কাজুবাদাম চাষে উজ্জ্বল সম্ভাবনা থাকায় এবং দামি ফল হওয়ায় পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন বাগানে ইতোমধ্যে ব্যাপক ভিত্তিতে কাজুবাদাম চাষের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। আমাদের বাংলাদেশের পার্বত্যাঞ্চলগুলোতে অনেক পরিত্যক্ত খালি জায়গা পড়ে আছে। এসব জায়গায় কাজুবাদাম চাষের ব্যাপারে সরকারের তরফ থেকে উদ্যোগ নেওয়া হলে অনেক উদ্যোক্ততা এগিয়ে আসবেন। দামি ফল কাজুবাদাম উৎপাদন করে দেশের প্রয়োজন মিটিয়ে বিদেশে রপ্তানি করার উদ্যোগ নেওয়া যাবে। এতে অনেক কর্মসংস্থানেরও ব্যবস্থা হবে। চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চলে কাজুবাদামের পাশাপাশি দামি মসলা গোলমরিচ চাষের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি এলাকায় গোলমরিচের চাষ শুরুর ব্যাপারে সরকারিভাবে সাহায্য-সহযোগিতা এবং উৎসাহিত করা হচ্ছে। প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা যায় ষাটের দশকের দিকে বাংলাদেশে গোলমরিচের চাষ শুরু হয়। তখন সিলেট অঞ্চলে বসতবাড়িতে কিছু কিছু গোলমরিচের গাছ ছিল। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক জৈন্তিয়া গোলমরিচ জাতটি ১৯৮৭ সালে উদ্ভাবিত হয়। যা বারিগোল মরিচ-১ নামে পরিচিত। এ ছাড়া কারিমুন্ডা, বালনকাট্টা আরকুলপাম মুন্ডা প্রভৃতি জাতের গোলমরিচ রয়েছে। সাধারণত গোলমরিচের চারা ডালের কলম থেকে তৈরি করা হয়। কৃষিবিজ্ঞানীরা জানান বাংলাদেশের মাটি এবং জলবায়ু গোলমরিচের চাষের জন্য উপযোগী। আর্দ্রতাযুক্ত স্থানে গোলমরিচের চাষ ভালো হয়। গোলমরিচের চারা এমন স্থানে রোপণ করতে হবে যেখানে পানি জমতে না পারে। এ জন্য পাহাড়ি এলাকায় গোলমরিচের চাষ ভালো হয়। গাছের কাটিং কলমের চারা রোপণ করতে হয়। বড় বড় গাছ যেমন- আম, কাঁঠাল, বাঁদি গাছের গোড়ায় গোড়ায় গোলমরিচের চারা রোপণ করা হয়। উচ্চমূল্যের মসলা গোলমরিচের চাষের ব্যাপারে আমাদের দেশে যে উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে তাতে যদি সফল হওয়া যায় তবে বিদেশ থেকে আর গোলমরিচ আমদানি করতে হবে না। এ ব্যাপারে সরকারিভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করা হচ্ছে। গোলমরিচ চাষে আমরা যদি সফল হই তবে দেশের গোলমরিচের চাহিদা অনেকটা মিটে যাবে। বিদেশ থেকে আর গোলমরিচ আমদানি করতে হবে না। পার্বত্য এলাকায় গোলমরিচ চাষের উপযুক্ত পরিবেশ রয়েছে। আমরা আশা করি আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে আমাদের উদ্যোগ সফল হবে। দেশের বিভিন্ন স্থানে ব্যাপকভিত্তিতে গোলমরিচ চাষের ব্যাপারে সরকারকে আরও তৎপর হতে হবে। তবেই দেশে গোলমরিচের উদ্যোগ সফল হবে। আমাদের পার্বত্য অঞ্চলে জনপ্রিয় পানীয় কফি চাষের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। কৃষি বিভাগ জানায় খাগড়াছড়ি, বান্দরবান ও রাঙামাটি তিন পার্বত্য জেলাসহ দেশের ২২টি উপজেলায় প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। আমাদের পার্বত্য অঞ্চলে বেশ কয়েক বছর আগে থেকেই ব্যক্তিগত উদ্যোগে কফি এবং কাজুবাদাম চাষের উদ্যোগ নেওয়া হয়। কফি এবং কাজুবাদামের উৎপাদন ভালো হলেও চাষিরা তাদের উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত করে প্রাপ্য মূল্য না পাওয়ায় কৃষকরা কাজুবাদাম এবং কফি চাষে আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। বর্তমানে কফি এবং কাজুবাদামের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় সরকার এ ব্যাপারে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। কৃষকদের কফি এবং কাজুবাদামের চাষের ব্যাপারে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে ঋণের ব্যবস্থা করেছে। চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চলে কফি চাষের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ বিদ্যমান। পাহাড়ের অনাবাদি এক লাখ হেক্টর জমিতে কফি চাষ করতে পারলে ২ লাখ টন কফি উৎপাদন সম্ভব। যার বাজারমূল্য দাঁড়াবে প্রায় ৮ হাজার কোটি টাকা। জানা যায় চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চলে ৫ লাখ হেক্টর পতিত জমি রয়েছে। এর মধ্যে ১ লাখ হেক্টর জমিতে কফির চাষ করতে পারলে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় হবে। সরকারের গৃহীত প্রকল্পের আওতায় তিন পার্বত্য জেলার মধ্যে ১৬ উপজেলায় গবেষণা কার্যক্রম চলছে। কফি এবং কাজুবাদামের সম্ভাব্যতা যাচাই কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। এ ছাড়া খাগড়াছড়িতে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, হিমাগার, গুদাম স্থাপন, বান্দরবানে কার্যালয়, রাঙামাটির রায়খালীতে কৃষি গবেষণা কেন্দ্র বীজ উদ্ভাবন, সংরক্ষণসহ প্রকল্পের কাজ চলছে। সরকার বিশ্ববাজারের চাহিদার কথা বিবেচনা করেই কফি এবং কাজুবাদাম উৎপাদন বৃদ্ধি করতে ২১১ কোটি টাকার প্রকল্প হাতে নিয়েছে। চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চলে যারা ইতোমধ্যেই কফিচাষের উদ্যোগ নিয়েছেন তারা জানান আমরা গত কয়েক বছর ধরে এখানে কফিচাষের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। এতে আমরা সফলও হয়েছি। কারণ এখানকার জলবায়ু এবং মাটি কফিচাষের জন্য খুবই উপযুক্ত। উষ্ণ এবং আর্দ্র আবহাওয়ায় কফি উৎপাদন ভালো হয়। কফি বীজ এবং কফির গুঁড়া (পাউডার) উচ্চমূল্যে হওয়ার কারণে কফিচাষিরা কফিচাষে এগিয়ে আসছেন। ব্যাপকভিত্তিতে কফিচাষ হলে আমাদের দেশে কফির উৎপাদন বেড়ে যাবে এবং দেশের কফির চাহিদা মেটানো সম্ভব হবে। বিদেশ থেকে উচ্চমূল্য দিয়ে আর কফি আমদানি করতে হবে না। কফিচাষিরা দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশে রপ্তানির আশা করছেন। কফিচাষে এতদিন কৃষক বিভিন্ন ধরনের সমস্যায় ভুগছিলেন। মূলধন সমস্যা, প্রশিক্ষণের অভাব, ভালো চারার অভাবসহ বিভিন্ন সমস্যা। বর্তমানে সরকার কফিচাষিদের এসব সমস্যা সমাধান করে অধিক পরিমাণে জমিতে কফিচাষের জন্য উৎসাহিত করছেন। সরকার এবং দেশের কফিচাষিরা আশা করছেন দেশে কফিচাষের ব্যাপারে বর্তমানে যে ব্যাপক উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে তা অবশ্যই সুফল আসবে। আশা করা যায় সবকিছু অনুকূলে থাকলে আগামী কয়েক বছরের মধ্যে বাংলাদেশ কফি উৎপাদনে উল্লেখ করার মতো দেশ হিসেবে চিহ্নিত হবে। আমরা সেই সুদিনের অপেক্ষায় থাকলাম। শুধু তাই নয়- পাহাড়ে উৎপাদিত সবজি আমাদের সবজির চাহিদা অনেকখানি মেটাচ্ছে। পার্বত্য অঞ্চলগুলোর লেকগুলোতে মাছের চাষ করে বাণিজ্যিকভাবে লাভবান হচ্ছেন উদ্যোক্তারা। লেকে উৎপাদিত মাছগুলো মাছের চাহিদা অনেকখানি মেটাচ্ছে। পাহাড়ি অঞ্চলে অনেকেই আবার গরু, ছাগল, ভেড়া, হাঁস-মুরগি বাণিজ্যিকভাবে লালন-পালন করে অনেকেই লাভবান হচ্ছেন। মোট কথা চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চলগুলো এখন অর্থনৈতিক দিক দিয়ে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যাচ্ছে। পরিত্যক্ত পাহাড়গুলোতে এখন সোনা ফলছে। আমাদের পার্বত্য চট্টগ্রামে বিশাল এলাকা রয়েছে। সরকার যদি এসব এলাকাগুলোকে উন্নয়নের উদ্যোগ নেয় লিজের মাধ্যমে জমি বিতরণের মাধ্যমে পাহাড়ে আবাদ করা হয় তবে আগামী দশ বছরের মধ্যে এই অঞ্চল দেশের সেরা অর্থনৈতিক জোন হিসেবে গড়ে উঠবে। বর্তমানে যেসব এলাকা এখনো পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে আছে। সেগুলো আবাদের উদ্যোগ নিয়ে উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা, বিদ্যুতের ব্যবস্থা, পানির ব্যবস্থা করতে পারলে অনেক সুফল পাওয়া যাবে। চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চলগুলোর ব্যাপারে সরকার পৃথকভাবে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করে এখানকার কৃষকদের উন্নত প্রশিক্ষণ, স্বল্পসুদে অথবা বিনা সুদে ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা, জায়গা লিজের ব্যাপারে সহজীকরণসহ বিভিন্ন উদ্যোগ নিতে হবে। চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চলগুলোর উন্নয়নের মাধ্যমে আমাদের অর্থনীতির সমৃদ্ধির পথ সুগম হবে। এ জন্য এখনই উদ্যোগ নিতে হবে। পাহাড়ে যেভাবে আবাদ হচ্ছে তা অব্যাহত রাখা জরুরি। এখানে নতুন অর্থনৈতিক জোন গড়ে উঠলে অনেক লোকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হবে।
লেখক: অর্থনৈতিক বিষয়ক প্রাবন্ধিক