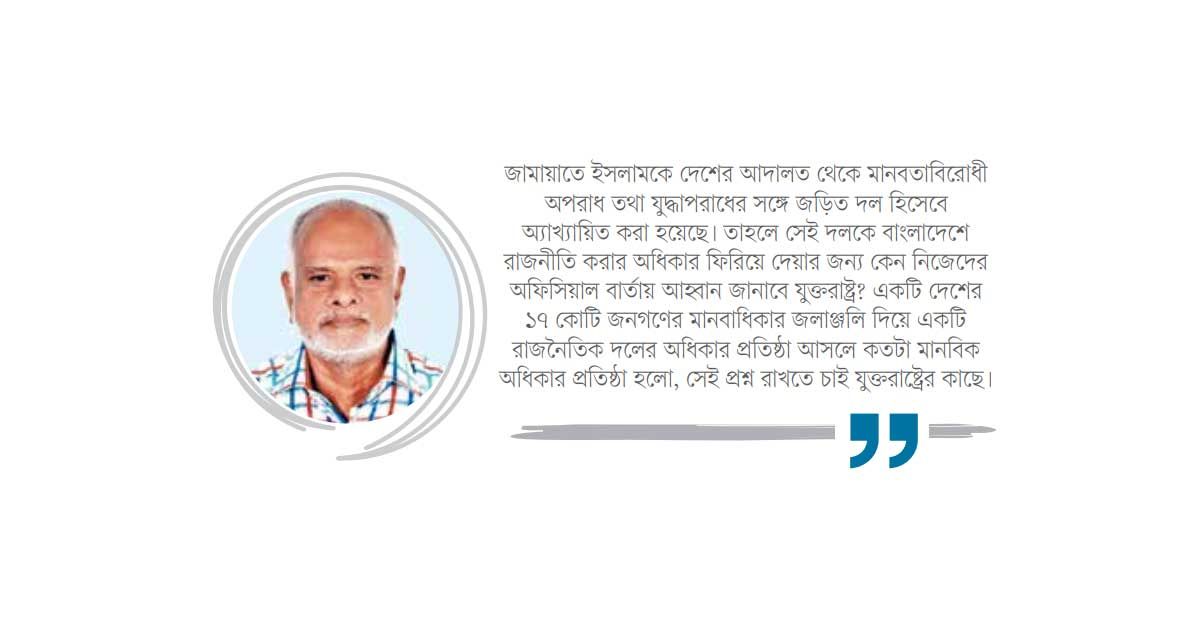
বিএনপির জ্বালাও-পোড়াও আন্দোলনে সরাসরি বা পরোক্ষভাবে বারবার উঠে আসছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাম। চতুর্থ ধাপে দেশজুড়ে জ্বালাও-পোড়াও আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে বিএনপি-জামায়াত। এ ক্ষেত্রে জামায়াত বেশ সাবধানে এগিয়ে গেলেও সরাসরি বাসে অগ্নিসংযোগ, রাস্তায় টায়ার পুড়িয়ে অবরোধ, গাড়ি ভাঙচুরসহ বেশ কিছু কাজে সরাসরি যুক্ত থাকতে দেখা গেছে বিএনপির বিভিন্ন ইউনিটের নেতা-কর্মীদের। বেশকিছু স্থানে জামায়াত শিবিরের সদস্যকেও গ্রেপ্তার করা হয় অগ্নিসংযোগকালে; কিন্তু কেন নির্বাচন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণে এত অনাগ্রহী বিএনপি?
২০১৩-১৫ সালে বিএনপি-জামায়াত দেশজুড়ে যেই ধ্বংসযজ্ঞ চালায় তা প্রত্যাখ্যান করে বাংলাদেশের মানুষ। জীবন্ত মানুষকে আগুনে পুড়িয়ে মারা। ঘুমিয়ে থাকা মানুষসহ গাড়ি ও দোকানে অগ্নিসংযোগ, অ্যাম্বুলেন্সে হামলাসহ এমন কোনো অপরাধ নেই, যা সে সময় করেননি বিএনপি-জামায়াতের নেতা-কর্মীরা। এর ফল হিসেবে বিএনপি বিশ্বের বুকে তৃতীয় শ্রেণির সন্ত্রাসী গোষ্ঠী বা দল হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। আর জামায়াত ২০০১-০৬ সালে তাদের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের জন্য আগে থেকেই বিশ্বের বুকে জঙ্গি ও জঙ্গিসংশ্লিষ্ট সংগঠন হিসেবে পরিচিত। জঙ্গি ও সন্ত্রাসের এই মেলবন্ধনের কারণে দেশের মানুষ ২০০৮ সালে প্রত্যাখ্যান করে বিএনপি-জামায়াতকে। রাজনৈতিক বিবেচনায় ২০১৪ সালে পরিপূর্ণভাবে ব্যর্থ হয় বিএনপি-জামায়াত তাদের জ্বালাও-পোড়াও নীতির কারণে।
এই যখন অবস্থা তখন নিজেদের ভাবমূর্তি পুনরুদ্ধারে ২০১৮ সালে শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচনে অংশ নেয় বিএনপি; কিন্তু দলটির কেন্দ্রীয় মনোনয়ন বাণিজ্যের কারণে বড় ব্যবধানে এ নির্বাচনেও হেরে যায় দলটি। জ্বালাও-পোড়াও ও সাধারণ মানুষের সরাসরি ক্ষতি করা থেকে বিরত থাকায় ২০২২ সালে কিছুটা জনসমর্থন লাভ করে দলটি। তাদের শান্তিপূর্ণ কর্মসূচিগুলো প্রধান প্রতিপক্ষ আওয়ামী লীগের কাছেও প্রশংসা কুড়ায়। আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে বারবার জানানো হয়, শান্তিপূর্ণ প্রক্রিয়ায় নির্বাচনে বিএনপিকে অংশগ্রহণের জন্য। বিএনপিকে আলোচনার জন্য আহ্বান জানায় নির্বাচন কমিশনও; কিন্তু হঠাৎ করেই নির্বাচনের আগ মুহূর্তে আবারও পুরোনো সন্ত্রাসী রূপে ফেরত যায় বিএনপি; কিন্তু কেন। এর উত্তর মিলবে ২০১৮ সাল থেকে যুক্তরাষ্ট্র তথা যুক্তরাষ্ট্রের বাংলাদেশ মিশন অফিস এবং বিএনপি-জামায়াতের বেশকিছু কর্মকাণ্ডকে আমলে নিলে। ২০১৮ সালের কিছু আগ থেকেই বাংলাদেশের মানবাধিকার ইস্যু নিয়ে কথা বলে শুরু করেন বিএনপির শাসনামলে অ্যাটর্নি জেনারেল পদে থাকা আদিলুর রহমান। এ সময় যুক্তরাষ্ট্র ও সংশ্লিষ্ট বেশকিছু দাতাসংস্থা থেকে অর্থ লাভ করেন তিনি। এরপর বিদেশে থাকা বেশ কিছু সংস্থা ও ওয়েব পোর্টালের সহযোগে একযোগে আওয়াজ তোলা হয় বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে। ঠিক এ সময়ই যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের এলিট ফোর্স র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়নের (র্যাব) ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। এরপর বিএনপির পলাতক বিভিন্ন নেতা-কর্মীর পরিবারকে নিয়ে শুরু হয় ‘জোরপূর্বক গুম’ নিয়ে আলোচনা। মূলত জ্বালাও-পোড়াও এবং হত্যাসহ বেশ কিছু মামলায় পালিয়ে থাকা বিএনপি-জামায়াত নেতা-কর্মীদের মুক্তি দিতেই মানবাধিকার নিয়ে বাংলাদেশে কাজ শুরু করে যুক্তরাষ্ট্রসংশ্লিষ্ট বেশ কিছু সংস্থা। এ সময় বিষয়গুলো নিয়ে বেশ সোচ্চার আওয়াজ তোলে নেত্র নিউজ নামে একটি ওয়েব পোর্টাল, যাকে অর্থায়ন করে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান এনইডি। বিষয়গুলো নিয়ে আরও কথা বলা শুরু করে ‘নাগরিক টিভি’ নামক পোর্টাল, ইলিয়াস, কনক সারওয়ার থেকে শুরু করে জামায়াত-বিএনপির প্রোপাগাণ্ডা মেশিনারিগুলো।
সম্মিলিত এ উদ্যোগের মূল লক্ষ্য ছিল- আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে বিব্রত করা এবং তাদের কিছুটা নিশ্চলতায় রাখার মাধ্যমে নিজেদের সন্ত্রাসী ও জঙ্গি কর্মকাণ্ডগুলোকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া।
বিএনপির বর্তমান এই আচরণের জন্য সরাসরি যে ব্যক্তিকে দায়ী করা হয়, তিনি হলেন ঢাকার মার্কিন মিশনের বর্তমান অ্যাম্বাসেডর পিটার ডি হাসকে। মার্চ ২০২২-এ পিটার হাস বাংলাদেশ মিশনে যোগ দেয়ার পর থেকে আরও দৃঢ় চিত্তে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়া শুরু করে বিএনপি। বিশেষত বিভিন্ন জেলা ও বিভাগ পর্যায়ে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বাংলাদেশে যোগদানের পর থেকে এ দেশের বিভিন্ন মন্ত্রী-এমপি এবং বর্তমান ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীদের চাইতে বেশি বার বিএনপির সিনিয়র থেকে শুরু করে তৃণমূলের বিভিন্ন নেতা-কর্মীর সঙ্গে দেখা করেন পিটার হাস। শুধু তাই নয়, বিএনপির হারিয়ে যাওয়া নেতা-কর্মীদের পরিবারের সঙ্গে সরাসরি গিয়েও দেখা করেন পিটার হাস; কিন্তু তিনি বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবী হত্যা দিবসে শ্রদ্ধা জানাননি গত বছর। সে সঙ্গে বিএনপির শাসনামলে গুম ও খুনের শিকার পরিবারগুলোর সঙ্গে আলোচনা করতে ও বসতেও দেখা যায়নি তাকে। উল্টো নিজেদের আর্জি নিয়ে পিটার হাসের কাছে চাইবার দাবি জানালে বিষয়টিকে ‘নিরাপত্তা হুমকি’ হিসেবে অভিহিত করেন তিনি।
যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র বাংলাদেশ ইস্যুতে যেকোনো আলোচনা হলেই সবার আগে যেই উক্তিটি করে তা হলো- ‘আমরা সুনির্দিষ্ট কোনো দলকে সমর্থন করি না।’ প্রশ্ন থেকে যায়, পিটার হাস যা করছেন, সে বিষয়ে কি কিছুই জানে না মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর? বিএনপির সিনিয়র নেতাদের সঙ্গে সকালের নাশতা থেকে শুরু করে রাতের ডিনার পর্যন্ত করেছেন পিটার হাস; কিন্তু আওয়ামী লীগের সঙ্গে তাকে এত বৈঠক করতে দেখা যায় না। এমনকি বিএনপি ছাড়া বাংলাদেশের আর কোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গেও এত বৈঠক করতে দেখা যায়নি পিটার হাসকে। এর কারণ কী? তাহলে কি এটা বলা যায় যে, পিটার ডি হাস এক তরফাভাবে বিএনপিকে সমর্থন জুগিয়ে যাচ্ছে। আর তার সমর্থনের কারণেই সংলাপ বা আলোচনায় না বসে জ্বালাও-পোড়াও, হরতাল-অবরোধ চালিয়ে যাচ্ছে বিএনপি ও তার সংশ্লিষ্ট দলগুলো।
সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনে বাধা দিলে সরকারি বা বিরোধী রাজনৈতিক দলের সদস্য ও সরকারি কর্মকর্তারা মার্কিন ভিসানীতির আওতায় পড়বেন। সম্প্রতি চতুর্থ ধাপে বিএনপির অবরোধ ও জ্বালাও-পোড়াও শুরুর বেশ আগেই মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র বেদান্ত প্যাটেল বিগত ১০-১২ দিন তাদের কার্যক্রমের সমালোচনা করে জানান, এটি কোনোভাবেই সমর্থনযোগ্য নয়। সে সঙ্গে তিনি সবাইকে শান্তিপূর্ণ অবস্থান ও আলোচনার মাধ্যমে এগিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান। অথচ বাংলাদেশে অবস্থান করে সরাসরি জ্বালাও পোড়াও কার্যক্রম চোখের সামনে দেখেও এ বিষয়ে কোনো মন্তব্য করেননি মার্কিন অ্যাম্বাসেডর পিটার ডি হাস। এমনকি যেই বিএনপির সঙ্গে নিয়মিত তার বৈঠক, তাদের এই জ্বালাও-পোড়াও বন্ধের সরাসরি কোনো আহ্বান জানাতেও দেখা যায়নি তাকে। এ দ্বিচারিতামূলক আচরণ কেন পিটার হাসের?
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যুদ্ধাপরাধের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের শাস্তি পেতে দেখা যায় যুদ্ধের আরও ৪০-৫০ বছর পরও। জার্মানে এখনো নাৎসি সমর্থকদের রাজনীতি করা বা ক্ষমতায় আসা নিয়ে কোনো আলোচনা কী রয়েছে? যদি না থাকে, তবে বাংলাদেশে জামায়াত ইসলামের মতো একটি যুদ্ধাপরাধী দলকে কেন মানবাধিকার ও রাজনৈতিক অধিকারের নামে পক্ষপাত আচরণ করবে যুক্তরাষ্ট্র। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের বিপক্ষে সরাসরি অবস্থান ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের। এ সময় জামায়াত ইসলাম বুদ্ধিজীবী হত্যাসহ দেশের অভ্যন্তরে ৩০ লাখ মানুষকে হত্যার সঙ্গে সরাসরি জড়িত ছিল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সঙ্গে। যুদ্ধাপরাধের দায়ে শাস্তি হয়েছে এবং এখনো বিচার কার্যক্রম চলছে বেশ কিছু জামায়াত নেতার। জামায়াতে ইসলামকে দেশের আদালত থেকে মানবতাবিরোধী অপরাধ তথা যুদ্ধাপরাধের সঙ্গে জড়িত দল হিসেবে অ্যাখ্যায়িত করা হয়েছে। তাহলে সেই দলকে বাংলাদেশে রাজনীতি করার অধিকার ফিরিয়ে দেয়ার জন্য কেন নিজেদের অফিসিয়াল বার্তায় আহ্বান জানাবে যুক্তরাষ্ট্র? একটি দেশের ১৭ কোটি জনগণের মানবাধিকার জলাঞ্জলি দিয়ে একটি রাজনৈতিক দলের অধিকার প্রতিষ্ঠা আসলে কতটা মানবিক অধিকার প্রতিষ্ঠা হলো, সেই প্রশ্ন রাখতে চাই যুক্তরাষ্ট্রের কাছে।
লেখক: সিনিয়র সাংবাদিক ও কলামিস্ট

লাল কার্ডের ব্যবহার সাধারণত ফুটবল খেলাতেই হয়ে থাকে। কোনো খেলোয়াড় ফুটবল খেলার আইন ভঙ্গ করলে বা মারাত্মক ফাউল করলে রেফারি তাকে লাল কার্ড দেখিয়ে বহিস্কার করতে পারেন। অবশ্য এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট খেলোয়াড়কে দুবার হলুদ কার্ড দেখিয়ে সতর্ক করার বিধান রয়েছে। হলুদ কার্ড দেখানোর পরও যদি ওই খেলোয়াড় নিবৃত্ত না হন বা রেফারির আদেশ না মানেন, ওই খেলোয়াড়কে লাল কার্ড দেখিয়ে মাঠের বাইরে পাঠিয়ে দেওয়ার এখতিয়ার রেফারির রয়েছে। খেলার মাঠের সে লাল কার্ড এবার উঠে এসেছে আমাদের রাজনৈতিক মাঠে।
আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রচারণা এখন তুঙ্গে। অংশগ্রহণকারী দলগুলো এখন তুমুল ব্যস্ত। ভোটারদের পক্ষে টানার জন্য নানা কথার ফুলঝুরির পাশাপাশি প্রতিদ্বন্দ্বী দলের দোষত্রুটি জনসমক্ষে তুলে ধরছে তারা। আর তা করতে গিয়ে তারা কখনো অসহিষ্ণুতার বহিঃপ্রকাশ ঘটাচ্ছে, কখনো শিষ্টাচারের সীমানা অতিক্রম করে যাচ্ছে। বলা নিস্প্রয়োজন, এবারের জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে ভিন্ন এক প্রেক্ষাপটে। প্রথমত. দীর্ঘ সতের বছর পরে বাংলাদেশের জনগণ নিঃশঙ্কচিত্তে, নির্ভয়ে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে যাচ্ছে। দ্বিতীয়ত. এ নির্বাচনে দেশের অন্যতম রাজনৈতিক শক্তি আওয়ামী লীগ অনুপস্থিত। ২০২৪ সালের জুলাই আন্দোলনে ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর গঠিত অন্তর্বর্তীকালীন সরকার কর্তৃক কার্যক্রম নিষিদ্ধ হওয়ায় তারা এখন নিষ্ক্রিয়। উপরন্তু তাদের শীর্ষনেতা শেখ হাসিনা রয়েছেন দেশের বাইরে; যিনি ইতোমধ্যে একটি আদালতে গণহত্যা মামলায় মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছেন। তাছাড়া দলটির প্রধম সারির নেতাদের বেশিরভাগ গণঅভ্যুত্থানের পরপরই কেউ দেশ ত্যাগ করেছেন কেউ গ্রেপ্তার হয়ে কারাগারে আছেন। ফলে দলটি এখন অস্তিত্ব সংকটে রয়েছে। এর আগেও ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নিহত হওয়ার পর আওয়ামী লীগ একই সংকটে পড়েছিল। তবে সে প্রেক্ষাপট ছিল ভিন্ন। কারণ দলটি তখন নিষিদ্ধ হয় নি। যার ফলে পঁচাত্তর পরবর্তী সব নির্বাচনেই দলটি অংশ নিতে পেরেছিল।
আওয়ামী লীগবিহীন নির্বাচন যে খুব একটা জমজমাট হচ্ছে না, তা ইতোমধ্যেই প্রতিভাত হয়ে উঠেছে। ১৯৭৫ পরবর্তী বাংলাদেশের নির্বাচন মানেই ছিল চির প্রতিদ্বন্দ্বী দুই দল বিএনপি ও আওয়ামী লীগের ভোটের লড়াই। যদিও ২০১৪ এবং ২০২৪ সালের নির্বাচনে বিএনপি নির্বাচনী মাঠে অনুপস্থিত ছিল। আর ২০১৮ সালের নির্বাচনী মাঠে নামলেও আওয়ামী লীগ ও সরকারের দ্বৈত চাপ এবং রেফারি নির্বাচন কমিশনের পক্ষপাতিত্বের কারণে শেষ পর্যন্ত লড়াইয়ে থাকতে পারে নি।
পত্র-পত্রিকার খবরে বলা হচ্ছে, আওয়ামী লীগ নির্বাচনী মাঠে না থাকায় উত্তাপ অনেকটাই নেই। কেউ কেউ এ নির্বাচনকে পানসে বলেও অভিহিত করেছেন। তবে আওয়ামী লীগ না থাকলেও নির্বাচনী মাঠে যারা রয়েছেন, তাদের কার্যকলাপ ও কথাবার্তায় উত্তাপ সৃষ্টির যথেষ্ট উপাদান রয়েছে। এবারের ভোটের লড়াইয়ে প্রধান দুই পক্ষ বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামী। এই দুই দল বর্তমানে লিপ্ত রয়েছে বাগ্যুদ্ধে। তারা পরস্পরকে আক্রমণ-প্রতিআক্রমণের দ্বারা পরিবেশ অনেকটাই উত্তপ্ত করে তুলেছে। শুধু বাগ্যুদ্ধ নয়, ইতোমধ্যে তারা দু’চার জায়গায় রক্তক্ষয়ী যুদ্ধেও অবতীর্ণ হয়েছে। শেরপুর জেলার ঝিনাইগাতিতে তেমনি এক সংঘর্ষে একজন নিহত ও কয়েকজন আহত হয়েছে।
রাজনৈতিক দলের জনপ্রিয়তা বা গ্রহণযোগ্যতার ব্যারোমিটার হলো নির্বাচন। একটি সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচনে জনগণ যদি অবাধে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারে, তাহলে প্রমাণিত হয় কোন দল কতটা জনপ্রিয় বা গ্রহণযোগ্য। বলার অপেক্ষা রাখেনা, বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে অনুষ্ঠিত নির্বাচনগুলোতে সেটা যাচাই করা সম্ভব ছিল না। কেননা, তখন জনগণ ভোটকেন্দ্রে গিয়ে ভোটই দিতে পারেনি। বাংলাদেশের জনগণ এবার নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগের অধিকার ফিরে পাবে এটাই প্রত্যাশিত। জনগণের সে ভোট পক্ষে টানার জন্য রাজনৈতিক দলের নেতা ও প্রার্থীরা সভা-সমাবেশে বক্তব্য রাখবেন, মিছিল করবেন, এসব স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। তবে সমালোচনার নামে প্রতিপক্ষের প্রতি বিষোদগার কিংবা শিষ্টাচার বহির্ভূত আক্রমণাত্মক বক্তব্য-মন্তব্য কখনোই কাম্য নয়। অবশ্য এটা অস্বীকার করার উপায় নেই, আমাদের দেশে জনগণ যেটা প্রত্যাশা করে, রাজনৈতিক দল ও সেগুলোর নেতারা বেশিরভাগ সময় তার বিপরীত কাজটি করেন।
অনেকেরই ধারণা ছিল, এবারের নির্বাচনে যেহেতু এক সময়ের মিত্রদের মধ্যে মূল প্রতিদ্বন্দ্বিতা হচ্ছে, তাই নির্বাচনী মাঠে তেমন কোনো অবাঞ্ছিত ঘটনা ঘটবে না। প্রতিদ্বন্দ্বী দলগুলোর নেতা ও প্রার্থীরা নির্বাচনী প্রচারণার সময় শিষ্টাচারের বিষয়ে সতর্ক থাকবেন। কিন্তু নির্বাচনী প্রচারণা শুরুর পর থেকে যেসব ঘটনা ঘটছে তাতে জনমনে একরাশ হতাশা ভর করেছে। জুলাই গণঅভ্যুত্থানের পর ‘নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্তের’ কথা শোনা গিয়েছিল। অনেকেই আশান্বিত হয়েছিলেন, পুরানো দোষারোপের ঐতিহ্য থেকে বেরিয়ে এসে আমাদের রাজনীতি সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যের পথে হাঁটতে শুরু করবে। বলা হয়েছিল, পুরানো বস্তাপচা রাজনীতির বদলে দেশবাসী নতুন রাজনীতি উপহার পাবে। কিন্তু হা হতোষ্মি! যারা নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্তের কথা শুনিয়েছিলেন, তারাও হাঁটছেন পুরনো পথে। বরং সমালোচনার নামে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর বিরুদ্ধে অশোভনীয় উক্তির নতুন নজির স্থাপন করেছেন। ঢাকা-৮ আসনে বিএনপির প্রার্থী দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য ও সিনিয়র রাজনীতিবিদ মির্জা আব্বাসকে এনসিপির প্রার্থী নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী যে ভাষায় আক্রমণ করেছেন তাকে শিষ্টাচার, শালীনতা এবং সভ্যতা-ভব্যতার চূড়ান্ত লঙ্ঘন বললে অত্যুক্তি হবে না। যদিও প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী সম্বন্ধে কোনো ধরনের কটুক্তি, বিষোদগার ও ব্যক্তিগত আক্রমণ নির্বাচন কমিশন প্রণীত আচরণবিধিতে নিষিদ্ধ। তবে তার তোয়াক্কা কেউ করছে বলে মনে হয় না।
এ মুহূর্তে প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী দুই দল বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামীর বাগ্যুদ্ধে দেশবাসী যুগপৎ বিস্মিত ও আতঙ্কিত। পরস্পরের প্রতি তাদের বাক্য-তীর নিক্ষেপের ধরন দেখে মনে হচ্ছেনা, তারা একসময় ‘জান পেহচান দোস্ত’ ছিল। জামায়াত নেতারা যখন বিএনপিকে ক্ষমতায় থাকতে দুর্নীতিতে চারবার বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হওয়ার খোঁটা দেন, তখন তারা বোধকরি ভুলে যান, তাদের দল সেই সরকারের শরিক ছিল এবং তাদের দুই শীর্ষনেতা সে সরকারের মস্ত্রী ছিলেন। ফলে চার দলীয় জোট সরকার যদি দুর্নীতিবাজ হয়ে থাকে, তাহলে সে আভিযোগ থেকে জামায়াতে ইসলামী কি বাদ যেতে পারে? ঠিক তেমনি বিএনপির পক্ষ থেকে যখন মুক্তিযুদ্ধে বিরোধিতার জন্য জামায়াতে ইসলামীকে তুলোধুনো করা হয়, তখন তারাও বোধকরি ভুলে যান, সব জেনেশুনেই তারা ওই বিষপান করেছিলেন। ২০০০ সালে জোটসঙ্গী করার সময় যদি জামায়াতের একাত্তরের ভূমিকা দোষের মনে না হয়ে থাকে, তাহলে এখন কেন তারা অস্পৃশ্য হবে? অন্যদিকে বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান বাংলাদেশের রাজনীতিতে ‘গুপ্ত’ বলে নতুন একটি শব্দের উদ্ভাবন করেছেন। এই শব্দের দ্বারা আওয়ামী লীগের শাসনামলে জামায়াতের কতিপয় নেতাকর্মীর ক্ষমতাসীনদের ছত্রছায়ায় থেকে সুযোগ বুঝে স্বমূর্তিতে আবির্ভূত হওয়াকেই কটাক্ষ করে থাকবেন। এর বিপরীতে জামায়াতের আমির ডাক্তার শফিকুর রহমান তারেক রহমানের লন্ডনে অবস্থান করাকে ‘সতের বছর গুপ্ত ছিলেন’ বলে কটাক্ষ করেছেন।
এদিকে গত ২ ফেব্রুয়ারি কক্সবাজারের নির্বাচনী জনসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে জামায়াতে ইসলামীর আমির ডাক্তার শফিকুর রহমান ‘বিএনপিকে জনগণ এবার লাল কার্ড দেখাবে’ বলে মন্তব্য করেছেন। বিপরীতে বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান ৪ ফেব্রুয়ারি বরিশালে নির্বাচনী জনসভায় জামায়াতে ইসলামীকে কটাক্ষ করে বলেছেন, ‘বর্তমানে বাংলাদেশে একটি ‘গুপ্ত সংগঠন’ নতুন জালিম হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে’। বর্তমান বাংলাদেশের রাজনীতির দুই শীর্ষনেতার এহেন বাক্য-শর নিক্ষেপকে রাজনীতি-সচেতন মানুষ অশনি সংকেত হিসেবেই দেখছেন। তারা বলছেন, জনগণ বিএনপিকে লাল কার্ড দেখাবে, নাকি লাল গোলাপের ফুলের তোড়ায় নতুন করে বরণ করে নেবে তা দেখা যাবে ১২ ফেব্রুয়ারি। জামায়াত আমিরের কাছ থেকে সেটা শুনতে বা জানতে তারা আগ্রহী নয়। অন্যদিকে প্রকাশ্যে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনাকারী একটি রাজনৈতিক দলকে তথাকথিত ‘গুপ্ত সংগঠন’ বলে অভিহিত করা যে একেবারেই সমীচীন হচ্ছেনা, বিএনপি চেয়ারম্যানের তা অনুধাবন করা দরকার।
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের ভোট গ্রহণের আর মাত্র কয়েকদিন বাকি। নির্বাচনী প্রচারণার শেষ পর্যায়ে এসে একসময়ের ‘হরিহর আত্মা’ বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামী যে ধরনের অরুচিকর ভাষায় পরস্পরকে আক্রমণ করছে তাতে দেশবাসী হতাশ ও উদ্বিগ্ন। তারা রাজনৈতিক দলগুলোর কাছ থেকে অপরের কুৎসা বা অরাজনৈতিক সমালোচনা শুনতে আগ্রহী নয়। তারা শুনতে চায় জাতির প্রতি দলগুলোর প্রতিশ্রুতির কথা। তারা চায় দলগুলো তাদের নির্বাচনী ইশতেহারে যেসব প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করছে, তা প্রতিপালনের নিশ্চয়তা। রাজনৈতিক দলের নেতাদের স্মরণে রাখা দরকার, জনগণ মৌখিক নয়, আন্তরিক গণতন্ত্রীদের ক্ষমতায় দেখতে চায়। আর সে গণতন্ত্রের প্রধান পূর্বশর্তই হলো পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ। তার পরিবর্তে তারা যদি পালাগানের স্টাইলে শালীন-অশালীন ভাষায় একে অপরকে আক্রমণ করেন, তাহলে দেশবাসীর হতাশার সাগরে নিমজ্জিত হওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকে না।
ফুটবল খেলায় কোনো খেলোয়াড়কে লাল কার্ড প্রদর্শনের একমাত্র ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি রেফারি। আর নির্বাচনে রাজনৈতিক দল বা প্রার্থীদের লাল কার্ড দেখানোর ক্ষমতা জনগণ তথা ভোটারদের হাতে। সুতরাং তারাই সিদ্ধান্ত নিক ১২ ফেব্রুয়ারি কোন দলকে লাল কার্ড দেখাবে। খামোখা বাহুল্য উক্তি করে নির্বাচনী পরিবেশ উত্তপ্ত করা নিশ্চয়ই বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক নয়।
লেখক: সাংবাদিক ও কলামিস্ট।

আসন্ন ১৩তম জাতীয় নির্বাচন যত ঘনিয়ে আসছে, ততই স্পষ্ট হচ্ছে-এটি কেবল ব্যালট, পোস্টার আর জনসভার নির্বাচন নয়; এটি একই সঙ্গে একটি অ্যালগরিদমিক নির্বাচন কিংবা ডিজিটাইলাইজড নির্বাচন। যেখানে প্রার্থী নয়, অনেক সময় কনটেন্টই কথা বলে; বক্তব্য নয়, বরং ভিডিও ‘প্রমাণ’ হিসেবে হাজির হয়; আর যুক্তি নয়, আবেগই শেষ কথা বলে। এই নতুন নির্বাচনী ময়দানে সবচেয়ে আলোচিত, আবার সবচেয়ে ভীতিকর খেলোয়াড় হচ্ছে- কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই। আর এআইয়ের এই আগমনেই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠছে দেশবাসী।
এক সময় নির্বাচনের অপপ্রচার বলতে বোঝাত ভুয়া লিফলেট, বিকৃত উক্তি কিংবা গুজব। সেগুলোর একটি সীমা ছিল-সবই ছিল মানুষের কণ্ঠ, মানুষের হাত, মানুষের সময়। এখন সেই সীমা ভেঙে গেছে। এআই কোনো ঘুম চেনে না, ক্লান্ত হয় না, নৈতিক দ্বিধায় পড়ে না। একটি ভিডিও বানাতে এখন আর শুটিং লাগে না, বক্তব্য বানাতে বক্তাও লাগে না। ফলে নির্বাচনের আগ মুহূর্তে কেউ যদি হঠাৎ দেখে, কোনো প্রার্থী রাষ্ট্রবিরোধী কথা বলছেন, সংবেদনশীল ইস্যুতে উসকানিমূলক মন্তব্য করছেন, কিংবা এমন কিছু করছেন যা জনমনে ক্ষোভ তৈরি করে-তখন প্রশ্ন ওঠে না
‘তিনি সত্যিই বলেছেন কি না’, প্রশ্ন ওঠে ‘এটা কতটা ভাইরাল হলো?’
এই জায়গাতেই এআইয়ের অপব্যবহার সবচেয়ে ভয়ংকর হয়ে ওঠে। ডীপফেইক ভিডিও ও অডিও এমন এক বাস্তবতা তৈরি করে, যেখানে চোখ-কান আর বিশ্বাসের নির্ভরযোগ্যতা হারায়। আগে মানুষ বলত, ‘নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করি না।’ এখন নিজের চোখেই দেখে মানুষ বিভ্রান্ত হয়। ফলে নির্বাচনের মতো সংবেদনশীল সময়ে এই প্রযুক্তি হয়ে ওঠে নিখুঁত রাজনৈতিক অস্ত্র-যার আঘাত নীরব এবং দ্রুত, কিন্তু গভীর।
বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এই ঝুঁকি আরও তীব্র। কারণ আমাদের সমাজে রাজনৈতিক মেরুকরণ নতুন কিছু নয়। সমাজও ডিজিটালি বিভক্ত। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আমরা আগে থেকেই দুই মেরুতে বিভক্ত। এআই এই বিভাজন তৈরি করে না; বরং সেটিকে আরও ধারালো করে। যে ভোটার আগে থেকেই কাউকে সন্দেহ করে, ডীপফেইক তাকে সেই সন্দেহের
‘দৃশ্যমান প্রমাণ’ দেয়। যে ভোটার অন্ধ সমর্থক, এআই তাকে বানিয়ে দেয় কৃত্রিম বীরত্বের ভিডিও। ফলে নির্বাচন হয়ে ওঠে যুক্তির নয়, বরং কাস্টমাইজড বাস্তবতার প্রতিযোগিতা।
এখানে ব্যঙ্গটা হলো-আমরা এখন এমন এক যুগে বাস করছি, যেখানে কেউ কথা না বললেও তাকে দিয়ে অনেক কিছু ‘বলানো’ যায়, আর কিছু না করলেও তাকে দিয়ে অনেক কিছু ‘করানো’ যায়। তাও আবার উচ্চ রেজোলিউশনে, পরিষ্কার অডিওতে, সাবটাইটেলসহ। এই কৃত্রিম সত্যের সামনে সাধারণ ভোটার কীভাবে টিকবে? যে ভোটার দিনে দশটা পোস্ট স্ক্রল করে, তার পক্ষে যাচাই করা কি আদৌ সম্ভব?
সরকার সম্প্রতি জাতীয় এআই নীতির খসড়া প্রকাশ করেছে, যেখানে দায়িত্বশীল ব্যবহার, স্বচ্ছতা ও ঝুঁকিপূর্ণ এআই নিয়ন্ত্রণের কথা বলা হয়েছে। নীতির ভাষা আশাব্যঞ্জক, কিন্তু নির্বাচনের বাস্তবতা অনেক কঠিন। নীতিপত্র আর নিউজফিডের মাঝে যে সময়ের ফারাক, সেটিই সবচেয়ে বড় সমস্যা। একটি ভুয়া ভিডিও শনাক্ত করতে যেখানে ঘণ্টা কিংবা দিন লাগে, সেখানে সেটি ছড়াতে লাগে মিনিট। পরে সংশোধনী এলেও ততক্ষণে আবেগ তার কাজ করে ফেলে। আইনের প্রশ্নেও বিষয়টি জটিল। কোনটি মতপ্রকাশ, আর কোনটি পরিকল্পিত এআই-ভিত্তিক অপপ্রচার-এই সীমারেখা সব সময় স্পষ্ট নয়। বেশি কড়াকড়ি করলে মতপ্রকাশের স্বাধীনতার প্রশ্ন আসে, আবার ঢিলেঢালা হলে অপপ্রচারকারীরা আরও সাহসী হয়। তার ওপর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমগুলোর বেশিরভাগই আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান-তাদের ওপর জাতীয় নির্বাচনী শাসন কার্যকর করা সহজ নয়।
তবে এআইয়ের এই অপব্যবহার শুধু প্রযুক্তিগত সমস্যা নয়; এটি মূলত একটি ডিজিটাল লিটারেসির সংকট। আমাদের সমাজে ইন্টারনেট আছে, কিন্তু ইন্টারনেট বোঝার সক্ষমতা সবার নেই! ভিডিও দেখলেই সত্য ধরে নেওয়া, আবেগ উসকে দেওয়া কনটেন্ট শেয়ার করা-এই অভ্যাসই এআই-ভিত্তিক অপপ্রচারের সবচেয়ে বড় শক্তি। ব্যঙ্গ করে বলা যায়, এআই যতটা বুদ্ধিমান, আমরা অনেক সময় ততটাই বেপরোয়া।
নির্বাচনে এআইয়ের অপব্যবহার সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করে গণতন্ত্রের আস্থায়। কারণ গণতন্ত্র টিকে থাকে তথ্যভিত্তিক সিদ্ধান্তের ওপর। যখন তথ্যই কৃত্রিম হয়ে যায়, তখন ভোট বাস্তব হলেও সিদ্ধান্ত হয়ে ওঠে কৃত্রিম। এটাই দেশবাসীর উদ্বেগের মূল জায়গা। মানুষ ভয় পাচ্ছে-ভোটটা আমি দেব, কিন্তু সিদ্ধান্তটা কি সত্যিই আমার হবে?
এখানে রাজনৈতিক দলগুলোর দায়িত্বও এড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ নেই। যদি দলগুলো নিজেরাই এআইকে প্রতিপক্ষ ঘায়েল করার হাতিয়ার বানায়, তাহলে শেষ পর্যন্ত কেউই নিরাপদ থাকবে না। আজ যে দল অপপ্রচারের শিকার, কাল সে-ই অপপ্রচারক হতে পারে। এই দুষ্টচক্র ভাঙতে না পারলে নির্বাচন ব্যবস্থা ক্রমেই বিশ্বাসযোগ্যতা হারাবে।
সবশেষে কথা আসে নাগরিকের ভূমিকায়। প্রযুক্তি যতই উন্নত হোক, গণতন্ত্রের শেষ রক্ষাকবচ নাগরিকের বিবেক। আমাদের শিখতে হবে সন্দেহ করতে-ভিডিও দেখেও, অডিও শুনেও। ‘এটা কেন এখন এলো’
‘উৎসটা কী?’, ‘অন্য নির্ভরযোগ্য মাধ্যমে আছে কি?’
-এই প্রশ্নগুলোই হতে পারে সবচেয়ে কার্যকর প্রতিরোধ। ঠাট্টা করে বললে, এখন সবচেয়ে বিপ্লবী কাজ হলো-সব কিছু সব সময় বিশ্বাস না করা!
সামনের ১৩তম জাতীয় নির্বাচন তাই শুধু ক্ষমতার লড়াই নয়; এটি সত্য আর কৃত্রিমতার মধ্যকার এক নীরব যুদ্ধ। এই যুদ্ধে এআই যদি অনিয়ন্ত্রিত থাকে, তাহলে ক্ষতিগ্রস্ত হবে শুধু একটি পক্ষ নয়, পুরো গণতান্ত্রিক কাঠামো। নীতিমালা, প্রযুক্তি, আইন-সবই দরকার। কিন্তু তার চেয়েও বেশি দরকার সচেতন নাগরিক। নইলে একদিন হয়তো আমরা এমন এক নির্বাচনে পৌঁছাব, যেখানে ব্যালট বাক্স বাস্তব থাকবে, কিন্তু সেই বাক্সে দেওয়া সিদ্ধান্তের ভিত্তি হবে পুরোপুরি কৃত্রিম।
প্রফেসর ড. ইকবাল আহমেদ, কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

আসন্ন ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ এর নির্বাচনে ইসলামী দলগুলোর অবস্থান বেশ পাকাপোক্ত করেছে।তারা সরকার গঠনের ইংগিতও দিচ্ছে।
ভোটের বাজার হলো: সর্বমোট ২৯৮ টি সিটের জন্য ১৯৮১ জন প্রার্থী। ৫১টি দল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে , স্বতন্ত্র আছে ২৪৯ জন। বিএনপির কেনডিডেট ২৮৮, ইসলামিক আন্দোলন বাংলাদেশ ২৫৩ , বাংলাদেশ জামায়াত ইসলাম ২২৪ জন, ১২ টি ছোট ছোট দলও আছে।
২০২৪ এর হিংস্রতাকে পুঁজি করে বিশৃঙ্খলার জন্য আওয়ামী লীগ ও তার সহযোগী দল এবারের নির্বাচনে নেই।
যুবক দের ভোট এবার ৩৩ শতাংশ আর মহিলাদের ভোট প্রায় ৫০ শতাংশ। যে দল এই অন্দর মহলের অন্তর জয় করতে পারবে তারাই নিশ্চিত সফলতা পাবে।
বিএনপি ১৯৯০ আর ২০০০ সনে ক্ষমতায় ছিল । তাদের আদি ও অকৃত্রিম শক্র আওয়ামী লীগ এবার ভোটে নেই। বিএনপির বেগম খালেদা জিয়া অল্প কিছুদিন আগে প্রয়াত আর শেখ হাসিনা দিল্লীতে মোদির সাহেদ অতিথি। দেশের দুই হেভিওয়েট না থাকাতে জামায়েত তার অবস্থান বেশ গুছিয়ে নিয়েছে। নির্বাচনে জুলাই বিপ্লবের মহারথীদের আসন নিশ্চিত হতেই পারত তবে তাদের অর্বাচীন কান্ড যেমন দ্রুত বড়লোক হবার প্রবনতা জনমনে বিরাগের সৃষ্টি করেছে।
তারেক জিয়া। নির্বাচনের অন্যতম ফ্যাক্টর। মৃত পথযাত্রী মা বেগম খালেদা জিয়ার শয্যাপাশে আসতে তার গড়িমসি দৃষ্টি কটু পরিবেশের সৃষ্টি করেছে।১৭ বছর পর দেশে আসার সাথে সাথে লক্ষ লোকের সমাগম তাকে এতই অভিভূত করে যে তিনি অনেকটা খেই হারিয়েছেন। দেশের মাটিতে পা দিতে না দিতেই এনআইডি কার্ড তৈরি, এয়ারপোর্ট থেকে জনগণের সাথে আর্মি গাড়ি র বহর তাকে বেরিকেড দিয়ে নিঁযে আসা এসব তার মধ্যে সৃষ্টি করে ‘আই হ্যাভে প্লান’। তিনি মার্টিন লুথার কিং এর মতন আওয়াজ তুলতে চাইলেন। সেই প্ল্যানটা হলো খাল কাটবেন আর গাছ লাগাবেন। এত এত খাল কাটা হবে আর গাছ লাগানো হবে যে দেশে মানুষ বসবাসের যায়গায়ই থাকবে না।
বিএনপির এবার লড়তে হবে জামায়াতের অভিজ্ঞ নেতৃবৃন্দের সাথে। ঐ যে শুরুর এয়ারপোর্টের ধামাকা তারেক জিঁযাকে এখনও ‘ বি ইন হিজ স্যু ‘ এর মধ্যে ঢুকাতে পারে নাই। আকাশ কুসুম অলীক ভাবনারেই তিনি বাস্তব মনে করছেন। ফ্যামিলি কার্ড ঘরে ঘরে পৌঁছে দিবেন। এটা কি ! খায় নাকি মাথায দেয়। ছিলেন ইংল্যান্ডে, ছিলেন বাংলাদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন এবং রাজনীতিতে অপরিপক্ক , বক্তা হিসাবেও ক্যারিশমেটিক নন এবং এ সব বুঝে শুনেই জামাত আর চোখে দেখছেন এবং ‘আই হ্যাভ্ প্লান ‘এই বাতচিত জামাত ই না সফল করে ফেলে, তাদের বয়স্ক ও বিজ্ঞ নেতারা সরকার গঠনের গন্ধ পাচ্ছেন। ভুল করে সুযোগ হাতছাড়া করবেন না।
নির্বাচনের জন্য সরকার বৈধ অস্ত্র জমা করে নিল। এখন দেশ ভরা অবৈধ অস্ত্রের হাট বাজার। বৈধ অস্ত্র দিয়ে পাখি শিকার পর্যন্ত করা যায় না। তবুও ঘরে থাকলে কিছুটা স্বস্তি, চারিদিকের উচ্ছৃঙ্খল পরিবেশের সামনে একটা শক্তি।
তারপরও সুষ্ঠ নির্বাচন চাই, চাই এলোমেলো বাংলাদেশ কে এক গুছানো বাংলাদেশ। আলহামদুলিল্লাহ।
— কলামিস্ট

অফিস আদালতে কর্মকর্তা বা সিনিয়র কর্মীদের স্যার বা ম্যাডাম বলে সম্বোধন না করলে, চলমান রীতিগত দিক দিয়ে তেমন ভালো চোখে দেখা হয় না। অনেক ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট অধস্তনের চাকুরী নিয়ে টানাটানি শুরু হয়; এমনকি অপরাধ হিসেবে গন্য করে নেতিবাচক স্থানে বদলি পর্যন্ত করা হয়ে থাকে, যার ভূড়ি ভূড়ি উদহারণ আছে। এ প্রেক্ষাপটে উল্লেখ্য যে, ১৭শ শতকে ব্রিটিশরা ভারতীয় উপমহাদেশে উপনিবেশ স্থাপন করলে স্যার বা ম্যাডাম শব্দের প্রচলন শুরু হয়। মূলত ব্রিটিশ প্রশাসনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট শ্বেতাঙ্গ কর্মকর্তাদের প্রতি স্থানীয় জনগণের আনুগত্য প্রকাশের সারথী ধরে স্যার বা ম্যাডাম সম্বোধন চালু হয়। আর এই সূত্র ধরে সাধারণ মানুষ ব্রিটিশ কর্মকর্তাদের স্যার, ব্রিটিশ নারীদের ম্যাডাম বলে ডাকতো। আর এই সম্বোধন ছিল কর্তৃত্ব ও আনুগত্যের প্রকাশ বৈ কিছু নয়। এদিকে ইংরেজরা উচ্চবর্ণের বাঙালিদের (বিশেষ করে সনাতনী ধর্মালম্বী) ‘বাবু’ বলে সম্বোধন করতো। তথ্য মতে জানা যায় যে, আঠার শতকের মাঝামাঝি সুদূরপ্রসারী বুদ্ধির আড়ালে ব্রিটিশরা এই মর্মে চিন্তা করে যে, এই উপনিবেশে এমন একটি শ্রেণি গড়ে তুলতে হবে, যারা ‘বর্ণে ভারতীয়; কিন্তু রুচিতে-বুদ্ধিতে এবং ভাবনায় হবে ব্রিটিশ’। আর এই নীতির সরণি ধরে ব্রিটিশ ভারতে গড়ে ওঠে ইংরেজি মাধ্যমে শিক্ষা এবং একই সঙ্গে সম্বোধনের ক্ষেত্রে ব্রিটিশ সামাজিক রীতি, যার একটি ছিল কর্তৃপক্ষকে ‘স্যার’ বলে ডাকা। সত্যিকারার্থে স্যার-ম্যাডাম সম্বোধনের উৎপত্তি নিয়ে যদি গভীরে যাই; তাহলে প্রতীয়মান হয় যে, অক্সফোর্ড ও ক্যামব্রিজ অভিধানের তথ্য অনুযায়ী ১২৯৭ সাল থেকে ইংরেজি ভাষায় ‘স্যার’ শব্দটি ব্যবহার শুরু হয়। আর সেই সময়ে ব্রিটিশ রাজতন্ত্রে বিশেষ ভূমিকা পালনের জন্য ‘নাইট’ উপাধি খেতাবী ব্যক্তিদের নামের আগে ‘স্যার’ শব্দটি যোগ করার প্রচলন ছিল বলে জানা যায়। অবশ্য এই শব্দটি ফরাসি শব্দ ঝরৎব থেকে এসেছে; যার অর্থ হলো প্রভু বা কর্তৃপক্ষ। মজার ব্যাপার হলো, তখন ইংল্যান্ডে ঝরৎ শব্দ দিয়ে এই মর্মে বোঝানো হতো যে আমি চাকরই থেকে গেলাম।
এদিকে বাংলার মধ্যযুগ বা মুঘল আমলের সংস্কৃতিতে রাজা বাদশাহদের জাঁহাপনা, হুজুর, ইত্যাদি এমন নামে সম্বোধন করা হতো। আর কর্মকর্তাদের ‘সাহেব’ বলে সম্বোধন করার প্রচলন ছিল। এ প্রেক্ষাপটে উল্লেখ্য যে, ইরানিরা ভারতবর্ষে আসার পর ‘সাহিব’ শব্দটির প্রচলন ঘটে। পরে তা অপভ্রংশ হয়ে ‘সাহেব’ এ রূপ নেয়। অবশ্য ‘সাহেব’ শব্দটি আরবি ‘সাহাবী’ শব্দ থেকে এসেছে; যার অর্থ হলো সঙ্গী, সাথী, সহচর কিংবা বন্ধু। আর তাই তখন পদবির সাথে সাহেব যোগ করে ডাকা হতো। এক্ষেত্রে উদহারণ হিসেবে খান সাহেব, সচিব সাহেব, শেখ, সাহেব ইত্যাদি। আর এটি মুসলমানদের ক্ষেত্রে অধিক প্রযোজ্য ছিল। এদিকে ব্রিটিশ ও শ্বেতাঙ্গ ইউরোপীয় নারীদের ‘মেমসাহেব’ বলে সম্বোধন করা হতো। তাছাড়া মুসলিম বাঙালি বিবাহিত নারীদের ‘বেগম সাহেব’ বলা হতো। আর অফিস আদালতে হেড ক্লার্ককে বড় বাবু বলে ডাকা হতো, যা এখনো অনেক স্থানে পরিলক্ষিত হয়ে থাকে।
সত্যি কথা বলতে কি, বাংলাদেশে স্যার বা ম্যাডাম সম্বোধন সংক্রান্ত কোনো সরকারি আইন বা কোন নীতিমালা নেই। এটি মূলত একটি প্রথাগত রীতি বা সামাজিক কালচার; যা শিক্ষা, প্রশাসন এবং করপোরেট সমাজে রিলে রেসের মতো চলে এসেছে। এ ব্যাপারে উল্লেখ্য যে, সাতচল্লিশে ব্রিটিশ থেকে স্বাধীন হওয়ার পর বাংলাদেশে (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান) শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে এই সংস্কৃতি বহাল থাকে। আর স্বাধীনতার পরেও শিক্ষা ও প্রশাসনে স্যার ও ম্যাডাম সম্বোধন অপরিবর্তিত থেকে যায়। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশে কিছুটা সংযোজনের মাধ্যমে নিম্ন আদালতের বিচারক মন্ডলীকে উদ্দেশ্য করে আইনজীবী বা বিচারপ্রার্থীরা ‘স্যার’ বা ‘ইওর অনার’ বলে থাকেন এবং উচ্চ আদালতের বিচারকমন্ডলীকে ‘মাই লর্ড’, ‘মি লর্ড’ বলে সম্বোধন করা হয়। অথচ বাংলাদেশের আইনজীবীদের পেশাগত শৃঙ্খলা ও আচরণ নিয়ন্ত্রণকারী আইনের কোথাও এমন কোনো বিধান নেই। এদিকে ১৯৯০ সালের শেষ দিকে বাংলাদেশের তৎকালীন সংস্থাপন মন্ত্রণালয় থেকে কর্মকর্তাদের স্যার/ম্যাডাম নামে সম্বোধনের রীতি বাতিল করে একটি প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়। এ প্রজ্ঞাপনে সরকারি অফিস বা প্রতিষ্ঠানে সম্বোধনের জন্য ‘স্যার’-এর পরিবর্তে ‘জনাব’ এবং ‘সরকারি অফিসার বা কর্মকর্তাদের নামে প্রেরিত পত্রাদির শুরুতে পুরুষের ক্ষেত্রে ‘মহোদয়’ ও মহিলাদের ক্ষেত্রে ‘মহোদয়া’ লেখার সুপারিশ করা হয়। এতদ্ব্যতীত ২০১০ সালের জাতীয় শিক্ষানীতি বা তার পরবর্তী হালনাগাদ সংস্করণে শিক্ষকের প্রতি সম্মান বজায় রাখা নিয়ে এতদসংক্রান্ত কিছু উল্লেখ থাকলেও স্যার বা ম্যাডাম ডাকার এমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই।
প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে, অর্ন্তরবর্তীকালীন সরকার ক্ষমতায় আসার পর ১০/০৭/২০২৫ইং তারিখে উপদেষ্টা পরিষদের ৩৩তম বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য সিনিয়র নারী কর্মকর্তাদের স্যার বলার নিয়ম বাতিল করা হয়। এদিকে আশ্চর্যর বিষয় হলো যে, আমি যখন নব্বইয়ের দশকে ইংল্যান্ডে পড়াশোনা করি। তখন কোথায় কেউ স্যার বা ম্যাডাম বলে সম্বোধন করেছেন, এমন কথা শুনিনি বা দেখিনি। আসলে স্যার বা ম্যাডাম সম্বোধনের পেছনে আইনগত কোন বাধ্যবাধকতা নেই। অথচ এটি ঔপনিবেশিক আমলে চাপিয়ে দেয়া রীতিনীতি বৈ কিছু নয়। অবশ্য এটি অফিস আদালতে সামাজিক কালচার হিসেবে আমাদের রক্তের সঙ্গে এমনভাবে মিশে গিয়েছে যে, যতই আইন-কানুন করা হোক না কেন, তা সহজে মুছে যাবে না।
লেখক : গবেষক, অথর্নীতিবিদ এবং লেখক হিসেবে মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সম্মাননা ও পদকপ্রাপ্ত।

ভেনিজুয়েলা দখল করার পর এবার গ্রীন ল্যান্ড এর বিস্তীর্ণ অঞ্চল দখলে নেবার ইচ্ছা ট্রাম্পের। এতে বিশ্বের সামরিক ভারসাম্য নাড়া খাচ্ছে। চীনের দরজায় দাঁড়ানো ফরমোজা দখল নিতে চাচ্ছে চীন, সামরিক মহড়া ও শুরু করেছে।
এই উত্তপ্ত পরিস্থিতিতে ফুটবল বিশ্বকাপেও বয়কটের হুমকি আসছে।
গ্রীনল্যান্ড ইস্যুতে ডোনাল্ড ট্রাম্প কে কোনঠাসা করতে একাধিক দেশ একাট্টা হয়েছে। জার্মানিত প্রকাশ্যে মুখ খুলেছে, ইংল্যান্ড, স্কটল্যান্ডসহ আরও একাধিক দেশের ফেডারেশন এই নিয়ে আলোচনা করেছে।
মেক্সিকো, কানাডার সাথে আমেরিকাও এবার বিশ্বকাপের আয়োযক দেশ। আগামী ১২ জুন মেগা আসরে বল গড়াবে। তবে ভেনিজুয়েলা দখলের পর গ্রীনল্যান্ড নিয়ে ট্রাম্পের গরম বাতচিত পরিস্থিতি বেসামাল করে ফেলেছে। যে সব দেশ ট্রাম্পের বিরোধিতা করবে তাদের উপর অতিরিক্ত শুল্ক আরোপের হুঁশিয়ারি দিয়েছে ট্রাম্প।গ্রীনল্যান্ড হলো ডেনমার্কের স্বশাসিত অঞ্চল।
সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর মধ্যে নরওয়ে, নেদারল্যান্ড, জার্মানি, ফ্রান্স, ইংল্যান্ড এবং স্কটল্যান্ড ইতোমধ্যেই বিশ্বকাপে জায়গা পাকা করেছে। এ ছাড়াও যোগ্যতা অর্জনের প্লে-অফে খেলবে ডেনমার্ক, সুইডেন এবং আয়ারল্যান্ড।
ডেনমার্ক আবার ন্যাটোর সদস্য। ন্যাটোর একটি দেশের উপর হামলা হলে সমগ্র ন্যাটো দেশ গুলির উপর হামলা বলে বিবেচিত হয়।ডেনমার্ক বলেছে আমেরিকা গ্রীনল্যান্ড নিয়ে বাড়াবাড়ি করলে তারাও ছেড়ে কথা বলবে না। এসব হুমকি ধামকি বিশ্বকাপ ফুটবলে আচর ফেলবেই।
বিশ্বকাপের টিকিটের দাম আমেরিকা আকাশছোঁয়া করেছে। ৭৫ টি দেশের অভিবাসীদের ভিসা স্থগিত করেছে। তবে বিশ্বকাপের জন্যই পর্যটকও স্বল্প মেয়াদি ভিসার ছাড় দেবার ঘোষণা দিলেও শন্কাত থেকেই যায়। রাজনৈতিক কারণে ব্রাজিলের সমর্থক দের নাকি ছাড় দেয়া হবে না। কয় কি ?ট্রাম্পের রাজনৈতিক আগ্রাসনের আঁচ বিশ্ব কাপ ফুটবলে প্রতি ইঞ্চিতে ইঞ্চিতে দৃশ্যমান। এই পরিস্থিতিতে কোন দেশ যদি বিশ্বকাপ বয়কট করে তবে ফিফার মুখ পুরবে।
আমেরিকা এক নুতন অস্ত্র ব্যহবার করে ছিল ভেনিজুয়েলার নিয়ন্ত্রন নেবার সময়, ভুক্তভোগী ক কথায় , সামরিক অভিযান চলাকালীন একটি জোরালো আওয়াজ শোনা গিয়েছিল। সেটা এতটাই জোরালো যে মনে হচ্ছিল মাথা ফেটে যাবে। তারপরই নাক মুখ দিয়ে রক্ত ঝরতে শুরু করে। কারো কারো রক্ত বমি শুরু হয়। ফলে অনেকের মতন প্রেসিডেন্ট মাদুরোর নিরাপত্তায় থাকা সৈন্য ধীরে ধীরে মাটিতে লুটির পরে।
ট্রাম্পের কিছু কিছু কাজ প্রবল আগ্রাসী, তিনি রাশিয়া আর চীনের নিরুত্তাপ বৈদেশিক নীতির পুর ফায়দা তুলছেন।
মজা করেই বলছিল, ধরুন আমেরিকা ফুটবল মাঠে হারছে তখন এই ধরনের ‘এয়ার কন্ট্রোল’ অস্ত্র যদি মাঠে প্রয়োগ করে? কারণ ট্রাম্পকে বিশ্বাস করা যায় না।
এ সব কখনই হবেনা তবে এখন ‘keep sports clean of politics’
এ সব আর ধোপে টিকে না । দেখেন না টি-২০ বিশ্বকাপে বাংলাদেশ খেলবে না। বাংলাদেশের যায়গায় স্কটল্যান্ড খেলবে কারন বাংলাদেশের পর তাদেরই র্যাংক সবার উপরে ছিল।
শুরুটা হয়ে ছিল কেকেআর এর মুস্তাফিজের খেলা নিয়ে। কেকেআর এর মালিক শাহরুখ খান। ভারতে এই মুহূর্তে চলছে মুসলিম বিদ্বেষ।আর ইস্যু হলো শাহরুখ, মুস্তাফিজ দুইজনই মুসলমান। মুসলমান কেন ক্রীড়াঙ্গন ডোমিনাইট করবে। প্রায় দশকোটি টাকায় মুস্তাফিজুর চুক্তিবদ্ধ হয়ে ছিল যেটি এবারের সর্বোচ্চ পেমেন্ট। মুসলমান নিয়ে এত রাগ অথচ শেখ হাসিনাকে মহা আনন্দে দিল্লি তে রেখেছে।
দাবা খেলায় ‘ ওয়েটিং মুভ’ বলে। মোদি সেই ওয়েটিং মুভ নিয়ে বসে আছে . ঘুঁটি হলো শেখ হাসিনা। সর্বত্রই খেলা। তাই না ?
-কলামিস্ট

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ও সামষ্টিক অর্থনীতির স্থিতিশীলতায় প্রবাসী বাংলাদেশিদের অবদান অপরিসীম। প্রতিবছর বিপুল পরিমাণ রেমিট্যান্স দেশের অর্থনীতিকে সচল রাখলেও প্রবাসীরা এখনো পর্যাপ্ত আইনি সুরক্ষা, সামাজিক নিরাপত্তা ও রাজনৈতিক অধিকারের বাইরে রয়ে গেছে।
সম্পত্তি দখল, বিনিয়োগ প্রতারণা, পারিবারিক অনিরাপত্তা, বিদেশে শ্রমিক নির্যাতন এবং ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়া—এই সমস্যাগুলো প্রবাসীদের জীবনকে ক্রমশ অনিশ্চিত করে তুলছে। এই গবেষণাধর্মী প্রবন্ধে প্রবাসীদের বর্তমান আইনি বাস্তবতা, সংকট, আন্তর্জাতিক মানদণ্ড এবং বাংলাদেশের জন্য একটি প্রস্তাবিত প্রবাসীবান্ধব আইন কাঠামো বিশ্লেষণ করা হয়েছে।
মোদ্দা কথা (Keywords): প্রবাসী বাংলাদেশিদের, রেমিট্যান্স সুরক্ষা, সম্পত্তি সুরক্ষা আইন, বিনিয়োগ আইন, রাজনৈতিক অধিকার ও মানবাধিকার নিশ্চিত করতে হবে।
১. ভূমিকা (Introduction):
বাংলাদেশের উন্নয়নযাত্রার নেপথ্যে সবচেয়ে নীরব অথচ শক্তিশালী অবদানকারীদের একটি অংশ হলো প্রবাসী বাংলাদেশিরা। গ্রাম থেকে শহর, জাতীয় বাজেট থেকে বৈদেশিক বাণিজ্য—সব ক্ষেত্রেই তাদের শ্রমলব্ধ অর্থ প্রবাহিত হচ্ছে। কিন্তু এই জনগোষ্ঠীর জন্য রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা ও সুরক্ষা কাঠামো এখনো পরিপূর্ণ ও কার্যকর নয়। রাষ্ট্র একদিকে প্রবাসীদের কাছ থেকে অর্থনৈতিক অবদান গ্রহণ করলেও অন্যদিকে তাদের জীবন, সম্পদ ও সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পর্যাপ্ত আইনি কাঠামো গড়ে তুলতে পারেনি। এই দ্বৈতনীতি একটি গুরুতর সাংবিধানিক ও নৈতিক সংকট তৈরি করেছে।
২. প্রবাসী ও রাষ্ট্র: অর্থনৈতিক নির্ভরতার বাস্তবতা:
মনে রাখতে হবে বাংলাদেশের রেমিট্যান্স প্রবাহ জাতীয় আয়ের অন্যতম প্রধান স্তম্ভ।
এই রেমিট্যান্স—
১। বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভ স্থিতিশীল রাখে।
২। ব্যাংকিং খাতে তারল্য সৃষ্টি করে।
৩। গ্রামীণ অর্থনীতিকে সচল রাখে।
৪। নির্মাণ, পরিবহন ও ভোগ্যপণ্য শিল্পে কর্মসংস্থান বাড়ায়।
৫। দারিদ্র্য হ্রাসে প্রত্যক্ষ ও পরক্ষ ভূমিকা রাখে।
তবুও প্রবাসীরা অনেক সময় দেশে নিজেদের ‘অদৃশ্য নাগরিক’ হিসেবে অনুভব করেন—যাদের অর্থ গ্রহণ করা হয়, কিন্তু অধিকার সুরক্ষায় আন্তরিকতা দেখা যায় না।
৩. প্রবাসীদের প্রধান আইনি সংকট:
৩.১ সম্পত্তি দখল ও ভূমি জালিয়াতি।
প্রবাসীদের জমি দখল বাংলাদেশের অন্যতম বড় সামাজিক ও আইনি সংকট। কারণ, প্রবাসী প্রবাসে অবস্থানের সুযোগে:—
১। জাল দলিল তৈরি করা হয়।
২। ভুয়া পাওয়ার অব অ্যাটর্নি করা হয়।
৩। প্রশাসনিক দুর্নীতি করা হয়।
৪। স্থানীয় প্রভাবশালীদের দখলদারিত্ব ভেড়ে যায়।
এসবের মাধ্যমে প্রবাসীদের সম্পত্তি হাতছাড়া হয়ে যায়। দেশে ফিরে মামলা করলেও বিচার পেতে দীর্ঘসূত্রতা ও হয়রানির শিকার হতে হয়।
৩.২ বিনিয়োগ প্রতারণা:
ফ্ল্যাট, ব্যবসা, শিল্পকারখানা ও শেয়ারবাজারে প্রবাসীরা ব্যাপক বিনিয়োগ করেন। কিন্তু দালাল, অসাধু অংশীদার ও দুর্নীতিগ্রস্ত চক্রের কারণে বহু প্রবাসী সর্বস্বান্ত হয়েছেন। বিনিয়োগ বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য আলাদা দ্রুতগতির আদালত বা ট্রাইব্যুনাল নেই—যা একটি বড় আইনি শূন্যতা তৈরী করে।
৩.৩ প্রবাসী পরিবার অনিরাপত্তা:
প্রবাসীর স্ত্রী, সন্তান ও বাবা-মা অনেক ক্ষেত্রে সামাজিক নির্যাতন, আর্থিক আত্মসাৎ ও সম্পত্তি বিরোধের শিকার হন। রাষ্ট্রীয় সুরক্ষা ব্যবস্থা দুর্বল হওয়ায় অপরাধীরা অধিকাংশ সময় শাস্তির আওতার বাইরে থেকে যায়।
৩.৪ বিদেশে শ্রমিক নির্যাতন ও মানবাধিকার লঙ্ঘন:
মধ্যপ্রাচ্য ও বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশি শ্রমিকরা নিম্ন মজুরি, অমানবিক কর্মপরিবেশ, শারীরিক নির্যাতন ও পাসপোর্ট জব্দের শিকার হন। দূতাবাসের সীমিত আইনি সক্ষমতার কারণে তাদের অনেকেই ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত হতে হয়।
৩.৫ রাজনৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত
প্রবাসীরা বাংলাদেশের নাগরিক হয়েও ভোটাধিকার ও জাতীয় রাজনীতিতে কার্যকর প্রতিনিধিত্ব থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকে। জাতীয় সংসদে তাদের জন্য কোনো নির্দিষ্ট আসন নেই, নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে তাদের কণ্ঠ দুর্বল করে রাখা হয়।
৪. বিদ্যমান আইনি কাঠামোর সীমাবদ্ধতা:
বর্তমানে প্রবাসীদের বিষয়গুলো বিভিন্ন সাধারণ আইনের মধ্যে খণ্ডিতভাবে বিদ্যমান। ফলে—
প্রবাসীর বিশেষ দুর্বলতা আইনে প্রতিফলিত হয় না
বিচারপ্রক্রিয়া দীর্ঘ ও ব্যয়বহুল:
১। প্রবাস থেকে মামলা পরিচালনা কার্যত অসম্ভব।
২। ডিজিটাল আইন ব্যবস্থাপনা পূর্ণাঙ্গ নয়
আইন থাকলেও বাস্তব সুফল প্রবাসীরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে পান না।
৫. আন্তর্জাতিক মানদণ্ড ও তুলনামূলক বিশ্লেষণ:
ভারত, ফিলিপাইন, মেক্সিকো ও শ্রীলঙ্কার মতো দেশগুলো প্রবাসীদের জন্য পৃথক আইন, ভোটাধিকার ও সামাজিক নিরাপত্তা কাঠামো গড়ে তুলেছে।
এসব দেশে—
১। প্রবাসীরা সম্পত্তি ও বিনিয়োগে রাষ্ট্রীয় গ্যারান্টি পান।
২। দূতাবাসে শক্তিশালী লিগ্যাল সেল রয়েছে।
৩। প্রবাসীরা সরাসরি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারেন।
৪। বাংলাদেশ এখনো এই মানদণ্ডে অনেক পিছিয়ে রয়েছে।
৬. প্রবাসীবান্ধব আইন প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা:
৬.১ অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার স্বার্থে:
আইনি সুরক্ষা থাকলে রেমিট্যান্সের ধারাবাহিকতা ও বিনিয়োগের প্রবাহ নিশ্চিত হবে।
৬.২ সামাজিক স্থিতি রক্ষায়
প্রবাসীর পরিবার নিরাপদ থাকলে সামাজিক অস্থিরতা কমবে।
৬.৩ রাষ্ট্র ও নাগরিকের আস্থা জোরদারে
আইনের মাধ্যমে সুরক্ষা নিশ্চিত হলে প্রবাসীদের রাষ্ট্রের প্রতি আস্থা দৃঢ় হবে।
৭. প্রস্তাবিত আইনসমূহ (সংক্ষিপ্ত কাঠামো):-
১। প্রবাসী নাগরিক মর্যাদা আইন।
২। প্রবাসী সম্পত্তি সুরক্ষা আইন।
৩। প্রবাসী বিনিয়োগ সুরক্ষা আইন।
৪। প্রবাসী পরিবার সুরক্ষা আইন।
৫। প্রবাসী শ্রমিক অধিকার আইন।
৬। প্রবাসী সামাজিক নিরাপত্তা আইন।
৭। প্রবাসী রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব আইন।
৮. বাস্তবায়ন কাঠামোতে এই আইনসমূহ বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন:-
১। প্রবাসী অধিকার কমিশন
২। বিশেষ প্রবাসী ট্রাইব্যুনাল
৩। অনলাইন মামলা ও সাক্ষ্যগ্রহণ ব্যবস্থা ও
৪। দূতাবাসভিত্তিক আইনি সহায়তা ইউনিট
এই দায়িত্ব রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইন প্রণয়নকারী প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহের ওপর বর্তায়।
৯. আইন না হলে সম্ভাব্য ঝুঁকি বাড়বে:
১। রেমিট্যান্স প্রবাহ হ্রাস পাবে
২। অবৈধ হুন্ডি বাজার বিস্তার কমবে।
৩। প্রবাসীদের দেশে বিনিয়োগে অনীহা বাড়বে।
৪। পারিবারিক ও সামাজিক ভাঙন
৫। রাষ্ট্র ও প্রবাসীর মধ্যে আস্থার সংকট
১০. উপসংহার (Conclusion)
প্রবাসী বাংলাদেশিরা শুধু বৈদেশিক মুদ্রার উৎস নয়—তারা রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড, বৈদেশিক কূটনীতির গুরুত্বপূর্ণ অংশ এবং ভবিষ্যৎ উন্নয়নের কৌশলগত শক্তি। অথচ তারা আজও জমি দখল, বিনিয়োগ প্রতারণা, পরিবারিক অনিরাপত্তা ও রাজনৈতিক বঞ্চনার শিকার। একটি ন্যায়ভিত্তিক ও আধুনিক রাষ্ট্রে এই অবস্থা গ্রহণযোগ্য নয়।
প্রবাসীদের জন্য পৃথক, শক্তিশালী ও কার্যকর আইন প্রণয়ন কোনো দয়ার বিষয় নয়—এটি রাষ্ট্রের সাংবিধানিক ও নৈতিক বাধ্যবাধকতা। প্রবাসীরা সমান মর্যাদার নাগরিক—এই সত্যকে আইনের ভাষায় প্রতিষ্ঠা করাই হবে আগামীর বাংলাদেশের প্রকৃত উন্নয়নের ভিত্তি।
লেখক : ড. রফিকুল ইসলাম, সম্পাদক, সমকণ্ঠ নিউজ পোর্টাল।

বাংলাদেশের স্বাস্থ্যব্যবস্থা আজ এক নীরব বিপর্যয়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে, যার নাম নার্সিং শিক্ষা সংকট। আমরা হাসপাতাল বানাচ্ছি, যন্ত্রপাতি আনছি, চিকিৎসকের সংখ্যা বাড়াচ্ছি—কিন্তু যাদের হাতে এই স্বাস্থ্যব্যবস্থা বাস্তবে চলে, সেই নার্সদের দক্ষতা তৈরিতে আমরা চরমভাবে ব্যর্থ হচ্ছি। নার্সিং একটি কর্মমুখী পেশা, কিন্তু বাংলাদেশে এটিকে রূপান্তর করা হয়েছে একটি তাত্ত্বিক সার্টিফিকেট প্রোগ্রামে। এর ফল আজ স্পষ্ট—রোগীর নিরাপত্তা ঝুঁকিতে, জনআস্থার সংকট গভীর, আর বৈশ্বিক সুযোগ হাতছাড়া।
নার্সিং শিক্ষা মানেই হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ, রোগীর পাশে দাঁড়িয়ে শেখা, ক্লিনিক্যাল সিদ্ধান্ত নেওয়া, সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণ, জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলা এবং মানবিক সেবা। অথচ বাস্তবে আমরা তৈরি করছি ‘পেপার নার্স’—যাদের ডিগ্রি আছে, কিন্তু দক্ষতা নেই। দেশে বর্তমানে প্রায় পাঁচ শতাধিক সরকারি ও বেসরকারি নার্সিং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান একই কায়দায় নার্স তৈরি করছে। মান নিয়ন্ত্রণের কার্যকর ব্যবস্থা না থাকায় এই প্রতিষ্ঠানগুলো সার্টিফিকেট উৎপাদনের কারখানায় পরিণত হয়েছে।
এই ব্যর্থতার সবচেয়ে ভয়াবহ দিক হলো—এটি সরাসরি রোগীর জীবনের ওপর প্রভাব ফেলছে। দক্ষ নার্স না থাকলে ওষুধ প্রদানে ভুল হয়, সংক্রমণ বাড়ে, রোগীর অবস্থা অবনতি শনাক্ত হয় না, ICU ও জরুরি সেবায় ঝুঁকি তৈরি হয়। অর্থাৎ নার্সিং শিক্ষার দুর্বলতা মানে হাসপাতাল নিজেই একটি হাই-রিস্ক জোনে পরিণত হওয়া।
আরও আশঙ্কাজনক বিষয় হলো, প্রতিবছর দেশে প্রায় ২০ হাজারের বেশি নার্স তৈরি হলেও তাদের বড় একটি অংশ কর্মসংস্থানের সুযোগ পাচ্ছে না। একদিকে দেশে হাসপাতালগুলো দক্ষ নার্সের অভাবে ভুগছে, অন্যদিকে নার্সরা বেকার—এই বৈপরীত্য প্রমাণ করে সমস্যাটি চাকরির নয়, দক্ষতার। বিদেশে নার্সদের বিপুল চাহিদা থাকা সত্ত্বেও আমাদের নার্সরা আন্তর্জাতিক মানের দক্ষতা ও পেশাগত ইংরেজির অভাবে সেই সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।
এই সংকট থেকে উত্তরণের জন্য এখন আর নরম ভাষা বা ধীর পদক্ষেপ চলবে না। সরকার, নিয়ন্ত্রক সংস্থা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ—সবাইকে জবাবদিহির আওতায় আনতে হবে। নার্সিং শিক্ষায় ৭০ শতাংশ ক্লিনিক্যাল প্রশিক্ষণ বাধ্যতামূলক করতে হবে। প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে পূর্ণাঙ্গ স্কিল ল্যাব, প্রশিক্ষিত ক্লিনিক্যাল ইনস্ট্রাক্টর এবং বাস্তব রোগীভিত্তিক প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে। লাইসেন্স পাওয়ার আগে OSCE ভিত্তিক দক্ষতা মূল্যায়ন বাধ্যতামূলক করা জরুরি।
একই সঙ্গে জাতীয়ভাবে ‘নার্সিং স্কিল ও পেশাগত ইংরেজি উন্নয়ন কর্মসূচি’ চালু করতে হবে, যাতে নতুন গ্র্যাজুয়েটরা ৩–৬ মাসের নিবিড় প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক উভয় কর্মবাজারে প্রবেশের যোগ্যতা অর্জন করে। এটি শুধু কর্মসংস্থানের প্রশ্ন নয়; এটি রোগীর নিরাপত্তা, হাসপাতালের মান এবং জাতীয় মর্যাদার প্রশ্ন।
আজ যদি আমরা দক্ষ নার্স তৈরির পথে না যাই, তবে আগামী দিনে হাসপাতাল থাকবে, কিন্তু নিরাপদ সেবা থাকবে না। ডিগ্রি থাকবে, কিন্তু দক্ষতা থাকবে না। আর একটি জাতির স্বাস্থ্যব্যবস্থা যখন দক্ষ নার্স ছাড়া চলে, তখন সেই জাতি কেবল অসুস্থ নয়—ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে ওঠে।
এখনই সময়—পেপার নার্স নয়, দক্ষ নার্স তৈরির।
লেখকঃ নার্সিং শিক্ষাবিদ ও গবেষণা পরামর্শক, বাংলাদেশ।

গত ২২ জানুয়ারি দৈনিক বাংলারে প্রধান শিরোনাম ছিল- ‘ভোটের লড়াই শুরু, প্রতীক নিয়ে মাঠে প্রার্থীরা’। একই দিন অপর একটি দৈনিকের শিরোনাম ছিল, ‘আজ থেকে মাঠের লড়াই শুরু।’ বলা নিষ্প্রয়োজন, আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আনুাষ্ঠিক প্রচারণা শুরুর বিষয়টি খবরে তুলে ধরা হয়েছে। লক্ষণীয় হলো, অধিকাংশ সংবাদপত্র ‘ভোটের লড়াই’ জোড়া শব্দ ব্যবহার করেছে। কেউ কেউ অবশ্য নির্বাচনকে ভোটযুদ্ধও বলে থাকেন। তা যুদ্ধ বলি আর লড়াই বলি, বিষয়টি আসলে প্রতিদ্বন্দ্বিতা। যেহেতু নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী দল ও প্রার্থীদের মধ্যে ভোট সংগ্রহের নিমিত্তে একটি যুদ্ধংদেহী মনোভাব কাজ করে, তাই এটাকে লড়াই বা যুদ্ধ: বলাটা অসমীচীন নয়।
লড়াই শব্দটি শুনলেই ঢাল-তলোয়ার অস্ত্র-গোলাবারুদ আর খুনোখুনির দৃশ্য চোখের সামনে ভেসে ওঠে। শিউরে ওঠে শরীর। তবে কিছু লড়াই আছে, যেগুলোতে অস্ত্রশস্ত্রের প্রয়োজন পড়েনা। কাউকে খুন-জখমেরও দরকার হয় না। বুদ্ধি আর কৌশলে সেসব লড়াইয়ে জয়-পরাজয় নির্ধারিত হয়। এমন লড়াইগুলোর মধ্যে খেলাধুলা বা ক্রীড়া অন্যতম। ফুটবল, ক্রিকেট কিংবা যে কোনো খেলাই হোক না কেন, মূলত সেটা শিরোপা দখলের লড়াই। এসব লড়াইয়ে খেলোয়াড়দের বুদ্ধিমত্তা ও ক্রীড়ানৈপুণ্য জয়লাভের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অবশ্য খেলার মাঠের শান্তিপূর্ণ লড়াই সবসময় শান্তিপূর্ণ থাকে না। কখনও কখনও তা সংঘর্ষে গড়ায়। সেটা মাঠের খেলোয়াড় কিংবা মাঠের বাইরে গ্যালারিতে বসে থাকা দর্শকদের মধ্যেও হতে পারে। একসময় ঢাকার বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব ও আবাহনী লিমিটেডের মধ্যে অনুষ্ঠিত খেলা সংঘর্ষ ছাড়া শেষ হয়েছে খুব কম। মাঠের সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়ত স্টেডিয়ামের বাইরে। আর তার অনিবার্য শিকার হতো নিরপরাধ মানুষ; মাঠের খেলা কিংবা গ্যালারির উল্লাস কোনোটাতেই যাদের কোনো ভূমিকা থাকত না। অথচ মাঠে যে দলই গোল খেয়ে থাকুক বা ফাউল করুক, ক্লাব দুটির জানবাজ সমর্থকদের লাঠি কিংবা ইটের আঘাত হজম করতে হতো স্টেডিয়ামের বাইরে পথের পাশের নীরিহ দোকানি, পথচারী এবং গাড়িগুলোকে। অনেকটা ‘রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়, উলুখড়ের জীবন যায়’ উপমার মতো।
রাজনীতি যদিও কোনো খেলা নয়, তবে এ প্রসঙ্গে অনেকেই ‘খেলোয়াড়ি মনোভাব’ কথাটি ব্যবহার করে থাকেন। মানে, রাজনীতি যারা করবেন, তাদের মনোভাব হতে হবে খেলোয়াড়দের মতো সৌহার্দ্যপূর্ণ। জয়-পরাজয়কে সহজভাবে মেনে নেওয়ার মানসিকতা থাকতে হবে। খেলা শেষ তো প্রতিদ্বন্দ্বিতা শেষ। মাঠের বাইরে সবাই সবার বন্ধু। তবে নিরেট সত্যি হলো, মুখে বললেও সে মানসিকতা আমাদের দেশের খুব কম রাজনীতিকেরই ছিল কিংবা আছে। আর এই না থাকাটা আমাদের জাতীয় জীবনে নানা উৎকট সমস্যা অতীতে সৃষ্টি করেছে। যেহেতু রাজনীতি রাষ্ট্রকে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করে, তাই এই গুরুত্বপূর্ণ কর্মকাণ্ডে যারা জড়িত থাকবেন, তাদের কাছ থেকে মানুষ পরমত সহিষ্ণুতা, জনরায় মেনে নেওয়ার মানসিকতা ও পারস্পরিক সৌহার্দ্যবোধ আশা করে। কিন্তু দুঃখজনক হলো, জনগণের সে আশা সবসময় হতাশার চোরাবালিতে হারিয়ে যায়।
বলা হয়ে থাকে রাজনীতির সৌন্দর্য হচ্ছে সমঝোতা ও প্রীতিসুলভ প্রতিদ্বান্দ্বিতা। প্রতিযোগিতাও বলা যায়। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা বা প্রতিযোগিতার বিষয়টি প্রাসঙ্গিক হয়ে দেখা দেয় নির্বাচনের সময়। নির্বাচন, বিশেষত জাতীয় নির্বাচন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণ সিদ্ধান্ত নেয়, পরবর্তী মেয়াদে কারা রাষ্ট্র নামের যানটির ড্রাইভিং সিটে বসবে। জনগণ যদি রাষ্ট্রের চালক নির্বাচনে ভুল করে, তাহলে দুর্ভোগটা তাদেরই পোহাতে হয়। তবে জনগণের রাষ্ট্র-চালক নির্বাচনের ক্ষেত্রে সুস্থ পরিবেশ থাকা অন্যতম একটি পূর্বশর্ত। গণতান্ত্রিক রীতি অনুযায়ী অবাধে যদি জনগণ তথা ভোটার সাধারণ ব্যালট পেপারে তাদের অভিমত ব্যক্ত করতে পারে, তাহলে চালক নির্বাচনে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে কম। অবশ্য অনেক সময় প্রচার-প্রপাগাণ্ডার আবহে সাধারণ মানুষ বিভ্রান্ত হয়ে ভুল সিদ্ধান্ত যে নেয়না, তা নয়। আর এক্ষেত্রে গোটা রাষ্ট্র ও নাগরিকদের খেসারত দিতে হয়।
বাংলাদেশে প্রায় দেড় দশক আদৌ কোনো নির্বাচন হয়নি। নির্বাচনের নামে হয়েছে প্রহসন। কখনো একতরফা, কখনো রাতেই ব্যালট পেপারে সিল মারা, আবার কখনো ‘আমরা-আমরাই তো’ ধরনের নির্বাচন। বলাই বাহুল্য, সেসব নির্বাচনে জনমতের বাস্তবিক প্রতিফলন ঘটে নি। হয়তো তৎকালীন ক্ষমতাসীন দলটি নির্বাচনে ‘জয়লাভে’র আত্মপ্রসাদ লাভ করেছে। তবে ক্ষতি হয়েছে গণতন্ত্রের। কেননা, ওই তিনটি নির্বাচন বাংলাদেশের জনগণকে রাজনীতি, গণতন্ত্র ও নির্বাচনের প্রতি আস্থাহীন করে তুলেছিল। ২০২৪ সালে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর দেশে পুনরায় অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের দ্বার উন্মুক্ত হয়েছে। সে নির্বাচনের মাঠের লড়াই শুরু হয়েছে গত ২২ জানুয়ারি থেকে, যে কথা আগেই উল্লেখ করেছি। রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে যারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে, তারা এতদিন বাগ্যুদ্ধে লিপ্ত ছিল। এবার তারা জনগণের ভোট নিজেদের পক্ষে নেয়ার জন্য মাঠে-ময়দানে তৎপরতা চালাবে। প্রচার চালাবে দ্বারে দ্বারে গিয়ে। এটাই ভোটের মূল লড়াই। এ লড়াই শেষ হবে সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি।
অবশ্য পূর্বের যেকোনো নির্বাচনের চেয়ে এবারের নির্বাচনী প্রচারণা হতে যাচ্ছে একটু ভিন্ন আবহে। আগে যেমন প্রার্থীদের পোস্টারে সারাদেশের বাড়ি-ঘরের দেয়াল ছেয়ে যেত, এবার তা হবেনা। নির্বাচন কমিশন পোস্টার ছাপানো নিষিদ্ধ করেছে। ব্যবহার করা যাবেনা ড্রোনও। তবে একটি সংসদীয় আসনে ২০টি বিলবোর্ড ব্যবহার করা যাবে। জনসংযোগ-জনসভা করা যাবে নির্বাচন কমিশন প্রণীত বিধি মেনে। একই সঙ্গে বিদেশে সভা-সমাবেশের প্রাচারণাও করা যাবে না। এছাড়া আগের নির্বাচনগুলোতে যেসব তৎপরতা নিষিদ্ধ ছিল এবারও তা নিষিদ্ধ থাকছে। তন্মধ্যে দল বা প্রার্থীর পক্ষে মিছিল করা যাবে না।
দীর্ঘদিন পরে দেশের মানুষ একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন পেতে চলেছে, এমনটি মনে করছেন রাজনীতি বিশ্লেষকগণ। তবে এ নির্বাচনকে সর্বাংশে অংশগ্রহণমূলক বলার সুযোগ নেই। কেননা, কার্যক্রম নিষিদ্ধ থাকায় দেশের অন্যতম রাজনৈতিক শক্তি আওয়ামী লীগ নির্বাচনে অংশ নিতে পারছে না। তাদের সাধারণ কর্মী-সমর্থকদের ভোট কাদের বাক্সে যাবে, তারচেয়ে বড় বিষয় হলো, নিরপেক্ষ নির্বাচনী পরিবেশে জনগণের কাছে দলটির গ্রহণযোগ্যতা পরিমাপ করা গেল না। যাক, সেটা ভিন্ন প্রসঙ্গ। এ মুহূর্তে সবচেয়ে আলোচ্য বিষয় হলো, জনগণের প্রত্যাশিত একটি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। গণতন্ত্রপ্রিয় নাগরিকদের প্রত্যাশা, নির্বাচনটি শান্তিপূর্ণ হোক, যাতে যার ভোট সে স্বহস্তে দিতে পারে। সরকার অবশ্য শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের জন্য প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থাই গ্রহণ করার কথা বলছে। তবে কিছু কিছু ঘটনা জনমনে শঙ্কার জন্ম দিয়েছে নির্বাচন আদৌ শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হবে কি না। সম্প্রতি সংঘটিত কয়েকটি হত্যাকাণ্ডকে অনেকেই অশনি সংকেত হিসেবে দেখছেন। জুলাই আন্দোলনের সময় লুট হওয়া আগ্নেয়াস্ত্রের একটি বিরাট অংশ এখনো উদ্ধার করতে পারেনি সরকার। তার ওপর সীমান্তের বাইরে থেকেও অস্ত্র প্রবশে করছে, এমন খবর গণমাধ্যমে এসেছে। এসব অবৈধ অস্ত্র নির্বাচনকালে ব্যবহৃত হয়ে পরিস্থিতির অবনতি ঘটাতে পারে, এমন আশঙ্কা অমূলক নয়। তাছাড়া দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রতিদ্বন্দ্বী দলগুলোর কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষের খবরও পাওয়া যাচ্ছে। গত ২০ জানুয়ারি রাজধানীর মিরপুরে জামায়াতে ইসলামী ও বিএনপির কর্মীদের মধ্যে যে সংঘর্ষ হয়েছে, তা মানুষকে ভাবিয়ে তুলেছে। আমাদের রাজনৈতিক ট্র্যাডিশন অনুযায়ী এই সংঘর্ষের দায় দল দুটি একে অপরের ওপর চাপাতে চাচ্ছে। তবে, এক হাতে যেমন তালি বাজেনা, তেমনি একটি পক্ষের কারণে সংঘর্ষ হয়না, এটা মনে রাখা দরকার। সবচেয়ে বড় কথা, রাজনৈতিক দলগুলো কিংবা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীরা যদি তাদের কর্মী-সমর্থকদের নিয়ন্ত্রণ না করেন, তাহলে পরিবেশ শেষ পর্যন্ত শান্তিপূর্ণ থাকবে এ নিশ্চয়তা দেওয়া যায় না।
যে নির্বাচনী লড়াইটি শুরু হয়েছে, তা শান্তিুপূর্ণ রাখতে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী ও দলগুলোর ধৈর্য্য, সংযম ও সহনশীলতা। অস্বীকার করার উপায় নেই, অতি উৎসাহী কতিপয় নেতাকর্মীর বাড়াবাড়ি পরিবেশ বিনষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। অতীতে দেখা গেছে, এক প্রার্থীর পোস্টারের ওপর অন্য প্রার্থীর পোস্টার সাঁটানো, ব্যানার ছিঁড়ে ফেলা, মিছিলে উসকানিমূল স্লোগান দেওয়া ইত্যাদি কারণে সংঘাত-সংঘর্ষের সৃষ্টি হয়েছে। রাজনৈতিক দলগুলোর উচিত হবে স্ব স্ব দলের প্রার্থীদের এ ব্যাপারে কঠোরভাবে সতর্ক করে দেওয়া। মোদ্দা কথা হলো, রাজনৈতিক দলগুলো ভোটের লড়াইকে যদি আদর্শ ও কর্মসূচির লড়াইয়ের পরিবর্তে পেশিশক্তির লড়াইয়ে পরিণত না করে, তাহলে দেশবাসী আরেকটি সুষ্ঠু, অবাধ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন দেখতে পাবে। আর যদি রাজনৈতিক দলগুলো ও তাদের প্রার্থীরা জনগণের ওপর আস্থা না রেখে পেশিশক্তির ওপর নির্ভর করে, তাহলে সুষ্ঠু নির্বাচন যেমন নির্বাসনে যাবে, তেমনি গণতন্ত্রও পড়বে মুখ থুবড়ে। দেশবাসী এ বিষয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর শুভবুদ্ধির প্রত্যাশা করছে।
লেখক: সাংবাদিক ও কলাম লেখক।

শিক্ষা ব্যবস্থার মূল চালিকাশক্তি শিক্ষক সমাজ। শিক্ষক সমাজের মধ্যে বৈষম্য বিরাজমান থাকলে তার বিরূপ প্রভাব সর্বত্রই কমবেশি পড়তে থাকে। বাংলাদেশে প্রধানত সরকারি ও বেসরকারি—এই দুই ধারার শিক্ষকই জাতি গঠনে ভূমিকা রেখে চলেছেন। যদিও বেসরকারি শিক্ষকগণ কমবেশি ৯৫ শতাংশ শিক্ষার্থীর দায়িত্বে নিয়োজিত। অথচ তাদের আর্থিক সুযোগ-সুবিধা, চাকরির নিরাপত্তা এবং চাকরি বহির্ভূত আর্থিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ততার ক্ষেত্রে দীর্ঘদিন ধরেই একটি স্পষ্ট বৈষম্য বিদ্যমান। সাম্প্রতিক সময়ে প্রণীত এমপিও নীতিমালা ২০২৫ এবং এর আলোকে কালকিনি উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা কর্তৃক জারিকৃত একটি সার্কুলার এই বৈষম্যের বিষয়টিকে নতুন করে আলোচনার কেন্দ্রে নিয়ে এসেছে।
এমপিও নীতিমালা ২০২৫ এর
১১.২৭ উপধারায় বলা হয়েছে: ‘(ক) এমপিওভুক্ত কোনো শিক্ষক-কর্মচারী একই সাথে একাধিক কোন পদে/চাকরিতে বা আর্থিক লাভজনক কোন পদে নিয়োজিত থাকতে পারবেন না। এটি তদন্তে প্রমাণিত হলে সরকার তার এমপিও বাতিলসহ দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে। [এ নিষেধাজ্ঞা পূর্বের নীতিমালায়ও ছিল]
(খ) আর্থিক লাভজনক পদ বলতে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত যেকোনো বেতন/ভাতা/সম্মানি এবং বেসরকারি কোনো প্রতিষ্ঠান/ সংস্থায়/বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান/আইন পেশায় কর্মের বিনিময়ে বেতন/ভাতা/সম্মানী কে বুঝাবে।’ [এমন ব্যাখ্যা পূর্বের নীতিমালায় ছিল না]
গত ১৪ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে দেওয়া উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তার নির্দেশনায় বলা হয়েছিল, ‘বর্তমান বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে (স্কুল ও কলেজ) জনবল কাঠামো ও এমপিও নীতিমালা-২০২৫ এর আলোকে এমপিওভুক্ত শিক্ষকগণ একটি সম্মানজনক ও পূর্ণকালীন রাষ্ট্রীয় আর্থিক সুবিধাপ্রাপ্ত পেশায় নিযুক্ত। এমতাবস্থায় তাদের পেশাগত দায়িত্ব ও সময়ের পূর্ণ সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শিক্ষকতার পাশাপশি কোনো অতিরিক্ত লাভজনক পেশায় সম্পৃক্ত হওয়া নীতিগতভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হলো। নির্দেশনা অমান্য করলে এমপিও নীতিমালা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’
নিষিদ্ধ ও সীমাবদ্ধ ১১টি পেশার মধ্যে রয়েছে— বাণিজ্যিক ভিত্তিতে সাংবাদিকতা, আইন পেশা, কোচিং সেন্টার পরিচালনা বা সেখানে শিক্ষকতা, প্রাইভেট বা কেজি স্কুল পরিচালনা, শিক্ষাবিষয়ক প্রকাশনা বা পাবলিকেশন্সের ব্যবসা, হজ এজেন্ট বা এর বিপণন কার্যক্রম, বিয়ের কাজী বা ঘটকালী পেশা, টং দোকান বা ক্ষুদ্র ব্যবসা, ঠিকাদারি বা নির্মাণ ব্যবসা, মসজিদের পূর্ণকালীন ইমামতি বা খতিবের দায়িত্ব পালন (যা শিক্ষকতার সময়কে প্রভাবিত করে) এবং কোনো রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের বিশেষ সহকারী বা চাটুকার হিসেবে নিয়োজিত থাকা।
তবে নির্দেশনায় উল্লেখ করা হয়েছে, কোনো শিক্ষক স্বেচ্ছাশ্রমে ধর্মীয় বা সামাজিক কাজে যুক্ত থাকতে পারবেন, তবে তা অবশ্যই নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে হতে হবে, যাতে মূল পেশাগত দায়িত্ব পালনে কোনো ব্যাঘাত না ঘটে।’ অবশ্য পত্রটি প্রকাশের পর দেশব্যাপী সমালোচনা শুরু হওয়ায় গত ১৭ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে তা প্রত্যাহার করা হয়েছে বলে সংবাদমাধ্যমে জানা গেছে।
পত্রটি জারি করা এবং প্রত্যাহার করার বিষয়টি ‘বজ্র আঁটুনি ফস্কা গেরুর মত হয়েছে’। এতে করে এমপিও নীতিমালা ২০২৫ এ উল্লিখিত নিষেধাজ্ঞার শক্তিও কমে যাবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। কেননা, সেটির রেফারেন্স করেই নোটিশ জারি করা হয়েছিল। আবার হয়তো এটি বা আরো কঠিন একটি আদেশ জারি করা প্রয়োজন হবে, করা হবে। কেননা, যে এমপিও নীতিমালার ভিত্তিতে এটি জারি করা হয়েছিল সে নীতিমালা কিন্তু রয়েই গেছে। যদিও ‘এমপিও নীতিমালা-২০২৫ এর ১৭ (ক ও খ) বিধান কেনো বাতিল ও অবৈধ ঘোষণা করা হবে না, তা জানতে চেয়ে সরকারের সংশ্লিষ্টদের প্রতি রুল জারি করেছেন হাইকোর্ট।’ অবশ্যই শ্রেণিকক্ষে পূর্ণকালীন পাঠদান শিক্ষকগণের নৈতিক দায়িত্ব। এ দায়িত্ব সরকারি ও বেসরকারি উভয় ধরনের শিক্ষকেরই সঠিকভাবে পালন করা উচিত। তাই উভয় ধরনের শিক্ষকের আর্থিক সুযোগ-সুবিধায় এবং তাদের উপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞায় সমতা থাকা উচিত। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, আমাদের দেশে তেমন অবস্থা বজায় আছে কি?
সরকারি স্কুল ও কলেজের শিক্ষকগণ রাষ্ট্রীয় কর্মচারী হিসেবে যে সুযোগ-সুবিধা ভোগ করেন, তা একটি পূর্ণাঙ্গ সামাজিক নিরাপত্তা কাঠামোর মধ্যে পড়ে। এর মধ্যে রয়েছে— পূর্ণ মূল বেতন ও নিয়মিত বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট; ৫০ শতাংশ বাড়ি ভাড়া, চিকিৎসা ও অন্যান্য ভাতা; দুটি ঈদসহ উৎসব ভাতা; অবসরকালীন পেনশন ও গ্র্যাচুইটি; দীর্ঘমেয়াদি চাকরির নিরাপত্তা ইত্যাদি। এসব সুবিধা সরকারি শিক্ষককে আর্থিকভাবে স্থিতিশীল রাখে এবং অতিরিক্ত আয়ের ওপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে আনে। যদিও অন্যান্য দেশের শিক্ষকদের তুলনায় এটি অনেক কম। অপরদিকে এমপিওভুক্ত বেসরকারি শিক্ষকগণের চাকরি পূর্ণকালীন হলেও রাষ্ট্রীয় আর্থিক সুবিধা এখনো পরিপূর্ণ নয়। তারা সরকারের কাছ থেকে মূলত মূল বেতন-এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ দীর্ঘদিন ধরে। তারা এখনো পূর্ণাঙ্গ বাড়ি ভাড়া ও চিকিৎসা ভাতা থেকে বঞ্চিত। সম্প্রতি মূল বেতনের মাত্র ১৫ শতাংশ হারে বাড়ি ভাড়া তাও আবার দুই ধাপে দেওয়ার ঘোষণা সামান্য ইতিবাচক অগ্রগতি হলেও, এটি সরকারি শিক্ষকদের প্রাপ্ত সুবিধার তুলনায় এখনও অনেক কম। এছাড়া— কল্যাণ তহবিল ও অবসর সুবিধা পেতে দীর্ঘ অপেক্ষা; পেনশন ব্যবস্থার অনুপস্থিতি; বেতন কাঠামোর ধীর অগ্রগতি; চাকরি হারানোর ঝুঁকি; রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক মর্যাদা কম। এই বাস্তবতায় অনেক বেসরকারি শিক্ষক ন্যূনতম জীবনমান বজায় রাখতে হিমশিম খান। তাই বাড়তি কাজ করে বাড়তি আয় করেই বেঁচে থাকতে হয় তাদের পরিবার-পরিজন নিয়ে।
এমতাবস্থায় কোনো বিধিনিষেধ আরোপ করা হলে অবশ্যই সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষকদের মধ্যে সমতা বিধান করা উচিত। তুলনামূলক কম সুবিধাভোগী বেসরকারি শিক্ষকদের চাকরি বহির্ভূত আয়ের উপর কঠোর বিধি নিষেধ আরোপ ও কার্যকর করার পূর্বে অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে অধিক সুবিধাভোগী সরকারি স্কুল-কলেজের শিক্ষকগণ অনুরূপ আর্থিক কর্মকাণ্ডে কোনোভাবেই যুক্ত নন। অর্থাৎ প্রাথমিক থেকে কলেজ পর্যায়ের সরকারি শিক্ষকগণ কোনো প্রাইভেট স্কুল প্রতিষ্ঠা, প্রাইভেট টিউশনি, কোচিং সেন্টার পরিচালনা, কোচিং সেন্টারে পাঠদান, নোট-গাইড লেখা, ক্ষুদ্র ব্যবসা পরিচালনা, প্রাইভেট চাকরি, শেয়ার ব্যবসা, দাদন ব্যবসা, মৌসুমী ব্যবসা, কৃষি কাজ, মৎস্য ও পোল্ট্রি খামার, পশু চিকিৎসা, হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা, পল্লী চিকিৎসা, এলোপ্যাথি ওষুধ বিক্রি ইত্যাদি অগণিত আর্থিক কর্মকান্ডে কোনভাবেই যুক্ত নন এবং রাজনৈতিক নেতাদের লেজুরবৃত্তি করে সুবিধাজনক পদায়ন ও পদোন্নতি নিচ্ছেন না।
যারা পূর্ণ বেতন, ভাতা, পেনশন ও অবসর সুবিধা পাচ্ছেন, তারা যদি চাকরি বহির্ভূত আয়মূলক কর্মকাণ্ডে যুক্ত থাকেন—তবে যারা শুধুমাত্র মূল বেতন পান, তাদের বাড়তি আয়ের পথ বন্ধ করে কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ ও কার্যকর কতটা যুক্তিযুক্ত? সেই নিষেধাজ্ঞা কতটা মান্য করা সম্ভব ক্ষুধার্ত শিক্ষকের পক্ষে? তথাপি শিক্ষকগণ শিক্ষকতা বহির্ভূত কোনো কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত থাকুক সেটি আমি কখনোই চাই না। চাকরির পাশাপাশি অন্যান্য কাজ করে অর্থ উপার্জন করতে সবার ভালো লাগে না, সবাই তা করে না, সবাই তা পারে না। শিক্ষার স্বার্থে শিক্ষকদের মূল পেশায় পূর্ণকালীন নিয়োজিত রাখা এবং মূল পেশা বহির্ভূত অন্যান্য কর্মকান্ড থেকে বিচ্ছিন্ন রাখা অবশ্যই সরকার ও সবার দায়িত্ব। সেজন্য প্রয়োজন সরকারি ও বেসরকারি সকল শিক্ষকের আর্থিক সুযোগ-সুবিধায় ও রাষ্ট্রীয়-সামাজিক মর্যাদায় সমতা আনয়ন করা, উভয়ের মানসম্পন্ন স্বচ্ছলতা নিশ্চিত করা, সকল স্তরে সর্বাধিক যোগ্য শিক্ষক নিয়োগ করা এবং সকল শিক্ষকের জন্য আরো কঠিন একই নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে তা শতভাগ কার্যকর করা। যাতে শিক্ষকগণ নিশ্চিন্তে মূল পেশায় অর্থাৎ শিক্ষকতায় সার্বক্ষণিক নিয়োজিত থাকেন, থাকতে পারে। যত দ্রুত এটি সম্ভব ততই মঙ্গলজনক। সকল শিক্ষক সফল শিক্ষক হলেই সর্বক্ষেত্রে সফলতা অর্জন সম্ভব।
লেখক: সাবেক অধ্যক্ষ, শিক্ষা গবেষক ও কলাম লেখক।

জনগণ অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোটাধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে সরকার গঠনে তাদের সার্বভৌম ক্ষমতা ব্যবহারের জন্য।
জনগণ রাষ্ট্রের মালিক। বছরের অন্য সময় তা প্রতীয়মান না হলেও জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সময় এটি প্রত্যক্ষ করা যায়। জাতির বিশেষ প্রয়োজনে অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হয়েছে প্রায় দেড় বছর আগে। নানামুখী সংস্কার কার্যক্রম সম্পাদনের চেষ্টা করা হলেও এই সরকারের মূল দায়িত্ব হচ্ছে নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে দেশে জনসমর্থিত রাজনৈতিক সরকারের কাছে দায়িত্ব বা ক্ষমতা হস্তান্তর করা। কোনো ফর্মেই অনির্বাচিত সরকার দীর্ঘদিন ক্ষমতায় থাকা কাম্য হতে পারে না। দেশের এই ক্রান্তিকালে গ্রহণযোগ্য জাতীয় সংসদ নির্বাচনের কোনো বিকল্প নেই।
আমরা যদি জাতিকে একটি ভালো নির্বাচন উপহার দিতে না পারি, তাহলে দেশ আবারও স্বৈরাচারের অন্ধকারে নিমজ্জিত হতে পারে। ব্যর্থ হতে পারে জুলাই শহীদদের আত্মদান।
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রবাসী বাংলাদেশি ভোটাররা তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করার সুযোগ পাচ্ছেন। দেশের মানুষের মধ্যে এই নির্বাচন নিয়ে প্রচণ্ড আগ্রহ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। কনকনে শীতের তীব্রতা উপেক্ষা করে শহর থেকে গ্রাম—সর্বত্রই এখন নির্বাচনী ব্যস্ততা।
জনগণ যাদের ভোট দেবে, তারাই পরবর্তী পাঁচ বছরের জন্য দেশ শাসনের অধিকার লাভ করবেন। ২০০৯ সালে যারা প্রাপ্তবয়স্ক হয়েছেন, তারা এবারই প্রথম তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন। কারণ বিগত ১৬ বছরে দলীয় সরকারের অধীনে দেশে যে তিনটি জাতীয় সংসদ নির্বাচন (২০১৪, ২০১৮ ও ২০২৪) অনুষ্ঠিত হয়েছে, তাতে সাধারণ ভোটাররা অংশগ্রহণের সুযোগ পাননি। সেসব নির্বাচন ছিল একতরফা এবং ভোটারবিহীন। এসব প্রহসনমূলক নির্বাচন স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ব্যাপকভাবে সমালোচিত এবং নিন্দিত হয়েছে। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অপব্যবহার করে নির্বাচনপ্রক্রিয়াকে কলুষিত না করা হলে হয়তো বিগত স্বৈরাচারী সরকারের এমন করুণ পরিণতি না-ও হতে পারত। নির্বাচনে ভোটাধিকার প্রয়োগ করে পছন্দনীয় সরকার গঠন করতে না পারার কারণে বিগত সরকারের প্রতি সাধারণ মানুষ প্রচণ্ড রকম ক্ষুব্ধ ছিল। আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সাধারণ মানুষ যদি নির্বিঘ্নে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে না পারে, তাহলে সেই নির্বাচনের গ্রহণযোগ্যতাও ক্ষুণ্ন হবে। সেই অবস্থায় অন্তর্বর্তী সরকারের পক্ষে ‘দায়’ এড়ানোর কোনো সুযোগ থাকবে না। একই সঙ্গে নির্বাচন কমিশন তার গ্রহণযোগ্যতা হারাবে এবং বিগত সরকারের মতোই আজ্ঞাবাহী নির্বাচন কমিশন হিসেবে তাদের খ্যাতি জুটবে।
এই মুহূর্তে পুরো জাতি নির্বাচনে অংশগ্রহণপূর্বক তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগের জন্য উন্মুখ হয়ে অপেক্ষা করছে। তাদের সেই আকাঙ্ক্ষা যাতে কোনোভাবেই ব্যর্থ না হয়, তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব নির্বাচন কমিশন তথা সরকারের। আগামী দিনে যারা রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করবেন, তাদের বৈধতাও নির্ভর করবে সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের ওপর। ভয়ভীতিহীন সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য জাতীয় সংসদ নির্বাচন আয়োজনের জন্য বেশ কিছু শর্ত পালন করতে হবে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এসব শর্ত পরিপালনে কিছুটা হলেও ঘাটতি প্রত্যক্ষ করা যাচ্ছে।
প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় দেশে বিদ্যমান আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির প্রসঙ্গটি। গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে সরকারের পতন ঘটলে কয়েক দিন দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটে, এটিই স্বাভাবিক। বাংলাদেশে অতীতে একাধিকবার গণঅভ্যুত্থানে সরকার পরিবর্তন হওয়ার পর কিছুদিন দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটেছিল, কিন্তু তাৎক্ষণিকভাবে বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণের কারণে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি দ্রুতই স্বাভাবিক হয়ে আসে। তবে চব্বিশে গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে আওয়ামী লীগ সরকারের পতন এবং সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভারতে পালিয়ে যাওয়ার পর দীর্ঘদিনেও দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়নি। এটি খুবই উদ্বেগজনক। কারণ আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক না থাকলে ভোটাররা স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভোটকেন্দ্রে উপস্থিত হতে পারবেন না।
বিগত সরকারের আমলে অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের মতো আইন প্রয়োগকারী সংস্থায় ব্যাপক দলীয়করণ হয়। চব্বিশের ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানের সময় আইন প্রয়োগকারী সংস্থার এক শ্রেণির সদস্য ও কর্মকর্তা বিক্ষোভকারীদের দমনের নামে অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করেছেন। অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে তারা ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থার মধ্যে রয়েছেন। অনেকেই চাকরিস্থল থেকে পালিয়ে গেছেন। ২০২৪ সালের ৫ আগস্টের পর বিভিন্ন থানা থেকে পুলিশ সদস্যদের অনেকেই প্রাণভয়ে পালিয়ে গেছেন। বিগত সরকার আমলে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার যেসব সদস্য রাজনৈতিক বিবেচনায় নানা ধরনের অনৈতিক সুবিধা ভোগ করেছেন, তারা অন্তর্বর্তী সরকারকে বিব্রত করার জন্য চেষ্টা করতে পারেন। একটি মহল উদ্দেশ্যমূলকভাবে রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলের লক্ষ্যে দেশে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির আরো অবনতি ঘটানোর চেষ্টা করছে বলে অনেকেই অভিযোগ করছেন। বিশেষ করে নির্বাচনের আগে দেশের বিভিন্ন স্থানে রাজনৈতিক ব্যক্তিদের লক্ষ্য করে টার্গেট কিলিং করা হতে পারে। অতি দ্রুত দেশের বিদ্যমান আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিকীকরণের জন্য কার্যকর উদ্যোগ নিতে হবে। বিগত সরকার আমলে অনৈতিক সুবিধাভোগী পুলিশ সদস্য ও কর্মকর্তাদের চিহ্নিত করে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। বিশেষ কোনো দলের প্রতি আনুগত্য পোষণকারী পুলিশ সদস্য ও কর্মকর্তাদের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দায়িত্ব পালন করা থেকে বিরত রাখা যেতে পারে। নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।
আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয়ে যাতে কোনো ধরনের বিতর্ক সৃষ্টি না হয় সে জন্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানে যারা দলীয় রাজনীতিচর্চায় নিয়োজিত ছিলেন, তাদের নির্বাচনী দায়িত্ব পালন করা থেকে বিরত রাখা যেতে পারে। সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রিসাইডিং অফিসার ও পোলিং অফিসারদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তারা চাইলে যেকোনো সময় নির্বাচনকে বিতর্কিত করে ফেলতে পারেন। প্রিসাইডিং অফিসারের একটি বিতর্কিত সিদ্ধান্ত পুরো নির্বাচন প্রক্রিয়াকে প্রশ্নবিদ্ধ করে তুলতে পারে। একটি বড় রাজনৈতিক দলের কার্যক্রম নিষিদ্ধ থাকায় তাদের কোনো প্রার্থী নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারছেন না। তারা নানাভাবে নির্বাচনকে প্রশ্নবিদ্ধ করার চেষ্টা চালাতে পারে। তাই সতর্ক থাকতে হবে।
নির্বাচনকালে অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টাদের সর্বোচ্চ নিরপেক্ষতা প্রদর্শন করতে হবে। কোনো বিশেষ দল বা মহলের প্রতি অনুরাগ বা বিরাগ প্রদর্শন করা যাবে না। স্বাধীনতার পর থেকে এ পর্যন্ত দলীয় সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত কোনো নির্বাচনই প্রশ্নমুক্ত ছিল না। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত ১৯৯১, ১৯৯৬ ও ২০০১ সালে অনুষ্ঠিত নির্বাচন মুক্ত এবং অবাধ ছিল। ২০০৮ সালে সেনা সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে। একটি রাজনৈতিক দলকে ক্ষমতায় আনার জন্য সহযোগিতা করা হয়েছিল বলে অভিযোগ রয়েছে। অনেকেই এমন অভিযোগ উত্থাপনের চেষ্টা করছেন যে বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারও ২০০৮ সালে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের মতো কোনো একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলকে বিজয়ী করার জন্য প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। এই অভিযোগ ভিত্তিহীন এবং মিথ্যা প্রমাণ করার দায়িত্ব অন্তর্বর্তী সরকারের। কোনো কারণে যদি নির্বাচন প্রশ্নবিদ্ধ হয়, তাহলে সে জন্য পুরো জাতিকে মাশুল দিতে হবে। আসন্ন নির্বাচনে ছোট-বড় সব রাজনৈতিক দলের প্রার্থীদের জন্য ‘লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড’ তৈরি করতে হবে। কারো প্রতি পক্ষপাত বা বৈরী আচরণ কাম্য নয়। অন্যদিকে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন অন্তর্বর্তী সরকারকে মহিমান্বিতও করতে পারে। আবার এই নির্বাচনই তাদের ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করতে পারে। তাই অনুরাগ-বিরাগের ঊর্ধ্বে উঠে নির্বাচনসংশ্লিষ্ট সবাইকে দায়িত্ব পালন করতে হবে। মনে রাখতে হবে, সুযোগ বারবার আসে না। তাই প্রাপ্ত সুযোগের সর্বোত্তম ব্যবহার করতে হবে।
নির্বাচনের আগে নির্বাচন কমিশন প্রার্থীদের জন্য আচরণবিধি ঘোষণা করে। নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক প্রার্থী যাতে সঠিকভাবে আচরণবিধি মেনে চলেন, তা নিশ্চিত করতে হবে। বড় দলের প্রার্থী অথবা ছোট দলের প্রার্থী বিবেচনায় কারো প্রতি বৈরী আচরণ করা যাবে না। প্রতিবারই লক্ষ্য করা যায়, নির্বাচনে অর্থ ব্যয়ের যে সীমা থাকে, তা বেশির ভাগ প্রার্থীই লঙ্ঘন করেন। এবারের নির্বাচনে যেন তেমনটি না ঘটে, তার ব্যবস্থা করতে হবে। ভোট প্রদানের ক্ষেত্রে ভোটারদের সচেতন এবং সতর্ক থাকতে হবে। ব্যক্তিগতভাবে তুলনামূলক সৎ ও যোগ্য প্রার্থীকে ভোট দিতে হবে। একটি জনপ্রিয় নির্বাচনী স্লোগান হচ্ছে, ‘আমার ভোট আমি দেব, যাকে খুশি তাকে দেব।’ কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে, ভোট যাকে খুশি তাকে প্রদানের বস্তু নয়। আমার দেওয়া ভোটে নির্বাচিত হয়ে কোনো প্রার্থী যদি অন্যায়-অপকর্ম করেন, এর ‘দায়’ কিছুটা হলেও আমার ওপর বর্তাবে। কাজেই ভোটাধিকার প্রয়োগের সময় সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। কোনোভাবেই দলীয় পরিচয় অথবা অন্য কোনো কারণে একজন অযোগ্য প্রার্থী যাতে নির্বাচিত না হতে পারেন সে ব্যাপারে আমাদের সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। কারো দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বা ক্ষুদ্র ব্যক্তিস্বার্থে অযোগ্য প্রার্থীকে নির্বাচনে বিজয়ী করা যাবে না।
সব ষড়যন্ত্র ও শঙ্কা কাটিয়ে আগামী ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সুষ্ঠু, সুন্দর, নিরপেক্ষ এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্য হোক, এমনটাই কামনা করছি।
লেখক : সাবেক উপাচার্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও বাহরাইনে নিযুক্ত বাংলাদেশের সাবেক রাষ্ট্রদূত।

মানুষের জীবন এক দীর্ঘ যাত্রা, যেখানে আলো ও অন্ধকার পাশাপাশি হাঁটে। এই পথচলায় গান হয়ে ওঠে নীরব সঙ্গী, অদৃশ্য বাতিঘর। শব্দের সুরে, তালের ছন্দে গান মানুষকে আশ্রয় দেয়, সাহস জোগায়, ভাঙা মনকে জোড়া লাগায়। জন্মের আগেই মায়ের লোরিতে মানুষের সংগীতযাত্রা শুরু হয়, আর জীবনের শেষ প্রান্তেও স্মৃতির ভেতর গান আলো জ্বালায়। প্রেম, বেদনা, সংগ্রাম কিংবা আনন্দ। মানবজীবনের প্রতিটি অনুভূতিই গানের কাছে আশ্রয় খুঁজে পায়। তাই গান শুধু বিনোদন নয়, এটি মানুষের অস্তিত্বের ভাষা। দিশাহীন সময়েও গান দেখায় আলোর পথ, জীবনের মানচিত্রে এঁকে দেয় আশার রেখা।
‘আমার বাবার মুখে প্রথম যেদিন শুনেছিলাম গান
সেদিন থেকে গানই জীবন গানই আমার প্রাণ,
আমার মায়ের আদেশ বাবার মতো গাইতে হবে গান
সেদিন থেকে গানই জীবন গানই আমার প্রাণ।’
মানুষের জীবনে এমন কিছু শক্তি আছে, যা নীরবে পথ দেখায়। ঠিক যেমন বাতিঘর ঝড়ের রাতে দিশাহীন নাবিককে নিরাপদ তীরে পৌঁছাতে সাহায্য করে, তেমনি গানও মানুষের জীবনসংগ্রামে মানসিক আশ্রয়, আত্মবিশ্বাস ও আশার আলো জ্বালায়। জন্মের আগেই মায়ের কণ্ঠে লোরি দিয়ে মানুষের সংগীতযাত্রা শুরু হয়, আর জীবনের শেষ প্রান্তেও গান হয়ে ওঠে স্মৃতি, প্রার্থনা ও আত্মসমর্পণের ভাষা। প্রেম, বেদনা, বিদ্রোহ, উৎসব, আধ্যাত্মিকতা মানবজীবনের প্রতিটি অনুভূতির সঙ্গেই গান ও সংগীত গভীরভাবে যুক্ত। পৃথিবীতে এমন কোন স্থান নেই যেখানে সুর নেই, ছন্দ নেই, প্রেম নেই। সুর আর ছন্দ রয়েছে বাতাসের শো শো শব্দে, নদীর কলকলিয়ে চলায়। পাথরের মর্মর শব্দে। পাখির কাকলীতে, পাকা ধানের বাতাসের দোলায়, বৃষ্টির ফোঁটায় রয়েছে স্বর্গীয় সংগীত। যা জীবনকে করে তোলে মোহনীয় ও সুন্দর। সংগীত ও জীবন যেন এক দোতারা। যেখানেই জীবন সেখানেই সংগীত।
সভ্যতার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, দাসত্ব কিংবা বৈষম্যের বিরুদ্ধে মানুষ অস্ত্রের আগে গানকেই বেছে নিয়েছে। আফ্রিকার দাসপ্রথার সময় গসপেল গান, ভারতীয় উপমহাদেশে স্বাধীনতা আন্দোলনের গান কিংবা লাতিন আমেরিকার প্রতিবাদী সংগীত সবখানেই গান হয়ে উঠেছে শক্তির উৎস। কারণ গান মানুষের মনন, বিবেক ও মানবিকতাকে জাগিয়ে তোলে। শুধু শিল্প বা বিনোদন নয়, সংগীত আজ একটি সামাজিক, মানসিক ও অর্থনৈতিক শক্তি। এই লেখায় সংগীতের সংজ্ঞা, বাংলা ও বিশ্বসংগীতের বৈচিত্র্য, মানুষের মানসিক ও অর্থনৈতিক জীবনে গানের ভূমিকা এবং গানকে উন্নয়ন ও দারিদ্র্যবিমোচনের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহারের সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করা হলো।
সংগীত কী এবং বাংলা সংগীতের বৈচিত্র্য:
সংগীত হলো- মানবমনের আবেগ, অনুভূতি ও চিন্তার সুরেলা প্রকাশ। তাল, লয় ও স্বরের সম্মিলনে যে নান্দনিক ধ্বনিশিল্প সৃষ্টি হয়, তাকেই সংগীত বলা হয়। ভারতীয় শাস্ত্রে সংগীতকে বলা হয়েছে নাদ ব্রহ্ম, অর্থাৎ ধ্বনিই সৃষ্টির মূল। পাশ্চাত্য দর্শনেও সংগীতকে আত্মার ভাষা হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। অর্থাৎ সংগীত শুধু শোনা নয়, এটি অনুভব ও উপলব্ধির বিষয়।
বাংলা সংগীত বাংলাভাষী মানুষের জীবন, প্রকৃতি ও সংস্কৃতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। নদীমাতৃক বাংলার সুখ-দুঃখ, প্রেম-বিরহ, ধর্মীয় অনুভূতি, কৃষিজীবন, সামাজিক বৈষম্য ও প্রতিবাদ বাংলা গানে বহুমাত্রিক রূপ পেয়েছে। সময়ের ধারায় বাংলা সংগীত কয়েকটি প্রধান ধারায় বিকশিত হয়েছে।
লোকসংগীত যেমন: ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া, জারি, সারি, বাউল ও মুর্শিদি যেখানে গ্রামীণ জীবনদর্শন, মানবতাবাদ ও আধ্যাত্মিকতা স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত।
শাস্ত্রীয় সংগীত ধ্রুপদ, খেয়াল ও ঠুমরির মাধ্যমে রাগ রাগিণী নির্ভর শুদ্ধ সংগীত চর্চার ধারা বহন করে।
রবীন্দ্রসংগীতে প্রেম, প্রকৃতি, দেশ, মানবতা ও আত্মদর্শনের অনন্য মেলবন্ধন দেখা যায়।
নজরুলগীতিতে বিদ্রোহ, সাম্য, ধর্মীয় চেতনা ও রোমান্টিকতার শক্তিশালী প্রকাশ ঘটে।
আধুনিক বাংলা গান চলচ্চিত্র ও একক গায়নকেন্দ্রিক সংগীতধারায় সময়ের পরিবর্তনকে তুলে ধরে।
ব্যান্ড ও ফিউশন সংগীতে রক, পপ ও লোকসংগীতের আধুনিক সংমিশ্রণ লক্ষ্য করা যায়।
বাংলা সংগীত তাই কেবল বিনোদন নয়। এটি বাঙালির আত্মপরিচয়, ইতিহাস ও সাংস্কৃতিক দলিল।
বিশ্বসংগীত ভাষা ও ধারার বৈচিত্র্য:
বর্তমানে পৃথিবীতে প্রায় সাত হাজারের বেশি ভাষা প্রচলিত রয়েছে এবং প্রায় প্রতিটি ভাষার নিজস্ব সংগীতধারা আছে। ফলে পৃথিবীর সংগীত বৈচিত্র্য প্রায় সীমাহীন। বিশ্বসংগীতকে সাধারণভাবে কয়েকটি বড় শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। যেমন, শাস্ত্রীয় সংগীতের মধ্যে রয়েছে ভারতীয় হিন্দুস্তানি ও কর্ণাটক সংগীত এবং ইউরোপীয় ক্লাসিক্যাল সংগীত।
লোকসংগীত আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকা, এশিয়া ও ইউরোপের আঞ্চলিক সংস্কৃতির প্রতিনিধিত্ব করে।
ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক সংগীতে কাওয়ালি, নাশিদ, গসপেল, ভজন ও বৌদ্ধ চ্যান্ট অন্তর্ভুক্ত।
আধুনিক ও জনপ্রিয় সংগীতের মধ্যে পপ, রক, জ্যাজ, ব্লুজ, হিপ হপ, র্যাপ ও ইলেকট্রনিক সংগীত রয়েছে।
আদিবাসী সংগীত হিসেবে অস্ট্রেলিয়ান অ্যাবরিজিনাল ও আমাজনের আদিবাসী সংগীত উল্লেখযোগ্য।
ডিজিটাল প্রযুক্তির কারণে আজ এক দেশের গান মুহূর্তেই অন্য দেশে পৌঁছে যাচ্ছে। কোরিয়ান পপ, আফ্রোবিটস কিংবা ল্যাটিন পপের বৈশ্বিক জনপ্রিয়তা তারই প্রমাণ।
গান ও মানুষের মানসিক ও অর্থনৈতিক জীবন
গান মানুষের মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত কার্যকর। মনোবিজ্ঞানের গবেষণায় দেখা গেছে, সংগীত শোনার সময় মস্তিষ্কে ডোপামিন নিঃসৃত হয়, যা আনন্দ ও প্রশান্তির অনুভূতি বাড়ায়। বিষণ্নতা, উদ্বেগ ও মানসিক চাপ কমাতে সংগীত থেরাপি বর্তমানে বিশ্বব্যাপী ব্যবহৃত হচ্ছে।
শিশুদের ক্ষেত্রে সংগীত স্মরণশক্তি বাড়ায়, ভাষা শেখার দক্ষতা উন্নত করে এবং সৃজনশীলতা জাগ্রত করে। প্রবীণদের ক্ষেত্রেও গান স্মৃতিভ্রংশ ও একাকিত্ব কমাতে সহায়ক ভূমিকা রাখে।
অর্থনৈতিক দিক থেকেও সংগীত একটি বড় শিল্প। আন্তর্জাতিক সংগীত সংস্থার তথ্যমতে বৈশ্বিক সংগীত শিল্পের বাজারমূল্য প্রায় ছাব্বিশ বিলিয়ন মার্কিন ডলারেরও বেশি। এই শিল্প-শিল্পী ও কলাকুশলীদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে, চলচ্চিত্র ও বিজ্ঞাপন শিল্পকে সমৃদ্ধ করে এবং পর্যটন ও সাংস্কৃতিক অর্থনীতিকে গতিশীল করে। গান তাই শুধু আবেগ নয়। এটি অর্থনীতিরও একটি শক্তিশালী চালিকাশক্তি।
গান, দারিদ্র্যবিমোচন ও উন্নয়ন:
ডিজিটাল যুগে গান দারিদ্র্য থেকে উত্তরণের একটি বাস্তব সম্ভাবনা তৈরি করেছে। ইউটিউব, ফেসবুক ও স্পটিফাইয়ের মতো প্ল্যাটফর্ম প্রান্তিক শিল্পীদের বৈশ্বিক মঞ্চে তুলে ধরছে। একজন গ্রামীণ লোকশিল্পী আজ মোবাইল ফোন দিয়েই গান রেকর্ড করে আয় করতে পারছেন।
বাংলাদেশে বহু বাউল ও লোকশিল্পী ইউটিউবের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক পরিচিতি পেয়েছেন। ভারতের কোক স্টুডিও কিংবা পাকিস্তানের সংগীতভিত্তিক ব্র্যান্ডিং দেখিয়েছে, গান কীভাবে সংস্কৃতির পাশাপাশি অর্থনীতিকেও শক্তিশালী করতে পারে। রাষ্ট্রীয়ভাবে সংগীত শিক্ষায় বিনিয়োগ, কপিরাইট সুরক্ষা এবং লোকশিল্পীদের পৃষ্ঠপোষকতা গানভিত্তিক অর্থনীতিকে আরও এগিয়ে নিতে পারে। গান মানুষের জীবনে শুধুই বিনোদন নয়। এটি সাহস, স্বপ্ন ও সম্ভাবনার ভাষা। হতাশার অন্ধকারে গান জ্বালায় আশার প্রদীপ, দারিদ্র্যের মাঝেও দেখায় আলোর পথ। ব্যক্তিমানস থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি পর্যন্ত সব ক্ষেত্রেই সংগীতের ভূমিকা গভীর ও বহুমাত্রিক। একটি মানবিক, সৃজনশীল ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ গঠনে গান হতে পারে সবচেয়ে শক্তিশালী হাতিয়ার। তাই গান শুধু শোনা নয়, গানকে ধারণ করতে হবে, লালন করতে হবে। কারণ গানই জীবনের প্রকৃত বাতিঘর।
লেখক: সঙ্গীতজ্ঞ এবং গবেষক।

নির্বাচনের মৌসুম এলেই নির্বাচনী ইশতেহারের প্রসঙ্গ আমাদের সামনে আসে। আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে রাজনৈতিক দলগুলো ইশতেহার তৈরিতে ব্যস্ত। সংবাদমাধ্যমে শোনা যাচ্ছে, কেউ কেউ ১৫-২০টি অগ্রাধিকারের কথা বলছে, কেউ আবার উন্নয়ন, গণতন্ত্র, কর্মসংস্থান বা রাষ্ট্র সংস্কারের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে। কিন্তু প্রশ্ন হলো- এই ইশতেহারগুলো আদৌ কতটা দেশের উন্নয়নের কার্যকর দলিল হয়ে উঠতে পারবে? নাকি এটি মূলত নির্বাচনী প্রচারণার আনুষ্ঠানিক ভাষ্য হয়েই থেকে যাবে?
রাজনীতিবিদরা সবসময়ই রাজনীতির গুণগত পরিবর্তনের স্লোগান দিয়ে থাকেন। নির্বাচনের ঠিক আগ মুহূর্তে এই স্লোগানগুলো একটু বেশি শোনা যায়। শুধু রাজনীতির গুণগত পরিবর্তন নয়, গোটা রাষ্ট্রীয় কাঠামোর উন্নয়নে এবং গুণগত পরিবর্তনে তাদের প্রতিশ্রুতি অনবরত চলতে থাকে। কীভাবে জনগণের মনে স্থান পাওয়া যায় সেই লক্ষ্যটাও রাজনীতিবিদদের বেশি থাকে নির্বাচনের আগে। নির্বাচনের পরে সেগুলো মানতে হবে কী হবে না, মানতে পারবে কী পারবে না- সেই চিন্তাটা অতটা উপলব্ধিতে থাকে না। কারণ মূল লক্ষ্য হলো- যেভাবেই হোক ক্ষমতায় যাওয়া। সাধারণত রাজনীতিবিদদের ভালো মুখরোচক প্রতিশ্রুতি, বক্তব্য, বিবৃতিতে দেশের ভোটাররা মুগ্ধ হয়ে যায়। এমনকি রাজনৈতিক দলগুলো সেসব প্রতিশ্রুতি সমৃদ্ধ একটি নির্বাচনী ইশতেহার তৈরি করে জনগণকে শুনিয়ে দেয়। যেটাকে বলা হয় তাদের ক্ষমতা-পরবর্তী কার্যক্রম এবং প্রতিশ্রুতির রোডম্যাপভিত্তিক একটি লিখিত দলিল। ইতোমধ্যে প্রতিটি সরকারই ক্ষমতায় আসার আগে এ ধরনের লিখিত একটি দলিল জনগণের সামনে ধরিয়ে দিয়েছিল। আবার লিখিত দলিলের পাশাপাশি মুখে মুখেও নানা প্রতিশ্রুতির ঝুলি আমাদের আকৃষ্ট করেছে। কিন্তু পূর্ববর্তী খুব কম সরকারই তাদের লিখিত, অলিখিত প্রতিশ্রুতিগুলো যথাযথভাবে পূরণ করতে পেরেছে বলে মনে হয়। এমনকি এও দেখা গেছে যে, ইশতেহারে নির্বাচনের আগে দেওয়া লিখিত প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের রাজপথে আন্দোলন করতে হয়েছে।
নির্বাচনী ইশতেহারে অনেক সময় জনগণের জন্য চমক থাকে। বর্ণিত চমকগুলো যদি রাজনৈতিক দলগুলো যথাযথভাবে মনে রাখতো তাহলে দেশের রাজনীতির গুণগত পরিবর্তনে আর কোনো সমস্যা থাকত না। নির্বাচনের পূর্বে ইশতেহারে জনগণের জন্য যে চমক উপস্থাপন করা হয়, সেটি যারা ক্ষমতায় আসে এবং যারা ক্ষমতায় আসে না সকল দল থেকেই দেওয়া হয়। বেশিরভাগ ইশতেহারে অভীন্ন একটি বৈশিষ্ট্য থাকে, সেটি হলো জনগণের উন্নয়নের মাধ্যমে সমগ্র রাজনৈতিক কাঠামোতে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা। একটি রাজনৈতিক দলের গণতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার মাধ্যমেই ওইসব ইশতেহারভিত্তিক প্রতিশ্রুতি জনগণের কাছে উত্থাপন করা হয়। সকল রাজনৈতিক দলেরই জনগণের সামনে উত্থাপিত প্রতিশ্রুতি মোতাবেক কিছু মৌলিক বিষয় উল্লেখ থাকা দরকার। এমন কিছু বিষয় থাকে, যেগুলো ক্ষমতায় যাওয়া ন যাওয়ার সাথে সম্পর্ক নেই।
যেসব রাজনৈতিক দল নির্বাচনে অংশ নেয় এবং ইশতেহার প্রদান করে সে দলগুলো প্রত্যেকটি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসতে পারবে না- এটি স্বাভাবিক। কিন্তু ক্ষমতায় না গেলেও ভবিষ্যতে ক্ষমতায় যাওয়ার কার্যক্রম অব্যাহত থাকার কথা রাজনৈতিক দলগুলোর। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ক্ষমতায় যেতে না পারলেও সেই দলটি রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারে। কারণ যারা ক্ষমতায় আসে তাদের কোনো কোনোটি বিরোধী দলের ভূমিকায় থাকে। গণতন্ত্রে বিরোধী দলের অস্তিত্ব সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃত। আর বিরোধী দল হিসেবে একটি রাজনৈতিক দলের গণতন্ত্র শুদ্ধিকরণে বিশেষ ভূমিকা থাকে। বিশেষ করে জবাবদিহিমূলক সরকার প্রতিষ্ঠায় বিরোধী দলের কোনো বিকল্প নেই। সংসদীয় গণতন্ত্রের ঐতিহ্য বজায় রাখতে সংসদে ও সংসদের বাইরে বিরোধী দলের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে।
রাজনৈতিক দলের ইশতেহারে ক্ষমতায় গেলে কী করবে আর ক্ষমতায় না গেলে কী করবে সেটাও সুনির্দিষ্টভাবে জনগণের সমনে উত্থাপন করার ন্যায্যতা রয়েছে। ক্ষমতায় গেলে সরকারি দল বিরোধী দলের ওপর দমন নিপীড়ন করবে আর ক্ষমতায় না গেলে নির্বাচনকে অস্বীকার করবে এমন সংস্কৃতি থেকে বের হয়ে আসার প্রতিশ্রুতি ইশতেহারে সুস্পষ্ট হওয়া দরকার।
অন্যদিকে রাজনৈতিক দলগুলো ক্ষমতায় যেতে না পারলে বিরোধী দল হিসেবে ক্রমাগত সংসদ বর্জন করবে নাকি সংসদে উপস্থিত হবে এমন বিষয়ও ইশতেহারে উল্লেখ করে দায়িত্বশীল ভূমিকা রাখতে হবে রাজনৈতিক দলগুলোকে।
একজন নির্বাচিত নেতার ওপরই নির্ভর করে দেশের উন্নয়ন, সুশাসন এবং জনগণের আস্থার বিষয়টি। সকল রাজনৈতিক দল যদি নির্দিষ্ট মাপকাঠি বিবেচনা করে রাজনৈতিক কমিটমেন্ট রক্ষা করে তাহলে জনগণের আস্থা এবং নেতাদের রাজনৈতিক জবাবদিহিতার ক্ষেত্র প্রসারিত হয়। রাজনৈতিক নেতা দুর্নীতিবাজ, জনবিচ্ছিন্ন হওয়া সত্ত্বেও তাকে মনোনয়ন দিয়ে দেশের উন্নয়ন আশা করাটা মোটেও যুক্তিসঙ্গত নয়।
রাজনৈতিক দলগুলোকে একটি স্থিতিশীল গণতান্ত্রিক পরিবেশ বজায় রাখতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর বিরোধী দলগুলোকে সাংবিধানিক সকল সুযোগ-সুবিধায় বাধা সৃষ্টি না করার বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে ইশতেহারভুক্ত করা উচিত। সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতা হস্তান্তর এবং সরকারের মেয়াদ শেষে নির্বাচনকালীন সরকার নিয়ে টানাপোড়েনের রাজনীতিমুখী না হওয়া রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতিশ্রুতিতে থাকারও ন্যায্যতা রয়েছে। কাজেই একটি রাজনৈতিক দল কীভাবে রাজনীতির গুণগত পরিবর্তন আনতে পারে সেটা তার ইশতেহারেই সুস্পষ্ট করা সম্ভব। এ ক্ষেত্রে ক্ষমতায় আসুক আর না আসুক গণতন্ত্র তথা সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য সকল রাজনৈতিক দলকে অভিন্ন কিছু মৌলিক বিষয় ইশতেহারে লিপিবদ্ধ করার বিষয়টি সময়োপযোগী এবং বাস্তবসম্মত।
ইশতেহার মূলত একটি রাজনৈতিক দলের রাষ্ট্রচিন্তার লিখিত রূপ। এটি বলে দেয় দলটি ক্ষমতায় গেলে কী করবে, কোন সমস্যাকে কীভাবে সমাধান করতে চায় এবং রাষ্ট্র পরিচালনায় তাদের দৃষ্টিভঙ্গি কী। উন্নত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোতে ইশতেহারকে কেবল প্রতিশ্রুতির কাগজ হিসেবে দেখা হয় না; বরং এটি ভবিষ্যৎ সরকারের নীতি কাঠামোর একটি চুক্তিপত্র হিসেবে বিবেচিত হয়। নাগরিকরা ইশতেহারের ভিত্তিতেই ভোট দেন এবং পরবর্তী সময়ে সরকারকে সেই ইশতেহারের আলোকে জবাবদিহির মুখোমুখি করেন। বাংলাদেশে এই সংস্কৃতি এখনো পুরোপুরি গড়ে ওঠেনি, ফলে ইশতেহার অনেক সময় বাস্তব উন্নয়নের হাতিয়ার না হয়ে রাজনৈতিক ভাষণের অংশে পরিণত হয়।
নির্বাচনী ইশতেহার কেবল রাজনৈতিক দল বা প্রার্থীর পরিকল্পনার তালিকা নয়; এটি ভোটার এবং রাজনীতির মধ্যে একটি বিশ্বাসযোগ্য চুক্তি। উন্নত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোতে ইশতেহার তৈরি করা হয় খুব যত্নের সঙ্গে, কারণ এটি নির্বাচনের পর বাস্তবায়নের মাধ্যমে গণতন্ত্রের প্রতি জনগণের আস্থা নির্ধারণ করে। উন্নত রাষ্ট্রে ইশতেহারের প্রধান ভিত্তি হলো- সামাজিক সমস্যা ও নাগরিক চাহিদার যথার্থ মূল্যায়ন। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবেশ, সামাজিক সুরক্ষা, নাগরিক অধিকার এবং কর্মসংস্থানের মতো বিষয়গুলোকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। ইশতেহার প্রস্তুতকারকরা শুধু জনপ্রিয় প্রতিশ্রুতি দেন না; তারা নিশ্চিত করে যে এই প্রতিশ্রুতিগুলো বাস্তবায়নযোগ্য এবং বাজেট ও প্রশাসনিক সক্ষমতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।
আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো- স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা। উন্নত গণতান্ত্রিক দেশগুলোতে প্রতিশ্রুতি দানের সঙ্গে সঙ্গে নির্দিষ্ট সূচক এবং সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়। যেমন, শিক্ষার মান উন্নত করার জন্য নির্দিষ্ট ক্যালেন্ডার, স্বাস্থ্যসেবার প্রসার বাড়ানোর জন্য নির্দিষ্ট প্রকল্প ও অগ্রগতি রিপোর্ট। ভোটাররা পরে এগুলো যাচাই করতে পারে, এবং ফলাফল অনুযায়ী দলের ওপর গণতান্ত্রিক দায়িত্ব আরোপ করা সম্ভব হয়। সাধারণ নাগরিকের অংশগ্রহণ ও মতামত গ্রহণ ইশতেহার তৈরির আরেকটি মূল ভিত্তি। উন্নত রাষ্ট্রে রাজনৈতিক দলগুলো ভোটারদের সঙ্গে আলোচনা করে, জরিপ ও মতামত সংগ্রহ করে, এবং ইশতেহারে বাস্তব চাহিদা প্রতিফলিত করে। এটি ভোটারদের জন্য স্বচ্ছতা বাড়ায় এবং নির্বাচনের আগে রাজনৈতিক সংলাপের পরিবেশ তৈরি করে।
নীতিনির্ভরতা এবং বাস্তবায়নযোগ্যতার ভারসাম্য উন্নত রাষ্ট্রের ইশতেহারকে শক্তিশালী করে। শুধু প্রচারণার জন্য অতিরঞ্জিত প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় না; প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের সক্ষমতা, প্রশাসনিক রূপায়ণ এবং অর্থনৈতিক বাস্তবতা বিবেচনা করা হয়। এটি ইশতেহারকে কেবল নির্বাচনী কাগজ নয়, বরং রাজনৈতিক দায়িত্বের একটি চুক্তিতে পরিণত করে।
উন্নত গণতন্ত্রে নির্বাচনী ইশতেহার জনগণকে দলের নীতি, লক্ষ্য ও অগ্রাধিকারের সঙ্গে যুক্ত রাখে। এটি ভোটারদের সচেতন অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে, রাজনৈতিক সংলাপকে শক্তিশালী করে এবং নির্বাচনের ফলাফল গ্রহণযোগ্য ও স্থিতিশীল করে। একটি সুনির্দিষ্ট, বাস্তবসম্মত এবং জবাবদিহিমূলক ইশতেহারই উন্নত রাষ্ট্রের গণতন্ত্রকে কার্যত শক্তিশালী রাখে।
বাংলাদেশের অন্যতম বাস্তবতা হলো- অনেক প্রতিশ্রুতি ইশতেহারে থেকে গেলেও তার বাস্তবায়ন বা মূল্যায়নের স্পষ্ট কাঠামো থাকে না। উদাহরণ হিসেবে কর্মসংস্থানের প্রশ্নটি ধরা যায়। প্রায় প্রতিটি নির্বাচনী ইশতেহারেই তরুণদের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টির কথা বলা হয়। কিন্তু কত বছরে কত কর্মসংস্থান হবে, কোন খাতে হবে, বেসরকারি ও সরকারি খাতের ভূমিকা কী- এই প্রশ্নগুলোর নির্দিষ্ট উত্তর ইশতেহারে খুব কমই পাওয়া যায়। ফলে নির্বাচন শেষে এই প্রতিশ্রুতি নিয়ে নাগরিকদের জবাবদিহি দাবি করার সুযোগও সীমিত থাকে। ইশতেহার যদি সত্যিকার অর্থে উন্নয়নের দলিল হিসেবে সামনে রাখতে হয় তাহলে তা দেশের বাস্তব সমস্যাগুলোর মুখোমুখি করতে হবে।
লেখক: অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের এক যুগসন্ধিক্ষণে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান এমন এক সময়ে রাষ্ট্রক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে আবির্ভূত হয়েছিলেন, যখন জাতি এক গভীর অনিশ্চয়তা, রাজনৈতিক শূন্যতা এবং অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হচ্ছিল। ১৯৭৫ সালের পরবর্তী সেই অস্থির সময়ে সিপাহি-জনতার বিপ্লবের মধ্য দিয়ে তার উত্থান কেবল একজন সামরিক কর্মকর্তার রাষ্ট্রপ্রধান হওয়া ছিল না, বরং তা ছিল একটি জাতির পরিচয় সংকট নিরসন এবং গণতন্ত্রের নতুন অভিযাত্রা শুরুর এক ঐতিহাসিক মাহেন্দ্রক্ষণ। জিয়াউর রহমানের রাষ্ট্রনায়কোচিত দূরদর্শিতার প্রধানতম দিক ছিল তার প্রবর্তিত ‘বহুদলীয় গণতন্ত্র’, যা বাংলাদেশকে একদলীয় শাসনের নিগড় থেকে মুক্ত করে একটি অংশগ্রহণমূলক এবং প্রতিযোগিতামূলক রাজনৈতিক কাঠামোর ওপর দাঁড় করিয়েছিল। তিনি কেবল একজন শাসক ছিলেন না, বরং ছিলেন জনবান্ধব উন্নয়নের এক অনন্য রূপকার। তার রাজনীতির মূলে ছিল সাধারণ মানুষ, কৃষি এবং আত্মনির্ভরশীলতা।
তিনি ‘বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ’ নামক এক অন্তর্ভুক্তিমূলক পরিচয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন, যা জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে এ দেশের প্রতিটি নাগরিককে একসূত্রে গেঁথেছিল। এই দর্শনের মাধ্যমে তিনি এ দেশের মানুষের মাঝে নিজস্ব সংস্কৃতির প্রতি মমত্ববোধ এবং সার্বভৌমত্বের প্রতি অটল চেতনা জাগ্রত করেছিলেন। বহুদলীয় গণতন্ত্রের প্রবক্তা হিসেবে জিয়াউর রহমানের ভূমিকা অনন্য এই কারণে যে, তিনি রাষ্ট্রীয় কাঠামোর ভেতর থেকেই রাজনৈতিক দল গঠনের অধিকার পুনরুজ্জীবিত করেছিলেন। ১৯৭৫ সালের পূর্ববর্তী শাসনব্যবস্থায় যখন দেশে সকল রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ করে একটি মাত্র দলের শাসন কায়েম করা হয়েছিল, তখন জিয়াউর রহমান রাষ্ট্রক্ষমতায় এসে সেই সংকীর্ণতা ভেঙে দেন। তিনি সংবাদপত্র ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ফিরিয়ে দেন এবং রাজনৈতিক দলগুলোর কর্মকাণ্ড পরিচালনার আইনগত বাধা অপসারণ করেন। তাঁর হাত ধরেই বাংলাদেশে জাতীয়তাবাদী রাজনীতির একটি শক্তিশালী ধারা সৃষ্টি হয়, যা আজও এ দেশের জনমানসে গভীরভাবে প্রোথিত।
শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান অনুধাবন করেছিলেন যে, কোনো জাতির উন্নয়ন কেবল উপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া নির্দেশ দিয়ে সম্ভব নয়, বরং এর জন্য প্রয়োজন জনসাধারণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ এবং একটি সুস্থ রাজনৈতিক প্রতিযোগিতা। ১৯৭৫ সালে চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে দেশে যে একদলীয় শাসনব্যবস্থা কায়েম করা হয়েছিল, তাতে রাজনৈতিক বৈচিত্র্য ও ভিন্নমতের কোনো স্থান ছিল না। তিনি রাজনৈতিক দল বিধি (PPR) প্রবর্তন করেন এবং পর্যায়ক্রমে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করেন। এটি ছিল বাংলাদেশের রাজনীতির ইতিহাসে এক বড় ধরনের বাঁক বদল। তিনি বামপন্থি থেকে শুরু করে ডানপন্থি সব মতাদর্শের মানুষের জন্য একটি উন্মুক্ত প্ল্যাটফর্ম তৈরি করেছিলেন।
প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের শাসনব্যবস্থা ছিল মূলত কর্মমুখী ও উৎপাদনমুখী। তিনি বিশ্বাস করতেন, প্রকৃত গণতন্ত্র তখনই সফল হয় যখন সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি ঘটে। এ কারণে তিনি ‘উনিশ দফা’ কর্মসূচি ঘোষণা করেছিলেন, যা ছিল গ্রামীণ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের একটি পূর্ণাঙ্গ রূপরেখা। এই ১৯-দফা ছিল শহীদ
প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের রাষ্ট্র পরিচালনার ‘ম্যাগনা কার্টা’ বা মূল সনদ। কর্মসূচির প্রথম দিকেই ছিল দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা এবং জাতীয় সংহতি সুদৃঢ় করা। অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য তিনি কৃষিভিত্তিক উন্নয়নের ওপর জোর দিয়েছিলেন। ১৯-দফার মাধ্যমে তিনি নিরক্ষরতা দূরীকরণ, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ এবং গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নের একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন। এই কর্মসূচির উল্লেখযোগ্য দিক ছিল ‘গণতন্ত্রের সুফলকে তৃণমূল পর্যায়ে পৌঁছে দেওয়া’। তিনি মনে করতেন, যতক্ষণ পর্যন্ত সাধারণ মানুষের অন্নের সংস্থান না হবে এবং তারা শিক্ষিত না হবে, ততক্ষণ গণতন্ত্র কেবল শিক্ষিত উচ্চবিত্তের বিলাসিতা হয়ে থাকবে। ১৯-দফার প্রতিটি দফা ছিল জনবান্ধব এবং বাস্তবায়নযোগ্য, যা তৎকালীন আমলাতন্ত্রকে ফাইলবন্দি কাজের বাইরে মাঠপর্যায়ে নিয়ে যেতে বাধ্য করেছিল।
জিয়াউর রহমানের শাসনামলে ‘খাল খনন’ আন্দোলন ছিল আধুনিক বাংলাদেশের ইতিহাসের প্রথম এবং সফলতম স্বেচ্ছাশ্রমভিত্তিক গণআন্দোলন। তৎকালীন সময়ে সেচ সুবিধার অভাবে বাংলাদেশের বিশাল কৃষি জমি অনাবাদী পড়ে থাকত। জিয়ার লক্ষ্য ছিল কৃষি উৎপাদন দ্বিগুণ করা এবং দেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করা। তিনি কেবল সরকারের বাজেট বা বিদেশি সাহায্যের ওপর নির্ভর না করে দেশের জনশক্তিকে কাজে লাগানোর পরিকল্পনা করেন। ১৯৭৯ সালে তিনি এই বৃহৎ কর্মসূচি শুরু করেন। নিজে কোদাল হাতে মাথায় মাটির ঝুড়ি নিয়ে যখন তিনি খালে নামলেন, তখন তা সারা দেশে এক নজিরবিহীন দেশপ্রেমের জোয়ার সৃষ্টি করেছিল। এর ফলে হাজার হাজার মাইল খাল খনন ও পুনঃখনন করা সম্ভব হয়েছিল, যা সেচ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটায়। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে দেশ আমদানিনির্ভরতা থেকে বেরিয়ে আসতে শুরু করে। এই খাল খনন কর্মসূচি কেবল অর্থনৈতিক সাফল্য ছিল না, এটি ছিল ‘জাতীয়তাবাদের ব্যবহারিক প্রয়োগ’। এটি প্রমাণ করেছিল যে, ঐক্যবদ্ধ জনশক্তি ও সঠিক নেতৃত্ব থাকলে সীমিত সম্পদ দিয়েও অসাধ্য সাধন করা সম্ভব।
জনবান্ধব রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে তাঁর আর একটি বড় কৃতিত্ব ছিল পল্লী বিদ্যুৎ বোর্ড গঠন করা। তিনি জানতেন যে, গ্রাম বাংলার উন্নয়ন ছাড়া জাতীয় উন্নয়ন সম্ভব নয়, আর আধুনিক জীবনের অন্যতম প্রধান শর্ত হলো বিদ্যুৎ। তার এই দূরদর্শী সিদ্ধান্তের ফলেই আজ বাংলাদেশের নিভৃত পল্লী অঞ্চলেও বিদ্যুতের আলো পৌঁছেছে। স্থানীয় সরকার কাঠামোর শক্তিশালীকরণে তিনি ‘গ্রাম সরকার’ ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছিলেন, যাতে গ্রামের মানুষ তাদের নিজস্ব সমস্যার সমাধান নিজেরাই করতে পারে। এটি ছিল ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের এক অনন্য মডেল। বর্তমানে আমরা যাকে তৃণমূল উন্নয়ন বা গ্রাসরুট ডেভেলপমেন্ট বলি, শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়া সেই সত্তর দশকেই তা প্রয়োগ করেছিলেন। তিনি নিজে বছরের সিংহভাগ সময় কাটাতেন দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে। তার এই ‘পথসভা’ এবং ‘জনসংযোগ’ রাজনীতিকে সাধারণ মানুষের অত্যন্ত কাছাকাছি নিয়ে গিয়েছিল।
প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের আধুনিক রাষ্ট্র গঠনের পরিকল্পনায় প্রশাসনিক কাঠামো পুনর্গঠন ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি অসংখ্য সরকারি দপ্তর, অধিদপ্তর এবং মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা ও সংস্কার করেছিলেন। বাংলাদেশের বিশাল যুবসমাজকে উৎপাদনমুখী করতে তিনি প্রথম ‘যুব মন্ত্রণালয়’ ও ‘যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর’ প্রতিষ্ঠা করেন। নারীদের রাষ্ট্রীয় মূলধারায় সম্পৃক্ত করতে গঠন করেন ‘মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয়’ চালু করেন। বিদেশে জনশক্তি রপ্তানিকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে ১৯৭৬ সালে তার হাতেই প্রতিষ্ঠিত হয় ‘জনশক্তি ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান ব্যুরো (BMET)’, যা আজ দেশের রেমিট্যান্স অর্থনীতির প্রধান স্তম্ভ। এছাড়াও গ্রামীণ উন্নয়নের লক্ষ্যে ‘পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (REB)’, ধর্মীয় মূল্যবোধ রক্ষায় ‘ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়’ এবং ‘মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর’-এর মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানগুলো তাঁরই প্রশাসনিক দূরদর্শিতার ফসল। তিনি বিশ্বাস করতেন একটি শক্তিশালী প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ছাড়া উন্নয়ন টেকসই হতে পারে না।
প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের কূটনীতিও ছিল অত্যন্ত প্রজ্ঞাময়। তিনি মুসলিম উম্মাহর সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক দৃঢ় করেন এবং মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে এ দেশের বিশাল শ্রমবাজারের দুয়ার খুলে দেন। তার পররাষ্ট্রনীতির মূল ভিত্তি ছিল ‘সবার সাথে বন্ধুত্ব, কারো সাথে বৈরিতা নয়’। এর সবচেয়ে বড় সাফল্য হলো দক্ষিণ এশীয় দেশগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সংহতির অভিন্ন প্ল্যাটফর্ম ‘সার্ক’ (SAARC) প্রতিষ্ঠার ঐতিহাসিক উদ্যোগ। ১৯৮০ সালে তিনি দক্ষিণ এশিয়ার সাতটি দেশের রাষ্ট্রপ্রধানদের কাছে আঞ্চলিক সহযোগিতার প্রস্তাব দিয়ে চিঠি পাঠান। এছাড়া চীনের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্কের উন্নয়ন এবং জাপানের সঙ্গে অর্থনৈতিক অংশীদারিত্বের সূচনা তাঁরই কৃতিত্ব। ফারাক্কা বাঁধের কারণে বাংলাদেশের পানিসংকটের বিষয়টি তিনি জাতিসংঘে উত্থাপন করেছিলেন, যা বাংলাদেশের ন্যায্য দাবির পক্ষে আন্তর্জাতিক সমর্থন আদায় করেছিল।
শহীদ জিয়ার সততা ও সাদামাটা জীবনযাপন তাকে সাধারণ মানুষের হৃদয়ে এক বিশেষ উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছিল। তিনি বারবার বলতেন, ‘ব্যক্তির চেয়ে দল বড়, আর দলের চেয়ে দেশ বড়’। তার এই দর্শনের প্রতিফলন দেখা যেত তার প্রতিটি রাজনৈতিক সিদ্ধান্তে। বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে জিয়াউর রহমানের অবস্থান কেবল একটি নির্দিষ্ট মেয়াদে ক্ষমতা উপভোগকারী শাসক হিসেবে নয়, বরং তিনি ছিলেন এমন একজন স্থপতি যিনি একটি তলাবিহীন ঝুড়ির অপবাদ পাওয়া দেশটিকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে শিখিয়েছিলেন। তার বহুদলীয় গণতন্ত্রের প্রবর্তন ছিল সেই সময়ের দাবি, যা বাংলাদেশকে একনায়কতন্ত্রের অন্ধকার থেকে মুক্তি দিয়েছিল।
শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ছিলেন আধুনিক বাংলাদেশের উন্নয়নের এক বিজ্ঞানসম্মত ব্লুপ্রিন্ট রচয়িতা। তার বহুদলীয় গণতন্ত্রের চর্চা এবং জনমুখী শাসনব্যবস্থা এ দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির এক ঐতিহাসিক দলিল। তার প্রবর্তিত পথ ধরেই বাংলাদেশ আজ এগিয়ে যাচ্ছে। আধুনিক বাংলাদেশের স্থপতি হিসেবে তার নাম ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে, কারণ তিনি কেবল রাষ্ট্র পরিচালনা করেননি, বরং রাষ্ট্রকে একটি টেকসই ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে দিয়ে গেছেন। তার সংগ্রামী জীবন এবং দেশপ্রেমের মহিমা আগামী প্রজন্মের কাছে সবসময় অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে।