
’৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধ আমাদের জাতীয় জীবনের সব থেকে গৌরবময় অধ্যায়। ৭১ সালের ২৬ মার্চ স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ইতোমধ্যে স্বাধীনতার ৫২ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। স্বাধীনতা অর্জনের পর বাংলাদেশ অনেক কিছু অর্জন করেছে। যদিও মুক্তিযুদ্ধের অনেক স্বপ্ন এখনো অধরা রয়ে গেছে। জাতি হিসাবে বাংলাদেশকে আরও অনেক পথ পাড়ি দিতে হবে। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ধীরে ধীরে বাংলাদেশ কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনের পথে হাঁটছে।
এই সময়ের ভিতর মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস নিয়ে বহু গ্রন্থ রচিত হয়েছে। এসব গ্রন্থে মুক্তিযুদ্ধের অজানা ঘটনা ও অনালোকিত অধ্যায় পাদপ্রদীপের আলোয় এসেছে। তারপরেও অনেক ঘটনা, মুক্তিযুদ্ধের বহু গৌরবদীপ্ত স্মৃতি ও বীরগাঁথা আজও স্বীকৃতি পায়নি। অনেক অর্জন ও স্বীকৃতি বেহাত অথবা বেহাত হয়ে যাওয়ার পথে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় ময়মনসিংহের পাগলা থানার গৌরব। মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে পাগলা থানা স্বতন্ত্র কোনো পরিচয় ছিল না। পাগলা ছিল গফরগাঁও থানা অন্তর্গত দত্তের বাজার ইউনিয়নের ছোট্ট একটি গ্রাম্য বাজার। তদুপরি অঞ্চলটি গফরগাঁও উপজেলার দক্ষিণের ৮টি ইউনিয়নের প্রায় মধ্যবিন্দু হওয়ার সব সময় এর একটি রাজনৈতিক গুরুত্ব ছিল। ২০১২ সালে পাগলা একটি নতুন থানা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে।
শুধু ময়মনসিংহের মধ্যে নয়- বাংলাদেশের ভিতর পাগলা অঞ্চলে মুক্তিযুদ্ধের অনেক গৌরবজনক ঘটনা ঘটে; কিন্তু প্রশাসনিক পরিচয়ের কারণে পাগলা অঞ্চলে সংগঠিত সকল যুদ্ধ ও যুদ্ধ সম্পর্কিত সকল ঘটনা- গৌরবময় বীরগাঁথা গফরগাঁও-এর নামে প্রচারিত হয়েছে। এই অঞ্চলের সিংহভাগ মুক্তিযুদ্ধ পাগলা থানার ৮টি ইউনিয়নের বিভিন্ন অঞ্চলে সংগঠিত হয়েছে।
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৭ মার্চ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে তার ঐতিহাসিক ভাষণে, ‘এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম’। মূলত এর মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার অনানুষ্ঠানিক ঘোষণা প্রদান করেন। তিনি আরও ঘোষণা করেন, ‘প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তুলুন, আমি যদি হুকুম দিবার নাও পারি, তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে।’ এই ঘোষণার পর বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে মুক্তিযুদ্ধের ট্রেনিং শুরু হয়ে যায়। একইভাবে তৎকালীন ঢাকা জেলা বর্তমান গাজীপুর জেলার কাওরাইদ কে এন উচ্চ বিদ্যালয়ে মুক্তিযুদ্ধের প্রাথমিক ট্রেনিং শুরু হয়। অঞ্চলটি গাজীপুর জেলার আওতাভুক্ত হলেও ময়মনসিংহ পাগলা থানার সীমান্তবর্তী অঞ্চল। এই ট্রেনিং সেন্টারের মূল নেতৃত্ব দিয়েছেন তিনজন নেতা। তন্মধ্যে সাইদুর রহমান সিরাজ তৎকালীন গফরগাঁও থানা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও মো. মফিজুল হক চেয়ারম্যান তৎকালীন গফরগাঁও থানা আওয়ামী লীগের ও ময়মনসিংহ সদর মহকুমা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক। তাদের দুজনের বাড়ি বর্তমান পাগলা থানার পাইথল ও নিগুয়ারী ইউনিয়নে। অপরজন কাওরাইদ ইউনিয়নের মনির উদ্দিন ফকির ছিলেন শ্রীপুর থানা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক। একইভাবে মশাখালী রেলস্টেশন সংলগ্ন চাইড়বাড়িয়া মাদ্রাসা মাঠে আরফান আলী চেয়ারম্যান, সাইদুর রহমান কামাল ও শাহাদাত হোসেন মাস্টার।
২৫ মার্চ পাকিস্তান বাহিনী ঢাকায় গণহত্যা চালায়। বঙ্গবন্ধু মুজিব গ্রেপ্তার হওয়ার পূর্ব মুহূর্তে ২৫ মার্চের রাত ১২টার পর অর্থাৎ ২৬ মার্চ বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। স্বাধীনতা ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে পাগলা থানার বিভিন্ন অঞ্চল যেমন- গয়েশপুর মাদ্রাসা মাঠে, মশাখালী চাইড়বাড়িয়া মাদ্রাসা, মাইজবাড়ি স্কুল মাঠ, দক্ষিণ হাড়িনা পার্বতীর মাঠ, দাওয়াদাইর প্রাইমারি স্কুল মাঠ, ছাপিলা মান্দারগড় প্রাইমারি স্কুল মাঠ, কুরচাই, তললী প্রাইমারি স্কুল মাঠ, অললী প্রাইমারি স্কুল মাঠে মুক্তিযুদ্ধের প্রাথমিক ট্রেনিং সেন্টার স্থাপিত হয়। এসব ট্রেনিং সেন্টারের নেতৃত্ব ও সংগঠকের দায়িত্ব পালন করেন তৎকালীন গফরগাঁও থানা আওয়ামী লীগ সভাপতি সাইদুর রহমান সিরাজ, গফরগাঁও থানা ও ময়মনসিংহ সদর মহকুমা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মো. মফিজুল হক চেয়ারম্যান, অধ্যাপক শেখ রেয়াজ উদ্দিন আহমদ, আরফান আলী চেয়ারম্যান, সাইদুর রহমান কামাল, শাহাদাত হোসেন মাস্টার, ইকবাল ই আলম কামাল এ কে এম নিজাম উদ্দিন মাস্টার প্রমুখ।
মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর মে-জুন মাসের দিকে সাইদুর রহমান সিরাজ, মফিজুল হক চেয়ারম্যান, অধ্যাপক শেখ রেয়াজ উদ্দিন আহমদ প্রমুখ কসবা সি অ্যান্ড বি ব্রিজ পার হয়ে আগরতলা হাঁপানিয়া যুব শিবিরে যান। সেখানে সাইদুর রহমান সিরাজ যমুনা যুব শিবিরে উপপ্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। আবার সোনার বাংলা যুব শিবিরের চিফ ও ডেপুটি চিফ হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন যথাক্রমে- অধ্যাপক শামসুল হুদা এম এন এ ও অধ্যাপক শেখ রেয়াজ উদ্দিন আহমদ। মফিজুল হক ও গিয়াস উদ্দিন মাস্টার পলিটিকাল মটিভেটর হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। ট্রেনিং কার্যক্রম শেষ হলে ৩নং সেক্টরের সেকেন্ড ইন কমান্ড ক্যাপ্টেন নুরুজ্জামান মফিজুল হককে গফরগাঁও থানা মুক্তিবাহিনীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা হিসাবে নিয়োগ দেন। তার ওপর ফজলুল হক কোম্পানি, হাবিবুল হক মন্টু কোম্পানি ও এম এ কাদির কোম্পানির দায়িত্ব ন্যস্ত করে গফরগাঁও ও ভালুকা অঞ্চলে পাঠিয়ে দেন। শুধু মফিজুল হক নয় তার সহোদর দুই ভাই বজলুল হক ও জহিরুল হক মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তন্মধ্যে জহিরুল হক নভেম্বর মাসের ২০ তারিখ ভালুকা অঞ্চলের ৯নং বাঁধ এলাকায় পাকিস্তান বাহিনীর বিরুদ্ধে সম্মুখ সমরে শহীদ হন। গফরগাঁও অঞ্চলের তিনজন কোম্পানি কমান্ডারের মতো চতুর্থ কোম্পানি কমান্ডার ইকবাল ই আলম কামালের বাড়িও পাগলা থানায়।
গফরগাঁও উপজেলার তালিকাভুক্ত মুক্তিযোদ্ধাদের সিংহভাগ মুক্তিযোদ্ধা বর্তমান পাগলা থানার ৮ ইউনিয়নের বাসিন্দা। গফরগাঁও-এর অধিকাংশ মুক্তিযুদ্ধ সংগঠিত হয়েছে বর্তমান পাগলা থানার বিভিন্ন অঞ্চলে।
পাগলা থানা এলাকায় মুক্তিবাহিনী পাকিস্তান বাহিনীর বিরুদ্ধে অনেক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে। ১ সেপ্টেম্বর ইকবাল ই আলম কামালের নেতৃত্বে মুক্তিবাহিনী রাজাকার ক্যাম্প দখল করে। এই যুদ্ধে মুক্তিবাহিনী বিপুল পরিমাণ অস্ত্র, বিস্ফোরক ও রসদ দখল করে। যুদ্ধে মাইজউদ্দীন ফকির নামে একজন মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হন। সেপ্টেম্বর মাসের ১১-১২ তারিখ ইকবাল ই আলম কামালের নেতৃত্বে মুক্তিবাহিনী বাগেরগাঁও- বাকশীতে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। এই যুদ্ধে কয়েকজন পাকিস্তান বাহিনীর একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা নিহত হন। এই যুদ্ধে আবদুল মজিদ, আবদুর রশিদ, আবদুস সাহিদ, মহর চাঁদ, মনিন্দ্র মোদক, আবদুল হাই, আফাজ, মফিজসহ ১১ জন নিরীহ গ্রামবাসী নিহত হন। ১৭ সেপ্টেম্বর ইকবাল ই আলম কামাল কোম্পানি দক্ষিণ পাড়ায় একটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। যুদ্ধে মোবারক ও আলাউদ্দীন নামে দুজন শহীদ হন। ২৪-২৫ সেপ্টেম্বর সীমাখালীর দ্বিতীয় যুদ্ধে মুক্তিবাহিনীর মাহতাব ও মান্নান শহীদ হোন। উস্থি- নয়াবাড়ির যুদ্ধে মুক্তিবাহিনীর হাতে পাকিস্তান বাহিনীর কয়েকজন সদস্য নিহত হন। পরবর্তীতে ইকবাল ই আলম কামাল কোম্পানি পাকিস্তান বাহিনীর বারইগাঁও ক্যাম্পে আকাশ করে সাফল্য পায়। ৯ ডিসেম্বর মুক্ত গফরগাঁওয়ে ইকবাল ই আলম কামাল কোম্পানির নেতৃত্বে মুক্তিবাহিনী বাংলাদেশের স্বাধীন পতাকা উত্তোলন করেন।
অন্যদিকে গফরগাঁও থানা মুক্তিবাহিনীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা মফিজুল হক চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে ফজলুল হক কোম্পানি ও হাবিবুল হক মন্টু কোম্পানি অনেক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। ভারত থেকে ট্রেনিং গ্রহণ করে মফিজুল হক, ফজলুল হক ও মো. সেলিমের নেতৃত্বে মুক্তিবাহিনীর একটি কোম্পানি নিয়ে গফরগাঁও-পাগলা ও ভালুকায় পদার্পণ করেন। তন্মধ্যে দুটি সেকশন ভালুকার মেজর আফসার উদ্দিনের সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। মফিজুল হক চেয়ারম্যান, ফজলুল হক ও এম এ সেলিম মূল বাহিনী নিয়ে প্রসাদপুর ওমর মেম্বারের বাড়িতে ঘাঁটি স্থাপন করেন। এই ঘাঁটি থেকে মুক্তিযোদ্ধারা ফরচুঙ্গি - শিলার রেলব্রিজে ও মশাখালী স্টেশনে হামলা চালিয়ে ব্যাপক সাফল্য পায়। মশাখালী রেলস্টেশনের যুদ্ধে মুক্তিবাহিনীর কাছে ৬৫ জন রাজাকার আত্মসমর্পণ করেন। কিছুদিন পর অতর্কিতে পাকিস্তান বাহিনী ওমর মেম্বারের বাড়িতে অবস্থানরত মুক্তিবাহিনীর ওপর হামলা চালায়। মুক্তিযোদ্ধারা প্রাথমিক প্রতিরোধ গড়ে তুললেও আক্রমণের তীব্রতায় একপর্যায়ে পিছু হটে যেতে বাধ্য হয়। যুদ্ধে হেলাল নামে একজন কিশোর মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হন।
ইব্রাহিম খান একজন সাহসী মুক্তিযোদ্ধা। পাকিস্তান বাহিনী কাওরাইদ থেকে রওনা হয়ে নিগুয়ারী গৈয়ারপাড়ের রয়ান বিল পর্যন্ত অগ্রসর হলে শিলানদীর তীরে গৈয়ারপাড়ে অবস্থান নিয়ে স্টেনগান দিয়ে গুলি করে পাকিস্তান বাহিনী অগ্রগতিকে রোধ করেন। ১৯ নভেম্বর পাকিস্তান বাহিনী কাওরাইদ থেকে রওনা হয়ে নান্দিয়াসাঙ্গন- নিগুয়ারী খান বাড়ি হয়ে ত্রিমোহনীতে অবস্থানরত মুক্তিবাহিনীর ওপর হামলা চালায়। মুক্তিবাহিনী তললী চৌকিদার বাড়ির ঘাট হয়ে সুতারচাপরে আশ্রয় নেয়। সেখানেও পাকিস্তান বাহিনী মুক্তিবাহিনীর ওপর হামলা চালায়। এই যুদ্ধে আ. রাজ্জাক, সালাহউদ্দিন, সুলতান ও মান্নানসহ অন্তত ৭ জন মুক্তিযোদ্ধা ও নিরীহ মানুষ শহীদ এবং নিহত হন। একই দিন পাকিস্তান বাহিনী নিগুয়ারীতে অপারেশন শেষ করে কাওরাইদ ফিরে যাওয়ার পথে হাবিবুল হক মন্টু কোম্পানি মুক্তিযোদ্ধারা কেল্লারপাড়ে পাকিস্তান বাহিনীর অবস্থানের ওপর একটি সফল আক্রমণ পরিচালনা করে। এই যুদ্ধে পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর বেশ কয়েকজন সদস্য নিহত ও আহত হয়।
নভেম্বর মাসে মোশাররফ হোসেন রতনের নেতৃত্বে শিলার বাজার যুদ্ধে মুক্তিবাহিনী পাকিস্তান বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করে। একপর্যায়ে পাকিস্তান বাহিনীর আক্রমণের তীব্রতায় মুক্তিবাহিনী পিছু হটে যেতে বাধ্য হয়। মোশারফ হোসেন রতন একটি পুরাতন কবরে আশ্রয় নিয়ে জীবন বাঁচায়। যুদ্ধে আবদুল আওয়াল ঝানু, সিদ্দিকুর রহমান চানুসহ কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হন। ২০ নভেম্বর ফটুয়ার টেকে পাকিস্তান বাহিনী ও মুক্তিবাহিনীর মধ্যে যুদ্ধ হয়। ডিসেম্বর মাসের প্রথম দিকে ফজলুল হক কোম্পানি, হাবিবুল হক মন্টু ও ইকবাল ই আলম কামাল কোম্পানির যৌথ নেতৃত্বে গয়েশপুর বাজারে পাকিস্তান বাহিনীর ওপর হামলা চালায়। দুই পক্ষের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে মুক্তিবাহিনীর বিজয় হলেও মহর আলী, আবদুস সাত্তার, আ. কাদের ও নিজাম উদ্দিনসহ মোট ১১ জন শহীদ হন।
স্বাধীনতার অর্ধশতক পেরিয়ে গেলেও মুক্তিযুদ্ধের চারণভূমি পাগলা থানায় কাঙ্ক্ষিত রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক অগ্রগতি- উন্নয়ন সাধিত হয়নি। পাগলা থানার সমন্বিত উন্নয়নে নিম্নোক্ত সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব করছি-
(১) সর্বাগ্রে পাগলা থানাকে উপজেলায় উন্নীত করতে হবে। (২) কিশোরগঞ্জ হতে হোসেনপুর, পাকুন্দিয়া, পাগলা ও কাওরাইদ হয়ে টাঙ্গাইল পর্যন্ত নতুন রেললাইন স্থাপন করতে হবে। (৩) পাগলা বাজারে একটি সরকারি মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে হবে। (৪) দত্তের বাজার ও পাকুন্দিয়ার মধ্যে সংযোগ সৃষ্টির জন্য পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদীর ওপর সড়ক সেতু নির্মাণ করতে হবে। (৫) পাগলা এলাকায় গ্যাস সংযোগসহ একটি অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা করতে হবে। (৬) পাগলা থানায় আইটি পার্ক নির্মাণ করতে হবে। (৭) পাগলা থানার অভ্যন্তরীণ নদী-খাল ও সড়কপথ সংস্কার করতে হবে।
উপরোক্ত দাবিসমূহ বাস্তবায়নের মধ্যে পাগলা থানার অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক মুক্তি নিহিত। অন্যথায় এ অঞ্চলের গণমানুষের কাছে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত স্বাধীনতার সুফল পৌঁছাবে না। সব অর্জন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। এ অঞ্চলের মুক্তিযোদ্ধা, শহীদ মুক্তিযোদ্ধা, মুক্তিযুদ্ধে নিহত গণমানুষ, নিপীড়িত মা-বোন প্রত্যেকের অতৃপ্ত আত্মা গুমরে গুমরে কেঁদে উঠবে। মুক্তিযুদ্ধের স্বপ্ন তাদের কাছে অর্থবহ না হয়ে ব্যর্থ বলে পরিগণিত হবে। কারণ মুক্তিযুদ্ধের অনেক স্বপ্নের মধ্যে পিছিয়ে পড়া অঞ্চল ও জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন নিশ্চিত করা, উন্নয়ন বৈষম্য নিরসন করা ও সবার জন্য সমান সুযোগ অধিকার নিশ্চিত করা। পাগলায় এসব সূচকের কোনোটি পূরণ হয়নি। বিষয়গুলো সংশ্লিষ্ট সব মহলকে ভেবে দেখার অনুরোধ করছি।
লেখক: সাধারণ সম্পাদক, পাগলা উপজেলা বাস্তবায়ন কমিটি ও মুক্তিযুদ্ধের গবেষক

বেসরকারি শিক্ষক নিয়োগের ষষ্ঠ গণবিজ্ঞপ্তিতে শূন্যপদ ছিল ১ লাখ ৮২২টি। এর বিপরীতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আবেদন জমা পড়েছে ৫৭ হাজারের কিছু বেশি। অর্থাৎ প্রায় ৪৩ হাজার পথ শূন্য থাকবে। চাহিদা দিয়েও শিক্ষক পাবে না অনেক প্রতিষ্ঠান। ক্লাস থেকে বঞ্চিত হবে শিক্ষার্থীরা! এ ব্যাপারে কেউ কেউ বলার চেষ্টা করছেন যে, আবেদনকালে প্রার্থীদের বয়স ৩৫ এর বেশি এবং নিবন্ধন সনদের মেয়াদ ৩ বছরের বেশি গ্রহণ না করার কারণে আবেদন কম পড়েছে। অর্থাৎ আরো কিছু ছাড় দেওয়া হলে আরো কিছু বেশি প্রার্থী আবেদন করতে পারত। বয়সে ও যোগ্যতায় বারবার ছাড় দিয়ে আবেদনের সুযোগ দিয়ে বেসরকারি শিক্ষক নিয়োগ করা কোনো উত্তম সমাধান নয়। ছাড় দিয়ে শিক্ষক নিয়োগ করা মানেই দীর্ঘ মেয়াদে দেশ ও জাতির অপূরণীয় ক্ষতি করা। একজন কম যোগ্য শিক্ষক তার শিক্ষকতা জীবনে তৈরি করেন অগণিত কম যোগ্য নাগরিক-কর্মী। তুলনামূলক কম যোগ্য শিক্ষক নিয়োগ দিয়ে অধিক যোগ্য নাগরিক-কর্মী তৈরির প্রত্যাশা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক, অবাস্তব!
শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রার্থীদের তৃতীয় বিভাগ বা শ্রেণি এখন আর গ্রহণযোগ্য থাকা উচিত নয়। সরকারি এমনকি প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা বা কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রেও এখন আর তৃতীয় বিভাগ বা শ্রেণিধারী প্রার্থীদের আবেদন করার সুযোগ থাকে না। নিয়োগের ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা, বয়স সীমা ও বাছাই প্রক্রিয়া অন্যদের তুলনায় বেসরকারি শিক্ষকদের শিথিল করা হলে এর অর্থ এমন দাঁড়ায় না যে বেসরকারি শিক্ষক তুলনামূলক কম যোগ্য হলেও চলে? এতে কি তাদের মান ও মর্যাদা হ্রাস পায় না? দেশের ৯৫ শতাংশের বেশি শিক্ষার্থীদের পাঠদানকারী বেসরকারি শিক্ষকদের অধিক যোগ্য হওয়া কি অধিক গুরুত্বপূর্ণ নয়? তারা তো আমাদের সন্তানদেরই শিক্ষক হন। তারা অধিক যোগ্য হলেই তো আমাদের সন্তানরা অধিক যোগ্য হবার সম্ভাবনা অধিক থাকে। অর্থাৎ বয়সে, যোগ্যতায়, পরীক্ষায় ছাড় দিয়ে তুলনামূলক কম যোগ্য শিক্ষক নিয়োগ দিয়ে নয়; বরং দ্রুত আর্থিক সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করে অধিক যোগ্যদের আকৃষ্ট করে শিক্ষক পদে নিয়োগ দেয়াই অধিক মঙ্গলজনক।
সার্বিক বিবেচনায় বেসরকারি শিক্ষক নিয়োগের ব্যবস্থাটিকে অতীতের ধারাবাহিকতায় আরও উন্নত করা আবশ্যক। সদিচ্ছা ও আন্তরিকতা থাকলে তা সহজেই সম্ভব। সে লক্ষ্যে সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষক নিয়োগের অনুরূপ শিক্ষাগত যোগ্যতা, বয়স সীমা ও বাছাই প্রক্রিয়া অনুসরণ করে বেসরকারি শিক্ষকদের নিয়োগ দেওয়া উচিত। অর্থাৎ শূন্য পদের বিপরীতে সরাসরি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দিয়ে উত্তম বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উত্তম প্রার্থী বাছাই করে বেসরকারি শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া প্রয়োজন। নিবন্ধনধারী সবাইকেই যদি নিয়োগ দিতে হয় তাহলে এটিকে নিবন্ধন পরীক্ষা না বলে নিয়োগ পরীক্ষা বলা ও কার্যকর করা অধিক যুক্তিযুক্ত নয় কি? তুলনামূলক কম নম্বর প্রাপ্ত নিবন্ধন ধারীরাও নিয়োগের দাবিদার হয়, নিয়োগের জন্য সোচ্চার হয়, বয়সের শিথিলতা দাবি করে, অশান্তি তৈরি করে। এমনকি অকৃতকার্যরাও আন্দোলন করে! অথচ সরাসরি নিয়োগ পরীক্ষায়/ প্রক্রিয়ায় কম নম্বর পেয়ে বাদ পড়ে যাওয়ারা আর নিয়োগের দাবিদার হতে পারে না, বয়সের শিথিলতা দাবি করতে পারে না, অশান্তি তৈরি করতে পারে না। অপরদিকে একবার নিবন্ধন পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তি দেওয়া, আবেদন নেওয়া, পরীক্ষা নেওয়া, তালিকা করা, সনদ দেওয়া এবং পরবর্তীতে আবার নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি দেওয়া, বাছাই করা, তালিকা করা, নিয়োগ করা ইত্যাদি নিয়োগ কর্তৃপক্ষ ও নিয়োগ প্রার্থী উভয়ের জন্যই দ্বিগুণ কষ্টসাধ্য ও সময় সাপেক্ষ। তদুপরি নিয়োগ প্রার্থীর জন্য দ্বিগুণ ব্যয় সাপেক্ষ। অধিক সংখ্যক শূন্য পদে নিয়োগ প্রার্থীদের বাছাই কেন্দ্রীয়ভাবে দ্রুত সম্পন্ন করা সম্ভব না হলে জেলা প্রশাসকগণের দায়িত্বে ঐ জেলার সরকারি স্কুল-কলেজের সুযোগ্য শিক্ষকগণের সহযোগিতা নিয়ে সারাদেশে একই প্রশ্নে ও প্রক্রিয়ায় বেসরকারি শিক্ষক নিয়োগের বাছাই দ্রুত সম্পাদন করা সম্ভব হয় কিনা তা ভেবে দেখা যেতে পারে। যেমন প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর করে থেকে।
অন্যান্য চাকরিতে প্রবেশের ক্ষেত্রে নির্ধারিত বয়স ও যোগ্যতার চেয়ে অধিক বয়স্কদের ও কম যোগ্যদের শিক্ষকতায় প্রবেশের সুযোগ দেওয়া মোটেও উচিত নয়। কিছুদিন পরপর নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দিয়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক যোগ্য শিক্ষক নিয়োগ করতে চাইলে বারবার অধিকতর যোগ্য ফ্রেশ ক্যান্ডিডেট পাওয়া যাবে। একজন ইয়ং এনার্জিটিক মেধাবী শিক্ষক প্রশিক্ষণ নিয়ে নিজেকে তৈরি করতে ও পূর্ণ উদ্যমে দীর্ঘদিন পাঠদান করতে যতটা সক্ষম একজন বয়স্ক লোক ততটা সক্ষম না হওয়াই স্বাভাবিক। ব্যতিক্রম নগণ্য। একজন নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকের প্রকৃত সফল শিক্ষক হয়ে উঠতে অনেক সময়, শ্রম, মেধা, চর্চা, উদ্যম, প্রশিক্ষণ, দক্ষতা, অভিজ্ঞতা লাগে। কেউ শিক্ষক হয়ে উঠতেই যদি বৃদ্ধ হয়ে পড়েন তো সফল পাঠদানে নিরলস থাকবেন কীভাবে, কতদিন?
আলোচিত বিষয়গুলো বিবেচনায় রেখে দেশ ও জাতির বৃহত্তর স্বার্থে অধিক যুক্তিযুক্ত উন্নত নীতিমালা প্রণয়ন করে ঢেলে সাজানো উচিত সকল শিক্ষক নিয়োগের বাছাই প্রক্রিয়া। মূল্যায়নে বিবেচনা করা উচিত প্রার্থীর শিক্ষা জীবনের কর্মকাণ্ড ও ডেমো ক্লাসের মান। দ্রুত দূর করা উচিত একই দায়িত্ব-কর্তব্যে নিয়োজিত সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা, বয়স সীমা, বাছাই প্রক্রিয়া এবং আর্থিক সুযোগ-সুবিধা সংক্রান্ত সকল বৈষম্য। অর্থাৎ বেসরকারি শিক্ষক নিয়োগের জন্য আর নিবন্ধন পরীক্ষা নয়, নিতে হবে সরাসরি নিয়োগ পরীক্ষা। সেই সঙ্গে বৃদ্ধি করতে হবে আর্থিক সুযোগ-সুবিধা। শিক্ষকতায় আকৃষ্ট করতে হবে সর্বাধিক যোগ্যদের।
লেখক: অধ্যক্ষ, শিক্ষাবিদ ও কলামিস্ট

ডিম পাড়ে হাসে, খায় বাগডাসে। গত ১৬ বছরে কথাটির বাস্তব প্রমাণ যেন দিয়ে গিয়েছিল পতিত আওয়ামী লীগ সরকার। দেশের মানুষের শ্রম আর ঘামের পয়সা তুঘলকি উপায়ে লুটে নিয়ে অবিশ্বাস্য অংকে বিদেশে পাচার করার নতুন নজির গড়েছিল তারা। এই লুটপাটের অন্যতম একটি খাত ছিল বিদ্যুৎখাত আর কুইক রেন্টাল কেরামতি। যেখানে মাত্র ৬ থেকে ৭ টাকার বিদ্যুৎ রাতারাতি সরকার কেনা শুরু করে সর্বোচ্চ ২৬ টাকায়।
আওয়ামী লীগ সরকারের গত ১৫ বছর দেশে বিদ্যুতের চাহিদা বৃদ্ধির অন্তরালে গড়ে ওঠা, দুর্নীতি এবং অপচয় বিদ্যুৎখাতকে ক্রমেই করে তুলেছে জনসাধারণের অর্থ লোপাটের কারখানা। বিশেষ করে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকারের শাসনামলে কুইক রেন্টাল নামের বিদ্যুৎ উৎপাদনের এক অস্বচ্ছ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়, যা আজো দেশের বিদ্যুৎ সেক্টরের একটি বড় শুভাঙ্করের ফাঁকি হিসেবে থেকে গেছে।
২০০৯ থেকে শুরু করে গত দশকজুড়ে দেশের বিদ্যুৎ উৎপাদনে দ্রুততা আনতে ‘কুইক রেন্টাল’ ব্যবস্থা চালু হয়। তবে, এই ব্যবস্থার আওতায় তৈরি হওয়া কেন্দ্রগুলো প্রায়শই তাদের সক্ষমতার মাত্র ২৫-৩০ শতাংশ বিদ্যুৎ উৎপাদন করে। বাদবাকি সময় এসব পাওয়ার প্ল্যান্ট বসে থাকলেও সরকার চুক্তি অনুযায়ী তাদের পূর্ণ ক্ষমতার জন্য ‘ক্যাপাসিটি চার্জ’ বা স্থায়ী পেমেন্ট দিতে বাধ্য হয়। এর ফলে একদিকে অতিরিক্ত সক্ষমতা থাকলেও, তা পূর্ণ ব্যবহার হয় না, এবং সরকারকে বছরে প্রায় ১৯ হাজার কোটি টাকার বেশি ক্যাপাসিটি চার্জ বাবদ ব্যয় করতে হয়। অন্যদিকে এই কুইক রেন্টাল পাওয়ার প্ল্যান্টে মাত্র ৬ টাকা ইউনিটের বিদ্যুৎ কেনা হয় সর্বোচ্চ ২৬ টাকা মূল্যে। যার দায় মেটাতে হয় দেশের সাধারণ মানুষের।
বর্তমানে বাংলাদেশের বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা প্রায় ৩০,৭৮৭ মেগাওয়াট, যেখানে চাহিদা প্রায় ১৮,০০০ মেগাওয়াটের আশেপাশে। এর ফলে প্রায় ১২,৭৮৭ মেগাওয়াট অতিরিক্ত ক্ষমতা থাকলেও, এ অতিরিক্ত ক্ষমতার জন্যও সরকারের পকেটে খরচ হয় কোটি কোটি টাকা। উপরন্তু বিদ্যুৎ বিভ্রাটের বিষয়টি ঘটে চলে ক্রমাগত। আর তাই প্রশ্ন ওঠে এত খরচ আর এত অর্থ পাচারের মচ্ছবে আমরা কি পুষছি সাদা হাতি? বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে, আওয়ামী লীগের আমলে এ খাতে হওয়া দুর্নীতির পুঙ্খানুপুঙ্খ দুর্নীতির চিত্র তুলে ধরা তো দূরের বিষয় বর্তমান সরকারের সময়ে কুইক রেন্টালের অর্থ কোথায় যাচ্ছে গণমাধ্যমে সে তথ্যও আসছে না।
দেশে কুইক রেন্টাল ব্যবস্থার এই উত্থান এবং অর্থ হরিলুটের পেছনে ছিলো ২০১০ সালে প্রণীত ‘দায়মুক্তি আইন’ (Quick Enhancement of Electricity and Energy Supply Act, 2010), যার মাধ্যমে দরপত্র ছাড়াই রাজনৈতিকভাবে সংযোগে থাকা ব্যবসায়ীদের হাতে দ্রুত কুইক রেন্টাল কেন্দ্র অনুমোদন দেওয়া হয়। এই আইনের আওতায় ক্ষমতাসীন দলের ঘনিষ্ঠদের মাধ্যমে কোটি কোটি টাকা সরকারি তহবিল থেকে সুবিধাভোগী হিসেবে গড়ে ওঠে। যদিও আইনটি বর্তমানে বাতিল ঘোষণা করা হয়েছে, তবুও সংশ্লিষ্ট চুক্তিগুলো এখনো বহাল রয়েছে এবং দ্রুত বাস্তবায়নে আইনি জটিলতা ও ক্ষতিপূরণ ইস্যু রয়ে গেছে।
সরকারের সাম্প্রতিক পদক্ষেপ হিসেবে কুইক রেন্টাল চুক্তি পুনর্বিবেচনা ও বাতিলের কথা বলা হলেও বাস্তবে অনেক কেন্দ্রে ক্যাপাসিটি চার্যের অতিরিক্ত অর্থ বাকি রয়েছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে শুধু ক্যাপাসিটি পেমেন্ট বাবদ সরকার প্রায় ২৬,৫০০ কোটি টাকা ব্যয় করেছে, যা আগের পাঁচ বছরের তুলনায় তিনগুণ বেশি। সরকারের সামগ্রিক ভর্তুকি ও অতিরিক্ত খরচ মিলিয়ে বিদ্যুৎ খাতে অপচয়ের পরিমাণ বছরে ৬০,০০০ কোটি টাকারও বেশি হতে পারে। বিদ্যুৎ খাতে গত অর্থবছরেই ভর্তুকি বরাদ্দ ছিল ৪৭ হাজার কোটি টাকা। তারা নিয়েছে ৬২ হাজার কোটি টাকা।
শ্বেতপত্র কমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী গত কয়েক বছরে বিদ্যুৎ খাতে প্রায় ৬০০ কোটি ডলার (৬০ হাজার কোটি টাকা) দুর্নীতি ও অর্থপাচার হয়েছে, অথচ দুর্নীতির বিরুদ্ধে কার্যকর কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। বকেয়া বিল আদায়ে কিছু অগ্রগতি হলেও, বিদ্যুৎ ও গ্যাস খাতে অনিয়ম ও অপচয় রোধে এখনো কাঙ্খিত পদক্ষেপগুলো অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে।
বিদ্যুৎ ব্যবস্থার সাশ্রয়ী এবং টেকসই বিকল্প গড়ার ক্ষেত্রে এখনো যথেষ্ট উদ্যোগ নেই। নবায়নযোগ্য শক্তি এবং দক্ষ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দেশ এই সংকট থেকে উত্তরণ পেতে পারত, তবে কুইক রেন্টালের বাইরে বিকল্প পথে যেতে সরকারের পদক্ষেপ দৃষ্টিগোচর হয়নি। প্রায়শই দেখা যায়, নবায়নযোগ্য শক্তি প্রকল্প বাতিল বা পেছনে পড়ে যাওয়ার ঘটনা ঘটেছে।
সরকারি রিপোর্ট ও সংবাদ বিশ্লেষণ থেকে স্পষ্ট যে, কুইক রেন্টাল সিস্টেম থেকে বেরিয়ে আসতে হলে চুক্তির পুনর্বিবেচনা ও আইনি জটিলতা কাটিয়ে ওঠা জরুরি। তবেই বছরের পর বছর ধরে চলা অর্থনৈতিক অপচয় রোধ করা সম্ভব হবে। একই সঙ্গে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ডিমান্ড সাইড ম্যানেজমেন্ট, এনার্জি এফিসিয়েন্সি বৃদ্ধি এবং নবায়নযোগ্য শক্তির উন্নয়নে দ্রুত কাজ করতে হবে।
বিদ্যুৎ উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান সাম্প্রতিক এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, ‘লোডশেডিং আছে এবং থাকবে, কারণ সরবরাহ ও চাহিদার ভারসাম্য ফেরানো সহজ নয়। বিদ্যুৎ উৎপাদন কর্মক্ষমতা বাড়ানো এবং অপ্রয়োজনীয় অর্থ প্রদান বন্ধ করাই এখন সময়ের দাবি।’ তিনি আরও বলেন, ‘সরকার দামের বিষয়ে কঠোর অবস্থানে রয়েছে এবং জনগণের স্বার্থ রক্ষা করবে।’
এই পরিস্থিতি থেকে উত্তরণে শুধু আইন পরিবর্তন বা চুক্তি বাতিল যথেষ্ট নয়। প্রযুক্তিগত দক্ষতা বৃদ্ধি, নবায়নযোগ্য শক্তির ব্যবহার বাড়ানো এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠা করাই প্রকৃত সমাধান। বিদ্যুৎ খাতের টেকসই উন্নয়নের জন্য তা জরুরি।
গণমানুষের দীর্ঘদিনের দাবি, বিদ্যুৎ খাতের এসব দুর্নীতি আর অর্থ লুট বন্ধ করার। দেশের মানুষের শ্রম, ঘাম, আর কষ্টের টাকায় প্রাসাদোপম অট্টালিকায় থাকার পর, আগের সরকার এর ফলাফল ঠিকই কড়ায় গণ্ডায় দেখেছে। তাই এ থেকে শিক্ষা নিয়ে পরবর্তী কার্যক্রম হাতে নেয়াই ভালো। দেশের অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রায় বড় বাধা হয়ে দাঁড়ানো এই অব্যবস্থাপনার বিরুদ্ধে প্রয়োজন দ্রুত ও দৃঢ় পদক্ষেপের, যেখানে দুর্নীতি রোধ, স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠা এবং উন্নত প্রযুক্তির মাধ্যমে বাংলাদেশকে বিদ্যুৎ সংকট থেকে মুক্ত করা যাবে।
কবি, সাংবাদিক, মিডিয়া ব্যক্তি

বাংলাদেশ একটি কৃষিনির্ভর দেশ। দেশের অর্থনীতি, কর্মসংস্থান এবং খাদ্য নিরাপত্তার বড় অংশই কৃষির ওপর নির্ভরশীল। অথচ স্বাধীনতার ৫০ বছর পরেও দেশে পর্যাপ্ত কৃষিভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠান, আধুনিক রাইস মিল, হিমাগার এবং প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প গড়ে ওঠেনি। এর ফলে কৃষকরা তাদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্য মূল্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন এবং কৃষি খাতের সম্ভাবনা পূর্ণভাবে কাজে লাগানো যাচ্ছে না।
কৃষি উৎপাদনের চিত্র: বাংলাদেশ একটি কৃষি নির্ভর দেশ, যেখানে প্রতিবছর বিপুল পরিমাণ কৃষিপণ্য উৎপাদিত হয়ে দেশের খাদ্যনিরাপত্তা ও অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এর মধ্যে ধান ও চাল প্রধানতম খাদ্যশস্য। বার্ষিক চাহিদা প্রায় ৩৫০–৩৮০ লাখ মেট্রিক টন ধান ও চাল উৎপাদনের মাধ্যমে পূরণ করা হয়, যা দেশের জনগণের প্রধান খাদ্যচাহিদা মেটাতে সহায়তা করে। সবজি উৎপাদনের ক্ষেত্রেও বাংলাদেশ দ্রুত অগ্রগতি অর্জন করেছে। বর্তমানে বছরে প্রায় ৬.৫ থেকে ১৯ মিলিয়ন টন সবজি উৎপাদিত হয়। উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, বাংলাদেশ এখন বিশ্বের তৃতীয়-সর্বোচ্চ সবজি উৎপাদক দেশ হিসেবে স্বীকৃত। বিভিন্ন মৌসুমি সবজি দেশের বাজারের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক বাজারেও রপ্তানি হচ্ছে, যা বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে অবদান রাখে। ফল উৎপাদনের দিক থেকেও বাংলাদেশ সমৃদ্ধ। প্রতি বছর প্রায় ১৪.৮ মিলিয়ন টন ফল উৎপাদিত হয়। এর মধ্যে কলা, আম, কাঁঠাল, পেয়ারা ও অনারস বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মৌসুমি ফলের পাশাপাশি সারাবছর বিভিন্ন ফলের সরবরাহ কৃষকদের আয়ের উৎস এবং জনগণের পুষ্টি চাহিদা পূরণে সহায়ক। মৎস্য খাতে বাংলাদেশ বিশ্বে গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান দখল করে আছে। ২০২৩–২৪ অর্থবছরে মোট মাছ উৎপাদন হয়েছে প্রায় ৫০.১৮ লাখ মেট্রিক টন। এর মধ্যে শুধু ইলিশ উৎপাদন ছিল ৫.২৯ লাখ মেট্রিক টন, যা বাংলাদেশকে বিশ্বে ইলিশ উৎপাদনে শীর্ষস্থান অধিকারী করেছে। মাছ বাংলাদেশের জনগণের প্রোটিন চাহিদার প্রধান উৎস, একইসঙ্গে রপ্তানি আয়েরও গুরুত্বপূর্ণ খাত। সব মিলিয়ে, ধান, সবজি, ফল ও মাছ উৎপাদনে বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য সাফল্য দেশের অর্থনীতি ও খাদ্যনিরাপত্তাকে শক্তিশালী করেছে। এই উৎপাদন ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধি ও সংরক্ষণে আধুনিক প্রযুক্তি, প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প ও কোল্ড চেইন অবকাঠামো উন্নয়ন আরও জরুরি। এতে কৃষক লাভবান হবে এবং টেকসই কৃষি উন্নয়ন নিশ্চিত হবে।
শিল্প প্রতিষ্ঠানের অভাব ও কৃষকের বঞ্চনা: বাংলাদেশ একটি কৃষি নির্ভর দেশ। এদেশের উর্বর মাটি ও অনুকূল আবহাওয়া বছরে বিপুল পরিমাণ ধান, ফল, সবজি, মাছ ও প্রাণিসম্পদ উৎপাদনে সহায়তা করে। কিন্তু এই বিপুল উৎপাদনের সঠিক ব্যবহার ও কৃষকের ন্যায্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করার মতো পর্যাপ্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান এখনো দেশে গড়ে ওঠেনি। এর ফলে কৃষকরা উৎপাদন করেও আর্থিকভাবে বঞ্চিত থেকে যাচ্ছেন। প্রথমত, দেশে আধুনিক রাইসমিল ও শস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্রের অভাব প্রকট। অধিকাংশ কৃষক ধান বা গম কাঁচা অবস্থায় বিক্রি করতে বাধ্য হন। ফলে তারা ধানের পূর্ণ মূল্য পান না। একইভাবে হিমাগার ও কোল্ড চেইন অবকাঠামোর ঘাটতির কারণে উৎপাদিত ফল ও সবজি দীর্ঘ সময় সংরক্ষণ করা যায় না। ফলে মৌসুমে প্রচুর উৎপাদন হলেও তা দ্রুত বাজারজাত করতে গিয়ে কৃষকরা কম দামে বিক্রি করতে বাধ্য হন। দ্বিতীয়ত, ফল ও সবজি প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের অভাব কৃষকদের সম্ভাবনা সীমিত করে রেখেছে। অনেক দেশে টমেটো, আম, লিচু, আনারস ইত্যাদি ফল থেকে রস, জুস, আচার বা ক্যানজাত পণ্য তৈরি হয়। বাংলাদেশেও এ ধরনের শিল্প প্রতিষ্ঠিত হলে কৃষকরা শুধু মৌসুমেই নয়, সারা বছর ধরে ন্যায্য দামে পণ্য বিক্রি করতে পারতেন। একইভাবে, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ ভিত্তিক শিল্পের অভাবে মাছ, মাংস, দুধ ইত্যাদি পণ্য প্রক্রিয়াজাত হয়ে আন্তর্জাতিক বাজারে রপ্তানি করার সুযোগ অনেকাংশে হাতছাড়া হচ্ছে। সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো, সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণের সুযোগ না থাকায় অতিরিক্ত উৎপাদনের সময় বাজারে দাম পড়ে যায়। এতে কৃষকরা তাদের উৎপাদনের ন্যায্য মূল্য থেকে বঞ্চিত হন এবং আয় অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। অতএব, কৃষিকে টেকসই ও লাভজনক করতে হলে দেশে দ্রুত আধুনিক রাইসমিল, হিমাগার, কোল্ড চেইন, ফল-সবজি ও মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প গড়ে তুলতে হবে। শিল্প ও কৃষির এই সমন্বয়ই কৃষকের ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করে দেশের অর্থনীতিকে আরও শক্তিশালী করতে পারে।
অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রভাব: কৃষকের আয় কমে যায়, ফলে তারা কৃষিকাজে আগ্রহ হারায়। বেকারত্ব বাড়ে, কারণ কৃষিভিত্তিক শিল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে পারে না। রপ্তানি সম্ভাবনা নষ্ট হয়, কারণ আন্তর্জাতিক মানের প্রক্রিয়াজাত পণ্য তৈরি হয় না। কৃষিখাতে আয় হ্রাসের ফলে শ্রমশক্তির উৎসাহে নেতিবাচক প্রভাব পড়ে, যা কৃষি-উৎপাদন ব্যবস্থায় অংশগ্রহণের হার কমিয়ে দেয়। এর ফলে গ্রামীণ অর্থনীতিতে কর্মসংস্থান সংকট তীব্রতর হয়, কারণ কৃষিভিত্তিক শিল্পসমূহ পর্যাপ্ত স্কেল-আপ সক্ষমতা অর্জন করতে ব্যর্থ হয়। পাশাপাশি, মূল্য সংযোজন ও গ্লোবাল ভ্যালু চেইনে অন্তর্ভুক্তির অভাবে রপ্তানিমুখী কৃষিপণ্যের আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা সক্ষমতা ক্ষুণ্ন হয়।
করণীয় ও সম্ভাবনা: বাংলাদেশের কৃষি খাতকে শিল্পায়নের মাধ্যমে এগিয়ে নিতে প্রয়োজন, সরকারি ও বেসরকারি বিনিয়োগ কৃষিভিত্তিক শিল্পে উৎসাহিত করা। প্রযুক্তিনির্ভর প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্র স্থাপন। কৃষক প্রশিক্ষণ ও বাজার সংযোগ উন্নয়ন। রপ্তানিভিত্তিক কৃষি শিল্প গড়ে তোলা। বাংলাদেশের কৃষি উৎপাদন বিশ্বমানের হলেও, এর পূর্ণ সম্ভাবনা কাজে লাগাতে হলে কৃষি ভিত্তিক শিল্পায়ন অপরিহার্য। স্বাধীনতা পরবর্তী এপর্যন্ত তেমন কোনো রকম কৃষিভিত্তিক কলকারখানা, সবজি ও ফল সংরক্ষণে হিমাগার, কৃষি শিল্পভিত্তিক ইন্ডাস্ট্রি স্থাপন, এসব নিয়ে তেমন কিছু দৃশ্যমান কৃষক বান্ধব কার্যক্রম হাতে নেয় নাই বিগত দিনের সরকার গুলি। পর্যাপ্ত গ্যাস সরবরাহ , হিমাগার স্থাপন ও পণ্য পরিবহনের সুবিধা না থাকায় কৃষিভিত্তিক শিল্প গড়ে ওঠে নাই বলে মত প্রকাশ করেন ব্যবসায়ীরা। আন্ত:জেলার সড়ক ও ট্রেন যোগাযোগ ব্যবস্থা কৃষিবান্ধব করা না গেলে কৃষকের স্বার্থ রক্ষা হবে না বলে মনে করেন স্থানীয় কৃষকরা। কৃষি খাতে সার্বিক উন্নয়নের জন্য সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সমন্বিত উদ্যোগ এবং আধুনিক প্রযুক্তি ও যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা না গেলে, টেকসই কৃষি বাস্তবায়ন সম্ভব হয়ে উঠবে না এবং সেই সঙ্গে কৃষকের ন্যায্যমূল্য পাওয়ার বিষয়টি অনিশ্চিত হয়ে পড়বে।
কৃষিভিত্তিক শিল্পের অভাবে আমাদের কৃষকের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত হয় না, ফসলের যথাযথ প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণের সুযোগ সীমিত থাকে, ফলে তারা মধ্যস্বত্বভোগীর কাছে নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। এর ফলে কৃষকের পরিশ্রমের সঠিক মূল্য তারা পায় না এবং গ্রামীণ অর্থনীতি উন্নতির সুযোগ হারায়। কৃষিভিত্তিক শিল্প গড়ে তোলা হলে শুধু কৃষকের জীবনমান উন্নত হবে না, বরং দেশের খাদ্য নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিও টেকসই হবে।
লেখক: সমীরণ বিশ্বাস, কৃষি ও পরিবেশ বিশেষজ্ঞ, ঢাকা।

বাংলাদেশ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতি ও বৈচিত্র্যময় জীববৈচিত্র্যের এক অনন্য ভাগ সবুজের সমারোহ, অসংখ্য নদী, পাহাড়, সমুদ্রসৈকত, ম্যানগ্রোভ বন, প্রাচীন স্থাপত্য ও লোকজ ঐতিহ্য মিলিয়ে এ দেশ পর্যটনের জন্য এক স্বর্ণখনি। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, এই অপরিসীম সম্পদকে এখনো পুরোপুরি কাজে লাগানো সম্ভব হয়নি। পৃথিবীর অনেক দেশ প্রাকৃতিক সম্পদ বা শিল্পের তুলনায় পর্যটনশিল্পকে প্রধান আয়ের উৎস হিসেবে দাঁড় করিয়েছে। মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড, মালদ্বীপ কিংবা নেপালের মতো দেশগুলো তাদের অর্থনীতিতে পর্যটনের অবদান দিয়ে বিশ্বে নিজেদের অবস্থান সুদৃঢ় করেছে। অথচ বাংলাদেশেও সেই সম্ভাবনা বিদ্যমান, তবে তা কাজে লাগানোর জন্য প্রয়োজন সঠিক পরিকল্পনা, অবকাঠামো উন্নয়ন, নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং আন্তর্জাতিক মানের প্রচারণা।
পর্যটনশিল্প কেবল বিদেশি মুদ্রা অর্জনের ক্ষেত্রই নয়, বরং স্থানীয় অর্থনীতি চাঙা করা, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, সাংস্কৃতিক বিনিময় এবং গ্রামীণ উন্নয়নের এক বড় মাধ্যম। এ শিল্পের প্রসার হলে হোটেল-মোটেল, রেস্টুরেন্ট, পরিবহন, হস্তশিল্প ও স্থানীয় পণ্যের বাজার সম্প্রসারিত হবে, যা সরাসরি লাখো মানুষের জীবিকা গড়ে তুলবে। তাছাড়া পর্যটনের মাধ্যমে দেশের ইতিবাচক ভাবমূর্তি বিশ্বে ছড়িয়ে পড়বে, যা বিনিয়োগ আকর্ষণ ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক উন্নয়নেও সহায়ক হবে।
সুতরাং দেশের অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রা ত্বরান্বিত করতে হলে পর্যটনশিল্পকে অন্যতম কৌশলগত খাত হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। সঠিক বিনিয়োগ, পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে এটি দেশের উন্নয়নের এক গুরুত্বপূর্ণ চালিকাশক্তি হয়ে উঠতে পারে। এই প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক ঐশ্বর্যকে কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশকে আন্তর্জাতিক পর্যটন মানচিত্রে শক্তিশালী অবস্থানে নেওয়াই এখন সময়ের দাবি।
বাংলাদেশ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, সংস্কৃতির বৈচিত্র্য, ঐতিহাসিক নিদর্শন এবং অতিথিপরায়ণ মানুষের দেশ। আমাদের দেশের ভূপ্রকৃতি এমনভাবে বিন্যস্ত যে এখানে পর্যটনের অসীম সম্ভাবনা বিদ্যমান। সমুদ্র, পাহাড়, নদী, বনভূমি, দ্বীপ, চরাঞ্চল থেকে শুরু করে প্রাচীন ঐতিহাসিক স্থাপনা—সবই এখানে ছড়িয়ে আছে। এই সম্পদগুলো শুধু দেশের মানুষের জন্য নয়, বিদেশি পর্যটকদের জন্যও এক বিরল অভিজ্ঞতার উৎস হতে পারে। অথচ পর্যটনশিল্পকে আমরা এখনও অর্থনীতির প্রধান খাতে রূপ দিতে পারিনি। উন্নত বিশ্বে পর্যটন এখন বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও আন্তর্জাতিক ভাবমূর্তি গঠনের বড় মাধ্যম হয়ে উঠেছে। বাংলাদেশও চাইলে এই খাতকে অর্থনীতির উন্নয়নের অন্যতম প্রধান চালিকাশক্তি হিসেবে গড়ে তুলতে পারে।
আমাদের দেশে বিশ্বের দীর্ঘতম সমুদ্রসৈকত কক্সবাজার, সুন্দরবনের রয়েল বেঙ্গল টাইগার, পাহাড়পুরের প্রাচীন বৌদ্ধবিহার, ষাটগম্বুজ মসজিদের অনন্য স্থাপত্য, মহাস্থানগড়ের ঐতিহাসিক গুরুত্ব এবং সিলেটের চা বাগান—সবই পর্যটনের জন্য অসামান্য সম্পদ। এছাড়া বান্দরবান ও রাঙামাটির সবুজ পাহাড়, খাগড়াছড়ির জলপ্রপাত, কাপ্তাই হ্রদ, চট্টগ্রামের পতেঙ্গা ও ইনানি সৈকত, ভোলা ও সেন্টমার্টিনের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য পর্যটকদের মুগ্ধ করতে পারে। নদীমাতৃক দেশের বৈশিষ্ট্য হিসেবে নদী ভ্রমণ, নৌকা বিহার, চরের জীবনযাপন এবং গ্রামীণ লোকসংস্কৃতি পর্যটন সম্ভাবনায় নতুন মাত্রা যোগ করতে পারে।
অর্থনৈতিক দিক থেকে পর্যটনশিল্প একটি বহুমুখী প্রভাব বিস্তারকারী খাত। প্রথমত, এটি সরাসরি কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে। হোটেল, রেস্তোরাঁ, রিসোর্ট, ট্রাভেল এজেন্সি, পরিবহন ও বিনোদন কেন্দ্রগুলোতে অসংখ্য মানুষের কাজের সুযোগ তৈরি হয়। দ্বিতীয়ত, এটি পরোক্ষভাবে কৃষি, মৎস্য, হস্তশিল্প, পরিবহন ও অন্যান্য সেবা খাতের চাহিদা বাড়ায়। তৃতীয়ত, বিদেশি পর্যটকদের আগমনে বৈদেশিক মুদ্রার প্রবাহ বৃদ্ধি পায়, যা দেশের রিজার্ভকে শক্তিশালী করে। পর্যটনের মাধ্যমে একটি দেশের পরিচিতি বিশ্বমঞ্চে বিস্তৃত হয়, যা ভবিষ্যতে বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণেও সহায়ক হয়।
বাংলাদেশের পর্যটনশিল্প শুধুমাত্র অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির নয়, এটি আমাদের সংস্কৃতি, ইতিহাস ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে বিশ্বের কাছে তুলে ধরারও এক দুর্দান্ত সুযোগ। এ খাতের উন্নয়নে সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারি বিনিয়োগ, স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতা জরুরি। পর্যটন উন্নয়ন পরিকল্পনায় স্থানীয়দের প্রশিক্ষণ, অংশীদারিত্ব এবং উপকার নিশ্চিত করতে হবে, যাতে তারা পর্যটনের সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ত হয়ে লাভবান হয়।
পর্যটনশিল্পের সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে এখনই কার্যকর উদ্যোগ নিতে হবে। দীর্ঘসূত্রিতা ও অবহেলার কারণে এই খাত দীর্ঘদিন ধরে উপেক্ষিত থেকেছে। সঠিক পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে এটি জাতীয় অর্থনীতির প্রধান আয় উৎসে পরিণত হতে পারে। পর্যটন আমাদের শুধু বৈদেশিক মুদ্রা ও কর্মসংস্থানই দেবে না, বরং দেশের আন্তর্জাতিক ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করবে। একবিংশ শতাব্দীতে উন্নয়নশীল অর্থনীতির জন্য পর্যটনশিল্প হতে পারে সবচেয়ে বড় শক্তি। তাই আজই সিদ্ধান্ত নিতে হবে—পর্যটনশিল্প হবে বাংলাদেশের অর্থনীতির অন্যতম প্রধান চালিকাশক্তি, যা দেশকে আরও সমৃদ্ধ, উন্নত ও বিশ্বে মর্যাদাবান করবে।
লেখক - সাংবাদিক ও কলামিস্ট

স্বল্পোন্নত দেশগুলোর (এলডিসি) উত্তরণের ছয় বছরের স্থগিতাদেশ বাস্তবায়নের প্রস্তাব অর্থনীতিবিদ, নীতিনির্ধারক এবং উন্নয়ন বিশেষজ্ঞদের মধ্যে তীব্র বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। একজন অর্থনীতিবিদ হিসেবে, আমি বাংলাদেশের স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণের জন্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে ছয় বছরের বর্ধিতকরণকে সমর্থন করি না। পরিবর্তে, আমি যুক্তি দিচ্ছি যে দেশটির উচিত তার অবশিষ্ট রূপান্তর সময়কাল (২০২৬ সাল পর্যন্ত) ব্যবহার করে দ্রুত স্থগিতাদেশের চেষ্টা না করে জরুরি কাঠামোগত সংস্কার বাস্তবায়ন করা। স্নাতক ডিগ্রি বিলম্বিত করার অন্যতম প্রধান সুবিধা হলো বাংলাদেশের জন্য টেকসই উন্নয়নের উপর মনোযোগ দেওয়ার সুযোগ। বর্তমানে, বাংলাদেশ সহ অনেক স্বল্পোন্নত দেশ অপর্যাপ্ত অবকাঠামো, উচ্চ দারিদ্র্যের হার এবং স্বাস্থ্যসেবা ও শিক্ষার সীমিত সুযোগের সাথে লড়াই করছে। ছয় বছরের মেয়াদ বৃদ্ধি বাংলাদেশকে এই গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলিতে যথেষ্ট বিনিয়োগ করতে সাহায্য করবে।
শিক্ষা ব্যবস্থা উন্নত করলে কর্মশক্তি উদীয়মান শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন করতে পারে, অন্যদিকে স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা উন্নত করলে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে অবদান রাখতে সক্ষম একটি স্বাস্থ্যকর জনসংখ্যা নিশ্চিত করা যেতে পারে। টেকসই অবকাঠামো উন্নয়ন, বিশেষ করে পরিবহন এবং জ্বালানি, বাণিজ্যকে সহজতর করতে পারে এবং বিদেশি সরাসরি বিনিয়োগ (FDI) আকর্ষণ করতে পারে। এই মৌলিক উপাদানগুলিকে অগ্রাধিকার দিয়ে, বাংলাদেশ একটি আরও শক্তিশালী অর্থনীতির ভিত্তি স্থাপন করতে পারে যা স্নাতকোত্তর পর্যায়ে উন্নতি করতে পারে। কেন ছয় বছরের স্থগিতাদেশ সমাধান নয়
কৃত্রিম বিলম্ব আত্মতুষ্টির জন্ম দিতে পারে
একটি সম্পূর্ণ সম্প্রসারণ নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে সংস্কারের তাগিদ কমাতে পারে: রপ্তানি বৈচিত্র্য, কর রাজস্ব সংগ্রহ, আর্থিক খাতের স্থিতিশীলতা ঐতিহাসিক ঘটনাগুলো (যেমন, মালদ্বীপ, ভিয়েতনাম) দেখায় যে ধীরে ধীরে, পূর্ব-পরিকল্পিত রূপান্তর আকস্মিক পরিবর্তনের চেয়ে ভালো কাজ করে। জাতিসংঘের স্বল্পোন্নত দেশের (মাথাপিছু জিএনআই, মানব সম্পদ, অর্থনৈতিক দুর্বলতা) মানদণ্ড থেকে বোঝা যায় যে বাংলাদেশ প্রস্তুত।
দীর্ঘস্থায়ী স্বল্পোন্নত দেশের মর্যাদা তাদের বিদেশী বিনিয়োগকারীদের বাধাগ্রস্ত করতে পারে যারা ‘উদীয়মান অর্থনীতির’ পরিবর্তে ‘অল্পোন্নত’ দেশগুলোর সঙ্গে সম্পর্কিত।
৩. বাণিজ্য সুবিধা ইতোমধ্যেই পর্যায়ক্রমে শেষ হয়ে যাচ্ছে। ইইউর অস্ত্র বাদে সবকিছু (ইবিএ) প্রকল্প অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থায়ী হবে না।
ভিয়েতনাম এবং কম্বোডিয়ার মতো প্রতিযোগীরা এলডিসি-পরবর্তী বাণিজ্য নিয়মের সাথে খাপ খাইয়ে নিয়েছে; বাংলাদেশকেও একই কাজ করতে হবে।
বিলম্বের পরিবর্তে কৌশলগত অগ্রাধিকার
রপ্তানি বৈচিত্র্য: আরএমজির বাইরে
ক্ষেত্রের বর্তমান শেয়ার বৃদ্ধির সম্ভাবনা মূল পদক্ষেপ:
আরএমজি ৮৪% রপ্তানি মাঝারি উচ্চমানের ফ্যাশন, কারিগরি টেক্সটাইলের দিকে অগ্রসর হওয়া।
ঔষধ শিল্প ২ বিলিয়ন ডলার উচ্চ এফডিএ অনুমোদন, এপিআই উৎপাদন।
আইটি/বিপিও ১.৫ বিলিয়ন ডলার অত্যন্ত উচ্চ দক্ষতা উন্নয়ন, স্টার্টআপ তহবিল।
চামড়া/পাদুকা $১.২ বিলিয়ন ডলার ইইউ ইকো-স্ট্যান্ডার্ডের সাথে উচ্চ সম্মতি।
হালকা প্রকৌশল।
কেস স্টাডি: ভিয়েতনাম ইলেকট্রনিক্স (স্যামসাং) এবং যন্ত্রপাতি বৃদ্ধি করে রপ্তানির উপর টেক্সটাইল নির্ভরতা ৬০% থেকে ৪০% এ কমিয়ে এনেছে।
এলডিসি-পরবর্তী বাজার অ্যাক্সেস নিশ্চিত করা
ইইউর সঙ্গে জিএসপি+: ২৭টি আন্তর্জাতিক কনভেনশন অনুমোদন করা প্রয়োজন (বাংলাদেশ ১৫টি পূরণ করেছে)।
দ্বিপক্ষীয় এফটিএ: চীন এবং ভারতের সঙ্গে আলোচনা ত্বরান্বিত করতে হবে।
আঞ্চলিক একীকরণ: বিমসটেক বাণিজ্য সুবিধা ইবিএ ক্ষতি পূরণ করতে পারে।
প্রতিযোগিতামূলকতার জন্য অভ্যন্তরীণ সংস্কার
ব্যাংকিং খাত: কঠোর তত্ত্বাবধানের মাধ্যমে খেলাপি ঋণ (বর্তমানে ঋণের ৮.৫%) হ্রাস করা।
কর সংস্কার: ডিজিটাল সংগ্রহের মাধ্যমে কর/জিডিপি অনুপাত (৯% বনাম ভিয়েতনামের ১৮%) বৃদ্ধি করা।
ব্যবসা করার সহজতা: লাল ফিতা কাটা (বিশ্বব্যাংক সূচকে ১৬৮তম স্থানে)।
অপ্রস্তুত স্নাতকের ঝুঁকি
১. বাণিজ্য ধাক্কা পরিস্থিতি
যদি বাংলাদেশ জিএসপি+ ছাড়াই স্নাতক হয়:
ইইউতে আরএমজি শুল্ক: ০% থেকে ১২% এ উন্নীত করুন → $২.৬ বিলিয়ন রপ্তানি ক্ষতি (সিপিডি অনুমান)।
চাকরি হ্রাস: ১০ লক্ষ আরএমজি কর্মী ঝুঁকিতে।
২. এফডিআই মন্দা
এলডিসি কর সুবিধা ইপিজেডগুলোতে এফডিআই আকর্ষণ করে। স্নাতকোত্তর, বাংলাদেশকে অবকাঠামো/দক্ষতার উপর প্রতিযোগিতা করতে হবে।
৩. সামাজিক অস্থিরতা
ক্রমবর্ধমান বেকারত্ব অস্থিরতা সৃষ্টি করতে পারে, বিশেষ করে যদি সুরক্ষা জাল (যেমন, আশ্রয়ণ আবাসন) দুর্বল হয়।
৬ বছরের কর্ম পরিকল্পনা (২০২৬-২০৩২)
বছর ১ (২০২৬)
অবশিষ্ট GSP+ কনভেনশনগুলো (শ্রম অধিকার, জলবায়ু) অনুমোদন করুন।
ফার্মা/আইটি স্টার্টআপগুলোর জন্য 500 মিলিয়ন ডলার দিয়ে ‘রপ্তানি বৈচিত্র্য তহবিল’ চালু করুন।
দ্বিতীয় বছর (২০২৭)
কৃষি-প্রক্রিয়াকরণের উপর জোর দিয়ে চীনের সাথে FTA স্বাক্ষর করুন।
রপ্তানি সময় কমাতে 90% শুল্ক প্রক্রিয়া ডিজিটালাইজ করুন।
তৃতীয় বছর থেকে ষষ্ঠ বছর (২০২৮-২০৩২)
স্নাতক হওয়ার আগে GSP+ মর্যাদা অর্জন করুন।
WTO-সম্মত ভর্তুকি (নগদ প্রণোদনার পরিবর্তে গবেষণা ও উন্নয়ন অনুদান) বাস্তবায়ন করুন।
উপসংহার: বিলম্বকে না, সংস্কারকে হ্যাঁ
LDC থেকে স্নাতক হওয়ার ছয় বছরের স্থগিতাদেশ একটি অস্থায়ী সমাধান যা উন্নয়নের পরবর্তী পর্যায়ের জন্য বাংলাদেশের প্রস্তুতিকে উপেক্ষা করে। পরিবর্তে, সরকারের উচিত:
2026-পরবর্তী বাজারে প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করার জন্য GSP+ এবং FTA দ্রুততর করা।
লক্ষ্যযুক্ত খাতভিত্তিক নীতিমালার মাধ্যমে রপ্তানি বৈচিত্র্যকরণ করুন।
LDC সুবিধার বাইরে FDI আকর্ষণ করার জন্য প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালী করুন।
মনোযোগী সংস্কারের মাধ্যমে, বাংলাদেশ স্নাতকোত্তরকে এশিয়ার পরবর্তী উদীয়মান অর্থনীতিতে পরিণত করার জন্য হুমকি নয় বরং একটি সুযোগে রূপান্তর করতে পারে। সময় দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে; কৌশলগত পদক্ষেপ এখনই শুরু করতে হবে।
লেখক: অর্থনীতিবিদ ও অর্থনীতির অধ্যাপক,
বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস অ্যান্ড টেকনোলজি (বিইউবিটি)

ইলিশ আমাদের জাতীয় মাছ। ইলিশের টেকসই উৎপাদন বৃদ্ধিতে ২০০৪ সালে ‘হিলশা ফিশারিজ ম্যানেজমেন্ট অ্যাকশন প্ল্যান’ প্রণয়ন করা হয় এবং তদনুযায়ী সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ইলিশের উৎপাদন উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়। দেশের মোট মৎস্য উৎপাদনে ইলিশের অবদান সর্বোচ্চ (প্রায় ১২%) এবং জিডিপিতে অবদান ১ শতাংশ। বিশ্বের মোট উৎপাদিত ইলিশের ৮০ শতাংশের বেশি আহরিত হয় এ দেশের নদ-নদী থেকে। শুধু তাই নয়; উপকূলীয় জেলে, মৎস্যজীবী সম্প্রদায় এবং উপকূলবাসীদের জীবন-জীবিকা নির্বাহে ইলিশের গুরুত্ব অপরিসীম। প্রায় ৬ লাখ মানুষ ইলিশ আহরণে সরাসরি নিয়োজিত এবং ২০-২৫ লাখ মানুষ ইলিশ পরিবহন, বিক্রয়, জাল ও নৌকা তৈরি, বরফ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ইত্যাদি কাজে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত। বৈচিত্র্যময় জীবন ইলিশের। ইলিশ মূলত সামুদ্রিক মাছ হলেও প্রজননকালীন এ মাছ ডিম ছাড়ার জন্য বেছে নেয় স্বাদুপানির উজানকে। এ সময় ইলিশ দৈনিক প্রায় ৭১ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিতে পারে। প্রজননের উদ্দেশে ইলিশ প্রায় ১ হাজার ২০০ কিলোমিটার উজানে পাড়ি দিতে সক্ষম। সাগর থেকে ইলিশ যত ভেতরের দিকে আসে, ততই শরীর থেকে লবণ কমে যায়। এতে স্বাদ বাড়ে ইলিশের।
ইলিশ মাছের প্রধান প্রজনন মৌসুমে নিরাপদে ডিম ছাড়ার সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে এ বছর প্রতি বছরের মতো এবারও বৈশাখের শুরু অর্থাৎ ১৪ এপ্রিল মধ্যরাত থেকে ১১ জুন পর্যন্ত ৫৮দিন বঙ্গোপসাগরে মাছ ধরায়, পরিবহন, মজুত, বাজারজাতকরণ, ক্রয়-বিক্রয় ও বিনিময় নিষেধাজ্ঞা দিয়েছিল মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়। নিষেধাজ্ঞা শেষে ১২ জুন থেকে সাগরে আবার মাছ আহরণ শুরু করেন জেলেরা, যে সময়টিকে ইলিশ আহরণের ভরা মৌসুম হিসেবে বিবেচনা করা হয়। দেশে ইলিশ উৎপাদন বৃদ্ধিকে সর্বসাধারণ, বিশেষ করে জেলে, মৎস্যজীবী সম্প্রদায় ও ইলিশের সঙ্গে সম্পৃক্ত ব্যবসায়ী, আড়তদার, বরফকল মালিক, দাদনদার, ভোক্তাসহ সবাইকে সচেতন ও উদ্বুদ্ধ করাই উদ্দেশ্য। ২০২৫ সালে প্রধান প্রজনন মৌসুমে ইলিশ সংরক্ষণ এলাকা হিসেবে অভিযানে ৩৮টি জেলার ১৭৮টি উপজেলাকে নির্ধারণ করা হয়।
মৎস্য অধিদপ্তরের তথ্যানুযায়ী, গত অর্থবছরে দেশে ইলিশ আহরণের পরিমাণ আগের বছরের চেয়ে কমে গিয়েছিল। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে দেশে ইলিশ আহরণ হয়েছিল ৫ লাখ ২৯ হাজার মেট্রিকটন। আর ২০২২-২৩ অর্থবছরে পরিমাণ ছিল ৫ লাখ ৭১ হাজার ৩৪২ টন। এর আগে, ২০২১-২২ সালে ইলিশ আহরণ হয়েছিল ৫ লাখ ৬৬ হাজার ৫৮৩ টন। ২০২০-২১ সালে ৫ লাখ ৬৫ হাজার ১৮৩ টন, ২০১৯-২০ সালে ৫ লাখ ৫০ হাজার ৪২৮ মেট্রিকটন, ২০১৮-১৯ সালে ৫ লাখ ৩২ হাজার ৭৯৫ মেট্রিকটন, ২০১৭-১৮ সালে ৫ লাখ ১৭ হাজার ১৯৮ টন এবং ২০১৬-১৭ সালে ৪ লাখ ৯৬ হাজার ৪১৭ মেট্রিকটন ইলিশ আহরণ হয়েছিল। সরকারি হিসাব অনুযায়ী, ২০০৪-০৫ অর্থবছরে ইলিশ আহরণ হয়েছিল ২ লাখ ৭৫ হাজার মেট্রিকটন। এক হিসেবে গত দেড় যুগে ইলিশের আহরণ দ্বিগুণেরও বেশি বেড়েছে। এর মধ্যে গত সাত বছরে ইলিশ আহরণের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য হারে বাড়ছে, শুধুমাত্র ২০২৩-২৪ অর্থবছর ছাড়া। কিন্তু এরপরও ইলিশের দাম ক্রেতা সাধারণের নাগালের মধ্যে থাকে না। গত আট বছরের রপ্তানির চিত্র বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, মোট আহরণের এক শতাংশেরও কম ইলিশ মাছ রপ্তানি হয়। বাকি ৯৯ শতাংশ ইলিশ মাছ দেশের বাজারেই বিক্রি হয়। এর পরও প্রতি বছর ইলিশের দাম ৩০ থেকে ৩৩ শতাংশ হারে বাড়ছে বলে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের তথ্যে জানা গেছে। সংস্থাটির তথ্যানুযায়ী, ২০১৬ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত আট বছরে ইলিশের দাম গড়ে কেজিতে ৪০০ থেকে ৫০০ টাকা বেড়েছে। আর ১৮ বছরের ব্যবধানে দেশে ইলিশের দাম বেড়েছে প্রায় ১০০ শতাংশ। মৎস্যজীবীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, ১২ জুন থেকে প্রায় দেড়মাস চাহিদা অনুযায়ী সাগরে ইলিশ ধরা পড়েনি। আবহাওয়াজনিত কারণে সাগর উত্তাল থাকছে প্রায়ই। ফলে মাছ ধরার নৌযানগুলো গভীর সাগরে যেতে পারছে না। কিংবা গেলেও আহরণ কম ছিল। কিন্তু চলতি সপ্তাহে এসে এ চিত্র পাল্টে গেছে। সপ্তাহজুড়ে নৌকাপ্রতি ইলিশ আহরণের পরিমাণ আগের চেয়ে দ্বিগুণ-তিনগুণ বেড়েছে। দেশে সবচেয়ে বেশি ইলিশ আহরণ হয় চট্টগ্রাম বিভাগের সমুদ্র উপকূলবর্তী জেলাগুলোয়। অবশ্য মাছ ধরার সমুদ্রগ্রামী বাণিজ্যিক জাহাজগুলোর হিসেব ওঠে চট্টগ্রামের তালিকায়। এর বাইরে পদ্মা-মেঘনার অববাহিকায় ভোলা, খুলনা, বরিশাল ও চাঁদপুর জেলায় প্রচুর ইলিশ ধরা পড়ে।
এ বছরও ভরা মৌসুমে ইলিশের দাম ক্রেতার নাগালের মধ্যে নেই। বর্তমানে
এক কেজি বা তার বেশি ওজনের প্রতি কেজি ইলিশ মাছ বিক্রি হয়েছে ১৩৭৫ টাকায়, ৬০০ থেকে ৮০০ গ্রাম ওজনের ১১০০ টাকা, ৫০০ গ্রাম ওজনের ইলিশ ৯০০ টাকা, ৩০০ থেকে ৪০০ গ্রাম ওজনের ইলিশ ৭০০ থেকে ৭৫০ টাকায় বিক্রি হয়েছে। আহরণকারীর নৌকা থেকে ইলিশ পৌঁছে আড়তে।, আড়তে বরফ দিয়ে সংরক্ষণের পর এক কেজি বা তার বেশি ওজনের প্রতি কেজি ইলিশ মাছ ১৪০০-১৪৫০ টাকা, ৬০০ থেকে ৮০০ গ্রাম ওজনের ১১৫০ টাকা, ৫০০ গ্রাম ওজনের ইলিশ ৯৫০-১০০০ টাকা, ৩০০ থেকে ৪০০ গ্রাম ওজনের ইলিশ ৮০০ থেকে ৯৫০ টাকায় বিক্রি করা হচ্ছে। আড়ত থেকে ইলিশ যায় বিভিন্ন পাইকারি বাজারে। সেখানে এক কেজি ওজনের ইলিশ মাছ ২ হাজার টাকা, দেড়-দুই কেজি ওজনের ইলিশ ৩ হাজার টাকা এবং ৫০০ গ্রাম বা তার কিছু কম-বেশি ওজনের ইলিশ বিক্রি হচ্ছে ৫০০ থেকে এক হাজার টাকায়। ইলিশ মাছের জোগান ও সরবরাহের ক্ষেত্রে কোনো ঘাটতি নেই। কিন্তু ইলিশের ব্যবসায় বিনিয়োগকারী, মৎস্যজীবী, আড়তদার এবং পাইকারি ব্যবসায়ীদের গড়ে তোলা ‘অদৃশ্য’ সিন্ডিকেটের কারণে দাম কমছে না। প্রতি বছর ইলিশের বাজার এই ‘চার হাতের চক্রের’ মধ্যে ঘুরতে থাকে।আবার কিছু কিছু অনলাইন ব্যবসায়ী ইলিশের বিক্রির নামে প্রতারনার ফাঁদ পেতেছে যা অত্যন্ত দুক্ষ্য জনক ।
একসময় মধ্যবিত্তের নিত্যবাজারে তালিকায় থাকলেও বর্তমানে উপলক্ষের মাছ হয়ে উঠেছে। সময়ের বিবর্তনে হয়ে উঠেছে উচ্চবিত্তের নিত্যখাদ্য অনুষঙ্গ। আর নিম্নবিত্তের কাছে ইলিশ দীর্ঘশ্বাসের অপর নাম, যাদের বছরে একটি উৎসবেও হয়তো খেয়ে দেখা হয় না এক টুকরো ইলিশ। রুপালি ইলিশের কেজিপ্রতি দাম যখন ২৮শ থেকে ৩২শ টাকা, তখন বাঙালি যেন চোখ মেলে প্রশ্ন করে, ইলিশ আসলে কার?, পাবনার তহুরা আজিজ ফাউন্ডেশনের পরিচালক একটি ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। শহরের কালাচাঁদপাড়ায় নিজ বাড়ির আঙিনায় তিনি আয়োজন করেন ‘গরিবের ইলিশ উৎসব’। এক দিনের এই উৎসবে শতাধিক দরিদ্র ও ছিন্নমূল মানুষকে পরিবেশন করা হয় ইলিশ। এই আয়োজনে শুধু পেট ভরে না; ভরে ইলিশপ্রেমী নিম্নবিত্তের মন। বর্তমান বাস্তবতায় এমন আয়োজন নিছক উৎসব; অর্থনৈতিক বৈষম্য ও বাজার নিয়ন্ত্রক সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে নীরব প্রতিবাদ। এই উদ্যোগ দেখিয়ে দেয়– দায় শুধু রাষ্ট্র বা নীতিনির্ধারকদের নয়; সমাজের সচেতন নাগরিকদেরও।
সরকার প্রতি বছর মা ইলিশ রক্ষায় অভিযান চালায়; আইন করে জাটকা ধরা বন্ধ রাখে। শূন্য রেখায় মাছ ধরা নিষিদ্ধ করে। এর ফলে কিছু বছর ভালো ফলও এসেছে। বিশেষ করে ২০২০ সালে রেকর্ড পরিমাণ ইলিশ ধরা পড়েছিল। কিন্তু সমস্যা হলো, উদ্যোগগুলোর ধারাবাহিকতা নেই। আইন আছে, প্রয়োগ নেই। সচেতনতা কম, বিকল্প ব্যবস্থা দুর্বল। দিনে দিনে কমছে ইলিশের উৎপাদন। অন্যদিকে অসাধু ব্যবসায়ীরা অধিক মুনাফার লোভে এই ইলিশকে ঢুকিয়ে রাখছে হিমাগারে। বাজারে হাহাকার ফেলে, সিন্ডিকেটের বেড়াজালে বাড়িয়ে ফেলা হচ্ছে ইলিশের দাম। নদীভিত্তিক জীবিকা চলে যাচ্ছে, আর মানুষ দোষ দিচ্ছে প্রকৃতিকে। এ অঞ্চলে মাছের অর্থনীতি, রাজনীতি এতটাই গভীর যে, একসময় ভারত সরকার যখন বাংলাদেশ থেকে ইলিশ আমদানির সিদ্ধান্ত নেয়, তখন সেটাকে কূটনৈতিক মাইলফলক বলে মনে করা হয়। আবার নির্বাচনের আগে বিশেষ রকম সুবিধা পেতে ইলিশ সরবরাহ নিয়েও গুঞ্জন ওঠে রাজনৈতিক মহলে। মাছ যদি রাজনীতিতে ঢুকে পড়ে, তাহলে বুঝতে হবে, সে আর মাছ নেই। আর গরিবের ইলিশ কেবল স্বপ্নেই রয়ে গেল।
লেখক: গবেষক ও অধ্যাপক

সিলেটে এক অনুষ্ঠানে বাউল সম্রাট শাহ আব্দুল করিমকে সংবর্ধনা দেয়া হচ্ছিল। অনুষ্ঠানের শেষের দিকে উপস্থাপক ঘোষণা দিলেন, এখন বাউল শাহ আবদুল করিমের হাতে সোয়া ৩ লাখ টাকার চেক তুলে দেয়া হবে। অনুষ্ঠানের এক পাশে শাহ আবদুল করিম বসে আছেন। ঘোষণা শুনতেই তিনি তার পাশে থাকা ছেলে শাহ নূর জালাল বাবুলকে বললেন- ‘সোয়া ৩ হাজার টাকা! এত টাকা দিয়া আমি কি করমু! এত টাকা আমার লাগবে না।’ পাশ থেকে বলা হলো সোয়া ৩ হাজার টাকা না, সোয়া ৩ লাখ টাকা। শাহ আবদুল করিম এবার টাকার অংক শুনে বলেই ফেললেন, ‘এত টাকা দিয়া আমার কাজ কী? মানুষ আমারে ভালোবাসে এটাই বড়। এই টাকা আমার লাগবো না। এই বাবুল চল, বাড়িত যাই।’ এই নির্লোভ বাউলকে কোনো একদিন দোহারের শিল্পী কালিকাপ্রসাদ ভট্টাচার্য জিজ্ঞেস করেছিলেন-‘মানুষ আপনার গান বিকৃত সুরে গায়। আপনার সুর ছাড়া অন্য সুরে গায়। অনেকে আপনার নামটা পর্যন্ত বলেন না। এসবে আপনার খারাপ লাগে না? ‘শাহ্ আবদুল করিম জবাবে বললেন- ‘কথা বোঝা গেলেই হইল, আমার আর কিচ্ছু দরকার নাই।’ কালিকাপ্রসাদ ভট্টাচার্য ভীষণ অবাক হলেন। তিনি আশ্চর্য হয়ে বললেন, ‘আপনার সৃষ্টি, আপনার গান। মানুষ আপনার সামনে বিকৃত করে গাইবে। আপনি কিছুই মনে করবেন না!এটা কোন কথা, এটার কোন অর্থ আছে!’ শাহ আবদুল করিম বললেন- ‘তুমি তো গান গাও, আমার একটা প্রশ্নের উত্তর দাও তো। ধরো, তোমাকে একটা অনুষ্ঠানে ডাকা হলো। হাজার হাজার চেয়ার রাখা আছে কিন্তু গান শুনতে কোন মানুষ আসে নাই। শুধু সামনের সারিতে একজন মানুষ বসে আছে। তুমি কি গান গাইতে পারবে?’ কালীপ্রসাদ কিছুক্ষণ ভেবে উত্তর দিলেন- ‘না, তা আমি পারব না।’ শাহ আবদুল করীম হেসে বললেন- ‘আমি পারব, কারণ আমার গানটার ভেতর দিয়ে আমি একটা আদর্শকে প্রচার করতে চাই। সেটা একজন মানুষের কাছে হলেও। সুর না থাকুক, নাম না থাকুক। কিন্তু সেই আদর্শটা থাকলেই হলো। আর কিছু দরকার নাই, সেজন্যই বললাম শুধু গানের কথা বোঝা গেলেই আমি খুশি! ‘কালীপ্রসাদ ভট্টাচার্য কৌতুহল বেড়ে গেলো,তিনি জানতে চাইলেন, ‘সেই আদর্শটা কি? বাউল বললেন’ একদিন এই পৃথিবীটা বাউলের পৃথিবী হবে, এই পৃথিবী একদিন বাউলের পৃথিবী হয়ে যাবে।’ এই বিখ্যাত মানুষটি যে কতটা নির্লোভী ছিলেন তা এই বাক্যের মধ্য দিয়েই প্রকাশ হয়েছে। ছিলেন কৃষকের সন্তান, মাঠে ঘাটে রাখাল হিসেব গরু চরাতেন, সেই রাখাল বালক থেকে তিনি হয়ে উঠেছিলেন বাউল সম্রাট। অথচ এত খ্যাতির পরও আজীবন তিনি ছিলেন মাটির মানুষ। তার মন-ধ্যান, চিন্তা-চেতনায় আন্তরিকতার কোনো অভাব ছিল না। এমনও হয়েছে তার ঘরে খাবার নেই, কিন্তু দূর দূরান্ত থেকে এসেছেন মেহমান। নিজে না খেয়ে তিনি অতিথি অ্যাপায়নে শান্তি খুঁজে পেয়েছেন। শাহ আব্দুল করিমই বাংলার বাউল সংগীতকে এক অনন্য উচ্চাতায় নিয়ে গেছেন। তার গানে ভাটি অঞ্চলের মানুষের জীবনের সুখ-দুঃখ, প্রেম-প্রীতি, ভালোবাসার পাশাপাশি উঠে এসেছে সকল অন্যায়, অবিচার, কুসংস্কার আর সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে বিশুদ্ধতার সুর। এই শিল্পী গানের অনুপ্রেরণা পেয়েছেন প্রখ্যাত বাউল সম্রাট ফকির লালন শাহ, পুঞ্জু শাহ এবং দুদ্দু শাহ এর দর্শন থেকে। তিনি বাউল গানের দীক্ষা নিয়েছিলেন সাধক রশীদ উদ্দীন, শাহ ইব্রাহীম মাস্তান বকশ এর মতো গুণিদের কাছ থেকে। কেবল বাউল গান না; শরীয়তী, মারফতি, দেহতত্ত্ব, গণসংগীতসহ সংগীতের বহুরূপ সৃষ্টি হয়েছে তার হাত ধরেই। তার রচিত প্রায় ৫শতাধিক গানের সম্ভারের ২০টির মতো গান ইংরেজি ভাষায় অনূদিতও হয়েছে। এই গুণি মানুষটি হতে পারে আমাদের অহংকারী সমাজের দৃষ্টান্তের প্রতীক, আদর্শের মিনার।

বাংলাদেশের অতি সাম্প্রতিককালের একটি বহুল আলোচিত ও ব্যাপক বিস্তৃত অনুষঙ্গ হচ্ছে মব (mob) বা উচ্ছৃঙ্খল জনতা। মানুষ সারাক্ষণই এ মবের ভয়ে এই ভেবে আতঙ্কে থাকে যে, কখন না কার উপর এটি ভর করে বসে। আর এ ভীতির মাত্রা ইদানীংকালে আরো বিস্তার লাভ করেছে এ কারণে যে, মবের পেছনে আগে কোনো সাংগঠনিক বা প্রাতিষ্ঠানিক শক্তির সংশ্লিষ্টতা না থাকলেও এখন তা প্রাতিষ্ঠানিকভাবেও সৃষ্টি করা হচ্ছে, যার নাম দেওয়া হয়েছে ‘চাপ’। তো এই মবের মতো সমান গতিতে বা তারচেয়েও অধিক শক্তিতে চারদিকে এখন দ্রুত বিস্তার লাভ করছে ধর্ষণ। এবং সে ধর্ষণের ঘটনা ইদানীং এতটাই বেড়ে গেছে যে, বিষয়টি এখন আর কেবল উদ্বেগের পর্যায়ে সীমাবদ্ধ নেই-- উদ্বেগের মাত্রা ছাড়িয়ে তা এরইমধ্যে এক ধরনের আতঙ্কময় পরিস্থিতিতে রূপান্তরিত হয়েছে। বাসগৃহ থেকে শুরু করে বাস, ট্রেন, লঞ্চ, জনপথ, পর্যটন কেন্দ্র সর্বত্রই এটি সংক্রামক ব্যাধির মতো ছড়িয়ে পড়েছে।
তবে উল্লিখিত ধর্ষণের যত সংখ্যক ঘটনার কথা সাধারণ মানুষ গণমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের সুবাদে জানতে পারছে, এক্ষেত্রে প্রকৃত ঘটনা তারচেয়েও অনেক বেশি। অর্থাৎ এ ভয়াবহতার প্রকৃত মাত্রা দৃশ্যমান বাহ্যিক অবস্থার চেয়েও অনেক বেশি নিষ্ঠুর। বর্তমান অবস্থায় ধর্ষণের যেসব ঘটনার কথা গণমাধ্যম বা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের কল্যাণে জনসমক্ষে প্রকাশ পাচ্ছে, বস্তুত সেগুলোর ধরন, বৈশিষ্ট্য ও সংখ্যা দেখেই মানুষ এর ভয়াবহতা সম্পর্কে একটি প্রাথমিক ধারণা তৈরি করে নিচ্ছে। কিন্তু তারাই জানলে আরো বিস্মিত হবেন যে, এ উভয় মাধ্যমের বিস্তার ও পরিধির বাইরে বাংলাদেশের প্রত্যন্ত ও প্রান্তিক জনপদগুলোতে এ জাতীয় বা এরচেয়েও জঘন্য ধর্ষণের ঘটনা প্রতিদিনই আরো অনেক বেশি সংখ্যায় ঘটে চলছে। কিন্তু লোকলজ্জা, ধর্ষকের সামাজিক প্রভাব, যোগাযোগ অবকাঠামোর পশ্চাৎপদতা ও অন্য নানাবিধ কারণে সেসব জনসমক্ষে প্রকাশ পাচ্ছে না।
উল্লিখিত পরিস্থিতিতে জনসমক্ষে প্রকাশ পাওয়া ও লোকচক্ষুর আড়ালে থাকা অর্থাৎ জনসমক্ষে প্রকাশ না পাওয়া-- এ উভয়বিধ ধর্ষণের বিস্তার, এসবের প্রকৃতি ও সম্ভাব্য কারণ নিয়ে এখানে অতি সংক্ষেপে খানিকটা আলোচনা করা হলো। আশা করব, সমস্যাটির ভয়াবহতা বিবেচনায় এবং এর বিস্তার রোধ ও প্রতিহতকরণের উদ্দেশে জনমত গড়ে তোলার লক্ষ্যে অন্যেরাও এ ধরনের আলোচনায় যুক্ত হবেন। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, দেশে হঠাৎ করেই ধর্ষণের ঘটনা এভাবে এতোটা বেড়ে গেল কেন? এর কারণ একাধিক। তবে মূল কারণ অবশ্যই সমাজ ও রাষ্ট্রে বিচার, ন্যায়ের শাসন, রাজনৈতিক স্থিরতা এবং সামাজিক ঐক্য ও সংহতি না থাকা। তদুপরি রয়েছে অর্থনীতির নানা নেতিবাচক অনুষঙ্গ যার মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য হচ্ছে বেকারত্ব, প্রয়োজনের তুলনায় আয়ের ঘাটতি, নিত্যপণ্যের ঊর্ধ্বমূল্য ইত্যাদি। আর উল্লিখিত এই উভয় শ্রেণির সমস্যা সমাজের সব শ্রেণি ও পেশার এবং সব বয়নি ও লিঙ্গের মানুষকে স্পর্শ করলেও তা সর্বাধিক সংখ্যায় করছে তরুণদেরকে। আর এই তরুণদের মধ্যে অভাব, বেকারত্ব ও ভবিষ্যৎ অনিশ্চিতির সমস্যা এতটাই প্রকট যে, সেসব থেকে তাদের ভেতরে যেসব কষ্ট, ক্ষোভ ও হতাশা পুঞ্জিভূত আকারে জমা হয়েছে, সেটাই ক্রমান্বয়ে নানা হিংস্রতাপূর্ণ পাশবিক প্রবণতার দিকে ধাবিত হতে হতে বর্তমানের ধর্ষণ বা গণধর্ষণ পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে। আর তারই এক ধরনের আদিম বহিঃপ্রকাশ হচ্ছে সাম্প্রতিক সময়ে অতিদ্রুত হারে বেড়ে চলা ধর্ষণের ঘটনাগুলো।
এসব ঘটনা বেড়ে যাওয়ার পেছনে ধর্ষকের সামাজিক ও রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতাও একটি বড় কারণ। এক্ষেত্রে সম্প্রতি ঘটে যাওয়া কিছু ঘটনা বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই ধর্ষক বা ধর্ষণকারীরা কোনো না রাজনৈতিক, সামাজিক ও পেশাজীবী সংগঠনের সঙ্গে জড়িত। এরূপ জড়িত থাকার উদাহরণ হচ্ছে: মুরাদনগরে রাজনৈতিক সংগঠনের সঙ্গে জড়িত থাকা, টাংগাইলে বাসে শ্রমিক ইউনিয়নের সঙ্গে, নোয়াখালীর গ্রামে স্থানীয় সমিতির সঙ্গে ইত্যাদি। মোটকথা ধর্ষক ধরেই নিচ্ছে যে, তাকে রক্ষা করার জন্য তার পেছনে সাংগঠনিক শক্তির সমর্থন যথেষ্টই রয়েছে। অন্যদিকে ধর্ষকের সামাজিক অবস্থানও তার একটি বড় রক্ষাকবচ। সমাজের বিত্তবান বা প্রভাবশালী পরিবারের সদস্যরা এসব ঘটনায় জড়িত হয়েও চারপাশের প্রভাব-প্রতিপত্তির কারণে সহজেই পার পেয়ে যাচ্ছে। আর তাদেরকে ধর্ষণের আনুষ্ঠানিক অভিযোগ থেকে মুক্তিদানের ব্যাপারে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর অস্বচ্ছ আচরণ, প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের উদ্যমহীন দায়িত্বহীনতা, বিচারব্যবস্থার নির্লিপ্ততা ও গাফিলতি ইত্যাদি এতোটাই দায়ী যে, এটিকে শুধু রাষ্ট্রব্যবস্থার ত্রুটি ও দুর্বলতা বললে খুবই সামান্য বলা হয়। আসলে এগুলো হচ্ছে অসহায় ধর্ষিতাদের প্রতি রাষ্ট্রের একধরনের শোষণ ও উপেক্ষামূলক বর্বর দৃষ্টিভঙ্গিরই বহিঃপ্রকাশ।
তবে ধর্ষণের ঘটনা ঘটা ও ঘটার পর ধর্ষককে সে অভিযোগ থেকে বাঁচিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি আগ্রাসী ভূমিকা রাখছে রাষ্ট্রের রাজনীতি। দেশে যখন যে রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় থাকছে, তখন সে দলের অনুসারীরা পুরো দেশ ও দেশের সমুদয় সম্পদকেই তাদের নিজেদের জন্য ‘মালে গণিমত’ ভাবতে শুরু করে, যে গণিমতের আওতায় তারা হয়তো ওই অসহায় ধর্ষিতা নারীকেও গণ্য করে বৈকি! কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় হচ্ছে, যে রাজনৈতিক নেতারা এসব অপকর্মকে প্রশ্রয় দেন, তারা যখন জনগণের কাছে ভোট চাইতে যান, তখন সে ভোটারদের কেউই তাকে প্রশ্ন করেন না যে, বিভিন্ন সময়ে ধর্ষকের পক্ষে দাঁড়ানোর কারণে ইতোমধ্যে তিনি তার ভোট চাওয়ার নৈতিক অধিকার হারিয়েছে ফেলেছেন কিনা। আশা করা হচ্ছে, সামনেই নির্বাচন। ধর্ষণের ক্ষত শুকিয়ে যাওয়ার আগেই ওই নির্বাচনের ভোটপ্রার্থীদের কাছে ভোটাররা কি দয়া করে এর কারণ জানতে চাইবেন? আর তাদের কাছে এটাও জানতে চাওয়া যেতে পারে যে: তুলনামূলকভাবে দরিদ্র, সংখ্যালঘু এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতার দিক থেকে পিছিয়েপড়া নারীরাই কেন অধিক হারে ধর্ষণের শিকার হচ্ছেন? রাজনীতিকদের কাছে এ প্রশ্নও রাখছি যে, ধর্ষককে প্রশ্রয় দিয়ে ও তাকে নিজ দলের কর্মী-কাম-লাঠিয়াল বানিয়ে এ দেশের জন্য কোন রাষ্ট্রব্যবস্থা তার গড়ে তুলবেন?
ধর্ষণের ঘটনা বেড়ে যাওয়ার পেছনে উপরোক্ত কারণসমূহ ছাড়াও সাম্প্রতিক সময়ে আরো কিছু নতুন কারণ সমাজে সৃষ্টি হয়েছে, যেসবের বেশিরভাগই আলোচনার বাইরে থেকে যাচ্ছে। এর একটি হচ্ছে: উপার্জনের প্রয়োজনে বাংলাদেশের গ্রামগুলোর এক বিরাট সংখ্যক মানুষ বর্তমানে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কাজ করছে, যে ক্ষেত্রে তার পরিবারের নারী সদস্যদেরকে অনেকটা ঝুঁকি নিয়েই দেশে বসবাস করতে হচ্ছে। কিছু বছর আগ পর্যন্তও বাংলাদেশের গ্রামগুলোর দীর্ঘকালীন ঐতিহ্যিক সংহতির কারণে এ নিয়ে তেমন কোনো সমস্যা ছিল না। কিন্তু সাম্প্রতিককালে এসব পরিবারের জন্য যৌন হয়রানিসহ নানাবিধ সামাজিক নিরাপত্তাহীনতার ঝুঁকি প্রচণ্ডভাবে বেড়ে গেছে। দেশে একটি শক্তিশালী স্থানীয় সরকারব্যবস্থা বহাল থাকলে এ দেখভালের কাজটি খুব সহজেই তারা করতে পারত। একইভাবে যেসব গ্রামীণ পরিবারের পুরুষ সদস্যরা বর্তমানে পরিবার-পরিজনকে গ্রামের বাড়িতে রেখে শহরে যেয়ে কাজ করছেন, সেসব পরিবারের নারী সদস্যদের জন্যও নিরাপত্তাহীনতার অনুরূপ ঝুঁকি দিন দিনই বেড়ে চলেছে। আর পোশাক শিল্পের দরিদ্র অসহায় দুঃখী মেয়েরাতো এখন ধর্ষণের সবচেয়ে বড় লক্ষ্য (target)। তথ্য পর্যালোনা করলে দেখা যাবে যে, সারাদেশে গত পাঁচ বা দশ বছরের মধ্যে যারা ধর্ষণের শিকার হয়েছেন, তাদের মধ্যে এই পোশাককর্মীর সংখ্যাই সর্বাধিক।
ধর্ষণের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণ নিয়ে উপরে যে আলোচনা করা হলো, তার বাইরে যেয়ে এসবের মনস্তাত্ত্বিক পর্যালোচনায় দেখা গেছে যে, এসব ঘটনায় ধর্ষকের মধ্যে যৌন আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করার চেয়েও অধিক হারে কাজ করে এক ধরনের রাগ, ক্ষোভ, ক্রোধ ও হতাশা, যার কিছুটা নিজের প্রতি হলেও বেশির ভাগটাই চলমান রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রতি। ওই যে দেশের তরুণেরা এখন বন্যার স্রোতের মতো বিদেশে চলে যাওয়ার জন্য হন্যে হয়ে ছুটছে, সেটি যেমন বহুলাংশে রাষ্ট্রের প্রতি ক্ষোভ ও হতাশা থেকে, এই ধর্ষকদের ক্ষেত্রেও বিষয়টি মোটামটি একই। ধর্ষণের মতো পাশবিক অমানবিকতা প্রকাশের মাধ্যমে সে বস্তুত রাষ্ট্রের প্রতিই এক ধরনের ঘৃণা প্রকাশ করতে চায়, যদিচ সে ঘৃণা প্রকাশের জন্য এটি কোনো গ্রহণযোগ্য পথ নয়। এমতাবস্থায় ধর্ষণ প্রতিরোধে আশু ও জরুরি ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় গ্রহণের পাশাপাশি রাষ্ট্রকে ঐসব ব্যবস্থাদিও গ্রহণ করতে হবে, যার প্রেক্ষিতে রাষ্ট্রের প্রতি ধর্ষকের ঘৃণা, ক্ষোভ ও হতাশাগুলোও দূরীভূত হশ।
শিরীন আমজাদ: সাবেক অধ্যক্ষ, মির্জা আব্বাস মহিলা কলেজ, ঢাকা।
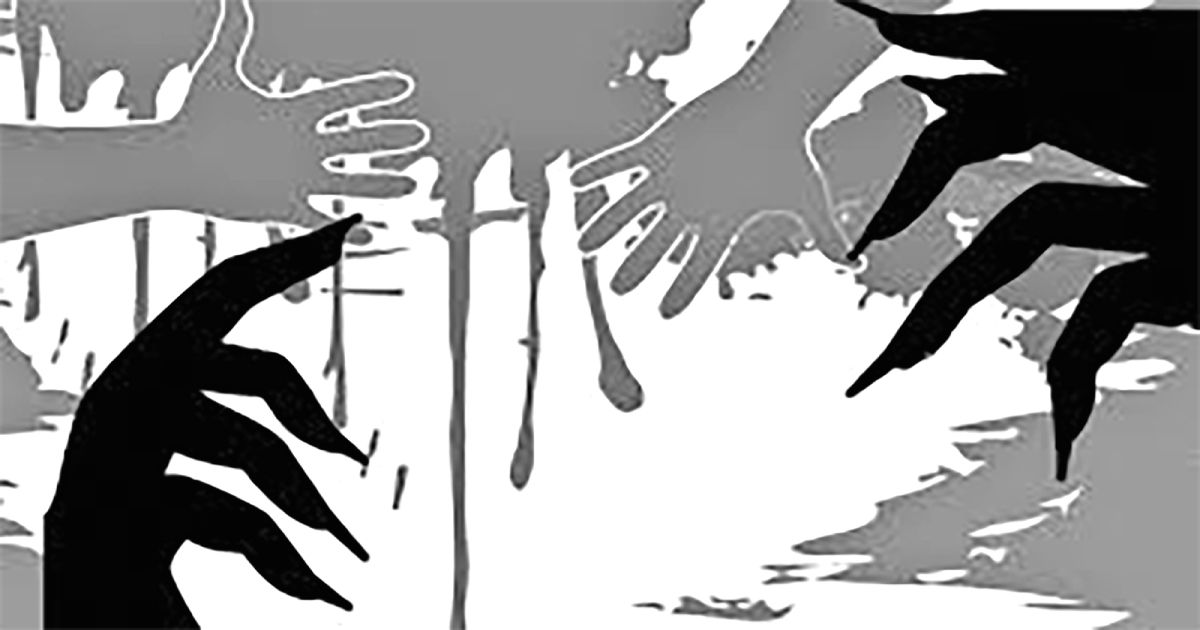
ষড়যন্ত্র হলো কিছু মানুষের গোপন পরিকল্পনা, যা সাধারণত অনৈতিক বা ক্ষতিকর উদ্দেশে করা হয়। এটি একটি গোপন চুক্তি, যা কোনো অন্যায় বা ক্ষতি করার জন্য করা হয়। ‘ষড়যন্ত্র তত্ত্ব’ বলতে বোঝায় কোনো ঘটনার পেছনে কিছু মানুষের তৈরি করা জটিল ও গোপন পরিকল্পনা, যা অস্পষ্ট ও বিতর্কিত হয়ে থাকে। ষড়যন্ত্র বহু ধরনের। সাধারণত নিম্নোক্ত ধরনের আওতাভুক্ত হতে পারে, যেমন: (১) পারিবারিক ষড়যন্ত্র; (২) সামাজিক ষড়যন্ত্র; (৩) সংগঠনগত ষড়যন্ত্র; (৪) অর্থনৈতিক ষড়যন্ত্র; (৫) রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র; (৬) প্রাসাদ ষড়যন্ত্র; (৭) ইত্যাদি। ষড়যন্ত্রের মূল বিষয় ইতিবাচক নয়; সবই নেতিবাচক ও ধ্বংসাত্বক। উল্লেখ্য যে, ইসলামে অন্যের ক্ষতি করার জন্য বা অন্যের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার ব্যাপারে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে। কুরআন ও হাদিসের মাধ্যমে যারা অন্যের ক্ষতি করার চেষ্টা করে, তাদের পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, অন্যের ক্ষতি করার চেষ্টা করলে আখিরাতে তার কঠিন প্রতিফল ভোগ করতে হবে। মূলত প্রতিহিংসাপরায়ন কতিপয় হীন মনের মানুষ কর্তৃক কর্তৃত্ব, লোভ, লালসা, জিঘাংসা, জিদ, আধিপত্য ইত্যাদির জন্য সংঘটিত হয়ে থাকে। এরা এতটাই জঘন্য মনের মানুষ যে শুধু ব্যক্তি বিশেষ নয়, সমাজ ও দেশের ক্ষতি হলেও তাদের কিছু আসে যায় না। ষড়যন্ত্রকারীদের সম্পর্কে ইংরেজিতে সুন্দর একটি কথা আছে, যা হলো ‘Dirty man with dirty mind in negative phenomena’।
ইতিহাস থেকে জানা যায় যে এই বিশ্বের প্রাথমিক অবস্থা থেকে ষড়যন্ত্র চলে আসছে। অবশ্য এ সব ষড়যন্ত্রের প্রকারভেদ আছে। দুঃখের বিষয় হলো যে, নবী-রাসূল (সা.) এর বিরুদ্ধে কম ষড়যন্ত্র হয়নি? এর স্বপক্ষে একটি জলন্ত উদহারণ হলো আমাদের প্রানপ্রিয় নবীজি (সা.) এর বিরুদ্ধে অন্যতম প্রধান একটি ষড়যন্ত্রের কথা তুলে ধরছি। এ সূত্র ধরে উল্লেখ্য যে, মক্কার মুশরিকরা যখন কোনোভাবেই সাহাবিদের দেশত্যাগ ঠেকাতে পারল না এবং বুঝতে পারল নবীজি (সা.) মদিনায় গিয়ে পৌঁছালে কোনোভাবেই ইসলামের উত্থান তারা ঠেকাতে পারবে না, তখন তারা নবীজি (সা.)-কে প্রতিহত করতে মক্কার ‘পরামর্শ কেন্দ্রে’ একত্র হলো। বৈঠকে উমাইয়া বিন খালফ, আবু জাহাল, নদর বিন হারিসসহ মক্কার শীর্ষ স্থানীয় সাত ব্যক্তি ছিল। কোনো কোনো বর্ণনায় পাওয়া যায় শয়তানও তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল। বৈঠকে আবু জাহাল নবীজি (সা.)-কে হত্যার পরামর্শ দেয়। নাউজুবিল্লাহ! সে বলে প্রত্যেক গোত্র থেকে একজন যুবক হত্যাকাণ্ডে অংশগ্রহণ করবে। সিদ্ধান্ত হয় রাতের আঁধারে তারা একযোগে নবীজির ওপর হামলা করবে। (মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস : ১/৩৮৫; আর-রাহিকুল মাখতুম, পৃষ্ঠা ১৬৭-১৬৮)। এদিকে পবিত্র কোরআনে এই ষড়যন্ত্র সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে, ‘স্মরণ করো, কাফিররা তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে তোমাকে বন্দি করার জন্য, হত্যা করার জন্য অথবা নির্বাসিত করার জন্য এবং তারা ষড়যন্ত্র করে এবং এক্ষেত্রে আল্লাহও কৌশল অবলম্বন করেন। আল্লাহই সর্বশ্রেষ্ঠ কৌশলী।’ (সুরা আনফাল, আয়াত : ৩০)। রাতের বেলা নীলনকশা বাস্তবায়নে আবু জাহাল, হাকাম ইবনে আস, উকবা ইবনে আবি মুয়িত, নদর ইবনে হারিস, উমাইয়া ইবনে খালফসহ ১১ ব্যক্তি মহানবী (সা.)-এর বাড়ি ঘেরাও করে। অন্যদিকে মহানবী (সা.) নিজের বিছানায় আলী ইবনে আবি তালিব (রা.)-কে শুইয়ে দেন। এরপর তিনি হাতে এক মুঠ মাটি নিয়ে কাফিরদের উদ্দেশ্যে নিক্ষেপ করেন এবং সুরা ইয়াসিনের প্রথম থেকে ৯ আয়াত তিলাওয়াত করেন। নিক্ষিপ্ত ধুলা প্রত্যেক দুর্বৃত্তের মাথায় গিয়ে পড়ল এবং তারা কার্যত অন্ধ হয়ে গেল। নবীজি (সা.) তাদের সামনে দিয়ে নিরাপদে বের হয়ে গেলেন। তিনি বের হয়ে যাওয়ার পর একজন আগন্তুক তাদের বলল, তোমাদের উদ্দেশ্য সফল হবে না। আল্লাহর কসম, মুহাম্মদ ঘর থেকে বের হয়ে গেছে। কিন্তু তারা যখন ঘরে উঁকি দিয়ে মহানবী (সা.)-এর বিছানায় অন্য কাউকে শোয়া দেখল, তখন তারা আগন্তুককে তিরস্কার করল। অথচ সকালে যখন আলী (রা.)-কে শয্যা ত্যাগ করতে দেখলেন তারা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেল। (সিরাতে খাতামুল আম্বিয়া, পৃষ্ঠা ৪৭; আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যা, পৃষ্ঠা ৪৫৬। এদিকে আবু সিরমা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি অন্য কারো ক্ষতিসাধন করে, আল্লাহ তাআলা তা দিয়েই তার ক্ষতিসাধন করেন। যে ব্যক্তি অন্যকে কষ্ট দেয়, আল্লাহ তাআলা তাকে কষ্টের মধ্যে ফেলেন। সবচেয়ে বড় কথা হলো, এ ধরনের লোক কিয়ামতের দিন দেউলিয়া হয়ে যাবে।
বাংলাদেশে অনেক ষড়যন্ত্র হয়েছে, যা পূর্ব থেকেই অনেকেই কম বেশি অবহিত ছিল। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, একজন সৎ ও দক্ষ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানকে গোপন ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে চট্টগ্রামে নির্মমভাবে হত্যা করা, যা কেউ এতটুকু বিশ্বাস করতে পারেনি। সত্যি কথা বলতে কি, প্রেসিডেন্ট জিয়া নিষ্ঠাবান ও সৎ ছিলেন। তিনি দেশের জন্য কাজের মাধ্যমে এমনভাবে বাংলাদেশীদের মনে স্থান করে নিয়েছিলেন যে তার জানাজায় লাখ লাখ লোক শরিক হয়েছিল, স্মরণকালে এমন নাকি হয়নি। যাহোক, এই রকম অনেক ষড়যন্ত্র পৃথিবী ব্যাপী সংঘটিত হয়েছে, যা প্রবন্ধের কলেবরের স্বার্থে সন্নিবেশন করা সম্ভব হলো না। এদিকে বর্তমান বাধা বিঘ্নের মধ্যে অন্তবর্তীকালীন সরকারের কার্যকাল ইতিমধ্যে এক বছর শেষ হয়ে গেছে। এই সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের শেষ নেই। শুধু দেশে নয়। দেশের বাইরে থেকেও ষড়যন্ত্র চলছে। বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমে এই সরকারের বিরুদ্ধে মিথ্যা, বানোয়াট ও গুজব ছড়ানো হচ্ছে।তাই সবাইকে সজাগ থাকতে হব।
যে কারণে ষড়যন্ত্রের উপর লিখতে হাতে কাগজ কলম তুলে নিয়েছি। তা হলো একটি বয়সি ও অবসরপ্রাপ্ত মানুষের সমবায় সমিতির মধ্যে ষড়যন্ত্র। ওই সমবায় সমিতির সঙ্গে প্রথম থেকেই সংশ্লিষ্ট ছিলাম। এ প্রেক্ষাপটে উল্লেখ্য যে, ২০১০ সাল থেকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে উদ্যোগী কার্যক্রমের সুবাদে ২০১৫ সালে এটি সমবায় অধিদপ্তরে নিবন্ধিত হয়। আর এর ৪ বছরের মাথার অর্থাৎ ২০১৯ সালে সফলতার মুখ দেখে এবং ৫ বছর ধরে সফলতার সঙ্গে চলে ২০২৫ সালে সমিতির মধ্যে কিছু নেতিবাচক সদস্য মাথা চারা দিয়ে উঠে। তৎপর থেকে বলতে গেলে, সমিতির মধ্যে অসন্তোষ ও বিশৃঙ্খলা চলছে। শুধু তাই নয়, তারা নানা বাহানার মাধ্যমে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে। আর সমিতিকে ধ্বংস করার জন্যে ভেতর বাইরে গুজব ছড়াচ্ছে। শুধু তাই নয়, ব্যক্তিগত আক্রমন করে কথা বলছে। এ প্রেক্ষাপটে উল্লেখ্য যে, ইতিমধ্যে সমবায় অধিদপ্তরসহ সাধারণ সদস্যগণের মধ্যে অনেকেই আশংকাগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন। শেয়ার মূলধন হিসেবে এককালীন টাকা উঠিয়ে নেয়ার জন্য অনেকেই প্রায়ই সমিতির অফিসে ধর্ণা দিচ্ছেন। আর এটি সমিতির জন্য মোটেই ভাল লক্ষন নয়। এদিকে আশ্চর্যের বিষয় হলো যে, মূল ষড়যন্ত্রকারীরা সংখায় খুব একটা বেশি নয়। বড় জোর ৩/৪ জন হবে। এরাই রাত দিন ষড়যন্ত্র করে চলছে। আমার এই মর্মে বাস্তবভিত্তিক ধারণা যে, এইভাবে ষড়যন্ত্র চললে, হয়তো এই সমিতি বেশি দিন টিকবে না।
পরিশেষে এই বলে ইতি টানছি যে ষড়যন্ত্র আছে, ছিল এবং আগামীতে বিভিন্ন আঙ্গিকে আসবে। তাই জীবন চলার পথে ষড়যন্ত্রকারী থেকে সাবধান থাকতে হবে এবং সদা চোখ-কান খোলা রাখতে হবে। কেননা অনেক ক্ষেত্রে ইবলিসও এদের কাছে হার মানে। এটি চিরন্তন সত্য যে ষড়যন্ত্রকারী বা আপাতত ভাল অবস্থানে থাকলেও, শেষ পর্যন্ত টিকে না এবং জনরোষে আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হয়। হয়তো আপনারা লক্ষ্য করেছেন যে, বাস্তব জীবন থেকে নিংড়ানো তিন ঘন্টার সব সিনেমায় ভিলেন দোর্দন্ড প্রতাপে প্রথম দিকে ভাল অবস্থান থাকলেও শেষ পর্যন্ত হয় করুণ পরিনতি। এক্ষেত্রে ‘যার শেষ ভালো তার সব ভালো’ দর্শনের আওতায় নায়ক মাথা উঁচু করে থাকে। আর এই ভিলেন তথা ষড়যন্ত্রকারীদের কি অবস্থা হয়, তা কম বেশি সবারই জানা। এদিকে সুক্ষ্ম দৃষ্টিতে চিন্তা করলে দেখা যায় যে, এই ষড়যন্ত্রকারীরা নায়কের বিরুদ্ধে নেতিবাচক কথা বলে তাকে যেমন প্রকারান্তরে উপরে উঠায়। তেমন ষড়যন্ত্রকারীরা নিচের দিকে যেয়ে নিজেরাই নিজেদের কবর রচনা করে থাকে।
বিশিষ্ট গবেষক, অর্থনীতিবিদ এবং লেখক হিসেবে মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সম্মাননা ও পদকপ্রাপ্ত।

আল্লাহপাক মানুষকে কোরআন শিক্ষা দিয়েছেন (সুরা আর রাহমান, আয়াত-২)। কোরআন গবেষণার জন্য আমাদের তাগিদ দিয়েছেন । সৃষ্টি রহস্য সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করত: আল্লাহ্ প্রদত্ত বিধান অনুযায়ী সঠিকভাবে জীবন যাপন করতে মানবসমাজকে নির্দেশনা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন-…‘পৃথিবীতে পরিভ্রমণ কর এবং অনুধাবন কর কিভাবে তিনি সৃষ্টি শুরু করেছেন? অতঃপর আল্লাহ পুনর্বার সৃষ্টি করবেন পরবর্তী সৃষ্টি। আল্লাহতো সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান’। (আন কাবুত, আয়াত ২০)। ‘এতে আমি জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য এক সুস্পষ্ট নিদর্শন রেখে দিয়েছি’ (আন কাবুত, আয়াত-৩৫)। ‘আর এটাই আপনার রব নির্দেশিত সরল পথ। যারা উপদেশ গ্রহণ করে আমরা তাদের জন্য নিদর্শনসমূহ বিশদভাবে বিবৃত করেছি’ (সুরা আনআম, আয়াত-১২৬)। ‘তিনি তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সব কিছু নিজ অনুগ্রহে। চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য এতে রয়েছে নিদর্শন’ (সুরা যাসিয়া আয়াত-১৩)’। গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যায় সম্পূর্ণ কোরআনের বিভিন্ন অংশে অসংখ্যার উল্লেখ করা হয়েছে যে, এতে জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য সুস্পষ্ট নিদর্শন আছে। অর্থাৎ কোরআন নিয়ে গবেষণার উপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। বিজ্ঞানের গবেষণায় এমন কিছু অজানা তথ্য আমরা জানতে পেরেছি যা প্রায় পনরশত বছর আগে পবিত্র কোরআনে উল্লেখ করা হয়েছিল। তবে, আমাদের মুসলিম চিন্তাবিদ কতটুকু গবেষণা করেছেন সে বিষয় নিয়ে উদাহরণসহ কয়েকটা আলোচনা করতে চাই :
১) বিগব্যাং থিওরি: ১৯২৭ সালে প্রথম বিগব্যাং থিওরি ধারণা দেয়া হয় যা ১৯৬৫ সালে বিজ্ঞান গবেষণা করে প্রমাণ পায় যে প্রথমে আকাশ ও পৃথিবী একত্রে ছিল, পরে একটা বিস্ফোরণ এর ফলে তারা পৃথক হয়ে গেছে। এই বক্তব্য পবিত্র কোরআনে বর্ণিত আছে-‘যারা কুফরী করে তারা কি ভেবে দেখেনা যে, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী মিশে ছিল ওতপ্রোতভাবে; অতঃপর আমি উভয়কে পৃথক করে দিলাম এবং প্রাণবান সমস্ত কিছু সৃষ্টি করলাম পানি হতে; তবুও কি তারা বিশ্বাস করবেনা?’ (সুরা আম্বিয়া, আয়াত ৩০।
২) পানি চক্র: ১৮৬১ সালে বিজ্ঞান আবিষ্কার করে পানি চক্র। কোরআনে বর্নিত আছে- ‘তুমি কি দেখনা যে, আল্লাহ আকাশ হতে বারি বর্ষণ করেন; অতঃপর ভূমিতে নির্ঝররূপে প্রবাহিত করেন এবং তদ্বারা বিবিধ বর্ণের ফসল উৎপন্ন করেন, অতঃপর ওটা শুকিয়ে যায় এবং তোমরা ওটা পীত বর্ণ দেখতে পাও, অবশেষে তিনি ওটা খড়কুটায় পরিণত করেন? এতে অবশ্যই উপদেশ রয়েছে বোধশক্তি সম্পন্নদের জন্য’। (যুমার, আয়াত-২১।
৩) ভ্রুণতত্ব: ১৯৫০ সালে আল্ট্রাসাউন্ড আবিষ্কার এর পর বিজ্ঞান জানতে পারে। অথচ কোরআন পনরশত বছর আগেই উল্লেখ করেছে যে, ‘সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট-বাঁধা রক্তপিণ্ড হতে’। (সুরা আলাক, আয়াত-২)।’ পরে আমি শুক্রবিন্দুকে পরিণত করি রক্তপিণ্ডে, অতঃপর রক্তপিণ্ডকে পরিণত করি মাংসপিণ্ডে এবং মাংসপিণ্ডকে পরিণত করি অস্থিপিঞ্জিরে; অতঃপর অস্থিপিঞ্জিরকে ঢেকে দিই মাংস দ্বারা; অবশেষে ওকে গড়ে তুলি অন্য এক সৃষ্টি রূপে; অতএব নিপুণতম স্রষ্টা আল্লাহ কত কল্যাণময়’। (সুরা মুমিনুন, আয়াত-১৪।
৪) সম্প্রসারণবাদ: এডউইন হাবল ১৯২৪ সালে প্রমাণ করেন বিশ্বজগৎ ক্রমান্বয়ে সম্প্রসারিত হচ্ছে। এই তথ্য পবিত্র কোরআনে বর্ণিত আছে- ‘আমি আকাশ নির্মাণ করেছি আমার ক্ষমতা বলে এবং আমি অবশ্যই মহাসম্প্রসারণকারী’ (সুরা যারিয়াত, আয়াত-৪৭)।
৫) রোজার বাধ্যবাধকতা : প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর জন্য রোজাকে ফরজ করা হয়েছে। পবিত্র কোরআন এর সুরা বাকারা ১৮৩ নম্বর আয়াত-’ হে মুমিনরা, তোমাদের উপর রোজা ফরজ করা হলো যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর ফরজ করা হয়েছিল যেন তোমরা মুত্তাকী হতে পারো।’ এই আয়াতে প্রধান দুটি বিষয় আছে, রোজা মুসলিমদের উপর ফরজ, এবং রোজার পালনের মাধ্যমে মুত্তাকি হতে পারি। এর মধ্যে স্বাস্থ্যের উপকারিতার কথা সরাসরি না থাক্লেও আমরা সবাই জানি রোজা পালন শরীর ও স্বাস্থ্যের জন্য ভালো। কিন্তু কোন মুসলিম কি কোন বৈজ্ঞানিক গবেষণা করেছেন কিভাবে শরীরের জন্য উপকারী, বা পবিত্র কোরআনের এই বক্তব্যের বৈজ্ঞানিক প্রমাণের জন্য কোন থিয়োরি প্রদান করেছেন? কেননা বৈজ্ঞানিক ভাবে প্রমাণিত যদি না হয় তো কোন অমুসলিম কেন ওই তথ্যের উপর সরল বিশ্বাস করবে?
৬) একটি নোবেল প্রাইজ : ২০১৬ সালে YOSHINORI OHSUMI, একজন জাপানি বিজ্ঞানীকে নোবেল প্রাইজ দেওয়া হয় ফিজিওলজি ও মেডিসিন ক্যাটেগরিতে। তিনি আবিষ্কার করেন ‘AUTOPHAGY’ নামের ফর্মুলা। অর্থ্যাৎ তিনি দেখতে পান মানব দেহে যদি ১২ ঘণ্টার অধিক কোন খাদ্য বা পানীয় পাকস্থলীতে না যায় তবে দেহের সুস্থ ও কার্যকরী কোষগুলো অসুস্থ মরা কোষগুলোকে খেয়ে ফেলে। এভাবে শরীর দূষণমুক্ত হয়। এই পদ্ধতির নাম অটোফেজি। ওই ঘটনার পর আমাদের দেশের মানুষের মধ্যে বিশেষ করে যে সব মৌলভি ওয়াজ করেন, তারা জোরে সোরে বলতে শুরু করেন যে ১৫০০ বছর আগে পবিত্র কোরআনের বাণী বিজ্ঞানের আবিষ্কারে প্রমাণিত। আমার কাছে তাদের আত্মতৃপ্তিটা হাস্যকর মনে হয়েছে। আমি প্রশ্ন করেছিলাম কুরআনের বাণী সত্য। কিন্তু কোনো মুসলিম কেন আবিষ্কার করে নোবেল প্রাইজ নিতে পারলেন না । আর যে বিজ্ঞানী আবিষ্কার করে নোবেল প্রাইজ পেলেন তিনি তো পরীক্ষা করার জন্য গবেষণা করে চলেছেন। তিনি কোরআনের বাণী সত্য প্রমাণ করেছেন। তার মনে নিশ্চয়ই প্রশ্ন ছিল মানব দেহের কোষগুলো কিভাবে কাজ করে সেটা জানতে চেষ্টা করেছেন। আমরা মুসলিম হিসেবে নন মুসলিমের সার্টিফিকেটের উপরে কেন নির্ভর করব কোরআনের নির্দেশনা প্রমাণ করতে? আমরা কেন ওই তথ্য আবিষ্কার করতে পারি না?
৭) সত্যমিথ্যা : আজকাল ন্যায় বিচার কায়েম করার জন্য কতই না প্রচেষ্টা করতে হয়। গত ৫৪ বছরে দেখলাম শুধুই আন্দোলন, সরকারের বিরুদ্ধে দাবী আদায়ের আন্দোলন। ৯৫% মুসলিমের দেশ, চিন্তা করতেই অবাক হই যে, ইমানদার অথচ অন্যায়ের বিপক্ষে বেশিরভাগই নেই। অথচ পবিত্র কোরআনে নির্দেশ করেছেন- ‘তিনি আকাশকে করেছেন সমুন্নত এবং স্থাপন করেছেন তুলাদণ্ড। যাতে তোমরা সিমালংঘন না কর তুলাদণ্ডে। তোমরা ন্যায্য ওজন কায়েম কর এবং ওজনে কম দিয়ো না’। (সুরা রহমান, আয়াত : ৭-৯)। অন্যত্র বলা হয়েছে, ‘তোমরা মাপ ও ওজন পূর্ণ করে দাও ন্যায়নিষ্ঠার সঙ্গে। আমরা কাউকে তার সাধ্যের অতিরিক্ত কষ্ট দিই না’। (সুরা আনআম, আয়াত : ১৫২)। পরিমাপে ও ওজনে কম দেওয়ার ফলে আল্লাহ তাআলা ফসলের উৎপাদন কমিয়ে দেন ও দুর্ভিক্ষ দেন। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, ‘দুর্ভোগ তাদের জন্য, যারা মাপে কম দেয়, যারা মানুষের কাছ থেকে ওজন করে নেওয়ার সময় পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করে, আর যখন মানুষকে মেপে কিংবা ওজন করে দেয়, তখন কম দেয়’। (সুরা মুতাফফিফিন, আয়াত : ১-৩)। অন্য আয়াতে বলা হয়েছে-‘তোমরা সত্যকে মিথ্যার সঙ্গে মিশ্রিত করো না এবং জেনেশুনে সত্য গোপন কর না’। (সুরা বাকারা, আয়াত-৪২)।
৮) সর্বশেষ: আমার মূল বক্তব্য কোরআনে বর্ণিত জ্ঞান বিজ্ঞানের কথা, অর্থাৎ চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য প্রদত্ত পরামর্শ আমরা যারা সিভিল সার্ভিসে কর্মরত বিশেষ করে মুসলিম অফিসার, তাদের জন্যই প্রযোজ্য। তাদের কাছেই প্রশ্ন, আমরা সবকিছু জেনেশুনে কিভাবে অন্যায়কে প্রশ্রয় দিতে পারি। আমাদের মধ্যে যেমন রাজনৈতিক বিশ্বাস ও বিভক্তি আছে, তেমনি আছে ধর্মীয় বিশ্বাস ও বিভক্তি। সাধারণ মানুষ সহজেই একটা দলভুক্ত হতে পারে। তাদের মধ্যে গোঁড়ামি অত্যন্ত কাজ করে। কিন্তু সিভিল সার্ভেন্ট অত্যন্ত শৃঙ্খলাবদ্ধ, দক্ষ, অভিজ্ঞ, শিক্ষিত ও বিবেকবান কর্মকর্তা, কোরআনের বর্ননা মতে চিন্তাশীল সম্প্রদায়। তাদের মধ্যে যেমন প্রফেশনালিজম থাকবে, তেমনি থাকবে ন্যায় পরায়নতা। তাতে থাকবে যুক্তি, এবং অপরের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধা ও সহনশীলতা। ওজনে কম দিয়ো না অর্থ ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা কর, বিচারে পক্ষপাতিত্ব কর না। অন্য আয়াতে আছে-‘তোমরা অন্যায়ভাবে একে অপরের সম্পদ ভোগ কর না। এবং জনগণের সম্পদের কিয়দংশ জেনেশুনে পাপ পন্থায় আত্মসাৎ করার উদ্দেশে শাসন কতৃপক্ষের হাতেও তুলে দিও না’। (সুরা বাকারা:১৮৮)। অন্য আয়াতে বলা হয়েছে-‘যে দানের পর কষ্ট দেয়া হয় তার চেয়ে ভালো কথা ও ক্ষমা উত্তম। আর আল্লাহ অভাবমুক্ত, পরম সহনশীল’। (সুরা বাকারা ২:২৬৩)। ‘যখন তোমরা মানুষের কোন বিচার মীমাংসা করতে আরম্ভ কর, তখন মীমাংসা কর ন্যায়ভিত্তিক। আল্লাহ তোমাদিগকে সদুপদেশ দান করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ শ্রবণকারী, দর্শনকারী’। (সুরা নিসা ৪:৫৮)। ‘বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা হত্যার চেয়েও ভয়ানক’। (সুরা বাকারা-১৯১)। ‘তোমরা আল্লার রুজ্জুকে শক্তভাবে সবাই আঁকড়ে ধর দলাদলি করো না’। (সুরা ইমরান -১০৩)। ‘নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের আদেশ দিচ্ছেন আমানতসমূহ তার হকদারদের কাছে পৌঁছে দিতে। আর যখন মানুষের মধ্যে ফয়সালা করবে তখন ন্যায়ভিত্তিক ফয়সালা করবে’। (সুরা নিসা-৫৮)। আমরা যারা মুসলিম, আমাদের সাধারণ জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা আছে স্বীকার করতেই হবে। আর কোরআনের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা তো আছেই। কিন্তু একজন মুসলিম, বিশেষ করে আলেমদের মধ্যে এই সীমাবদ্ধতা কতটুকু রয়েছে সে প্রশ্ন করাই যায়। প্রায় পনরশত বছর আগে পবিত্র কোরআনে অনুরূপ অনেক জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথা এসেছে যা এখন বিজ্ঞানের বিভিন্ন গবেষণায় প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে, কোরআন একদিকে আধ্যাত্মিক ও নৈতিক নির্দেশনা প্রদান করে অন্যদিকে আধুনিক বিজ্ঞানের আলোর প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করত: যুক্তি ও ধর্মীয় বিশ্বাসের সাথে একটা সেতুবন্ধন তৈরি করেছে। জ্ঞান অন্বেষণের তাগিদ প্রদান করেছে যা মহান সৃস্টিকর্তার প্রকৃতিতে বিরাজমান বিভিন্ন নমুনা ও তার অস্তিত্ব খুঁজে বের করতে উৎসাহ যোগায়। সুতরাং কোরআনের সব অজানা তথ্য যে সঠিক তা মহান আল্লাহ পাকের কৃপায় আমরা সময়মতো আবিষ্কার করতে পারবো ইনশাআল্লাহ্। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, কোরআনের কথা বিজ্ঞানের প্রমাণের উপর নির্ভরশীল। সিভিল সার্ভিসের একটা অন্যতম কাজ জনসেবা নিশ্চিত করা। জনগণের কাজকে সহজ করে তোলা। পার্লামেন্টে আইন পাস হয় কিন্তু তারপর প্রয়োগ হয় সিভিল সার্ভেন্টের মাধ্যমে। সেজন্য একজন সিভিল সার্ভেন্টের মনোভাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমরা সবাই জানি আইনের ভাষা, শর্ত, শাস্তি বা পুরস্কার, আইন অমান্যের কারণ, অপরাধী সনাক্তকরণ এইসব যাবতীয় বিষয় একই আইনের বইয়ে লেখা থাকে। কিন্তু নির্ম আদালত যে রায় দেয় উচ্চ আদালতে যেয়ে দেখা যায় আদেশ পরিবর্তন হয়ে গেছে। এখানে যুক্ত হিসেবে দেখা যায় উচ্চ আদালতের বিচারকের মনোভাব। তিনি কোন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করছেন তার উপর নির্ভর করে একজন অপরাধী অপরাধের মাত্রা, অথবা তার নিরপরাধের যৌক্তিকতা, ইত্যাদি নির্ণয় করা।
মো. জহিরুল হক, সরকারি কর্মকর্তা

চব্বিশের জুলাই থেকে পঁচিশের জুলাই-আগস্ট। ঐতিহাসিক গত অভ্যুত্থানের একটি বছর পূর্ণ না হতেই দেশের রাজনৈতিক অঙ্গনের ঘটনাপ্রবাহ দেখে ব্যথিত ও হতাশ হতে হচ্ছে। জুলাই অভ্যুত্থানে একসঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে জীবন বাজি রেখে লড়াই করা সৈনিকদের মধ্যে এখন নানা মতবিরোধ, সন্দেহ , অবিশ্বাস, মতানৈক্য, পরস্পরের প্রতি বিষেদগার করা, অপরের চরিত্র হননের হীন চেষ্টা এমনকি এক পক্ষের ওপর আরেক পক্ষের সরাসরি আক্রমণের ঘটনা প্রত্যক্ষ করছি গত কিছুদিন ধরে। একসঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়ে স্বৈরাচারী স্বেচ্ছাচারী দুঃশাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন করা রাজনৈতিক শক্তিগুলোর বিভেদ প্রকারন্তরে পতিত স্বৈরাচারের দোসরদের জুলাই অভ্যুত্থানের বিজয় নস্যাৎয়ের ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে দুঃসাহসী করে তুলেছে। বৈষম্যহীন, শোষণমুক্ত ন্যায়বিচারভিত্তিক নতুন বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন নিয়ে যাত্রা শুরু করে এখন শিক্ষার্থী নেতাদের কেউ কেউ নিজেরাই চাঁদাবাজিতে লিপ্ত হয়েছে। অথচ তারাই সেদিন দেশকে চাঁদাবাজ মুক্ত, দখলদার মুক্ত, দুর্নীতি মুক্ত করার দীপ্ত শপথ নিয়েছিল। তাদের ওপর ভরসা করতে শুরু করেছিলাম আমরা। ভেবেছিলাম তাদের মাধ্যমে দেশে রাজনীতিতে পচা-গলা নষ্ট সংস্কৃতির অবসান ঘটিয়ে সম্পূর্ণ নতুন বন্দোবস্ত প্রতিষ্ঠিত হবে। নতুন সুস্থ সুন্দর রাজনৈতিক সংস্কৃতি চর্চা শুরু হবে। কিন্তু ১ বছর না যেতেই তাদের চরিত্র এমনভাবে কলঙ্কিত হয়েছে, যা আমাদের হতাশ, ব্যথিত এবং লজ্জিত করেছে।
পতিত স্বৈরাচার আওয়ামী লীগের দোসররা এখন অনায়াসেই চব্বিশের গণঅভ্যুত্থানকে কটাক্ষ করে কথা বলার সাহস পেয়ে যাচ্ছে। এটা আমাদের মতো সাধারণ মানুষের কারও কাছে কাম্য নয়। জুলাই গণঅভ্যুত্থানের বর্ষপূর্তিতে আমাদের আকুল আবেদন, আমরা যেন কোনোভাবেই দিকভ্রান্ত পথিক না হই। স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে আগে যেভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়ে লড়াই করেছি, এখনো তেমন ঐক্যবদ্ধ থেকে অর্জিত বিজয়কে সুসংহত করতে হবে। অনৈতিক আচরণ, বিশৃঙ্খলা, পারস্পরিক বিভেদ, অবিশ্বাস, ঈর্ষাকাতরতা, লোভ-লালসা ত্যাগ করে সবাই ঐক্যবদ্ধ থেকে পরাজিত শত্রুর নানা ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্ন করে গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে আরও সতর্ক ও সক্রিয় হতে হবে দেশের সকল গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক শক্তিকে। বিভেদ, সংঘাত, পারস্পরিক অশ্রদ্ধার প্রকাশ ঘটিয়ে নতুন চেতনার উন্মেষ ঘটাতে হবে। সব রাজনৈতিক দলেরই অধিকার রয়েছে সারাদেশে সর্বত্র সভা সমাবেশ অনুষ্ঠানের। কাউকে বাধা দেওয়া কিংবা ঘোষণা দিয়ে তাদের প্রতিরোধের অধিকারও নেই কারও। অথচ সাম্প্রতিক সময়ে গোপালগঞ্জে যা ঘটেছে তা নিজের চোখে বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে প্রচারিত লাইভ টেলিকাস্টে সরাসরি দেখেছি আমরা। যেখানে এডিট কিংবা বানোয়াট কিছু প্রচারের সুযোগ ছিল না। যেখানে একটি রাজনৈতিক দলের নেতারা সভায় কোনো উসকানিমূলক বক্তব্য দিলেন না, অথচ পূর্ব পরিকল্পিতভাবে তাদের ওপর জঙ্গি হামলা চালাল দুর্বৃত্তের দল। পতিত স্বৈরাচারের দোসর, সমর্থকরা। তাদের ফ্যাসিস্ট স্বভাব রক্তমজ্জায় এমনভাবে মিশে আছে ক্ষমতা হারিয়ে ফেলার পরও তারা সেই আগের মতো আচরণ করছে। বিরোধী দলের উপস্থিতি সহ্য করতে পারছে না। তারা কেন উপলব্ধি করতে পারছে না, গোপালগঞ্জটাই বাংলাদেশ নয়। সারাদেশের মানুষ কী ভাবছেন, কী চাইছেন, তাদের আকাঙ্ক্ষা কী? গোপালগঞ্জ নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রেখে এক ধরনের আত্মতুষ্টিতে ভোগা মানসিক ভারসাম্যহীন মানুষ মনে হয় ওদের। আওয়ামী লীগের দুঃশাসনের স্মৃতি আমরা ভুলে যাইনি। শহীদ আবু সাঈদ, মুগ্ধ, ওয়াসিম, নাফিসারা আমাদের স্মৃতিতে হানা দেয় বারবার।
আজকাল একশ্রেণির তথাকথিত বুদ্ধিজীবী, লেখক, সাংবাদিক চব্বিশের গণঅভ্যুত্থান এবং পরবর্তীতে দেশ পরিচালনায় নিয়োজিত অন্তর্বর্তীকালীন সরকার প্রধান প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূস এবং তার উপদেষ্টামণ্ডলীর নানা সীমাবদ্ধতা, দুর্বলতা, ব্যর্থতা, অক্ষমতা ইত্যাদি নিয়ে নানা মন্তব্য করছেন, প্রায় সময়ই দেখছি। এটা এক ধরনের অসুস্থ মন মানসিকতার প্রকাশ ছাড়া আর কিছুই নয়। এক ধরনের হীনমন্যতাবোধ, পতিত স্বৈরাচারের আমলে অন্যায় সুযোগ-সুবিধা ভোগের স্মৃতি ভুলতে না পারাসহ নিজেদের অনেক সুপ্ত বাসনা কামনা পূরণ না হওয়ার বেদনা থেকে এমন আবলতাবোল বকছেন তারা। অনায়াসেই অন্যের সমালোচনা করা যায়। কিন্তু নিজের ঘাড়ে সেই দায়িত্ব অর্পিত হলে বোঝা যায় ওটা পরিপূর্ণভাবে পরিপালন করা কতটা কঠিন। আমরা দেশের বেশির ভাগ মানুষই তো জুলাই অভ্যুত্থান পরবর্তী অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রতি আস্থা রেখে এসেছি। এখনো তা বিদ্যমান। আমরা তো সুবিধাভোগী কোনো গোষ্ঠী বা পরিবারের লোক নই। পিওর আমজনতা বলতে যা বোঝায়, আমরা তাই। এখন যারা মজা লুটতে পারছে না,প তিত স্বৈরাচার আওয়ামী লীগের সময়ের মতো হালুয়া রুটির ভাগ পাচ্ছে না। কোনো পদ-পদবি পাচ্ছে না, হয়তো মনে বড় আশা ছিল কিছু একটা না একটা পদ বাগিয়ে নেব এই আমলেও। সেই সব লোভী তথাকথিত বিশিষ্টজনদের মনে নানা প্রশ্ন, নানা জ্বালা যন্ত্রণার আগুন দাউদাউ করে জ্বলছে। মোদ্দা কথা, আমরা এখন আওয়ামী লীগের দুঃশাসনের সময় থেকে অনেক অনেক ভালো আছি। হয়তো সব সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি ড. মুহাম্মদ ইউনূস সাহেবের পক্ষে। এটা কারও পক্ষেই সম্ভব নয়। কারও পক্ষে হান্ড্রেট পার্সেন্ট সুখী করা যাবে না, কখনো কোনো মানুষকে। যিনি এইসব লম্বা চওড়া কথা বলেন, তাকে বসিয়ে দেওয়া হোক কোনো চেয়ারে, তখন তিনি বোঝতে- পারবেন কত ধানে কত চাল। আমি নিজে একজন উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তা ছিলাম। চেয়ারে বসে টের পেয়েছি, কী যে মহা ঝামেলা সবকিছু সামাল দেওয়া ও দায়িত্ব পালন করার যন্ত্রণা। কেবলই মনে হতো এই চেয়ার-টেয়ার ফেলে একদিকে ছুটে পালিয়ে যাই। দূরে কোনো পাহাড় কিংবা জঙ্গলে গিয়ে শান্তিতে বসবাস করি। অতএব, কথা বলতে একটু হুঁশ করে বলা উচিত। মুখে বা মনে যা এলো তা বলে ফেলা একটা ছাগলামি ছাড়া আর কিছু নয়।
পতিত স্বৈরাচারের কান্ডারী শেখ হাসিনা নিজেকে গণতন্ত্রের মানসকন্যা বলে জাহির করে পুলকিত হতেন। বিভিন্ন জনসভায় বক্তৃতা দেওয়ার সময় তার নামের আগে ‘গণতন্ত্রের মানসকন্যা’ বলাটা নাকি সব নেতাদের জন্য ছিল বাধ্যতামুলক। এটা তার নির্দেশ। ২০১৪, ২০১৮ আর ২০২৪ এর জালিয়াতির নির্বাচনের মাধ্যমে গায়ের জোরে ক্ষমতা আঁকড়ে থাকা মানুষটাই গণতন্ত্রের মানসকন্যা। এখন সেই গণতন্ত্রের মানসকন্যার স্বরূপ বেরিয়ে আসছে একে একে। এখনতো সব তথ্যই বেরিয়ে আসছে আস্তে আস্তে। সাবেক সিইসি স্বীকার করেছেন, আগের রাতেই ভোটের বাক্স ভরে রাখার নির্দেশ তিনিই দিয়েছিলেন। সাবেক পুলিশ প্রধানও স্বীকার করেছেন, হেলিকপ্টার থেকে আন্দোলনরত ছাত্র-জনতার ওপর গুলি করার নির্দেশ তিনিই দিয়েছিলেন। বালুভর্তি ট্রাক আর গোপালী পুলিশ দিয়ে খালেদা জিয়ার বাড়ি থেকে বের হওয়ার পথ যিনি আটকে রেখেছিলেন তিনিই। তিনি নাকি গণতন্ত্রের মানসকন্যা। স্বৈরাচারী শেখ হাসিনা বিভিন্ন জনসভায় বক্তৃতা দেওয়ার সময় প্রায়শই ২০৪৯ সালের কথা বলতেন। হয়তো তার স্বপ্ন ছিল যে প্রকারেই হোক ২০৪৯ সাল পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী থাকবেন। তখন তার বয়স হতো ১০০ বছর। তিনি হয়তো ধরেই নিয়েছিলেন যে তিনি ওই পর্যন্ত বাঁচবেন এবং সাধারণ ‘পাবলিক’ নয়, প্রধানমন্ত্রী হিসেবেই সর্গে প্রবেশ করবেন। আচ্ছা, তিনি কি আজরাইল (আঃ) কেও ম্যানেজ করার চেষ্টা চালাচ্ছিলেন? প্রশ্ন জাগে। কিন্তু বিধি বাম। পৃথিবীতে অন্যায় অবিচার অনিয়ম বর্বরতা নৃশংসতা চালিয়ে আজীবন টিকে থাকা যায় না। তিনি ভুলেই গিয়েছিলেন, মহান সৃষ্টিকর্তা বলে একজন আছেন সবার ওপরে। তার ইশারায়ই পৃথিবীর সবকিছু পরিচালিত হয়ে আসছে। তিনি মাঝে মধ্যে কাউকে কিছুটা ছাড় দেন হয়তো, কিন্তু একেবারে ছেড়ে দেন না। পতিত স্বৈরাচারের দোসররা এখনো চারদিকে ষড়যন্ত্রের জাল বুনে চলেছে। সুযোগ পেলেই বিষধর সাপের মতো- ছোবল মারতে নানা কলাকৌশল প্রয়োগ করছে। এখন ছাত্র-জনতার দৌড় খেয়ে ভারতে পালিয়ে গিয়ে আবারও এই গণতন্ত্রের মানসকন্যা নানা গণতান্ত্রিক- উপায় খুঁজে বের করছেন ক্ষমতায় ফেরার জন্য। প্রথমে তিনি আশা করেছিলেন, প্রতিবেশী দেশের আশির্বাদপুষ্ট হয়ে আবার যেকোনোভাবেই হোক ক্ষমতা ফিরে পাবেন। ভিন দেশের সরকার তাকে ঘাড়ে করে বাংলাদেশে নিয়ে এসে প্রধানমন্ত্রীর চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে যাবেন। সেটাতে ব্যর্থ হওয়ার পর তিনি ফন্দি করছিলেন, বিশ্বের অন্যতম শক্তিশালী দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প সবাইকে ধমক দিয়ে সরিয়ে দিয়ে আবার তাকেই প্রধানমন্ত্রীর চেয়ারে বসিয়ে দেবেন। সম্প্রতি পতিত স্বৈরাচারের দোসরদের ভয়ংকর ষড়যন্ত্রের চাঞ্চল্যকর তথ্য বেরিয়ে এসেছে। যেখানে নিষিদ্ধ ঘোষিত গণতন্ত্রের শত্রু আওয়ামী লীগের কিছু নেতা-কর্মীদের সক্রিয় অংশগ্রহণসহ সেনাবাহিনীর কারও সহযোগিতা নিয়ে দেশের অভ্যন্তরে নৈরাজ্য, বিশৃঙ্খলা, আতঙ্ক, ভয়ংকর সব ঘটনা সৃষ্টির মাধ্যমে পরিস্থিতি অশান্ত করে তোলার ষড়যন্ত্রের কথা প্রকাশ পেয়েছে। দেশের আপামর জনসাধারণের বিরুদ্ধে গিয়ে আবার ক্ষমতায় ফেরার স্বপ্নে বিভোর পতিত স্বৈরাচারের নেত্রী শেখ হাসিনার উচ্চাভিলাসী ভাবনা দেখে অবাক হয়ে গেছি আমরা। তার স্মরণ রাখা উচিত, যে যায় সে আর ফিরে না এত সহজে। আফগান বাদশাহ ফিরেনি, ইরানের শাহ ফিরেনি, ফিলিপাইনের মার্কোস ফিরেনি, তিনিও ফিরবেন না। তার প্রতি অনুরোধ, অনুসারীদের সুপরামর্শ দিন, বলুন পজিটিভ হতে, দেশ-সেবা করতে চাইলে ভালো বিকল্প বেছে নিতে।
এই সময়ে চারদিকে নানা ষড়যন্ত্রের জাল বুনছে গণতন্ত্রের শত্রুরা। তারা একেরপর এক ঘটনার জন্ম দিয়ে নৈরাজ্য বিশৃঙ্খলা অরাজকতা সৃষ্টির পাঁয়তারা করছে। এ ব্যাপারে সরকারকে যেমন সতর্ক ও সচেতন থাকতে হবে। তেমনিভাবে সকল ফ্যাসিস্টবিরোধী গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। সাধারণ জনগণের ভবিষ্যৎ নিয়ে ছিনিমিনি খেলার অধিকার নেই কারও। আমরা সবাই একটি সুষ্ঠু অবাধ নিরপেক্ষ সুন্দর নির্বাচনের জন্য অধীরভাবে অপেক্ষা করছি। অতীতে পতিত স্বৈরাচার পরপর তিনটি কলঙ্কজনক নির্বাচন করে দেশে-বিদেশে নিন্দিত হয়েছেন। আমরা সেই নষ্ট , কলঙ্কিত নির্বাচনের পুনরাবৃত্তি দেখতে চাই না। সে জন্য দেশের সামগ্রিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি সুন্দর ও নিরাপদ রাখতে হবে। অতএব, কান্ডারী হুঁশিয়ার। কোনোভাবেই ফ্যাসিস্ট, স্বৈরাচারী স্বেচ্ছাচারী দুঃশাসন আর ফিরে আসতে না পারে সে দিকে সতর্ক দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখতে হবে।
লেখক : অবসরপ্রাপ্ত ব্যাংকার , কলাম লেখক।

২০০৮ এর ২৯ ডিসেম্বর থেকে ৫ আগস্ট ২০২৪। সুদীর্ঘ এই সময়ে বাংলাদেশের রাজনীতিতে দুর্বৃত্তায়ন, দুর্নীতি, অপশাসনের নতুন রাজত্ব সৃষ্টি করা আওয়ামী লীগ বাংলাদেশের সমাজ বাস্তবতায় এখন কার্যত অবাঞ্ছিত, নিষিদ্ধ। বিশেষ করে ৫ আগস্ট বাংলাদেশের মাটিতে হাজারও ছাত্র জনতার বুকের রক্ত ঝরানো আওয়ামী লীগকে দেশের সাধারণ মানুষ সম্মিলিত গণঅভ্যুত্থানে ছুড়ে ফেলেছে ঘৃণার সাগরে। ছুড়ে ফেলেছে শেখ হাসিনা ও তার মন্ত্রিপরিষদে থাকা অপরাজনীতির দোসরদের। দেশের মাটিতে তাই আওয়ামী লীগের রাজনীতি এখন অপ্রাসঙ্গিকই নয় বরং জনধিকৃতও বটে। তবে বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ দীর্ঘদিনের এই ফ্যাসিস্ট দলটিকে সমর্থন না জানালেও শেখ হাসিনা ও তার প্রভাবশালী নেতাদের আশ্রয় দেওয়া ভারত নিজেদের রক্ষায় সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে আওয়ামী লীগকে। বাংলাদেশে বসে ভারতের ছত্রছায়ায়, ভারতীয় নীতি করা আওয়ামী লীগ এখনো রাজনীতি করছে ভারতেরই প্রত্যক্ষ সহায়তা এবং মদদে।
দেশের মাটিতে ঘৃণার প্রতীক হয়ে উঠলেও, শেখ হাসিনা এবং তার ঘনিষ্ঠ নেতৃত্ব ভারতীয় আশ্রয়ে রাজনৈতিক কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। এই রাজনৈতিক আশ্রয়গ্রহণ একদিকে যেমন প্রশ্ন তোলে ভারতের নৈতিক অবস্থান নিয়ে, অন্যদিকে তা বাংলাদেশের জাতীয় সার্বভৌমত্বকেও করে প্রশ্নবিদ্ধ। কারণ শেখ হাসিনা এবং তার দল যে কৌশলে ভারতের ছায়াতলে থেকে বাংলাদেশে প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা চালাচ্ছে, সেটি কেবল আশ্রয়ের গল্প নয়, বরং একটি পরিপূর্ণ ভূরাজনৈতিক প্রকল্পের অংশ।
সম্প্রতি প্রকাশিত সংবাদে জানা গেছে, কলকাতার উপনগরীর এক বাণিজ্যিক কমপ্লেক্সে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ একটি ‘পার্টি অফিস’ খুলে রাজনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। অফিসটির আকার ছোট মাত্র ৫০০-৬০০ স্কয়ার ফুট। কোনো সাইনবোর্ড নেই, বঙ্গবন্ধু বা শেখ হাসিনার কোনো ছবি নেই, এমনকি দলীয় দপ্তরের ফাইলপত্রও নেই। সবকিছুই অত্যন্ত গোপনীয়ভাবে পরিচালিত হচ্ছে, যেন দলটির অস্তিত্ব সেখানে দৃশ্যমান না হয়। এ যেন এক ধরনের ‘আন্ডারগ্রাউন্ড অপারেশন’, যার মাধ্যমে ভারতে অবস্থানরত আওয়ামী নেতারা দলকে সংগঠিত করার কাজ করছেন।
ভারতে আওয়ামী লীগের এই ‘পার্টি অফিস’ শুধু ভবিষ্যতের প্রত্যাবর্তনের পরিকল্পনা নয়, বরং এটি ভারতের একটি কৌশলগত দাবার চাল, যার মাধ্যমে তারা বাংলাদেশে নিজেদের প্রভাব পুনঃপ্রতিষ্ঠার পথ খুঁজছে। স্বাধীন দেশের একটি রাজনৈতিক দল যদি অন্য দেশের মাটিতে গিয়ে কর্মকাণ্ড চালায়, তবে সেটি কি কেবল আত্মরক্ষার কৌশল, নাকি একটি বৃহৎ আগ্রাসী রাজনীতির অংশ? এই প্রশ্ন এখন বাংলাদেশি জনগণের মনে গভীরভাবে দাগ কাটছে। যারা ১৯৭১ সালে ভারতের সহযোগিতাকে কৃতজ্ঞচিত্তে স্বীকার করেছিলেন, তারাই আজ প্রশ্ন তুলছেন, ভারত কি সত্যিই বাংলাদেশের বন্ধু, না কি এক বিকাশমান শাসক?
আওয়ামী লীগের কলকাতা অফিস কার্যত একটি ‘পলিটিক্যাল এক্সাইলের দৃষ্টান্ত। এটি ইঙ্গিত দেয়, বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে ভারত একটি সরাসরি পক্ষ হয়ে উঠেছে।
ভারতীয় সংবাদমাধ্যমের কিছু অংশ এ ঘটনাকে স্বাভাবিক বলে প্রচার করছে। তাদের যুক্তি, ‘আওয়ামী লীগ হচ্ছে ভারত-বান্ধব দল, আর কলকাতা হচ্ছে বাঙালির রাজধানী। তাই এখানে তাদের পার্টি অফিস থাকাটা অস্বাভাবিক কিছু নয়।’ কিন্তু এই ব্যাখ্যা রাজনৈতিক বাস্তবতা থেকে অনেক দূরে। এটি কূটনৈতিক শিষ্টাচার লঙ্ঘনের নামান্তর। কোনো স্বাধীন দেশের রাজনৈতিক দল অন্য দেশের ভেতরে সংগঠিতভাবে কার্যক্রম চালাতে পারে না। এটি আন্তর্জাতিক রাজনীতির মৌলিক নীতি। ভারত যদি সত্যিই গণতান্ত্রিক মূল্যবোধে বিশ্বাসী হয়, তবে তাদের উচিত ছিল এই ধরনের অফিস চালানোর অনুমতি না দেওয়া।
২০২৪ সালের ৫ আগস্টের পর ভারতে আশ্রয় নেওয়া আওয়ামী লীগের নেতারা মূলত কলকাতা ও তার আশপাশের এলাকায় অবস্থান করছেন। এদের মধ্যে রয়েছেন সাবেক সংসদ সদস্য, মন্ত্রী, মেয়র, জেলা পর্যায়ের নেতা, এমনকি অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ ও সামরিক কর্মকর্তারাও। কেউ কেউ সপরিবারে, কেউ বা কয়েকজন মিলে একটি ফ্ল্যাটে বাস করছেন। আনুমানিক ৮০ জন সাবেক সংসদ সদস্যসহ প্রায় ২০০ জন আওয়ামী ঘরানার ব্যক্তি এখন কলকাতায় রয়েছেন। এই সংখ্যা সময়ের সঙ্গে হয়তো আরও বাড়বে।
বাংলাদেশে ২০২৪ সালের গণঅভ্যুত্থান কোনো আকস্মিক ঘটনা ছিল না। এটি ছিল দীর্ঘদিনের দমন-পীড়ন, দুর্নীতি, দলীয়করণ এবং ভারতনির্ভর পররাষ্ট্রনীতির বিরুদ্ধে জনগণের জাগরণ। এই আন্দোলনের অন্যতম দাবি ছিল ভারতের প্রভাবমুক্ত, স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতি। অথচ সেই প্রেক্ষাপটে দেখা যায়, পরাজিত সরকারদল বিদেশে গিয়ে ‘শরণার্থী রাজনীতি’ করছে, তখন জনগণের আশঙ্কা আরও দৃঢ় হয় এই দলটি শুধু বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিমণ্ডল নয়, সার্বভৌমত্বকেও বিকিয়ে দিতে প্রস্তুত।
ভারতের আগ্রাসনের রাজনীতি নতুন কিছু নয়। দেশের জলসীমায় আগ্রাসন, সীমান্ত হত্যা, অভিন্ন নদীর পানির ন্যায্য হিস্যা না দেওয়া, বাজার দখল, ট্রানজিট, এমনকি বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ এসবই দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে। আওয়ামী লীগের মাধ্যমে ভারত যেন একটি ‘ডিপ্লোম্যাটিক প্রক্সি’ তৈরি করেছিল। তারা জানত, এই দল ক্ষমতায় থাকলে বাংলাদেশের নীতিনির্ধারণ ভারতের পক্ষে থাকবে। তাই আওয়ামী লীগের পতনের পর ভারত সরকার উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়ে। আর সেই উৎকণ্ঠা থেকেই এই ‘কলকাতা অফিস’ যা এক অর্থে ভারতীয় ভূরাজনীতির নিরাপত্তা বলয়ের অংশ।
বাংলাদেশের জনগণ আজ সচেতন। তারা ১৯৭১ সালে ভারতের ভূমিকার মূল্যায়ন করতে জানে, আবার দীর্ঘ ৫০ বছর দেশের অভ্যন্তরে ভারতের হস্তক্ষেপকেও অনুধাবন করতে শিখেছে। আর কলকাতায় আওয়ামী লীগের ‘পার্টি অফিস’ জনগণের কাছে এক ভয়ংকর বার্তা বহন করছে বাংলাদেশের রাজনীতিতে এখনো এক বিদেশি শক্তি সক্রিয় থাকতে চায়, যেটি গণতন্ত্র নয়, বরং তাদের জাতীয় স্বার্থকে প্রাধান্য দেবে।
বছরের পর বছর ধরে ভারত নিজেদের বাংলাদেশের ‘বড় ভাই’ হিসেবে জাহির করে আসছে। অথচ সীমান্তে গুলি করে মানুষ হত্যা, বাংলাদেশের ন্যায্য অধিকার অস্বীকার, এবং রাজনৈতিকভাবে অনুগত সরকার প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা এই ‘বড় ভাই’-এর মুখোশ খুলে দিয়েছে। কলকাতায় ‘পার্টি অফিস’ খোলা এই আগ্রাসনেরই নতুন রূপ একটি সফট কূটনৈতিক অভিযান, যার মূল লক্ষ্য বাংলাদেশের অভ্যন্তরে একটি অনুগত রাজনৈতিক শক্তিকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা।
ভারত সরকারের স্পষ্ট অনুমোদন ছাড়া এই ধরনের রাজনৈতিক দপ্তর পরিচালনা অসম্ভব। অর্থাৎ ভারত সরকারের প্রত্যক্ষ মদদ ও গোয়েন্দা তদারকির মধ্য দিয়েই কলকাতার মাটিতে বাংলাদেশের একটি বিতাড়িত রাজনৈতিক শক্তি টিকে রয়েছে। এটি ভারতের ভূরাজনৈতিক কৌশলেরই অংশ যেখানে বাংলাদেশে তাদের একক অনুগত শক্তি হিসেবে আওয়ামী লীগকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করাই উদ্দেশ্য। ভারত অতীতে সীমান্ত হত্যা, পানিবণ্টনে বৈষম্য, ট্রানজিট ও অর্থনৈতিক নির্ভরতার মাধ্যমে বাংলাদেশের ওপর প্রভাব বিস্তার করেছে। এবার তাদের নতুন কৌশল হচ্ছে সরাসরি রাজনৈতিক আশ্রয় দিয়ে নিজেদের অনুগত শক্তিকে টিকিয়ে রাখা।
আওয়ামী লীগ ভারতে বসে রাজনৈতিক বৈঠক করছে, ভার্চুয়ালি নেতা-কর্মীদের দিকনির্দেশনা দিচ্ছে, হোয়াটসঅ্যাপ ও টেলিগ্রামে দল পরিচালিত হচ্ছে। শেখ হাসিনা দিল্লির উপকণ্ঠে থাকলেও মাঝে মধ্যে দলের শীর্ষ নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করছেন। সর্বশেষ বৈঠকটি হয়েছিল ৩১ জুলাই। এইসব আয়োজন প্রমাণ করে, দলটির মূল নেতৃত্ব এখন দেশের বাইরে, কিন্তু রাজনৈতিক অভিসন্ধি থেকে সরে আসেনি।
আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরেও আওয়ামী লীগের এই অবস্থান অনেক প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে। সাধারণ কর্মীরা দেশে দমন-পীড়নের শিকার হলেও শীর্ষ নেতারা ভারতে নিরাপদে অবস্থান করছেন এটি সাংগঠনিক নৈতিকতার দিক থেকেও প্রশ্নবিদ্ধ। যদিও পঙ্কজ দেবনাথের মতো নেতারা বলছেন, ‘জেলে গেলে বা মারা পড়লে সংগঠন গড়া যেত না।’ এই অবস্থান নিঃসন্দেহে বিতর্কিত। কারণ এটি দেশপ্রেম নয়, বরং ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার এক চাতুর্যপূর্ণ প্রয়াস।
অর্থনৈতিকভাবে এই সংগঠনের ভার বহন করা হচ্ছে তথাকথিত ‘শুভাকাঙ্ক্ষীদের’ সহায়তায়। এই অর্থায়ন কতটা স্বচ্ছ তা নিয়েও যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে।
কলকাতায় আওয়ামী লীগের এই ‘পার্টি অফিস’ শুধু একটি রাজনৈতিক দপ্তর নয়, এটি ভারতের ভূরাজনীতির মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি হুমকির জীবন্ত প্রতীক। ভারতের সরকারি অনুমোদনে এই অফিসের মাধ্যমে রাজনৈতিক কৌশল নির্ধারণ ও পুনর্গঠন চলছে। বিদেশে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা কোনো সার্বভৌম দেশের জন্য গ্রহণযোগ্য নয় এবং এটি দেশের স্বাধিকার ও নিরাপত্তার জন্য বড় হুমকি।
কবি, লেখক মিডিয়া ব্যক্তি

সাদা পাথর এলাকা আজ মরুভূমি। আমরা নতুন প্রজন্ম প্রাকৃতিক এই মহামূল্যবান সম্পদ ধরে রাখতে পারলাম না। কিছু রাজনৈতিক প্রভাবশালী নেতার কারণে সিলেটের ভোলাগঞ্জের সাদা পাথর এলাকা আজ মরুভূমিতে রূপ নিয়েছে। গলা টিপে হত্যা করা হয়েছে এই অপার সৌন্দর্যের প্রাকৃতিক সম্পদকে। তথাকথিত সভ্য সমাজ প্রকৃতির সঙ্গে এমন আচরণ করেছে, যেন প্রকৃতি কেবল ভোগের বস্তু।
নিজ দেশের সৌন্দর্য রক্ষা ও উন্নয়নে নাগরিকদের দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে এগিয়ে আসতে হবে তবেই আমরা আমাদের প্রাকৃতিক ঐশ্বর্যকে আগামীর জন্য বাঁচিয়ে রাখতে পারব।
বাংলাদেশের উত্তর-পূর্ব প্রান্ত সিলেট একটি ভূখণ্ড, যা প্রকৃতির উদার দান, পাহাড়-নদী-ঝর্ণার অপার মেলবন্ধন, চা-বাগানের সবুজ সমারোহ, সীমান্তের পাহাড়ি বাতাস আর মানুষের আন্তরিক আতিথেয়তা মিলিয়ে একটি অনন্য সৌন্দর্যের আঁধার। এই সিলেটের কোম্পানিগঞ্জ উপজেলার ভোলাগঞ্জ ছিল এমনই এক প্রাকৃতিক রত্নভাণ্ডার, যেখানে ধলাই নদীর স্বচ্ছ জল, সাদা পাথরের স্তূপ আর মেঘালয়ের পাহাড় থেকে নেমে আসা ঝর্ণাধারার মিলনে সৃষ্টি হয়েছে অপরূপ দৃশ্যপট। দেশি-বিদেশি পর্যটকদের জন্য এটি ছিল যেন এক ভূ-স্বর্গীয় গন্তব্য।
কিন্তু আজ, সেই ভোলাগঞ্জ সাদা পাথরের চিত্র দেখে শিউরে উঠতে হয়। একসময়ের অপূর্ব প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এখন ধূলিধূসর মরুভূমির মতো। নদীর বুক ফাঁকা, পাথরের স্তূপ নেই, স্বচ্ছ জল ঘোলা, তলদেশে সৃষ্টি হয়েছে গভীর গর্ত। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সম্প্রতি ছড়িয়ে পড়া আগের ও বর্তমান ছবির তুলনা আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে আমরা নিজেরাই প্রকৃতির গলা টিপে হত্যা করছি।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া অসংখ্য ভিডিও যেন প্রমাণ দিচ্ছে সিলেটের ভোলাগঞ্জে সাদা পাথর এখন আর প্রকৃতির অলঙ্কার নয়, লুটেরাদের লোভের শিকার। ভিডিও ফুটেজে দেখা যাচ্ছে, জিরো পয়েন্টে খোঁড়াখুঁড়ি করে পাথর তোলা হচ্ছে নির্বিচারে। ভাগ-বাটোয়ারা নিয়ে লুটেরাদের মধ্যে হাতাহাতি এমনকি মারামারির ঘটনাও ঘটছে প্রকাশ্যে।
ধলাই নদীতে দিনের আলো কিংবা গভীর রাত সময় যেন কোনো বাধা নয়। প্রভাবশালী একটি চক্র শত শত বারকি নৌকা ভরে তুলছে পাথর। এমন প্রভাব যে, স্থানীয় মানুষ মুখ খুলতে ভয় পান; প্রশাসনের নীরবতা ও রাজনৈতিক আশ্রয়-প্রশ্রয় এই বেপরোয়া কর্মকাণ্ডকে আরও বেগবান করে তুলেছে। মাসের পর মাস ধরে চলা এই অবৈধ উত্তোলনে নদীর তলদেশে সৃষ্টি হয়েছে গভীর গর্ত, ব্যাহত হয়েছে নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ, আর পাথরশূন্য তীরে ভোলাগঞ্জ হারাচ্ছে তার প্রাকৃতিক রূপ।
গত বছরের ৫ আগস্ট থেকেই সাদা পাথরে লুটপাটের সূত্রপাত, তবে গত দুই সপ্তাহে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে পড়েছে। স্থানীয়দের অভিযোগ ক্ষমতাশীন রাজনৈতিক নেতাদের নেতৃত্বে চলছে এই লুটপাট; তবে অন্যান্য দলের নেতাকর্মীরাও নেপথ্যে রয়েছে। সরকার পতনের পর চিত্রটি হয়েছে আরও ভয়াবহ। পাহাড়ি ঢলের সঙ্গে ভেসে আসা পাথর লুটে চলছে প্রতিযোগিতা, বাদ যাচ্ছে না ভোলাগঞ্জ রোপওয়ে বাঙ্কার এলাকাও। লুটেরাদের তালিকায় রাজনৈতিক রঙের ভেদাভেদ নেই চাঁদাবাজির ধরন বদলে গিয়ে সব পক্ষ মিলে ভাগ বসাচ্ছে প্রাকৃতিক সম্পদে।
গত দুই-তিন মাসে দিন-রাত মিলিয়ে অন্তত হাজারের বেশি বারকি নৌকা ব্যবহার করে পাথর লুট হয়েছে। পুলিশের ভূমিকাও ছিল প্রায় নিষ্ক্রিয় যেন তারা শুধু দর্শকের আসনে।
শ্রমিকদের কার্যক্রমও ভয়াবহ চিত্র আঁকে। দিনরাত সমানতালে হাজার হাজার শ্রমিক কোদাল, বেলচা, শাবল ও টুকরি নিয়ে কোয়ারি ও আশপাশের এলাকা থেকে মাটি খুঁড়ে পাথর তুলছেন। পরে বারকি নৌকায় করে সেই পাথর মিল মালিকদের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে মেশিনে পাথর ভেঙে ছোট করা হয় এবং ট্রাক-পিকআপে করে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে পাঠানো হয় যেন এই ধ্বংসযজ্ঞের কোনো শেষ নেই।
ভোলাগঞ্জের সাদা পাথর ধ্বংসের এই লুটযজ্ঞ কেবল সৌন্দর্যের ক্ষতি নয়; এটি এক গভীর ও দীর্ঘমেয়াদি পরিবেশগত সংকটের জন্ম দিচ্ছে। নদী, পাহাড়, জলজ প্রাণী এবং মানুষের জীবন সবই এই বিপর্যয়ের শিকার হচ্ছে।
প্রথমত, নদীর তলদেশে গভীর গর্ত তৈরি হওয়ায় ধলাই নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। পানির গতি ও দিক পরিবর্তনের ফলে বন্যা ও ভাঙনের ঝুঁকি আশঙ্কাজনকভাবে বাড়ছে। বর্ষাকালে অতিরিক্ত স্রোতে তীর ভাঙন ও বসতভিটা হারানোর সম্ভাবনা বেড়ে যায়, যা স্থানীয় মানুষের নিরাপত্তা ও বসবাসের স্থায়িত্বকে হুমকির মুখে ফেলে।
দ্বিতীয়ত, জলজ প্রাণীর স্বাভাবিক বাসস্থান ধ্বংস হচ্ছে। নদীর পাথরশয্যা মাছ ও অন্যান্য জলজ জীবের প্রজনন ও আশ্রয়ের জন্য অপরিহার্য। পাথর হারিয়ে যাওয়ায় তাদের প্রাকৃতিক আবাসস্থল বিলীন হচ্ছে, ফলে জীববৈচিত্র্য দ্রুত কমে যাচ্ছে। এর প্রভাব নদীর সম্পূর্ণ খাদ্যচক্রে পড়ছে যা শেষ পর্যন্ত মানুষের খাদ্য ও অর্থনীতিকেও প্রভাবিত করছে।
তৃতীয়ত, ধলাই নদীর স্বচ্ছতা হারিয়ে জলদূষণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। পাথর উত্তোলনের সময় নদীর তলদেশ থেকে মাটি, বালি ও কাদা উঠে এসে পানিকে ঘোলা করে তোলে। এর ফলে পানির মান নষ্ট হয়, নদী ব্যবস্থার প্রাকৃতিক স্বচ্ছতা ও সৌন্দর্য হারিয়ে যায়, আর পানি ব্যবহারের যোগ্যতা কমে যায়।
চতুর্থত, পর্যটনশিল্পের উপর বিরূপ প্রভাব মারাত্মক আকার ধারণ করছে। একসময় যেখানে দেশি-বিদেশি পর্যটকদের ভিড় থাকত, এখন সেখানে হতাশা ও বিমুখতা। পর্যটক না আসায় হোটেল-মোটেল, রেস্তোরাঁ, নৌকা ভাড়া, স্থানীয় গাইড, হস্তশিল্প বিক্রেতা সবাই অর্থনৈতিক সংকটে পড়ছে। শতাধিক পরিবার, যারা পুরোপুরি এই পর্যটন নির্ভর জীবিকার সঙ্গে জড়িত, তারা এখন বেকারত্ব ও দারিদ্র্যের মুখে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে।
সব মিলিয়ে, ভোলাগঞ্জের সাদা পাথরের এই ধ্বংসযজ্ঞ একটি পরিবেশ, অর্থনীতি ও সমাজ সবক্ষেত্রের সমন্বিত বিপর্যয়। প্রকৃতি ও মানুষের সহাবস্থানকে ধ্বংস করে যে উন্নয়ন সম্ভব নয়, তা এই উদাহরণ আমাদের স্পষ্টভাবে দেখিয়ে দিচ্ছে।
বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন, এবং বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের বিধিনিষেধ থাকা সত্ত্বেও এই অবৈধ পাথর উত্তোলন বন্ধ হয়নি। প্রশ্ন ওঠে প্রশাসন কি অসহায়, নাকি প্রভাবশালীদের চাপে নীরব?
ভোলাগঞ্জের সাদা পাথর কেবল একটি পর্যটন স্পট নয়; এটি একটি জাতীয় সম্পদ। এই সম্পদ ধ্বংস করা মানে জাতীয় ঐতিহ্যের অপচয়। টেকসই সমাধানের প্রয়োজন
এই পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য জরুরি কিছু পদক্ষেপ নেওয়া দরকার - ভোলাগঞ্জের সাদা পাথর কেবল প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের প্রতীক নয় এটি সিলেটের জীববৈচিত্র্য, সংস্কৃতি ও অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ। অথচ অবৈধ উত্তোলন ও পরিবেশ ধ্বংসের কারণে এই অনন্য সম্পদ মারাত্মক হুমকির মুখে। এখনই কিছু জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণ না করলে, অদূর ভবিষ্যতে এই অঞ্চল হারিয়ে যাবে আমাদের চোখের সামনে।
ভোলাগঞ্জ ও এর আশপাশের অঞ্চলকে ‘সংরক্ষিত প্রাকৃতিক অঞ্চল’ হিসেবে আইনি স্বীকৃতি দিতে হবে। এতে করে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান অনুমতি ছাড়া পাথর উত্তোলন, ভূমি খনন বা পরিবেশ বিনষ্টমূলক কর্মকাণ্ড চালাতে পারবে না।
প্রভাবশালী চক্রের বিরুদ্ধে আইন প্রয়োগ শুধু অভিযান চালানো নয়, বরং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে, যাতে ভবিষ্যতে আর কেউ একই অপরাধ করার সাহস না পায়।
পাথর উত্তোলনের সঙ্গে জড়িত হাজারো শ্রমজীবী মানুষ হঠাৎ বেকার হয়ে পড়লে সামাজিক সংকট সৃষ্টি হবে। তাই তাদের জন্য বিকল্প আয়ের পথ, যেমন ইকো-ট্যুরিজম, হস্তশিল্প, বা কৃষিভিত্তিক প্রকল্প চালু করতে হবে।
ভোলাগঞ্জকে একটি পরিবেশবান্ধব পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলতে হবে নিয়ন্ত্রিত পর্যটন, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, নিরাপদ অবকাঠামো এবং প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণের মাধ্যমে।
প্রকৃতি রক্ষার ক্ষেত্রে স্থানীয় মানুষকেই অভিভাবক হিসেবে গড়ে তোলা জরুরি। তারা যদি সরাসরি পর্যটন ও সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনায় সম্পৃক্ত হয়, তাহলে নিজেদের স্বার্থেই প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষায় এগিয়ে আসবে।
পর্যটন কেবল বিনোদনের একটি মাধ্যম নয়; এটি একটি শক্তিশালী অর্থনৈতিক ইঞ্জিন। সিলেটের পর্যটন খাত বছরে কোটি কোটি টাকার রাজস্ব আয় করতে সক্ষম, যদি প্রাকৃতিক সম্পদগুলো সঠিকভাবে সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা করা হয়। ভোলাগঞ্জের সাদা পাথর শুধু স্থানীয় নয়, আন্তর্জাতিক পর্যটন মানচিত্রেও একটি গুরুত্বপূর্ণ আকর্ষণ।
বিদেশি পর্যটকরা কেবল প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করতেই আসেন না তারা নিরাপত্তা, অবকাঠামো, পরিবেশের স্থায়িত্ব, এবং স্থানীয় সংস্কৃতির সংরক্ষণকেও মূল্যায়ন করেন। যদি এই অনন্য প্রাকৃতিক দৃশ্য হারিয়ে যায়, তবে সিলেটের পর্যটন আয় ও কর্মসংস্থান উভয় ক্ষেত্রেই বড় ধাক্কা লাগবে। প্রায় হাজার হাজার মানুষ, যারা পর্যটন নির্ভর হোটেল, রেস্টুরেন্ট, নৌকা সেবা, গাইডিং এবং হস্তশিল্পের সঙ্গে যুক্ত, তারা সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত হবেন।
ভোলাগঞ্জ হারিয়ে গেলে শুধু সিলেট নয়, সমগ্র বাংলাদেশের পর্যটন মানচিত্রে একটি বড় শূন্যতা তৈরি হবে, যা দেশের অর্থনীতিতেও দীর্ঘমেয়াদি নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে।
প্রকৃতি আমাদের শত্রু নয় সে আমাদের জীবনদাতা, আশ্রয়দাতা, এবং সংস্কৃতির ধারক। আমরা যদি প্রকৃতিকে রক্ষা না করি, তবে একদিন প্রকৃতিও আমাদের রক্ষা করতে পারবে না। ভোলাগঞ্জের সাদা পাথর ধ্বংস হওয়া মানে কেবল একটি মনোমুগ্ধকর প্রাকৃতিক স্থান হারানো নয় এটি আমাদের পরিবেশ, অর্থনীতি, সংস্কৃতি এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রতি এক অমার্জনীয় অপরাধ।
এখনই সময় কঠোর আইন প্রয়োগ, স্থানীয় জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধি, এবং টেকসই পর্যটন নীতি বাস্তবায়নের। নয়তো অদূর ভবিষ্যতে ভোলাগঞ্জের সাদা পাথর শুধু পুরনো ছবিতে, গল্পে, আর আক্ষেপে বেঁচে থাকবে যেখানে আমরা গর্বের পরিবর্তে অপরাধবোধ অনুভব করব।
লেখক : গণমাধ্যমকর্মী ও কলামিস্ট