
জন্মদিন একা আসে না। এর সাথে আসে আরেকটি শব্দ, ‘শুভ’। আর এটি যে ‘শুভ’ সেটি প্রমাণ করতে পিতামাতা চেষ্টায় থাকেন সন্তানের চাহিদা মতো আনন্দ-আয়োজন করার।
‘বাবা, আমার বন্ধুর জন্মদিন হলো, কত লোক এসেছিল! আমার জন্মদিনের আর কতদিন দেরি?’
‘এবার আমার জন্মদিন আমরা কি রেস্টুরেন্টে এরেঞ্জ করতে পারি, মা? আমার বান্ধবীর বেলায় যেমন হলো?’
‘এবার কেক কিন্তু অনেক বড় হতে হবে। এক্সট্রাঅর্ডিনারি!’
‘হাতে কম টাকা থাকলে ড্রেস দিওনা আম্মু, কিন্তু বন্ধুদের ছাড়া কেক কাটতে পারবোনা। এটা প্রেস্টিজ ইস্যু।’
এরকম নানাবিধ প্রেস্টিজ ইস্যুতে নির্দিষ্ট বেতন আর মাসিক খরচের হিসাবহীন হিসাবের জটিল অঙ্কের সমাধান করতে থাকে পিতা বা মাতাটি। জন্মদিনটি বিজয়কেতন উড়িয়ে এসে উপস্থিত হয় বাড়ির দরজায়। আর তাকে শুভ’ হিসেবে প্রতীয়মান করতে দরজা খুলে কেক-মোমবাতি-বেলুন দিয়ে বরণ করতে হয় আগের দিনের রাত বারোটায়। আগে একটি কেক দিয়ে হলেও, এখন যোগ হয়েছে এই রাত বারোটার অতিরিক্ত একটি কেক। পার্টির জন্য জন্মদিনের সকালে সন্তানের চাহিদা মতো কেক এর অর্ডার দেওয়া হলো। বিকেল না গড়াতেই কেকখানাকে অতিযত্নে এনে রাখা হলো ফ্রিজে। সন্তানটি বারকয়েক ঢাকনা উঠিয়ে দেখে আসছে কেকটি তার কখন কেমন আছে।
সন্ধ্যার পার্টিখানা বাড়িতে হলে সাজানো হচ্ছে বাসার ড্রইংরুমের দেওয়াল। রদবদল করা হচ্ছে সোফা-টুল-চেয়ারগুলোর পজিশন। হয়তো বের করা হলো আলমারিতে যত্নে তুলে রাখা সোফার কভারের এক্সট্রা সেটখানা, যা হয়তো এরকম দুয়েকটা দিবসেই আলমারি থেকে বের হওয়ার সুযোগ পায়। আয়োজন যাই হোক, টেবিলে কেকের পাশে স্থান পাবে প্রতিটি আইটেম। বাদ যায়না বিস্কিট-চানাচুরও।
আর, পার্টিখানা কোনো রেস্টুরেন্টে হলে বার্থডে বয় বা বার্থডে গার্ল ছাড়া বাকিরা যেন রেস্টুরেন্টের ঝা-চকচকে পরিবেশে নিজেদের ত্রুটিবিচ্যুতিগুলো আবিষ্কার করতে শুরু করে। রেস্টুরেন্টীয় মানের পোশাক হলো কি না? শার্ট যদিও মানানসই, বেল্ট টা নতুন হলে ভালো হতো। শাড়ি যদিও বা হলো, সাথে হ্যান্ডব্যাগটা বড্ড বেমানান। চকচকে চমকপ্রদ চামচ আর চাকুর বহরের সাথে যুদ্ধের শেষে অন্তত আধাপেট খাওয়ার চিন্তায় অনেকটা অস্বস্তি। নিজেদের অপারগতায় সন্তানের যেন বন্ধুবর্গের সামনে প্রেস্টিজ না যায় সেই বিষয়ে অস্বস্তি। কিংবা বাড়ির বয়স্ক সদস্যকে সাথে না আনতে পারার অস্বস্তি। এত রকম অস্বস্তিকে ছাপিয়ে পিতা ও মাতাটির মনে হিসাবের দৌড় চলতে থাকে পার্টি শেষে ওয়েটারের দেওয়া বিলটি দেখার আগে পর্যন্ত। তবে বিল যতোই হোক সন্তানের হাসিটুকুর জন্য এ আয়োজনে মধ্যবিত্ত পিতা বা মাতাটি এক শান্তি অনুভব করার চেষ্টা করেন। তারা জানেন, মাসের বাকি কটা দিন অনেক গুনে চলতে হবে। হয়তো ধারও করতে হতে পারে। তারা জানেন, সামনে যে সন্তানের জন্মদিন আসছে তার জন্মদিনের আগে ‘শুভ’ সংযোজনের জন্যও প্রস্তুত থাকতে হবে মনে মনে।
আরও মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা মধ্যবিত্ত ঘরের শিশুরা অনিচ্ছায় অর্জন করে থাকেন। সন্তানটি রাতে গিফ্ট প্যাকেট খুলে কখনো কখনো ডিসহার্টেন হয়। কারন, সে তার যে উচ্চবিত্ত বন্ধুকে জন্মদিনে শীতাতপনিয়ন্ত্রিত শপিংমল থেকে মায়ের মাস চলার টাকা থেকে টাকা নিয়ে এক্সক্লুসিভ উপহার কিনে দিয়েছিল, সেই উচ্চবিত্ত বন্ধুটি তাকে একটি অর্ডিনারি মধ্যবিত্ত মানের উপহার দিয়ে পার পেয়ে গেছে। এটা একবার দুইবার নয়, জীবনে বহুবার দেখার সম্ভাবনা থাকে।
যতটুকু জানা গেছে জন্মদিনের সূচনা হয়েছে প্রাচীন মিশরে, যা রাজকীয় আভিজাত্য থেকে শুরু হয়ে ধীরে ধীরে গ্রিক ও রোমান সভ্যতার মধ্য দিয়ে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছেছে এবং জার্মানিতে এসে আধুনিক রূপ লাভ করেছে। কালের পরিক্রমায় জন্মদিন উদযাপনে সাধারণ ভোজের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে কেক, কার্ড, কোক, বেলুন, ফাস্টফুড এবং অন্যান্য পার্টি সামগ্রী। ইদানীং যুক্ত হয়েছে ওয়ানটাইম প্লেট-গ্লাস-চামচ। লুচি-পায়েস, মাংস-পোলাও এর জায়গা নিয়েছে স্যান্ডউইচ-পাস্তা-স্যুপ আর রাইস-সিজলিং-মিটবক্স ইত্যাদি। এই আয়োজনে সামগ্রিকভাবে লাভবান হয় এর সঙ্গে জড়িত শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীরা। জন্মদিন মূলত জন্মের ক্ষণকে আনন্দের সাথে অভিবাদন জানানোর একটি মহৎ আয়োজন। জন্মদিন নিজের জন্মের জন্য গর্বিত হওয়ার সুযোগ দেয় প্রত্যেককে। তাই এই দিনটিকে আনন্দঘন করার বিশেষ প্রয়োজন নিশ্চয়ই রয়েছে। কিন্তু আমরা দেখবো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরসহ অনেক বিখ্যাত লেখকের লেখায় শুভদিনে অতি আড়ম্বরের চেয়ে আত্ম-অনুসন্ধান (self-reflection) এবং নতুন চেতনার উদয়কে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। শুভক্ষণে রবীন্দ্রনাথের ‘প্রাণ ভরিয়ে তৃষা হরিয়ে মোরে আরও আরও আরও দাও প্রাণ’, ‘হে নূতন, দেখা দিক আরবার জন্মের প্রথম শুভক্ষণ/ তোমার প্রকাশ হোক কুহেলিকা করি উদঘাটন সূর্যের মতো’ এরূপ অক্ষরগুলিতে বিশেষ দিনে সৃষ্টিকর্তার নিকট প্রার্থনাকেই সর্বাগ্রে বিবেচনা করা হয়েছে। বিভিন্ন সামাজিক উৎসবের অতি-আড়ম্বর মধ্যবিত্তের সামাজিক প্রত্যাশার সাথে কীভাবে আর্থিক দুশ্চিন্তা ও চাপকে অন্তর্ভুক্ত করে থাকে তার সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ পাওয়া যায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, হুমায়ুন আহমেদের মতো সাধারণ জনজীবনের লেখকের লেখায়।
সৃষ্টিকর্তার নিকট নিজের জন্ম ও নিরাপদ জীবনের জন্য কৃতজ্ঞতা জানানো, বড়দের আশীর্বাদ বা দোয়া প্রার্থনা করা, নতুন বস্ত্রে নিজেকে সজ্জিত করা, প্রিয় খাবার খাওয়া এবং প্রিয় মানুষগুলোকে নিয়ে আনন্দে সময় কাটানো এগুলোই যেখানে উদ্দেশ্য, সেখানে শুধু সোস্যাল প্রেস্টিজকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে মধ্যবিত্ত পিতামাতার সন্তানদের তাদের পরিবারের সামর্থ্য ও সংস্কৃতির বাইরে গিয়ে জন্মদিন পালনটি কতটুকু সুবিবেচ্য সেটি ভেবে দেখা দরকার। জন্মদিনের আনন্দ আয়োজন কোনো অদৃশ্য দুশ্চিন্তার কারণ হচ্ছে কিনা সেটা ভেবে দেখা দরকার। কারণ, পরিবারের এত আয়োজন, ড্রইংরুমের এত বেলুন, রেস্টুরেন্টের সুসজ্জিত টেবিল, কেক, মোমবাতি সব দেখা যায়। কিন্তু মধ্যবিত্তের অন্তরের মধ্যবিত্তীয় যাতনা অদৃশ্যই থেকে যায়।
লেখক: ঊর্মিলা চক্রবর্তী: ৩৩ বিসিএস (ইংরেজি), রাজশাহী কলেজ, রাজশাহী।

বাংলাদেশ ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ে প্রবেশ করেছে। পৃথিবীর ইতিহাসে ইতোপূর্বে ঘটে যাওয়া বহু তাৎপর্যপূর্ণ রাজনৈতিক পরিবর্তনের প্রেক্ষাপট, পরিণতি ও অর্জনের ঘটনাগুলো বিচার-বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাই, যে কোনো ন্যায়ভিত্তিক যৌক্তিক রাজনৈতিক আন্দোলন সাফল্য অর্জন করেছে, কখনো ব্যর্থ হয়নি। এসব আন্দোলন-সংগ্রামের প্রকৃতি ও আদর্শগত অবস্থানের মধ্যে ভিন্নতা থাকলেও অবৈধভাবে ক্ষমতা দখলদারি স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে এগুলো সর্বদাই বিজয় লাভ করেছে। বিশ্বের প্রাচীন ইতিহাসেও স্বৈরশাসকদের বিরুদ্ধে বারবার বিদ্রোহ ঘোষিত হয়েছে। কোথাও বিদ্রোহ সফল হয়েছে, কোথাও আবার ব্যর্থ হয়েছে। সাফল্য ও ব্যর্থতার ধারাবাহিকতায় আমরা দেখেছি আধুনিককালে কোনো স্বৈরশাসকই গণ-অভ্যুত্থানের প্রবল প্রতিরোধের মুখে তার মসনদ রক্ষা করতে পারেনি। জুলাই গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে সেকথা আবারও প্রমাণিত হয়েছে।
আপনারা নিশ্চয়ই অবগত আছেন, অন্তর্বর্তী সরকার আগামী বছর ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথমার্ধে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রস্তুতি নিচ্ছে। সবকিছু ঠিক থাকলে পবিত্র রমজান শুরু হওয়ার আগেই আমরা জনগণের ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত একটি নতুন সরকার পেয়ে যাব। বিগত সরকারের আমলে ২০১৪, ২০১৮ ও ২০২৪ সালে যে তিনটি সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সেগুলোর ন্যূনতম গ্রহণযোগ্যতা ছিল না। আগের সরকার রাজনৈতিক দলগুলোর বিভাজনকে পুঁজি করে পুরো জাতিকে অনৈক্যের দিকে ঠেলে দিয়েছিল। জাতি ছিল দ্বিধাবিভক্ত। এ বিভক্তির সুযোগ নিয়ে আওয়ামী লীগ সরকার বিগত সাড়ে ১৫ বছর (২০০৯ থেকে ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট পর্যন্ত) জনগণের ওপর নির্মম নির্যাতন ও স্বৈরাচারী শাসন কায়েম করেছিল। দেশের প্রতিটি প্রতিষ্ঠানকে ব্যাপক মাত্রায় দলীয়করণ ও আত্মীয়করণের মাধ্যমে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে যায়। কিন্তু এক সময় দেশের মানুষ আওয়ামী দুঃশাসনের বিরুদ্ধে ফুঁসে ওঠে।
বিগত সরকারের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক দলগুলো যখন আন্দোলন-সংগ্রামে রত ছিল, তখন ছাত্ররা বৈষম্য নিরসনের দাবিতে সরকারের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক আন্দোলন গড়ে তোলে। শিক্ষার্থীরা প্রথমে সরকারি চাকরিতে বিদ্যমান কোটা সুবিধা সংস্কারের জন্য আন্দোলন শুরু করলেও সরকারের ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণের কারণে কোটা সংস্কার আন্দোলন একপর্যায়ে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে পরিণত হয় এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে তা সরকার পতনের একদফা আন্দোলনে রূপ নেয়। কোটা সংস্কার আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারী ছাত্রদের নানাভাবে বৃহত্তর আন্দোলন থেকে বিরত রাখার জন্য সরকারি এজেন্সিগুলো তাদের প্রলোভন দেখায়, তাদের ওপর নির্মম নির্যাতন চালায়। কিন্তু তারপরও তারা উদ্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনে ইস্পাতকঠিন দৃঢ় ঐক্য বজায় রাখে। একপর্যায়ে ছাত্রদের আন্দোলনে দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক দল এবং জনগণ সম্পৃক্ত হয়। ফলে সরকারের পতন অনিবার্য হয়ে ওঠে। আন্দোলনের মাধ্যমে ছাত্রদের মধ্যে বৃহত্তর ঐক্য গড়ে উঠেছিল এবং শেষ পর্যন্ত তা বহাল ছিল বলেই দোর্দণ্ডপ্রতাপশালী সরকারপ্রধান শেখ হাসিনা পদত্যাগ করে দেশ ছেড়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হন। এর মাধ্যমে আবারও প্রমাণ হলো, যে কোনো লক্ষ্য অর্জনের জন্য জনগণের বৃহত্তর ঐক্যের কোনো বিকল্প নেই। ঐক্যবদ্ধ জাতি কখনোই পরাজিত বা লক্ষ্যচুত হয় না। একটি দেশের উন্নয়ন-অগ্রগতি ত্বরান্বিত করার জন্যও জনগণের মধ্যে সুদৃঢ় ঐক্যের বন্ধন গড়ে তোলা একান্ত প্রয়োজন।
কথায় বলে, ‘United we stand, divided we fall’. একটি জাতি যদি তাদের বৃহত্তর স্বার্থে ঐক্যবদ্ধ থাকে, তাহলে কোনো জাগতিক শক্তি তাদের পরাজিত করতে পারে না। কিন্তু বৃহত্তর জাতীয় ঐক্যে ফাটল দেখা দিলে একটি সম্ভাবনাময় জাতিও ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। তাই আমাদের সর্বাবস্থায় জাতীয় স্বার্থের প্রশ্নে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। বিশেষ করে চব্বিশের গণঅভ্যুত্থানের পর জাতীয় ঐক্য ধরে রাখার বিষয়টি আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। কোনো কারণে আমরা যদি জাতীয় ঐক্য ধরে রাখতে না পারি, ক্ষুদ্র স্বার্থে পরস্পর বিচ্ছিন্ন বা বিভক্ত হয়ে পড়ি, তাহলে পরাজিত শক্তি সেই সুযোগে আবারও মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারে। কাজেই এ মুহূর্তে আমাদের সবচেয়ে জরুরি কর্তব্য হচ্ছে গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে সৃষ্ট ঐক্য ধরে রাখা। কোনোভাবেই এ ঐক্যকে ভন্ডুল হতে দেওয়া যাবে না।
এখানে কিছু বিষয় উল্লেখ করতে চাই, যা সবারই জানা আছে। তারপরও ইতিহাসের শিক্ষাকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। প্রাচীনকালে বাংলাদেশ ছিল বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে উর্বর একটি জনপদ। এখানে সম্পদের কোনো অভাব ছিল না। বিদেশি বণিক ও ব্যবসায়ীরা এখানে এসে ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে অর্থবিত্ত অর্জন করতেন। সপ্তদশ শতাব্দীতে ফরাসি পরিব্রাজক ফ্রাঁসোয়া বার্ণিয়ার বাংলাদেশের অপরূপ সৌন্দর্য এবং সম্পদের প্রাচুর্য দেখে এতটাই অভিভূত হয়েছিলেন যে, তিনি মন্তব্য করেন, ‘There are hundred gates open to enter bengal, but there is not a singal gate to come out of it’ . ফ্রাঁসোয়া বার্নিয়ার কোনো সাধারণ পর্যটক ছিলেন না, তাকে বলা হয় দার্শনিক পর্যটক। তিনি গভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে তৎকালীন ভারতীয় সমাজ, রাজনীতি ও সংস্কৃতিকে অবলোকন করে সত্যনির্ভর তথ্য গ্রহণ করেছিলেন। তাই তাকে স্বপ্নদ্রষ্টা হিসাবে আখ্যায়িত করা যায়। বার্নিয়ার যে সোনার বাংলা দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন, আমরা সেই বাংলাকে আর আগের মতো সম্পদশালী করে রাখতে পারিনি। বাংলাদেশ আজ একটি স্বাধীন-সার্বভৌম দেশ। বহু রক্ত ও ত্যাগের বিনিময়ে এদেশের মানুষ ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতার সূর্য ছিনিয়ে এনেছে। কিন্তু বার্নিয়ারের দেখা সেই সোনার বাংলার সৌন্দর্য ও প্রাচুর্য আজ রূপকথার মতো শোনায়। আমরা যদি ক্ষুদ্র ব্যক্তিস্বার্থকে জলাঞ্জলি দিয়ে বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থে সবসময় ঐক্যবদ্ধ
জাতীয় ঐক্য বিনষ্ট করার জন্য বিভিন্ন সময় নানা কৌশল অবলম্বন করা হয়। এর মধ্যে অন্যতম হলো ম্যাকিয়াভিলির মতবাদ। বিশিষ্ট রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ম্যাকিয়াভিলি তার ‘The Prince’ গ্রন্থে বলেছিলেন, ‘The prince should be as mighty as a lion and as clever as a fox’। অর্থাৎ একজন শাসককে হতে হবে সিংহের মতো শক্তিশালী এবং শৃগালের মতো ধূর্ত। তাকে ক্ষমতায় যেতে হবে এবং যে কোনো মূল্যে তা ধরে রাখতে হবে। তার কাছে নীতি-নৈতিকতা কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। তাকে শুধু রাষ্ট্রক্ষমতায় টিকে থাকতে হবে। এজন্য যে কোনো পন্থা অবলম্বন করা যেতে পারে। তাই তার মতে, End will justify the means; অর্থাৎ চূড়ান্ত পরিণতিই গৃহীত পদক্ষেপের যৌক্তিকতা নির্ধারণ করে। বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে ম্যাকিয়াভিলির থিয়োরির বাস্তব প্রয়োগ লক্ষ্য করা গেছে। ২০০৯ সালে শেখ হাসিনা রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে ম্যাকিয়াভিলির দীক্ষা গ্রহণ করেন। তবে ইতিহাসের সেই বহুকথিত আপ্তবাক্য : ‘ইতিহাস থেকে কেউ শিক্ষা গ্রহণ করে না।’ ইতিহাসের শিক্ষা কেন ক্ষমতার কষ্টকল্পিত প্রাসাদের ভেতরে প্রবেশ করতে পারে না-সে এক আশ্চর্য রহস্যময় জিজ্ঞাসা, যার উত্তর কোনোদিন, কোনোকালেই কোনো স্বৈরাচার দিতে পারেননি। তবে নিষ্ঠুরভাবে ভোগ করেছেন ইতিহাসের অমোঘ পরিণতি।
বিভিন্ন বিষয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে এখনো যে মতভেদ রয়েছে, তা আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করতে হবে। মনে রাখতে হবে, এমন কোনো সমস্যা নেই, যা আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করা সম্ভব নয়। এমনকি যুদ্ধের মাধ্যমে বিজয়ী পক্ষকেও শান্তির জন্য আলোচনার টেবিলে বসতে হয়। আমাদের রাজনৈতিক দলগুলো নিশ্চয়ই দেশে অশান্তি চায় না। তারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নয়ন এবং জনগণের ভাগ্য পরিবর্তন করতে চায়। তাই তাদের আলোচনার টেবিলে বসে বিভিন্ন ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। বিশেষ করে ফেব্রুয়ারির নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যাপারে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ইস্পাতকঠিন ঐক্য গড়ে তুলতে হবে, যাতে শান্তিপূর্ণ ও উৎসবমুখর পরিবেশে জনগণ তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারে। মনে রাখতে হবে, নির্বাচনে জয়-পরাজয় স্বাভাবিক ঘটনা।
নভেম্বর বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত সংবেদনশীল একটি মাস। এ মাসেই মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচারের রায় প্রকাশ শুরু হবে বলে আশা করা হচ্ছে। এছাড়া নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার সময় আগত। বিচারের রায় প্রকাশের আগে সারাদেশে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির অপচেষ্টা চালানো হতে পারে। রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনায় হামলা হতে পারে। বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ওপর আক্রমণ হতে পারে। বাংলাদেশের মানুষ সরল প্রকৃতির। তাদের খুব সহজেই বিভ্রান্ত করা যায়। একটি মহল ইতোমধ্যেই সোশ্যাল মিডিয়ায় নানা ধরনের বিভ্রান্তিমূলক প্রচারণা চালাতে শুরু করেছে। এসব প্রচারণা দেখে যে কোনো মানুষ বিভ্রান্ত হতে পারে। তারা পথভ্রষ্ট হতে পারে। এদের ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে।
বিগত সরকারের আমলে যারা নানা ধরনের অনৈতিক সুবিধা ভোগ করেছে, তারা আবারও সক্রিয় হয়ে ওঠার অপেক্ষায় আছে। রাজনৈতিক দলগুলো যদি নিজেদের মধ্যে সম্প্রীতি বজায় রাখতে না পারে, তাহলে জাতীয় ঐক্য বিনষ্ট হবে। সেই সুযোগে পরাজিত শত্রুরা ছোবল মারতে পারে। যে কোনো মূল্যেই হোক, আগামী দিনে জাতীয় ঐক্য বজায় রাখতে হবে। আমাদের মনে রাখতে হবে, সুযোগ বারবার আসে না। চব্বিশের গণঅভ্যুত্থান আমাদের জন্য যে সুযোগ সৃষ্টি এবং ঐক্যের ভিত রচনা করে দিয়েছে, তা কোনোভাবেই ধ্বংস হতে দেওয়া যাবে না। মনে রাখতে হবে, ঐক্যেই উত্থান, অনৈক্যেই পতন।
বিগত সরকার আমলে দেশের জনগণের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে রাখা সম্ভব হয়েছিল বলেই তারা দীর্ঘকাল দেশে স্বৈরশাসন চালাতে সক্ষম হয়েছিল। আমি একজন প্রবীণ শিক্ষক হিসাবে সব রাজনৈতিক দল এবং জনগণের কাছে বিনীত অনুরোধ জানাব-আপনারা ক্ষুদ্র স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে যে কোনো মূল্যে হোক জাতীয় ঐক্য ধরে রাখুন। আমরা এটি করতে ব্যর্থ হলে দেশের ভবিষ্যৎ আবারও অন্ধকারে নিমজ্জিত হতে পারে।
লেখক: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য এবং বাহরাইনে নিযুক্ত সাবেক রাষ্ট্রদূত।

বাংলাদেশের স্বাস্থ্য সেবার ধাঁচ পরিবর্তনের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো নার্সিং ও মিডওয়াইফারি। হয়রানিমুক্ত ও কার্যকর পেশা হিসাবে গড়ে তোলা। তার জন্য শিক্ষা-প্রশিক্ষণ, নিয়োগ-পরিষেবা, কর্তৃত্ব-সামঞ্জস্য ও প্রশাসনিক সাপোর্ট-ব্যবস্থার উন্নয়ন অত্যাবশ্যক। কিন্তু সেদিক থেকে আমাদের দেশে এখনো বহু চ্যালেঞ্জ রয়ে গেছে। বিশেষভাবে, যখন আমরা কথা বলি সাধারণ নার্সদের অবস্থান নিয়ে— তাদের ভয় ও অনিশ্চয়তার বিবেচনায়, বর্তমানে নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরকে প্রথম সারির এডমিনিস্ট্রেটিভ দায়িত্বে স্বাস্থয় বিভাগের অধীনে ন্যস্ত করার প্রসঙ্গে সেখানে নতুন সুযোগ ও সম্ভাবনার পাশাপাশি প্রশাসনিক কর্তৃত্বের সম্ভাব্য অপব্যবহার, অধিকারহীনতা ও ভয়ভীতি-সৃষ্ট পরিস্থিতিও দেখা দিচ্ছে। এই সম্পাদকীয়তে প্রথমে নার্সিং শিক্ষা ও সার্ভিসের বর্তমান পরিস্থিতি সংক্ষেপে তুলে ধরা হবে, এরপর ওই নতুন প্রশাসনিক রূপান্তরের প্রেক্ষাপট ও নার্সসহ বিভিন্ন পক্ষের উদ্বেগ বিশ্লেষণ করা হবে। শেষে থাকবে সংকট ও সম্ভাবনা এক সাথে-সাথে, এবং কিছু সুপারিশও দেওয়া হবে।
এক: নার্সিং শিক্ষা ও সার্ভিসের বর্তমান অবস্থা
শিক্ষা-এর অবস্থা
বাংলাদেশে নার্সিং ও মিডওয়াইফারি শিক্ষা গত কয়েক দশকে ব্যাপকভাবে বিস্তৃত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, মাত্র এক দশক পনেরেকের মধ্যে নার্সিং ও মিডওয়াইফারি কলেজ-প্রতিষ্ঠান প্রায় ৪২০ % বাড়িয়েছে। তবে, সংখ্যায় বৃদ্ধি হলেও ‘মান’-সংক্রান্ত সমস্যা এখনো রয়ে গেছে। যেমন এখনো ডিপ্লোমা-, ব্যাচেলর- ও মাস্টার্স-স্তরে পড়াশোনা করলেও বিশেষায়িত নার্সিং (যেমন ICU, কার্ডিয়াক নার্সিং ইত্যাদি) খুব কম।
একাধিক গবেষণা দেখিয়েছে শিক্ষার্থীরা ক্লিনিকাল প্রশিক্ষণে অভিজ্ঞতা পাচ্ছে কম, তাদের শিক্ষক বা সুপারভাইজার অনেক সময় অভিজ্ঞ নয়, এবং তাদের শিক্ষাগত পরিবেশ ও বাস্তব ক্লিনিকাল পরিবেশের মধ্যে বড় ব্যবধান রয়েছে।
এছাড়া, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর দ্রুত বৃদ্ধি হয়েছে, তবে অনেক ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য-সেবার সঙ্গে যুক্ত হসপিটাল-ক্লিনিকাল অনুশীলনের সুযোগ কম।
সেবার অবস্থা
সেবার ক্ষেত্রে নার্সিং সেক্টরের বড় চ্যালেঞ্জ হলো পূর্ণসংখ্যায় নার্স নেই, এবং তাদের দক্ষতা ও অবস্থান এখনো কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে পৌঁছায়নি।
উদাহরণস্বরূপ, এক প্রতিবেদন বলছে— বাংলাদেশের দরকার রয়েছে প্রায় ৩১০,৫০০ জন নার্স, কিন্তু বাস্তবে রয়েছে মাত্র≈৫৬,৭৩৪ জন (১৮ % মাত্র)। অন্য রিপোর্ট বলছে দেশজুড়ে রয়েছে মাত্র ৮৫,০০০ জন নার্স—এতে স্পষ্ট যে ডাক্তার-নার্সের অনুপাত অত্যন্ত বিপরীতে।
আরও বলা হয়েছে, নার্সিং পেশা সামাজিকভাবে এখনো অনেক বাধার সম্মুখীন—কর্মঘণ্টা, শিফট কাজ, পুরুষ রোগীর পাশে রাতেও কাজ, ঘন-পরিবারিক দায়িত্বসহ সামাজিক মনোভাব ইত্যাদি।
সংক্ষেপে: শিক্ষা ও সেবা মিলিয়ে রয়েছে ২৩৪
এই প্রেক্ষাপটে, নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরকে স্বাস্থ্য বিভাগে ন্যস্ত করার উদ্যোগ এসেছে—যেটি নতুন প্রশাসনিক রূপান্তর এনে দিতে পারে। তবে সেই রূপান্তরকে ঘিরে নার্সদের মধ্যে উদ্বেগও বেড়েছে।
দুই: প্রশাসনিক রূপান্তর-প্রেক্ষাপট ও উদ্বেগ
রূপান্তরের ধারণা
নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর (DGNM) হলো জনসাধারণ সেবা-মাধ্যমে নার্সিং ও মিডওয়াইফারি শিক্ষা-ও-সেবা-পরিচালনার জন্য বিশেষ কর্তৃপক্ষ। বর্তমানে এটি স্বাস্থ্য বিভাগ (Health Division) বা সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক সেকশনের অধীনে রেখে, নার্সিং শিক্ষা-সেবা খাতকে আরও শক্তিশালী ও স্বল্পাভিজ্ঞ প্রশাসনিক গঠন দেয়া হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। আধুনিক স্বাস্থ্যসেবায় নার্সিংকে কেবল
‘সহায়ক’ নয়, মূল সেবাদায়ী অংশীদার হিসেবে বিবেচনা করার ধারাক্রমে এই ধরনের রূপান্তর কেন্দ্রীয় হয়ে উঠেছে।
উদাহরণস্বরূপ, জাপানের Japan International Cooperation Agency (JICA)-র একটি প্রকল্প দেখায়, নার্সিং সেবার সক্ষমতা বাড়াতে DGNM-কে প্রযুক্তিগত সহায়তা দেওয়া হচ্ছে।
নার্সদের উদ্বেগ ও আশঙ্কা
তবে এই রূপান্তরের সাথেই কিছু সঙ্কট ও উদ্বেগ উৎপন্ন হয়েছে। বিশেষ করে সাধারণ নার্স-পেশাজীবীদের জন্য নিচের বিষয়গুলো উদ্বেগে রূপ নিচ্ছে:
সাধারণ নার্সদের হত বিহ্বলতা কেন বাড়ছে?
একদিকে রয়েছে বাড়তি ডাকচাপ, দীর্ঘ কাজের সময়, ঘোর তাড়াহুড়ো; অন্যদিকে রয়েছে নিয়োগ-সংক্রান্ত অনিশ্চয়তা ও কর্তৃত্বহীনতা। এমন পরিস্থিতিতে যখন প্রশাসনের নতুন রূপান্তর হচ্ছে, তখন সাধারণ নার্সরা বোধ করা শুরু করেছেন যে—এই রূপান্তর হয়তো তাদের জন্য বৃহৎ সুযোগ নয়, বড় ঝামেলা হতে পারে।
অতিরিক্তভাবে, অনেক সময় প্রশাসনিক কর্মকর্তারা নার্সিং সেক্টরের প্রকৃত দৃষ্টিকোণ সবসময় বোঝেন না, নার্সিংয়ের ক্লিনিকাল ও শিক্ষাগত প্রয়োজন, পেশাগত মর্যাদা-সংক্রান্ত বিষয়, দীর্ঘ সেবা-শিফট বা রেসিডেন্স সুবিধাবিষয়ক বিষয় তারা গুরুত্ব সহকারে না নেওয়ার ফলে নার্সদের ভয় হচ্ছে—নতুন প্রশাসন তাদের ওপর ‘উচ্চস্তরের’ নিয়ন্ত্রণ আরোপ করবে, তাদের কর্তৃত্ব কমিয়ে দেবে।
তিন: হুঁশিয়ারি ও প্রতিক্রিয়া – কোথায় সমস্যার মূলোৎপতন?
মূল সমস্যার উৎস
নিয়োগ-স্থানান্তর-পদোন্নতি প্রক্রিয়া স্বচ্ছ করুন: প্রশাসনিক রূপান্তরের ফলে যদি নিয়োগ-নীতি ও ট্রান্সফার হয় তবে তা স্বচ্ছভাবে সম্পন্ন হোক—মেরিট, অভিজ্ঞতা, শিক্ষাগত যোগ্যতার ভিত্তিতে।
পরিশেষে
বাংলাদেশে নার্সিং শিক্ষা ও সার্ভিসের সামগ্রিক চিত্র যতটা সম্ভাবনাময়, ঠিক ততটাই বিপর্যয়ের সম্ভাবনাও রয়েছে। শিক্ষার প্রসার, কলেজ-প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা এবং মিডওয়াইফারি-সেবার উন্নয়নের দিকে ইতিবাচক পদক্ষেপ ইতোমধ্যে দেখা গেছে। কিন্তু গুণগত মান, নিয়োগ-সংস্থান, পেশাগত মর্যাদা ও প্রশাসনিক সাপোর্ট এখনো অনেকটাই পিছিয়ে রয়েছে।
বর্তমানে নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরকে স্বাস্থ্য বিভাগ–এর অধীনে নেওয়ার এই উদ্যোগ একদমই সময়োপযোগী। কারণ নার্সিং খাতে শুধু সেবা নয়, নেতৃত্ব, পরিকল্পনা, উন্নয়ন এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভূমিকা এখন সময় দাবি করছে। তবে এই রূপান্তর যাতে সাধারণ নার্সদের ওপর অতিরিক্ত কর্তৃত্ব আরোপের মাধ্যমে না হয়, তার জন্য সতর্ক থাকতে হবে। যদি না হয়—তাহলে সাধারণ নার্সরা হতো বিহ্বল অবস্থায় পড়তে পারে, আর তা থেকে সবার জন্য সেবার মানও কমে যেতে পারে।
সুতরাং, শুধু প্রশাসনিক রূপান্তর নয়—তার সঙ্গে স্বায়ত্তশাসন, অংশগ্রহণ, নিয়োগ-পদোন্নতি সুনিশ্চিতকরণ, শিক্ষাগত উৎকর্ষতা ও সামাজিক মর্যাদার উন্নয়ন একসাথে গড়ে তুলতে হবে। তবেই নার্সিং খাত দেশের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ স্বাস্থ্য প্রয়োজনে কার্যকর ভূমিকা নিতে পারবে, এবং সাধারণ নার্সরা নির্ভয়ে, দায়বদ্ধভাবে, সম্মানসহ কাজে নিয়োজিত হতে পারবেন।
এটি একটি যাত্রা—যাতে নার্সিং শিক্ষা-সেবা শুধুই সম্প্রসারিত নয়, গভীর ও গুণগতভাবে শক্তিশালী হবে। সেই দিকে এখন সচেতন উদ্যোগ নেওয়াই সময়ের দাবি।

জাতীয় অধ্যাপক মোহাম্মদ রফি খান ( জন্ম ১ আগস্ট ১৯২৮- মৃত্যু ৫ নভেম্বর, ২০১৬ ) যিনি এম আর খান হিসেবে ছিলেন অতি পরিচিত। বাংলাদেশে ঋধঃযবৎ ড়ভ চবফরধঃৎরপং হিসাবে খ্যাত অধ্যাপক খান ছিলেন একজন অনুকরনীয় ও প্রাত:স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। শিশু চিকিৎসাক্ষেত্রে প্রবাদ পুরুষ, শিশুবন্ধু, সমাজ হিতৈষী, শিক্ষাবিদ, দক্ষ চিকিৎসা প্রশাসক ও সফল শিল্প উদ্যোক্তা যিনি সমাজসেবায় একাধারে একুশে পদক ও স্বাধীনতা পুরষ্কার পদকে ভূষিত হয়েছিলেন। নির্লোভ, প্রচারবিমুখ, সদাহাস্য মানুষটি তার বিভিন্ন জনহিতকর কাজের মধ্য দিয়ে দীর্ঘদিন যাবত সমাজে অসংখ্য মানুষকে সেবা দিয়ে গেছেন।
শিশুবন্ধু এম আর খান এর জীবন দর্শন ছিল -কর্মচাঞ্চল্য আর মহৎ ভাবনার সরোবরে সাঁতার দিয়ে মানব কল্যাণে নিবেদিত চিত্ততা। নিবেদিতা মেডিকেল ইনস্টিটিউট আর অগণিত শিশু চিকিৎসা সদন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তার সেই স্বপ্নেরা ডানা মেলে ফিরেছে সাফল্যের আকাশে। এসব প্রতিষ্ঠানে শিশু, নারী ও অসহায়জনের নতশীর, মূক ও ম্লান মুখে হাসি ফুটিয়ে সাফল্যের তারকারা ঝিলিমিলি করে ফিরত তার ললাটে, তার মুখে-তার সানন্দ তৃপ্তির নিলয়ে। সুদক্ষ পরিচালনায়, সাংগঠনিক দক্ষতায়, পৃষ্ঠপোষকতায়, নৈপুণ্যে, নিবেদনে স্বাস্থ্য ও সমাজসেবা খাতে অর্থবহ অবকাঠামো নির্মাণ ছিল তার ব্রত। এ সবের মাঝে চির ভাস্বর হয়ে রইবে তার স্মৃতি। ‘উপকার কর এবং উপকৃত হও’ এই মহাজন বাক্য তার জীবন ও কর্মে, মনন ও মেধায় পথ চলা ও জীবন সাধনায় স্বতঃসিদ্ধের মতো অর্থবহ হয়ে উঠেছিল। আর এ সবের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়ায় শিশুদের মতো সারল্যে, সহজিয়া কড়চায়, বন্ধু বাৎসল্যে, স্নেহাস্পদনায়, মুরুব্বীয়ানার মাধুর্যে ছিল তার ব্যক্তি ও চরিত্র উদ্ভাসিত।
জাতীয় অধ্যাপক ডা. এম আর খান মনে করতেন রোগীও একজন মানুষ। আর এ রোগীটি সামাজে আমাদেরই কারো না কারো আত্মীয়-স্বজন, এমন কি আপনজন। রোগী যখন ডাক্তারের কাছে আসেন; তখন সাহায্য প্রার্থী, কখনও কখনও অসহায় বটে। আর রোগীটি যদি শিশু হয় তা হলে তো কথাই নেই। ডাক্তারের কর্তব্য হবে রোগীর কষ্ট গভীর মনোযোগের সাথে ধৈর্য সহকারে শোনা, রোগীর শারীরিক অবস্থা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া। রোগীকে সুস্থ করে তুলতে সঠিক রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা যেমন প্রয়োজন; তেমনি রোগীর অভিভাবকদের প্রতি ডাক্তারের সহমর্মিতা প্রদর্শন ও আশ্বস্ত করাও প্রয়োজন। সব রোগীই তাড়াতাড়ি সুস্থ হবে এমনটিও ঠিক নয়। কারো কারো সুস্থ হতে সময় লাগতে পারে। মহান আল্লাহর প্রতি অবিচল আস্থা রেখে তিনি বলতেন, হায়াত ও মউতের মালিক যেমন আল্লাহতায়ালা; তেমনি রোগ হতে মুক্তি দাতাও তিনি। তবে রোগীর আপনজনরা এমন যেন বলতে না পারেন যে- ডাক্তার আন্তরিক ছিলেন না, ডাক্তারের অবহেলায় রোগীর মৃত্যু হয়েছে।
মৃত্যুর আগে বেশ কয়েক মাস তিনি তার প্রতিষ্ঠিত সেন্ট্রাল হাসপাতালে পরিচর্যাধীন ছিলেন। হাসপাতালের বেডে শুয়ে ৯ সেপ্টেম্বর (২০১৬) ‘দুটি কথা’ শীর্ষক শেষ লেখায় তিনি বলেন -
‘মানুষ বাঁচে আশায়, দেশ বাঁচে ভালোবাসায়। আপনি আশা করেন এটা-ওটা করবেন। ভবিষ্যতের পরিকল্পনা আছে, কিন্তু আল্লাহ জানেন আপনি কত দিন এ দুনিয়ায় আছেন। সুতরাং আপনি যেটা ভালো মনে করেন এখুনি বা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব করবেন। এসুযোগ আর নাও আসতে পারে। ‘শুভষ্য শীঘ্রম’ - রাম রাবনের একটা গল্প শুনাতে চাই। রাবন বললেন আমি স্বর্গের সিঁড়ি বানাতে চেয়েছিলাম কিন্তু আমার সময় শেষ। সেজন্য আমি তোমাকে একটা উপদেশ দেব, যদি তুমি কোন ভালো কাজ করতে চাও ঝঃধৎঃ হড়ি ফড়হ’ঃ ধিরঃ ভড়ৎ ঃড়সড়ৎৎড়।ি”
এ প্রসঙ্গে তিনি তার জীবনের দুটি ঘটনা তুলে ধরেন-
‘প্রথমত : শিশুদের জন্য পথকলি নামে এক সংস্থায় কাজ করার সুযোগ আমার হয়েছিল। তাদের চিকিৎসা সেবা দেওয়া হত বর্তমান শেরাটন হোটেলের উত্তর দিকে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের বাড়িতে। আমি তৎকালীন সরকার প্রধানের কাছে তাদের চিকিৎসাসেবা প্রদানের জন্য একটা জায়গা চেয়েছিলাম। সেটা হলো মিরপুরের এশিয়া সিনেমা হলের উল্টো দিকে। একবিঘা জমিতে একটা টিনের ঘর করে সেখানে আউট ডোর শুরু করা যেত। তখন পথকলি ট্রাস্ট গঠনের লক্ষ্যে অনেক টাকাও উঠেছে সেই টাকা দিয়ে ট্রাস্ট ফান্ডের মাধ্যমে একটা প্রতিষ্ঠান চালানোর উদ্যোগ নেওয়া যেত। হাসপাতাল ও মসজিদ সবাই চান কেউ এর বিনাশ চান না। সরকার প্রধান বললেন পরে হবে। এ বাড়িটা তো কেউ নিচ্ছে না, এখানেই কাজ চলতে থাকুক। আমি স্থায়ী জায়গার জন্য আবেদন জানাই। তিনি বললেন দেখা যাক পরে হবে। কিছু দিনের মধ্যে পট পরিবর্তন হলো। পথকলি ট্রাস্ট বন্ধ হয়ে গেল। সব শেষ। অসচ্ছল শিশুদের সেবা সুযোগ মিলিয়ে গেল।
দ্বিতীয়ত : তৎকালীন আই পি জি এম আর বর্তমানে বঙ্গ বন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের পশ্চিম পার্শ্বে একটা জায়গা ছিল। আমি ও প্রফেসর নূরুল ইসলাম সাহেব এ হাসপাতাল বর্ধিত করার লক্ষ্যে ঐ জায়গাটি হাসপাতালের নামে বরাদ্দের জন্য ভূমি মন্ত্রী জনাব আব্দুল হক সাহেবের সাথে দেখা করি। কয়েকদিন যাতায়াতের পর সেখানে দেখলাম খুবই হৈ চৈ। আমি মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ জানালাম, স্যার কাজটা ভালো মনে করলে আজকে করে দেন। আপনার এখানে যে অবস্থা না জানি আপনি কয়দিন এ দায়িত্বে থাকবেন? মন্ত্রী মহোদয় বললেন আজ তো অফিস প্রায় শেষ কালকে আসেন। আমি বললাম কালকে আপনি এ পদে না থাকতে পারেন। সবাই আমার কথায় অবাক। বললাম আজকে সম্ভব হলে করে দেন। সন্ধ্যায় আমাদের পি.এ-কে টাইপ মেশিনসহ তার কাছে পাঠালাম, রাতের মধ্যে কাজ শেষ হয়ে গেল। ভাগ্যের পরিহাস পরের দিন তার মন্ত্রীত্ব চলে গেল। সুতরাং শুভষ্য শীঘ্রম কত উপকারী। আমার এই দুটি ঘটনা বলার উদ্দেশ্য - প্রথমটি পরে করবেন বলে রেখে দিলেন কিন্তু আর করতে পারলেন না। আর দ্বিতীয়টি তিনি যদি ঐদিন রাত্রে না করতেন তাহলে হয়তো এটিও হতো না।
‘দেশ বাঁচে ভালোবাসায়’ শিরোনামে তিনি আরো লিখেছেন-
‘আপনি টাকার ২.৫% যাকাত দেন। সময়ের যাকাত যদি ২.৫% ধরি তবে সপ্তাহে প্রায় ৪.৫ ঘণ্টা হয়। সপ্তাহে ২দিন ২.১৫ মি:, ২.১৫মি: ঘন্টা সময় দিতে পারেন। এতে অনেক ভালো ভালো কাজ করতে পারবেন। আপনারা সবাই ব্যস্ত আপনাদের সময় অনেক মূল্যবান। তবুও সবার জন্য ২৪ ঘণ্টা সমান। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামারও ২৪ ঘণ্টা, আপনাদেরও ২৪ ঘণ্টা, আমারও ২৪ ঘণ্টা। ব্যাপার হলো এই ২৪ ঘণ্টা আমরা কে কিভাবে ব্যবহার করি। সেটাই ভবিষ্যতের সফলতা। যদি আপনি আপনার গ্রামের বা ইউনিয়নের বা উপজেলার বা জেলার একজন লোককে যদি ভাল কাজে উদ্বুদ্ধ করতে পারেন তাহলে তিনি তার পরিবারের, তার গ্রামের একজন আদর্শ মানুষ হতে পারেন। যার দ্বারা সমাজ ও দেশ উপকৃত হবে। তবে এর ঘবমধঃরাব ধংঢ়বপঃ আছে, তিনি যদি লাঞ্ছিত, বাধাপ্রাপ্ত বা নির্যাতিত হন তবে একাজ আর করবেন না। এমনকি তার আত্মীয়রা তাকে অন্যভাবে নিবৃত রাখার চেষ্টা করবেন। এখানে আমি সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্রোপাধ্যয়ের ‘কপাল কুন্ডলা’ হতে একটি ঘটনা তুলে ধরবো। নবকুমার ও তার সঙ্গীরা নৌকাতে করে যাচ্ছিলেন পথিমধ্যে রান্নার জন্য কাঠের প্রয়োজন হলো। তখন নবকুমারকে কাঠ সংগ্রহের জন্য একটা দ্বীপে নামিয়ে দেওয়া হল। দিন গড়িয়ে সন্ধ্যা নামলো, নদীতে জোয়ার এল, কিন্তু নবকুমার আর ফিরে এল না। তখন তার সঙ্গীরা মনস্থীর করলেন, কতক্ষণ আর অপেক্ষা করবো? তখন নবকুমারকে রেখে তার সঙ্গীরা চলে গেলেন। নবকুমারের ভাগ্যে আসলে কি ঘটেছিল আমরা কিন্তু জানিনা। তাই সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্রোপাধ্যয় বলেছেন ‘নবকুমারের কাষ্ঠ হরণের বিপর্যয় দেখিয়া যদি কেহ পর উপকারে ব্রতী না হন তাহলে তিনি মহা ভুল করবেন’।
অর্থাৎ ভালো কাজে প্রতিবন্ধকতা আসতে পারে কিন্তু আপনার যদি নিয়ত ঠিক থাকে, ধৈর্য্য, সাহস ও নিষ্ঠা থাকে তবে সফলতা আসতে বাধ্য।’
লেখক: সরকারের সাবেক সচিব, এন বি আরের প্রাক্তন চেয়ারম্যান।

এই মুহূর্তে সবার মনে, একটি প্রশ্ন শেষ পর্যন্ত কী ঘটতে চলেছে দেশে? চরম এক অনিশ্চয়তা গ্রাস করেছে বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে। দারুণ হতাশা, পারস্পরিক অশ্রদ্ধা, অবিশ্বাস, বিদ্বেষ, নানা ধরনের ষড়যন্ত্রের আলামত লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ঐতিহাসিক জুলাই গণঅভ্যুত্থানে স্বৈরাচারী দুঃশাসনের অবসান ঘটিয়ে সবার সর্বসম্মতিক্রমে ও সমঝোতার ভিত্তিতে একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বাংলাদেশের একমাত্র নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস এর নেতৃত্বে। আমরা আশাবাদী হয়েছিলাম, এবার বাংলাদেশ সত্যিকারের গণতন্ত্রের পথে এগিয়ে যাবে। দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশের নির্বাচনী ব্যবস্থা নিয়ে যে বিশৃঙ্খলা অরাজকতা অনিয়ম চলছিল তা কাটিয়ে এবার একটি অবাধ সুষ্ঠু নিরপেক্ষ শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের মাধ্যমে নতুন গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হবে দেশে, তেমন আশায় বুক বাঁধলেও এখন যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে তাতে সবকিছু তছনছ হয়ে যাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে। চব্বিশের ঐতিহাসিক গণ অভ্যুত্থান স্বৈরাচারী স্বেচ্ছাচারি শেখ হাসিনার দুঃশাসন হটাতে দেশের বিভিন্ন শ্রণিপেশার মানুষ ছাত্র জনতা, গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক শক্তি কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে রাজপথে নেমে এসেছিল। অগ্নিঝরা ৩৬ দিনের আন্দোলনে সামিল দেশের মানুষের সামনে টিকতে না পেরে স্বৈরাচারী শাসক শেখ হাসিনা দেশ ছেড়ে পালিয়েছিল। সেটা ছিল বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে এক অসাধারণ অধ্যায়ের সূচনা। গোটা বিশ্বে চমক সৃষ্টি করেছিল লৌহ মানবী হিসেবে কুখ্যাত স্বৈরাচারী শাসক শেখ হাসিনার ভয়ানক পতন। দেশে ভয়ংকর একটা পরিস্থিতি বিরাজ করছে। বলতে হয়, সর্বাঙ্গে ব্যথা ওষুধ দিব কোথা? দেশের এক জায়গায় মলম লাগাবেন আরেক জায়গায় ফোড়া বের হবে। টোটকা-ফোটকায় কাজ হবে না। একটা সামাজিক বিপ্লব আজকে ফরজ হয়ে গেছে। কেউ জনগণের স্বার্থ রক্ষা করে না, আমরা আমজনতা ঠকি। কেন ঠকি? জমি বর্গা দেওয়া যায়, স্বার্থ বর্গা দেওয়া যায় না।যারা এতদিন দেশ চালিয়েছে, লুটপাটতন্ত্র কায়েম হয়েছে। লুটপাটের রাজত্ব বহাল রাখার জন্য মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ করেছে। এমনকি ভোটাধিকার পর্যন্ত হরণ করেছে। বাংলাদেশের রাজনীতির আকাশে এক দুর্যোগের ঘনঘটা। একটা গভীর সংকটের মধ্যে বাংলাদেশ নিপতিত হচ্ছে। একটা গভীর খাদের কিনারে এসে বাংলাদেশ এখন উপনীত হয়েছে। ঐকমত্য কমিশনের সুপারিশে যে কিছু অসংগতি রয়েছে, এটা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। জুলাই সনদে রাজনৈতিক দলগুলোর ভিন্নমতের কথা উল্লেখ ছিল। বলা হয়েছিল, সব রাজনৈতিক দল এই ভিন্নমতগুলো নির্বাচনী ইশতেহারে উল্লেখ করে জনগণের সম্মতি গ্রহণ করবে এবং সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নেবে। কিন্তু ঐকমত্য কমিশনের গণভোটের প্রস্তাবে এই ভিন্নমতগুলো রাখা হয়নি। আরেকটি বড় অসংগতি হলো সংবিধান সংস্কারের জন্য ২৭০ দিনের বাধ্যবাধকতা আরোপ করা। ২৭০ দিন পেরিয়ে গেলে সংস্কার প্রস্তাব কেন স্বয়ংক্রিয়ভাবে সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত হবে? তাহলে সংসদে আলাপ-আলোচনা, তর্কবিতর্কের কী মূল্য থাকল? ভুলে গেলে চলবে না, একটা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সংবিধান সংস্কারের বৈধতা আসে আলাপ-আলোচনা ও পারস্পরিক বোঝাপড়ার মাধ্যমে পাওয়া নৈতিক সম্মতি থেকে, কোনো সময়সীমার বাধ্যবাধকতা থেকে নয়। যে বিষয়টি সবার মনে রাখা দরকার, তা হলো জোর করে বা চালাকি করে কোনো সংস্কার চাপিয়ে দেওয়া যায় না। সে রকম হলে সংস্কার টেকসই হবে না। এর আগে বিভিন্ন সময়ে এ রকম চেষ্টা দেখা গেছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা ব্যর্থই হয়েছে। সংস্কারপ্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত সব পক্ষ, অর্থাৎ অন্তর্বর্তী সরকার, ঐকমত্য কমিশন ও রাজনৈতিক দলগুলোকে এ বিষয়গুলো বিবেচনায় রাখার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করছি। বাংলাদেশের রাজনীতিতে ‘জুলাই সনদ’ ও ঐকমত্য কমিশনের সংবিধান সংস্কার-সংক্রান্ত সুপারিশগুলো নিয়ে ব্যাপক আলাপ-আলোচনা চলছে। এক কথায় বলা যায়, সব মহলে এ বিষয়ে আলোচনার ঝড় উঠেছে। এটি নিছক কোনো রাজনৈতিক বিতর্ক নয়। এটি রাষ্ট্র পরিচালনার দিকনির্দেশনা, ক্ষমতার ভারসাম্য এবং গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ নিয়ে এক গভীর চিন্তার প্রতিফলন। এ বিষয়ের সঙ্গে অনেক কিছু জড়িত। কমিশনের প্রস্তাবগুলো একদিকে রাজনৈতিক সংস্কারের সাহসী পদক্ষেপ, অন্যদিকে এগুলোর বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় রয়েছে নানা জটিলতা, দ্বন্দ্ব ও আশঙ্কা।
বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস বারবার দেখিয়েছে যে, কোনো সংস্কার তখনই টেকসই হয় যখন তা রাজনৈতিক ঐকমত্য ও জনগণের অংশগ্রহণের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। ১৯৯১ সালের ১২তম সংশোধনী তার এক উজ্জ্বল উদাহরণ- যেখানে শাসনব্যবস্থার রূপান্তর হয়েছিল সংসদীয় ঐকমত্যের মধ্যদিয়ে। কিন্তু আজকের প্রেক্ষাপটে দেখা যাচ্ছে, দলীয় বিভাজন এত গভীর যে, ‘ঐকমত্য’ শব্দটাই অনেকের কাছে সন্দেহজনক হয়ে উঠেছে। তাই কমিশনের প্রস্তাব কেবল সংবিধান সংস্কার নয়, বরং আস্থা পুনর্গঠনেরও একটি সুযোগ। অবশ্য এ কথাও অস্বীকার করা যায় না যে, বাংলাদেশের জনগণ এখন প্রশাসনিক স্বচ্ছতা, বিচার বিভাগের জবাবদিহি ও সেবা প্রদানে কার্যকারিতা চায়। কমিশনের সুপারিশে এসব বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকায় এটি নিঃসন্দেহে নাগরিক প্রত্যাশার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। যদি এ সুপারিশগুলো বাস্তবায়িত হয়, তবে প্রশাসনিক দক্ষতা বাড়বে, বিচারব্যবস্থায় গতি আসবে এবং রাষ্ট্রের সেবাদান প্রক্রিয়া আরও ডিজিটাল হবে। রাজনৈতিক সংস্কার ছাড়া এসব কাঠামোগত পরিবর্তন কেবল উপসর্গ নিরাময়ের সমাধান- মূল রোগ থেকে মুক্তি নয়। ঐকমত্য কমিশনের সুপারিশকে ঘিরে যে বিতর্ক চলছে, তা বাংলাদেশের গণতন্ত্রের বিকাশের জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা। একদিকে আছে সংস্কারের আশাবাদ, অন্যদিকে রয়েছে আস্থার সংকট। এ দুই মেরুর মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করাই এখন সময়ের দাবি।একদিকে জাতীয় ঐকমত্য কমিশন সরকারের কাছে জুলাই সনদ বাস্তবায়নের আইনি ভিত্তি দেওয়ার লক্ষ্যে যে সুপারিশমালা সরকারের কাছে পেশ করেছে, তা নিয়ে রাজনীতির মাঠ বেশ গরম। বিএনপিসহ বেশ কিছু দল একে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ ও তামাশা বলেও অভিহিত করেছে। আবার কেউ কেউ স্বাগতও জানিয়েছে। রাজনৈতিক দলগুলোর পরস্পরবিরোধী অবস্থান নিয়ে অনেকেই প্রশ্ন করেছেন, জুলাই সনদ ও আইনি ভিত্তি নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলো একমত না হতে পারলে নির্বাচন হবে কীভাবে? রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে তিনটি বলয় তৈরি হয়েছে। একটি বলয় হলো বিএনপি ও তাদের সমর্থক-অনুসারী দল। আরেকটি হলো জামায়াতে ইসলামী ও এর অনুসারী দল। তৃতীয়টি হলো জাতীয় নাগরিক পার্টি। আবার কোনো কোনো দল দুই নৌকায় পা দিয়ে রেখেছে। যেখানে গিয়ে ভোটের মাঠে সুবিধা করা যাবে, শেষ পর্যন্ত তাদের সঙ্গে যাবে। মাঠে সক্রিয় থাকা ৩০টি রাজনৈতিক দলকে নিয়েই সরকার তথা জাতীয় ঐকমত্য কমিশন দীর্ঘ আট মাস ধরে আলোচনা করে ৮৪টি বিষয়ে ঐকমত্যে পৌঁছেছে। এর মধ্যে ৪৮টি বিষয় যেহেতু সংবিধানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, সেহেতু এগুলোর আইনি ভিত্তি তৈরির জন্য জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের পক্ষ থেকে কিছু সুপারিশ করা হয়েছে, যা নিয়ে আবার মতভেদ দেখা দিয়েছে। যদিও সনদ তৈরির সময় বলা হয়েছিল, তারা আইনি ভিত্তির সুপারিশ করবে না। কিন্তু অসমাপ্ত সনদ করতে গিয়ে জাতীয় ঐকমত্য কমিশন আরও জট পাকিয়ে ফেলেছে। যেসব বিষয়ে রাজনৈতিক পক্ষগুলোর মধ্যে মতবিরোধ তীব্র, তার একটি হলো গণভোটের তারিখ। জামায়াতে ইসলামী ও তাদের অনুসারীরা বলছে, নভেম্বরেই গণভোট হতে হবে। অন্যদিকে বিএনপি ও তাদের অনুসারীদের দাবি, সংসদ নির্বাচনের আগে গণভোট হতে পারবে না। তারা মনে করেন, আগে গণভোটের দাবি তোলা নির্বাচনকে পিছিয়ে দেওয়ার দুরভিসন্ধি ছাড়া কিছু নয়। জাতীয় ঐকমত্য কমিশন অবশ্য দুই বিকল্প প্রস্তাবই সরকারের কাছে পেশ করেছে। সমস্যা হলো যিনি সরকারপ্রধান, তিনি ঐকমত্য কমিশনেরও প্রধান। স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন আসে কে কার কাছে প্রস্তাব পেশ করেছেন। দ্বিতীয়ত, জুলাই সনদে ঐকমত্যের পাশাপাশি রাজনৈতিক দলের আপত্তিগুলো লিপিবদ্ধ হলেও আইনি ভিত্তির সুপারিশে বাদ দেওয়া হয়েছে। বিএনপি ও তাদের অনুসারীদের প্রধান আপত্তি এখানেই। জুলাই সনদে বলা হয়েছে, যেসব বিষয় রাজনৈতিক দলগুলো আপত্তি জানিয়েছে, নির্বাচনে তারা জনগণের রায় পেলে সেটি বাস্তবায়ন করতে বাধ্য নয়। কিন্তু আইনি ভিত্তিতে যখন সেটি বাদ দেওয়া হয়েছে এবং সংসদ নির্বাচনের আগে গণভোটের মাধ্যমে সেটি অনুমোদন করে নিলে সংসদের সার্বভৌমত্ব নষ্ট হবে। তাদের তৃতীয় আপত্তির জায়গা হলো স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে আইনি ভিত্তি অনুমোদিত হয়ে যাওয়া। জাতীয় ঐকমত্য কমিশন বলেছে, যদি ৯ মাসের মধ্যে জাতীয় সংসদ উল্লিখিত বিষয়ে আইন পাস না করে, তাহলে সেটা স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে অনুমোদিত হয়ে যাবে। ঐকমত্য কমিশনের এই আইনি ভিত্তির সঙ্গে ১৯৭০ সালে ইয়াহিয়া খান প্রণীত এলএফওর মিল খুঁজেও পেয়েছেন কোনো কোনো বিশ্লেষক।সিদ্ধান্তটি কবে হবে, কেমন হবে? যদি একই দিনে দুই ভোট করার পক্ষে সরকার সিদ্ধান্ত নেয়, তাহলে জামায়াত ও এনসিপি কি মেনে নেবে? আর যদি সংসদ নির্বাচনের আগে গণভোট হয়, বিএনপি কি তা গ্রহণ করবে? যদি না করে, কী পরিস্থিতি তৈরি হবে? রাজনৈতিক দলগুলোকে জুলাই সনদের পক্ষে এনে সরকার যতটুকু বাহবা পেয়েছিল, তার বেশি সমালোচিত হয়েছে আইনি ভিত্তি দিতে গিয়ে। এখানে কোনটি ন্যায্য, কোনটি অন্যায্য; তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হলো তারা রাজনৈতিক দলগুলোকে একমতে আনতে ব্যর্থ হয়েছে। রাজনৈতিক দলগুলো যেমন একে অপরকে বিশ্বাস করবে না, তেমনি তাদের বড় অংশ সরকারের প্রতিও আস্থাশীল নয়। নির্বাচনের বিষয়ে শুরু থেকে সরকারের দ্বিধাদ্বন্দ্ব রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে যেমন সন্দেহ বাড়িয়েছে, তেমনি সরকারের প্রতিও এক ধরনের অনাস্থা সৃষ্টি করেছে। জুলাই জাতীয় সনদ ও তা বাস্তবায়নের সুপারিশ নিয়ে যে বিতর্ক তৈরি হয়েছে, তার অবসান ঘটিয়ে সংসদ নির্বাচন আয়োজনের দিকে মনোযোগী হতে হবে অন্তর্বর্তী সরকারকে। যা হওয়ার হয়েছে। ওই সমস্যাগুলো সমাধান করে যাতে সবাই একসঙ্গে আমরা নির্বাচনের দিকে যেতে পারি, এই সমস্যার সমাধান করে আমরা জনগণের কল্যাণের জন্য কাজ করতে পারি, সেই পথে এগিয়ে যেতে হবে।
আজকে যে সংকট তৈরি করেছে এই অন্তর্বর্তী সরকার ও ঐকমত্য কমিশন। আমরা বিশ্বাস করি যে এই সংকট কেটে যাবে। এই দেশের মানুষ কখনো পরাজিত হয় না। পরাজয় বরণ করেনি, পরাজয় বরণ করবে না। যেকোনো চক্রান্তকে পরাজিত করতে সব রাজনৈতিক দলের ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। আমাদের বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্র হচ্ছে, তাকে পরাজিত করতে হবে। এখানে আমরা বিভিন্ন দল করতে পারি, বিভিন্ন মত থাকতে পারে, বিভিন্ন পথ থাকতে পারে, কিন্তু একটা বিষয়ে আমরা সব সময় এক ছিলাম, বাংলাদেশের ব্যাপারে; সবার আগে বাংলাদেশ—এ ব্যাপারে আমাদের কোনো সন্দেহ নেই। রাজনৈতিক জীবনে হতাশাবাদী হলে চলবে না; কারণ, আমরা বিশ্বাস করি যে ন্যায়ের জয় হবেই, সত্যের জয় হবে। আওয়ামী লীগকে ক্ষমতা থেকে হটাতে যুগপৎ কর্মসূচিতে থাকা সব রাজনৈতিক দলের ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। আমরা যেমন অতীতে একসঙ্গে ছিলাম, সব সময় একসঙ্গে থাকব।
লেখক: অবসরপ্রাপ্ত ব্যাংকার, কলামিস্ট।

বাংলাদেশের রাষ্ট্রচিন্তার ইতিহাস মূলত একটি চলমান যাত্রা, যেখানে প্রতিটি প্রজন্ম নতুন বাস্তবতার মুখোমুখি হয়ে রাষ্ট্রকে পুনর্বিবেচনা করেছে, পুনর্গঠন করেছে। শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের ১৯ দফা কর্মসূচি এবং বিএনপি’র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের ৩১ দফা রাষ্ট্রসংস্কার প্রস্তাব, এই দুই নীতিনথি সেই যাত্রার দুই গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক।
একটি জন্ম নিয়েছিল পুনর্গঠনের অপরিহার্য প্রেক্ষাপটে; অন্যটি উদ্ভূত হয়েছে প্রশাসনিক সংস্কার ও জবাবদিহির চাহিদা থেকে।।দুটি সময়, দুটি প্রজন্ম, দুটি ভাষা; কিন্তু উদ্দেশ্য এক: রাষ্ট্রকে জনগণের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া।
স্বাধীনতার পর রাষ্ট্রগঠনের প্রেক্ষাপট ১৯৭৭ সালের বাংলাদেশ ছিল এক অনিশ্চিত ক্রান্তিকাল। মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তী অস্থিরতা, দুর্ভিক্ষ, রাজনৈতিক সংকট ও প্রশাসনিক জটিলতায় তখনো কাঁপছিল দেশ। অর্থনীতি ছিল প্রায় বিপর্যস্ত; জনগণের আস্থা হারিয়ে ফেলেছিল রাষ্ট্রযন্ত্র।
এই বাস্তবতায় রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান উপস্থাপন করেন ১৯ দফা কর্মসূচি, যা ছিল কেবল অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের নীতি নয়, বরং এক নতুন জাতীয় দর্শনের সূচনা। তার মূল বিশ্বাস; উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দু মানুষ নিজেই, রাষ্ট্র নয়।
তাই তিনি জোর দেন তিনটি মূল ভিত্তিতে:
১️. আত্মনির্ভরতা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, বিশেষ করে কৃষি ও খাদ্যে।
২️. বিকেন্দ্রীকরণ ও স্থানীয় সরকার শক্তিশালীকরণ, গ্রামীণ জনগণকে উন্নয়নের অংশীদার করা।
৩️. প্রশাসনের দক্ষতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি, রাষ্ট্রকে সেবামুখী করা।
জিয়ার জনপ্রিয় স্লোগান ‘আমরাই রাষ্ট্র, আমরাই শক্তি’ কেবল রাজনৈতিক ভাষণ নয়; এটি ছিল রাষ্ট্রদর্শনের ঘোষণা। তার নীতিতে রাষ্ট্র কোনো দূরবর্তী ক্ষমতার কেন্দ্র নয়, বরং নাগরিকের শ্রম ও অংশগ্রহণে নির্মিত এক যৌথ সত্তা।
এই দৃষ্টিভঙ্গি বাংলাদেশের উন্নয়ন চিন্তায় নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে। গ্রামীণ পুনর্গঠন, পরিবার পরিকল্পনা, খাদ্যনিরাপত্তা ও বেসরকারি উদ্যোক্তা বিকাশে এর প্রভাব আজও স্পষ্ট।
১৯ দফা কর্মসূচি তাই ছিল বেঁচে থাকা থেকে এগিয়ে চলার এক রাষ্ট্রদর্শন, যেখানে জাতীয় পুনর্জাগরণ ও আত্মনির্ভরতার বার্তা মিলেছিল একই সঙ্গে।
চল্লিশ বছর পর: রাষ্ট্রসংস্কারের আহ্বান
চার দশক পর, বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক বাস্তবতা আবারও এক নতুন মোড়ে এসে দাঁড়িয়েছে।
অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি সত্ত্বেও নাগরিক আস্থার ঘাটতি, প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা ও রাজনৈতিক মেরুকরণ; এই তিন সংকট রাষ্ট্রের কাঠামোগত পুনর্বিবেচনার দাবি তুলেছে।
এই প্রেক্ষাপটেই বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ২০২৩ সালে উপস্থাপন করেন ৩১ দফা রাষ্ট্রসংস্কার প্রস্তাব—একবিংশ শতাব্দীর নাগরিক রাষ্ট্রের আধুনিক নকশা হিসেবে।
যেখানে জিয়ার লক্ষ্য ছিল পুনর্গঠন, সেখানে তারেকের লক্ষ্য সংস্কার ও পুনঃপ্রতিষ্ঠা।
৩১ দফার মূল লক্ষ্য হলো—জবাবদিহিমূলক, বিকেন্দ্রীভূত ও নাগরিকমুখী রাষ্ট্র।
এই প্রস্তাবে গুরুত্ব পেয়েছে কয়েকটি মৌলিক দিক—নির্বাচন কমিশনের পূর্ণ স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা, বিচার বিভাগের কার্যকর স্বায়ত্তশাসন, দুর্নীতিমুক্ত, পেশাদার ও রাজনৈতিকভাবে নিরপেক্ষ প্রশাসন, সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা ও তথ্যপ্রবাহের নিশ্চয়তা, স্থানীয় সরকারের আর্থিক ক্ষমতায়ন, তরুণ ও প্রবাসী বাংলাদেশিদের রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্তি, নারীর রাজনৈতিক অংশগ্রহণে কাঠামোগত সুযোগ সৃষ্টি।
তারেক রহমান গণতন্ত্রকে কেবল ভোটের প্রক্রিয়া নয় বরং অংশগ্রহণের প্রাতিষ্ঠানিক নিশ্চয়তা হিসেবে দেখেন। তার মতে, ‘গণতন্ত্র মানে ভোট নয়—গণতন্ত্র মানে জবাবদিহি।’
এই দৃষ্টিভঙ্গিতে ৩১ দফা দাঁড় করিয়েছে এক নতুন রাষ্ট্রদর্শন, যেখানে প্রশাসনিক সংস্কৃতি, প্রযুক্তিনির্ভরতা এবং নাগরিক অধিকার একে অপরের পরিপূরক।
দুটি নীতিনথি: ধারাবাহিকতা ও রূপান্তরের সেতুবন্ধন জিয়াউর রহমানের ১৯ দফা ও তারেক রহমানের ৩১ দফা দুটি সময়ের প্রয়োজনভিত্তিক দুই রাষ্ট্রচিন্তা, কিন্তু মূল দর্শনে একীভূত। একটি বলেছিল—‘আমরা পারব’; অন্যটি বলছে—‘আমাদের বদলাতে হবে।’ ১৯ দফা যেখানে রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ভিত্তি নির্মাণ করেছে, ৩১ দফা সেখানে ন্যায়, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির কাঠামো দাঁড় করাতে চায়।
এই ধারাবাহিকতার মূল তিনটি স্তম্ভ—
১️. জনগণই রাষ্ট্রের কেন্দ্র, ২️. ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ, ৩️. প্রশাসনের জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা।
জিয়ার ১৯ দফায় ছিল ‘উন্নয়ন’; তারেকের ৩১ দফায় এসেছে ‘ন্যায় ও জবাবদিহি’— অর্থাৎ রাষ্ট্রচিন্তা ক্রমশ অর্থনৈতিক পুনর্গঠন থেকে ন্যায়ভিত্তিক শাসনে পরিণত হয়েছে। প্রথমটি বাঁচার ভিত্তি দিয়েছে, দ্বিতীয়টি দিয়েছে মর্যাদার নিশ্চয়তা।
এই রূপান্তরই প্রমাণ করে, বাংলাদেশের রাষ্ট্রচিন্তা কেবল রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতির ধারায় নয়, বরং সময়ের দাবি অনুযায়ী এক বিবর্তনশীল দর্শন। জিয়া রাষ্ট্রকে মানুষের কাছে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন; তারেক রাষ্ট্রকে মানুষের মধ্যে ন্যায় ও জবাবদিহির কাঠামোয় পুনর্গঠন করতে চান।
রাষ্ট্রচিন্তার পরিবর্তিত ধারা: উন্নয়ন থেকে ন্যায়বিচারে বাংলাদেশের রাজনৈতিক চিন্তায় প্রজন্মভেদে পরিবর্তন এসেছে দাবির প্রকৃতিতে। প্রথম প্রজন্মের দাবি ছিল—খাদ্য, বস্ত্র, আশ্রয় ও কর্মসংস্থান। দ্বিতীয় প্রজন্মের দাবি—ন্যায্য সুযোগ, প্রশাসনিক স্বচ্ছতা ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা।
এই পরিবর্তনকে রাষ্ট্রচিন্তার প্রগতিশীল ধারা বলা যায়, যেখানে বেঁচে থাকার রাজনীতি থেকে বেরিয়ে এসেছে মর্যাদা ও ন্যায়ের রাজনীতি। ১৯ দফার ‘উৎপাদনমুখী সমাজ’ আজ পরিণত হয়েছে ৩১ দফার ‘জবাবদিহিমূলক রাষ্ট্রে’। এটি কেবল রাজনৈতিক দলের বিবর্তন নয়, বরং বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক চেতনার পরিণত রূপ।
দলীয় সীমানা পেরিয়ে রাষ্ট্রদর্শন
যদিও এই দুই নীতিনথি বিএনপির রাজনৈতিক ইতিহাসের অংশ, তবু এগুলোকে কেবল দলীয় ইশতেহার হিসেবে দেখা ভুল হবে। ১৯ দফা যেমন স্বাধীনতার পর পুরো জাতিকে আত্মনির্ভরতার বার্তা দিয়েছিল, ৩১ দফাও তেমনি নতুন প্রজন্মকে দিচ্ছে অংশগ্রহণমূলক গণতন্ত্রের দিকনির্দেশ। রাষ্ট্রচিন্তার এই যাত্রা দলীয় গণ্ডি পেরিয়ে এক জাতীয় প্রয়াস, যেখানে রাষ্ট্রযন্ত্রকে জনগণের সেবক হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার অঙ্গীকারই চূড়ান্ত লক্ষ্য।
এই দৃষ্টিতে, দুই দফার সংযোগরেখা দাঁড়ায় তিনটি মূল প্রতিশ্রুতিতে—
১️. আস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠা, ২️. প্রশাসনিক সংস্কার, ৩️. রাজনৈতিক
এই তিন স্তম্ভই রাষ্ট্রকে মানুষের কাছে ফিরিয়ে আনার প্রকৃত মাধ্যম।
উপসংহার: অংশগ্রহণমূলক ও ন্যায়ের রাষ্ট্রের পথে আজকের বিশ্বে উন্নয়ন আর কেবল অবকাঠামো নয়, এটি মানুষের মর্যাদা ও অংশগ্রহণের সমন্বিত প্রক্রিয়া। বাংলাদেশও এখন সেই পথে হাঁটছে। রাষ্ট্র যদি ন্যায়হীন হয়, উন্নয়ন স্থায়ী হয় না; আর গণতন্ত্র যদি দুর্বল হয়, উন্নয়নও অনিরাপদ হয়ে পড়ে।
এই বাস্তবতায় শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের ১৯ দফা ও তারেক রহমানের ৩১ দফা, উভয়ই একে অপরের পরিপূরক ঐতিহাসিক দলিল। একটি রাষ্ট্রের ভিত্তি গড়েছে, অন্যটি সেই রাষ্ট্রের আধুনিক কাঠামো রচনা করছে। ১৯ দফা আমাদের শিখিয়েছে আত্মনির্ভরতা; ৩১ দফা শেখাচ্ছে স্বচ্ছতা, ন্যায় ও জবাবদিহি। রাষ্ট্রচিন্তার এই ধারাবাহিকতা আসলে একটি অবিরাম যাত্রা, মানুষকেন্দ্রিক রাষ্ট্র থেকে ন্যায়কেন্দ্রিক রাষ্ট্রের দিকে।
শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান বলেছিলেন—‘রাষ্ট্র হবে জনগণের, রাষ্ট্র হবে অংশগ্রহণের।’ আজ তারেক রহমান সেই দর্শনকে আধুনিক প্রজন্মের ভাষায় পুনর্লিখছেন—‘রাষ্ট্র হবে ন্যায়, স্বচ্ছতা ও জনগণের জবাবদিহির প্রতিষ্ঠান।’ এই সেতুবন্ধনই বাংলাদেশের রাষ্ট্রচিন্তার ধারাবাহিকতার প্রকৃত রূপান্তর।
লেখক: এ কে এম মাজহারুল ইসলাম খান, কবি ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক।
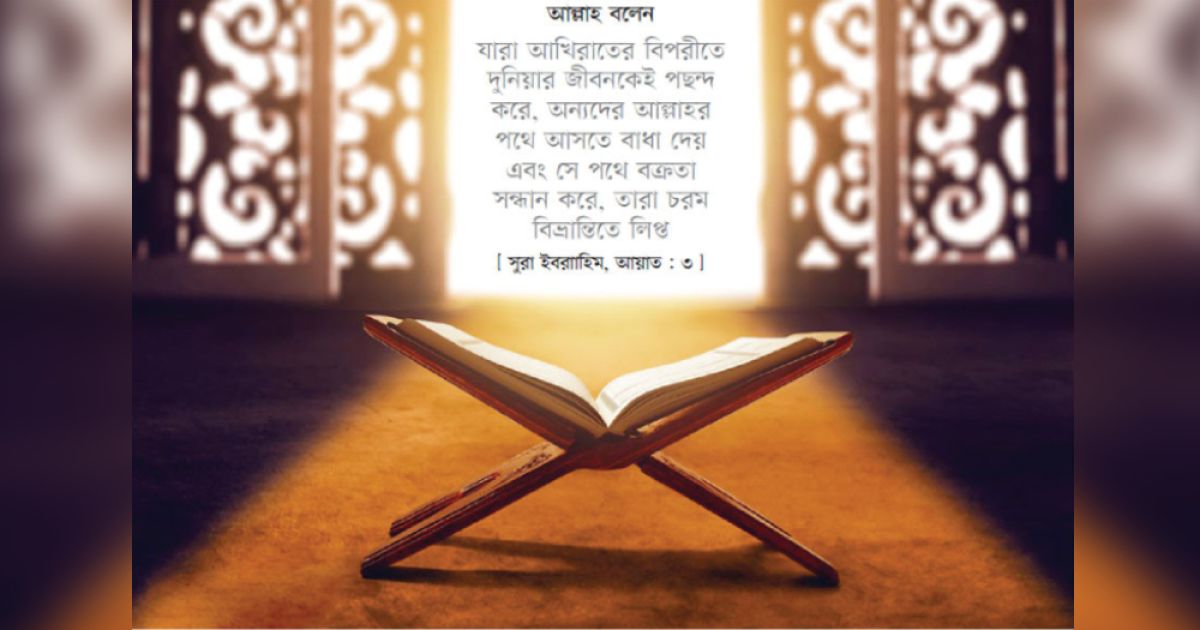
সমস্ত নিখুঁত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি সকল সৃষ্টির প্রতিপালক, এবং তার শেষ রাসূল মুহাম্মদ (সা.) এর উপর চিরস্থায়ী শান্তি ও আশীর্বাদ বর্ষিত হোক, যার আদর্শ জীবন সকল মানুষের জন্য চিরস্থায়ী পথপ্রদর্শক হিসেবে কাজ করে। ইসলামের প্রদত্ত বিশাল দিকনির্দেশনাকে সত্যিকার অর্থে বোঝার জন্য, একজনকে ঐশ্বরিক ন্যায়বিচার এবং করুণার উপর ভিত্তি করে এর আন্তঃসংযুক্ত শিক্ষাগুলি গভীরভাবে অনুসন্ধান করতে হবে। এই যাত্রা শুরু হয় ইসলামী ন্যায়বিচার আধুনিক সম্প্রদায়গুলিকে কীভাবে গঠন করে তা অন্বেষণ করে, যা বাণিজ্য ও বাণিজ্য পরিচালনাকারী নৈতিক ভিত্তির সাথে সহজাতভাবে সংযুক্ত যা সমস্ত লেনদেনে ধার্মিকতাকে উৎসাহিত করে। ব্যক্তিগত জীবনে, বিবাহবিচ্ছেদ এবং পারিবারিক বিষয়গুলিকে ঘিরে থাকা নিয়মগুলি মানবিক মর্যাদা বজায় রাখার জন্য ডিজাইন করা একটি কাঠামো তৈরি করে, যখন বিবাহিত অংশীদারদের সুষম অধিকার এবং কর্তব্যগুলি সুরেলা ঘর স্থাপন করে। তদুপরি, উত্তরাধিকারের বিস্তারিত ইসলামী আইন অর্থনৈতিক ন্যায্যতা নিশ্চিত করে এবং ইসলামে নারীর সম্মানিত অবস্থান সমাজে তাদের ঐশ্বরিকভাবে নির্ধারিত অধিকার এবং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা উদযাপন করে। এই ব্যাপক শিক্ষাগুলি কোরআন ও নবীর রহমতের অপরিহার্য বিষয় থেকে প্রবাহিত হয়, যা একজন মুসলিমের আধ্যাত্মিক বিকাশ এবং ব্যক্তিগত পরিশুদ্ধিকে অনুপ্রাণিত করে। মানবজাতির জন্য নিখুঁত দিকনির্দেশনা প্রদানকারী এই সম্পূর্ণ জীবনধারা এই নিশ্চিততার পরিণামে পৌঁছে যে কোনও নবী মুহাম্মদ (সা.) কে অনুসরণ করবেন না, যা আন্তরিক বিশ্বাসীদের জন্য আল্লাহর বার্তার পরিপূর্ণতা নিশ্চিত করে।
এই মৌলিক সচেতনতা অনিবার্যভাবে আমাদের ব্যক্তিগত জবাবদিহিতার দিকে পরিচালিত করে: দৈনন্দিন কর্মকাণ্ডে বিশ্বাসকে একীভূত করা। রমজানের আধ্যাত্মিকভাবে উন্নত দিনগুলিতে, যখন বিশ্বব্যাপী মুসলমানরা তাদের ইবাদতকে তীব্র করে তোলে, তখন একটি গুরুত্বপূর্ণ নৈতিক প্রশ্ন উঠে আসে: উচ্চ চাহিদাকে কাজে লাগিয়ে, তারপর সেই অতিরিক্ত মুনাফাকে ওমরাহর মতো পবিত্র কাজ সম্পাদনের জন্য ব্যবহার করে কি কেউ প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের নাটকীয়ভাবে দাম বৃদ্ধিকে ন্যায্যতা দিতে পারে? এই আন্তরিক অনুসন্ধান ইসলামী জীবনযাত্রার মূলকে স্পর্শ করে - যেখানে ধর্মীয় পালন এবং দৈনন্দিন নীতিমালাকে নির্বিঘ্নে একত্রিত করতে হবে। বিনীত শ্রদ্ধার সাথে, আমরা ধর্মীয় বিধান জারি করার জন্য নয় বরং আমাদের জীবন পরিচালনাকারী নীতিগুলি সম্পর্কে চিন্তাশীল আলোচনা প্রচার করার জন্য এই জাতীয় নৈতিক চ্যালেঞ্জগুলি নিয়ে চিন্তা করতে পারি।পবিত্র কোরআন এবং সহীহ আল-বুখারীর মতো সংগ্রহে পাওয়া নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর কঠোরভাবে প্রমাণিত অনুশীলন থেকে প্রাপ্ত ইসলামী শিক্ষাগুলি একটি সম্পূর্ণ জীবন পরিকল্পনা উপস্থাপন করে। এই ঐশ্বরিক নীলনকশা বাণিজ্যিক কেন্দ্র থেকে শুরু করে পারিবারিক বসার ঘর পর্যন্ত সকল ক্ষেত্রে ন্যায্যতা, সহানুভূতি এবং সততার পক্ষে কথা বলে, যা আমাদের খাঁটি শান্তি এবং নীতিগতভাবে বিশুদ্ধ রিযিকের দিকে পরিচালিত করে। গবেষণার জন্য, আমি দেখেছি যে কিছু ব্যক্তি অবৈধভাবে অর্থ উপার্জন করে কিন্তু কোনও আগ্রহ ছাড়াই তা দান করে। কিছু শিক্ষক তাদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করেন না বরং সর্বদা মহান ব্যক্তির মতো আচরণ করেন। অন্যান্য পেশায়ও আমি একই রকম ঘটনা পেয়েছি। বাণিজ্যে সততার পবিত্রতা সম্পর্কে চিন্তা করলে দেখা যায় যে, বিশেষ করে রমজানের মতো পবিত্র মাসে শোষণমূলক মূল্য নির্ধারণ কীভাবে বস্তুগত লাভ এবং আধ্যাত্মিক পবিত্রতার মধ্যে সরাসরি উত্তেজনা তৈরি করে। ইসলামী আইনশাস্ত্র, ফিকহ, ন্যায়সঙ্গত বাণিজ্যকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়। ইহতিকারের অনুশীলন, খরচ বাড়ানোর জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র মজুদ করা, নবীর শিক্ষায় স্পষ্ট নিন্দা করা হয়েছে। তীব্র ইবাদতের সময় সম্প্রদায়ের চাহিদাগুলিকে কাজে লাগানো সম্ভাব্য দানশীলতাকে স্পষ্ট অবিচারে পরিণত করে। এই ধরনের শোষণের মাধ্যমে সঞ্চিত সম্পদ, এমনকি যদি পরে তীর্থযাত্রার মতো পুণ্যের উদ্দেশে ব্যয় করা হয়, তবে তা একটি অনৈতিক ভিত্তি থেকে উদ্ভূত হয়। কিছু সংবাদপত্রে আমরা দেখতে পাই যে কীভাবে তরুণ প্রজন্মের একটি অংশ একে অপরের সাথে মিশে যাচ্ছে, নৈতিকতা হ্রাস পাচ্ছে। ইসলামী পণ্ডিতরা বিজ্ঞতার সাথে মনে করেন যে আল্লাহ স্বর্গীয়ভাবে পবিত্র এবং তিনি কেবল পবিত্র জিনিসই গ্রহণ করেন। ঐশ্বরিক গ্রহণযোগ্যতা অর্জনের জন্য যে কোনও নিষ্ঠার কাজকে হালাল বিশ্বাসের এই নীতি ব্যবসা-বাণিজ্যের বাইরেও বিস্তৃতভাবে প্রযোজ্য। কল্পনা করুন যে পরিবারগুলি তাদের সম্পূর্ণ সঞ্চয় একটি বাড়িতে বিনিয়োগ করে, কিন্তু নির্মাতার কাছ থেকে সীমাহীন স্থগিতাদেশের সম্মুখীন হয়। ইসলামে, একটি ব্যবসায়িক চুক্তি (‘আকদ) আইনি কাগজপত্রের বাইরে; এটি একটি পবিত্র অঙ্গীকারের প্রতিনিধিত্ব করে। অর্থ গ্রহণকারী একজন ডেভেলপার অর্থ এবং পরিবারের আকাঙ্ক্ষা উভয়ের জন্যই একজন ট্রাস্টি (আমীন) এর ভূমিকা গ্রহণ করে। বৈধ যুক্তি ছাড়া সম্পত্তি প্রত্যাখ্যান করা এই পবিত্র দায়িত্ব (আমানত) ভঙ্গ করে। কুরআন দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করে, ‘হে ঈমানদারগণ, তোমাদের চুক্তি পূরণ করো’ (কোরআন, ৫:১)। ইসলাম বিজ্ঞতার সাথে সমাধানের পদক্ষেপগুলিও রূপরেখা দেয়: সৌজন্যমূলক যোগাযোগের মাধ্যমে শুরু করা, সম্প্রদায়ের নেতাদের বা ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মতো সংস্থার সাথে সালিশের দিকে অগ্রসর হওয়া এবং অবশেষে ন্যায়বিচার পুনরুদ্ধারের জন্য প্রয়োজনে আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করা। (বৈধ) উপায়ে সমর্থন করা আবশ্যক। অন্যদের শোষণ করে অর্থায়ন করা তীর্থযাত্রার আধ্যাত্মিক মূল্য সহজাতভাবে হ্রাস পায়, কারণ এর আর্থিক উৎস যাত্রার পবিত্র উদ্দেশের সাথে সাংঘর্ষিক। এই নৈতিক ব্যবস্থা দুর্নীতির ক্ষতি প্রতিরোধ পর্যন্ত বিস্তৃত, কারণ ইসলামী মতবাদে ঘুষ (রিশওয়া) স্পষ্টভাবে নিন্দিত। এটি একটি গুরুতর পাপ যা সামাজিক ভিত্তিকে দুর্বল করে দেয়। নবী (সা.) ঘুষদাতা এবং গ্রহীতা উভয়কেই নিন্দা করেছেন। যখন সরকারি কর্মচারীরা এই ধরনের কাজে অংশগ্রহণ করে বা উপেক্ষা করে, তখন তারা স্বর্গীয় আইন লঙ্ঘন করে এবং পদ্ধতিগত অন্যায়কে স্থায়ী করে। ‘অন্যরা এটা করে’ দাবি করা আল্লাহর চূড়ান্ত বিচারের সামনে কোনও যুক্তি দেয় না। দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই ব্যক্তিগত নৈতিক সাহস, অসৎ অনুশীলনে জড়িত হওয়া প্রত্যাখ্যান এবং সম্মিলিত সামাজিক দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে শুরু হয়। এই নৈতিক অবস্থান সুদভিত্তিক ব্যবস্থার মতো আর্থিক পদ্ধতিগুলিকেও প্রশ্নবিদ্ধ করে, যা ইসলামে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। ইসলামী আইনের সাথে তাদের বিরোধ জানা সত্ত্বেও, ইচ্ছাকৃতভাবে এই ধরণের ব্যবস্থায় জড়িত হওয়া বা সমর্থন করা, আন্তরিক অনুতাপ এবং শরিয়া-অনুমোদিত বিকল্পগুলির দিকে দৃঢ় পরিবর্তনের দাবি করে, আমাদের সম্পদকে পবিত্র করে এবং একটি শান্তিপূর্ণ সমাজের জন্য আমাদের অর্থনীতিকে ঐশ্বরিক ইচ্ছার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে। ইসলামের সুচিন্তিতভাবে পরিকল্পিত পারিবারিক দৃষ্টিভঙ্গিতে, প্রতিটি সম্পর্ক পারস্পরিক শ্রদ্ধা, সহানুভূতি এবং বাধ্যবাধকতা অনুসরণ করে। পুত্রবধূ - একজন পুত্রের স্ত্রী - তার স্বামীর পিতামাতার প্রতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যা নীতিগত দৃষ্টিকোণ থেকে সবচেয়ে ভালোভাবে বোঝা যায় যা স্বেচ্ছায় দানশীলতার উচ্চতর আধ্যাত্মিক মূল্যের সাথে আইনি কর্তব্যের সামঞ্জস্যপূর্ণ। আইনত, পিতামাতার জন্য আর্থিক এবং শারীরিক সহায়তা প্রদান তাদের নিজস্ব সন্তানদের, বিশেষ করে পুত্রদের কর্তব্য। অতএব, একজন পুত্র তার পিতামাতার চাহিদার জন্য আইনি দায়িত্ব বহন করে, যেখানে তার স্ত্রী তার স্বামী এবং সন্তানদের জন্য তার শ্বশুরবাড়ির প্রতি সমতুল্য কোনও বাধ্যবাধকতা রাখে না। এই পার্থক্যটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ ইসলাম কখনই পুত্রবধূর উপর দাসত্ব চাপিয়ে দেয় না; পরিবর্তে, এটি তাকে শ্বশুরবাড়ির সাথে তার সম্পর্ককে মৌলিক কর্তব্য থেকে মহান আধ্যাত্মিক আশীর্বাদ এবং বিশ্বাসভিত্তিক বিকাশের জন্য একটি মাধ্যম হিসাবে উন্নীত করতে অনুপ্রাণিত করে।যদিও ইসলামী আইন পুত্রবধূকে তার স্বামীর বাবা-মায়ের প্রতি আইনত দায়বদ্ধ করে না, তবুও ধর্ম তাকে পরম শ্রদ্ধা, দয়া এবং সহানুভূতির উপর ভিত্তি করে সম্পর্ক গড়ে তুলতে উৎসাহিত করে। তার অবস্থান বাধ্যতামূলক পরিচারিকার নয়, বরং বৃহত্তর পরিবারের একজন সহানুভূতিশীল, অপরিহার্য অংশের, যার স্বেচ্ছাসেবী কর্মকাণ্ড একটি স্থিতিস্থাপক, সহায়ক এবং স্নেহপূর্ণ মুসলিম সমাজের কাঠামোকে শক্তিশালী করে। তিনি তার শ্বশুরবাড়ির প্রতি যে দয়া প্রদর্শন করেন তা সামাজিক কর্তব্যের চেয়েও বেশি; এটি একটি গভীর আধ্যাত্মিক কাজ যা পারিবারিক সংযোগকে শক্তিশালী করে, তার স্বামীকে আনন্দিত করে এবং আল্লাহর কাছ থেকে মহান পুরষ্কারের এক অবিরাম ঝর্ণা হিসেবে কাজ করে, যা ইসলামী বিশ্বাসের কেন্দ্রবিন্দুতে গভীর করুণা এবং বুদ্ধিমত্তা প্রদর্শন করে। ব্যবসা, জনসেবা বা পারিবারিক জীবনে আমরা যে পরীক্ষার মুখোমুখি হই - সেগুলি আমাদের বিশ্বাসকে শক্তিশালী করার এবং ইসলাম যে শান্তি ও প্রশান্তি প্রদান করে তা মূর্ত করার সুযোগকে প্রতিনিধিত্ব করে। উত্তরটি বিরক্তি থেকে নয়, বরং আমাদের আধ্যাত্মিক ও নৈতিকভিত্তির সাথে আন্তরিক পুনঃসংযোগ থেকে উদ্ভূত হয়। দিও ইসলামী আইন পুত্রবধূকে তার স্বামীর বাবা-মায়ের প্রতি আইনত দায়বদ্ধ করে না, তবুও ধর্ম তাকে পরম শ্রদ্ধা, দয়া এবং সহানুভূতির উপর ভিত্তি করে সম্পর্ক গড়ে তুলতে উৎসাহিত করে। তার অবস্থান বাধ্যতামূলক পরিচারিকার নয়, বরং বৃহত্তর পরিবারের একজন সহানুভূতিশীল, অপরিহার্য অংশের, যার স্বেচ্ছাসেবী কর্মকাণ্ড একটি স্থিতিস্থাপক, সহায়ক এবং স্নেহপূর্ণ মুসলিম সমাজের কাঠামোকে শক্তিশালী করে। তিনি তার শ্বশুরবাড়ির প্রতি যে দয়া প্রদর্শন করেন তা সামাজিক কর্তব্যের চেয়েও বেশি; এটি একটি গভীর আধ্যাত্মিক কাজ যা পারিবারিক সংযোগকে শক্তিশালী করে, তার স্বামীকে আনন্দিত করে এবং আল্লাহর কাছ থেকে মহান পুরষ্কারের এক অবিরাম ঝর্ণা হিসেবে কাজ করে, যা ইসলামী বিশ্বাসের কেন্দ্রবিন্দুতে গভীর করুণা এবং বুদ্ধিমত্তা প্রদর্শন করে। ব্যবসা, জনসেবা বা পারিবারিক জীবনে আমরা যে পরীক্ষার মুখোমুখি হই - সেগুলি আমাদের বিশ্বাসকে শক্তিশালী করার এবং ইসলাম যে শান্তি ও প্রশান্তি প্রদান করে তা মূর্ত করার সুযোগকে প্রতিনিধিত্ব করে। উত্তরটি বিরক্তি থেকে নয়, বরং আমাদের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক ভিত্তির সাথে আন্তরিক পুনঃসংযোগ থেকে উদ্ভূত হয়।
সকল বাঙালির ইসলামী আইন, মূল্যবোধ, নৈতিকতা ও নীতি অনুসারে অন্য ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া উচিত এবং ইসলাম শান্তি ও সমাজের সামাজিক কল্যাণে বিশ্বাস করে।
লেখক : ম্যাক্রো এবং ফিন্যান্সিয়াল অর্থনীতিবিদ, আইটি এবং উদ্যোক্তা ব্যবস্থাপনা বিশেষজ্ঞ, অর্থনীতির অধ্যাপক, বাংলাদেশ ব্যবসা ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়।

মাটি ও ফসলের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় জৈব সারের গুরুত্ব অপরিসীম। আধুনিক কৃষিতে উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে অতিরিক্ত রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের ব্যবহার মাটির উর্বরতা হ্রাস করছে এবং পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট করছে। মাটির জীবাণু, কেঁচোসহ প্রাকৃতিক উপাদানগুলো ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, ফলে মাটির গুণগত মান কমে যাচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে জৈব সার ব্যবহারই হতে পারে টেকসই কৃষির অন্যতম সমাধান। জৈব সার প্রাকৃতিক উপাদান যেমন গোবর, কম্পোস্ট, জৈব বর্জ্য ও সবুজ সার থেকে তৈরি হয়, যা মাটিতে প্রয়োজনীয় পুষ্টি সরবরাহ করে এবং মাটির গঠন উন্নত করে। এটি মাটির জৈব পদার্থের পরিমাণ বাড়িয়ে জলধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে, ফলে খরা বা অতিবৃষ্টিতেও ফসলের উৎপাদন তুলনামূলক স্থিতিশীল থাকে। একই সঙ্গে জৈব সার ব্যবহারে ফসলের গুণমান উন্নত হয় ও মানব স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর রাসায়নিক অবশিষ্টাংশের ঝুঁকি কমে। অতএব, মাটি ও ফসলের দীর্ঘমেয়াদি স্বাস্থ্য রক্ষায় জৈব সার ব্যবহারের কোনো বিকল্প নেই। টেকসই কৃষি ও নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনের জন্য কৃষকদের জৈব সার ব্যবহারে উৎসাহিত করা এবং প্রশিক্ষণ প্রদান এখন সময়ের দাবি।
জৈব সারের ব্যবহার ও টেকসই কৃষি:
বাংলাদেশের কৃষি খাত গত কয়েক দশকে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে। উৎপাদন বেড়েছে, খাদ্য ঘাটতি কমেছে এবং কৃষি অর্থনীতি আরও শক্ত ভিত্তি লাভ করেছে। তবে এই উন্নয়ন মূলত রাসায়নিক সার ও কীটনাশক নির্ভর হওয়ায় দীর্ঘমেয়াদে মাটির স্বাভাবিক গঠন ও উর্বরতা নষ্ট হচ্ছে। অতিরিক্ত রাসায়নিক ব্যবহারে উপকারী অনুজীব ধ্বংস হচ্ছে, পানির মান নষ্ট হচ্ছে এবং ফসলের পুষ্টিগুণ কমে যাচ্ছে। ফলে কৃষির উৎপাদনশীলতা কিছু সময়ের জন্য বাড়লেও, টেকসই উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। এই প্রেক্ষাপটে জৈব সার ব্যবহারের গুরুত্ব দিন দিন বাড়ছে। জৈব সার প্রাকৃতিক উপাদান যেমন গবাদিপশুর গোবর, ফসলের অবশিষ্টাংশ, পচা পাতা ও কম্পোস্ট থেকে তৈরি হয়। এটি মাটির জৈব পদার্থ বৃদ্ধি করে, জল ধারণক্ষমতা উন্নত করে এবং পরিবেশ দূষণ রোধে সহায়তা করে। পাশাপাশি জৈব সার ব্যবহারে উৎপাদিত ফসল হয় নিরাপদ, পুষ্টিকর ও পরিবেশবান্ধব। টেকসই কৃষি নিশ্চিত করতে রাসায়নিক সারের ওপর নির্ভরতা কমিয়ে জৈব সারের ব্যবহার বাড়ানো জরুরি। এর জন্য কৃষকদের সচেতনতা বৃদ্ধি, স্থানীয় পর্যায়ে জৈব সার উৎপাদন কেন্দ্র গড়ে তোলা এবং সরকার ও বেসরকারি খাতে সহযোগিতা বাড়ানো প্রয়োজন। সঠিক পরিকল্পনা ও প্রয়োগের মাধ্যমে জৈব সারভিত্তিক কৃষি বাংলাদেশকে একটি পরিবেশবান্ধব, নিরাপদ ও টেকসই কৃষি ব্যবস্থার পথে এগিয়ে নিতে পারে।
রাসায়নিক নির্ভরতার ফলাফল:
গত কয়েক দশকে বাংলাদেশের কৃষিক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ঘটেছে। আধুনিক প্রযুক্তি, উচ্চফলনশীল জাতের বীজ, এবং রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের ব্যবহারে উৎপাদন বেড়েছে বহুগুণ। কিন্তু এই অগ্রগতির আড়ালে লুকিয়ে আছে এক গুরুতর উদ্বেগ—অতিরিক্ত রাসায়নিক উপকরণনির্ভরতা। গত পাঁচ বছরে কৃষি খাতে প্রবৃদ্ধি বাড়লেও এর বেশিরভাগই এসেছে রাসায়নিক সার, কীটনাশক ও হরমোননির্ভর চাষাবাদের মাধ্যমে। এর ফলে কৃষি উৎপাদন সাময়িকভাবে বাড়লেও মাটির প্রাকৃতিক গঠন ধীরে ধীরে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। অতিরিক্ত ইউরিয়া, টিএসপি, এমওপি বা অন্যান্য রাসায়নিক সার ব্যবহারে মাটির জৈব উপাদান ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। উপকারী অনুজীব বা মাটির ক্ষুদ্র জীবগুলো মরে যাচ্ছে, যা মাটির উর্বরতা বজায় রাখতে অপরিহার্য। ফলে মাটির পানি ধারণক্ষমতা ও প্রাকৃতিক পুনরুজ্জীবন ক্ষমতা কমে যাচ্ছে। একসময় যে জমিতে সহজেই ভালো ফলন হতো, এখন সেখানে একই ফলনের জন্য দ্বিগুণ বা তারও বেশি রাসায়নিক ব্যবহার করতে হচ্ছে। এতে উৎপাদন খরচ বাড়ছে এবং কৃষক আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। শুধু মাটি নয়, অতিরিক্ত রাসায়নিক ব্যবহারের প্রভাব পড়ছে পরিবেশ ও মানবস্বাস্থ্যের ওপরও। কীটনাশক ও রাসায়নিক সার মিশ্রিত পানি নদী ও খালের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ছে, যা মাছ ও অন্যান্য জীববৈচিত্র্যের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। একইসঙ্গে খাদ্যশস্যে রাসায়নিক অবশিষ্টাংশ থেকে যাচ্ছে, যা মানুষের শরীরে দীর্ঘমেয়াদে বিভিন্ন রোগ সৃষ্টি করছে, যেমন কিডনি ও লিভারের সমস্যা, ক্যান্সার এবং হরমোনজনিত জটিলতা। এই প্রবণতা কৃষির টেকসই উন্নয়ন ও খাদ্য নিরাপত্তার জন্য বড় হুমকি হয়ে উঠেছে। টেকসই কৃষি নিশ্চিত করতে হলে এখনই রাসায়নিক নির্ভরতা কমিয়ে জৈব ও প্রাকৃতিক কৃষি পদ্ধতির দিকে ফিরে যাওয়া জরুরি। এতে মাটির স্বাস্থ্য রক্ষা পাবে, কৃষক লাভবান হবে এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্ম নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্য পাবে।
জৈব সারের গুরুত্ব:
জৈব সার হলো এমন একটি প্রাকৃতিক সার, যা উদ্ভিদ ও প্রাণীর পচনশীল অংশ, যেমন গোবর, ছাই, পাতা, ফসলের অবশিষ্টাংশ, এবং বিভিন্ন জৈব পদার্থ থেকে তৈরি হয়। এটি রাসায়নিক সার ব্যবহারের একটি পরিবেশবান্ধব বিকল্প হিসেবে কৃষিক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। জৈব সার ব্যবহারে মাটির গুণগত মান উন্নত হয়, কারণ এটি মাটির ভৌত, রাসায়নিক ও জৈবিক বৈশিষ্ট্যে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। প্রথমত, জৈব সার মাটির গঠনকে ঝুরঝুরে ও বায়ু সঞ্চালনযোগ্য করে তোলে, ফলে উদ্ভিদের শিকড় সহজে বৃদ্ধি পায়। এটি মাটিতে পানির ধারণক্ষমতা বৃদ্ধি করে, যা খরা পরিস্থিতিতেও ফসলের বৃদ্ধি টিকিয়ে রাখতে সাহায্য করে। দ্বিতীয়ত, জৈব সার ধীরে ধীরে পুষ্টি সরবরাহ করে, ফলে মাটিতে পুষ্টির ভারসাম্য বজায় থাকে এবং দীর্ঘমেয়াদে মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি পায়। এছাড়া, জৈব সার মাটিতে জীবাণু ও অণুজীবের কার্যক্রমকে সক্রিয় করে তোলে, যা মাটির জৈবিক জীবনকে সমৃদ্ধ করে। এই অণুজীবগুলো মাটির জৈব পদার্থ ভেঙে উদ্ভিদের জন্য সহজলভ্য পুষ্টি তৈরি করে। ফলে মাটির জীববৈচিত্র্য বৃদ্ধি পায়, যা টেকসই কৃষির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অন্যদিকে, জৈব সার ব্যবহারে ফসল হয় অধিক পুষ্টিকর, সুস্বাদু ও বিষমুক্ত, যা মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী। বাজারে জৈব পণ্যের চাহিদা ক্রমশ বাড়ছে, ফলে কৃষকরা অর্থনৈতিকভাবেও লাভবান হচ্ছেন। সারসংক্ষেপে বলা যায়, জৈব সার শুধু মাটির উর্বরতা রক্ষা করে না, বরং পরিবেশ সংরক্ষণ, স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও টেকসই কৃষি ব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপন করে। তাই মাটির স্বাস্থ্য ও ফসলের গুণগত মান বজায় রাখতে জৈব সার ব্যবহারের গুরুত্ব অনস্বীকার্য।বাংলাদেশে জৈব সার ব্যবহার চিত্র: দেশে জৈব সারের বার্ষিক চাহিদা ৬০-৬৫ লাখ টন। এর মধ্যে ৭৫ শতাংশের বেশি কাঁচামাল দেশেই পাওয়া যায়। অর্থাৎ, কার্যকর উদ্যোগ নিলে অভ্যন্তরীণভাবে পুরো চাহিদা পূরণ সম্ভব। এতে প্রাণিসম্পদ খাতের উন্নয়ন, গ্রামীণ অর্থনীতির চাঙ্গা হওয়া, এবং পরিবেশবান্ধব কৃষি নিশ্চিত করা যাবে।
নীতিগত উদ্যোগ ও ভর্তুকি:
বর্তমানে কৃষি খাতে বরাদ্দের ৭০ শতাংশই ভর্তুকিতে ব্যয় হয়, যার ৮০ শতাংশ রাসায়নিক সারে। সরকার এখন রাসায়নিক সারের ব্যবহার ৩২-৩৫ শতাংশ কমিয়ে জৈব সারের ব্যবহার বাড়ানোর লক্ষ্যে কাজ করছে। বিশেষজ্ঞরা জৈব সার ব্যবহারে ভর্তুকি ও প্রণোদনা দেয়ার আহ্বান জানিয়েছেন, যাতে কৃষকরা সহজে এটি গ্রহণ করতে পারেন।
জৈব সার ব্যবহারে চ্যালেঞ্জ ও করণীয়:
জৈব সার ব্যবহারের গুরুত্ব আজ সর্বজনবিদিত হলেও এর প্রয়োগে কিছু চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান। প্রধান চ্যালেঞ্জগুলোর মধ্যে রয়েছে—জৈব সার উৎপাদনের ধীরগতি, কৃষকদের মধ্যে পর্যাপ্ত সচেতনতার অভাব, এবং বাজারে জৈব সার সহজলভ্য না থাকা। অনেক কৃষক এখনো রাসায়নিক সারের দ্রুত ফলপ্রদ প্রভাবের কারণে জৈব সার ব্যবহারে আগ্রহী নন। এছাড়া, উৎপাদন ও সংরক্ষণ প্রক্রিয়ায় প্রযুক্তিগত ঘাটতি এবং মানসম্মত জৈব সারের অভাবও বড় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে।
এই চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলায় প্রয়োজন সমন্বিত উদ্যোগ। সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে কৃষকদের প্রশিক্ষণ ও সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে, যাতে তারা জৈব সারের দীর্ঘমেয়াদি উপকারিতা সম্পর্কে জানেন। স্থানীয় পর্যায়ে জৈব সার উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন করা হলে তা সহজলভ্য হবে এবং পরিবহন ব্যয়ও কমবে। পাশাপাশি বাজারে জৈব সারের মূল্য সহনীয় রাখার উদ্যোগ নিতে হবে, যাতে কৃষকেরা সহজে এটি ব্যবহার করতে পারেন। গবেষণা ও প্রযুক্তিগত সহায়তা বাড়িয়ে উৎপাদন প্রক্রিয়া আরও কার্যকর ও সময়সাশ্রয়ী করা জরুরি।
বাংলাদেশের কৃষি খাতের টেকসই ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করতে হলে জৈব সারের ব্যবহার বৃদ্ধি অপরিহার্য। এটি শুধু মাটি ও ফসলের স্বাস্থ্য রক্ষায় নয়, বরং মানবস্বাস্থ্য, পরিবেশ সংরক্ষণ এবং খাদ্যনিরাপত্তা নিশ্চিত করতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এখনই সময় রাসায়নিক নির্ভরতা কমিয়ে পরিবেশবান্ধব ও টেকসই কৃষির পথে এগিয়ে যাওয়ার।
লেখক: কৃষি ও পরিবেশ বিশেষজ্ঞ।

শাহবাগ, প্রেসক্লাব, শহীদ মিনার, যমুনা এই জায়গাগুলো এখন আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দু হয়েছে। এখানে অবস্থান নিলে কেউ খালি হাতে ফিরে না। এটা বুঝতে পেরে আন্দোলনের ধারাবাহিকতা চলছেই। অনশন,অবস্থান কর্মসূচী, ভূখা মিছিল এইগুলো করে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে সবসময় ব্যস্ত থাকতে হচ্ছে। জনগণকে প্রবল যানজটের স্বীকার হতে হচ্ছে। প্রতিনিয়ত রাজনৈতিক দলগুলোর মাঝে জুলাই সনদ, গণভোট, পিআর পদ্ধতি নির্বাচন, প্রতীক নিয়ে দ্বন্দ্বে ঢাকার রাজপথ এমনিতেই উত্তপ্ত। তার ওপর বিভিন্ন পেশার লোকদের প্রাপ্তি অপ্রাপ্তি নিয়ে ক্ষোভত আছেই। এই রুটিন মফিক আন্দোলন অন্তর্বর্তী সরকারকে সবসময় টেনশনের মধ্যে রাখা হচ্ছে। তাহলে কিভাবে দেশ জাতীয় নির্বচনের প্রস্ততির দিকে এগুবে?
সারাদেশে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক অধিদপ্তরের অধীনে প্রায় ৪ লাখ এবং মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা মন্ত্রনালয়ের অধীনে আছে প্রায় ২ লাখ শিক্ষক কর্মচারী আছেন। তাদের বেতন ভাতা কত ভাগ বাড়াতে কত অর্থ ব্যয় হবে সেটি অর্থ মন্ত্রণালয়ের কষে দেখিয়েছে। কিন্তু তারা এই হিসাব কষে দেখেননি এই স্বল্প বেতন ভাতায় একটি সংসার কি চালানো যায়? কি কঠিন জীবনযাপন করতে হচ্ছে সেটা কি কর্তৃপক্ষের টনক নড়েছে কোন দিন? ২০২৫-২৬ এর অর্থবছরে শিক্ষা খাতে বাজেট হল আটাশ হাজার ৫৫৭ কোটি টাকা। ১৮ কোটি জনসংখ্যার দেশে তা একেবারে কম।উচ্চ শিক্ষা গবেষণার খাতে কত অর্থের অপচয় এবং এই ফান্ড নয় ছয় হয় এর হিসাব কারও কাছে কি আছে? মাধ্যমিকের শিক্ষকরা সংসার চালাতে হিমসীম খেয়ে ছুটির দিনে কেউ কেউ কৃষি কাজ করে অথবা বাড়তি শ্রম দিয়ে বিকল্প কাজের সন্ধান খোঁজে। এতদিন যাবত এদের চাহিদাগুলো দৃষ্টির অগোচরে রয়ে গেছে। সরকার যায় সরকার আসে প্রতিশ্রুতি দেয় কিন্তু বাস্তবায়নের বালাই নাই। তাই শিক্ষকরা আন্দোলনে ফুঁসে উঠেছিল।-শিক্ষকদের দাবি ছিল( ক) বাড়ি ভাড়া ভাতা মুল বেতনের ২০% করতে হবে এবং তা কমপক্ষে ৩০০০/ টাকা হতে হবে (খ) চিকিৎসা ভাতা ১৫০০ টাকা করতে হবে। (গ) উৎসাহ ভাতা মূল বেতনের ৭৫% করতে হবে। আন্দোলনের দশম দিনে বাড়ি ভাড়া ভাতা ১৫% সংশোধিত করে দাবি পেশ করে। এই দাবি বাস্তবায়ন করতে চরম পুলিশের নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছে। শিক্ষক নেতারা কিন্তু ছিল নাছোড়বান্দা। অনেক তর্ক বিতর্ক আলোচনা ও গবেষণা এবং রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে পরামর্শ করে এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের ১৫% বাড়ি ভাড়া দেওয়ার সিদ্ধান্ত মেনে নেয় যেমন…নভেম্বর/২৫ থেকে মূল বেতনের ৭.৫০%। আগামী বছরের জুলাই /২৬ থেকে বাকি ৭.৫০%। এতে করে জাতীয় বাজেটের উপর প্রভাব ফেলবে না। এমপিওভুক্ত শিক্ষকরা এই দাবি মেনে নিয়ে স্ব স্ব স্কুলে ফিরে গিয়েছে। যে কয়দিন আন্দোলন করে ক্ষতি করেছে তা শনিবারে বিদ্যালয় খোলা রেখে পুষিয়ে নেবেন।
যেহেতু মাধ্যমিক শিক্ষকরা আন্দোলন করে এদের দাবিসমূহ রাজপথের মাধ্যমে আদায় করে নিয়েছেন, এই বিষয়টি স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদ্রাসার শিক্ষকদের মাঝে আশা জাগিয়ে লংমার্চ করে এলো রাজধানীতে।
শিক্ষকদের আন্দোলন শেষ না হতেই দীর্ঘদিন জাতীয়করণের দাবি জানিয়ে আসা স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদ্রাসার শিক্ষকরা জোড়ালো আন্দোলন গড়ে তুলেন…গত বছর ৫ আগস্ট পটপরিবর্তনের পর। গত জানুয়ারি মাসে যখন আবার আন্দোলনে নামে ২৮ জানুয়ারি শিক্ষকদের কর্মসূচিতে এসে এসব মাদ্রাসাকে জাতীয়করণের ঘোষণা দেয় সরকার। জাতীয়করণের কোনো লক্ষ্মণ না দেখে শিক্ষকরা গত ১৩ অক্টোবর থেকে রাজধানীর প্রেসক্লাবে অবস্থান কর্মসূচি করে যাচ্ছেন। সর্বশেষ গত বুধবার প্রেসক্লাব থেকে সচিবালয়ে যাওয়ার প্রাক্কালে জলকামান লাঠিচার্জ, ট্রিয়ার গ্যাস ও সাউন্ড গ্রেনেড হামলায় অর্ধশত শিক্ষক আহত হয়।
স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদ্রাসা শিক্ষক ঐক্যজোটের চেয়ারম্যান কাজি মোখলেছুর রহমান মিডিয়াকে জানায় পূর্ব ঘোষিত কর্মসূচি হিসেবে আমরা শান্তিপূর্ণভাবে ভুখামিছিল বের করে সচিবালয়ের পঞ্চম গেইটে অবস্থান নিয়ে শিক্ষা উপদেষ্টার কাছে দাবি দাওয়া জানানোর চেষ্টা করছিলাম। অমন সময় পুলিশ আমাদের শিক্ষকদের ওপর অতর্কিত হামলা চালায়। এতে করে অর্ধশত শিক্ষক আহত হয়। এর মধ্যে অনেক বয়োজ্যেষ্ঠ শিক্ষক ও রয়েছে।
স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদ্রাসা শিক্ষা উন্নয়ন বাংলাদেশে সূত্রের এর ভাষ্য অনুযায়ী ১৯৭৮ সালের অডিন্যান্স ও ১৯৮৪ সালের মাদ্রাসা বোর্ডের নিবন্ধনের মাধ্যমে স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদ্রাসা প্রাথমিক শিক্ষার সমতুল্য শিক্ষা কার্যক্রম চালিয়ে আসছিল।এক সময় শিক্ষার্থীরা উপবৃত্তি ও ফিডিং সুবিধা পেলেও ২০২২ সাল থেকে তা বন্ধ হয়ে আছে।
ইসলামী ও সাধারণ শিক্ষার সমন্বয়ে যে শিক্ষা ব্যবস্থা রয়েছে… সেই আলিয়া মাদ্রাসার প্রাথমিক স্তরটা পঠিত হয় এবতেদায়ী মাদ্রাসায়। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সমমান এ ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গোড়াপত্তন হয় ১৯৮৪ সালে। এরপর চার দশক কেটে গেলে ও শিক্ষকরা মানবেতর জীবনযাপন করছেন। শিক্ষকদের সাথে আলাপ করে জানা গেছে তাদের অনেকেরই কর্মজীবন শেষ করেছেন কোনো রাষ্ট্রীয় সুযোগ সুবিধা ছাড়াই। অথচ ১৯৭৩ সাল থেকে প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ করেছে। ২০১৩ সালে ছাব্বিশ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়কে জাতীয়করণ করা হয়েছে।
-দেশে বর্তমানে স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদ্রাসা সংখ্যা সাত হাজার ৪৫১টি। এর মধ্যে মাত্র এক হাজার ৫১৯টি মাদ্রাসার শিক্ষকরা সরকারি অনুদান পান। এবতেদায়ী মাদ্রাসার প্রধানের অনুদান ৫ হাজার টাকা সহকারী শিক্ষকের বেতন ৩ হাজার টাকা। বাকী পাঁচ হাজার ৯৩২টি মাদ্রাসার শিক্ষকরা দীর্ঘ ৪০ বছর ধরে সরকারি বেতন ভাতা পান না। অথচ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মতো একই পাঠ্যক্রমে তার শিক্ষার্থীদের জ্ঞান চর্চা করে যাচ্ছেন। সব প্রাথমিক বিদ্যালয় সরকারি করায় এবতেদায়ী মাদ্রাসা সরকারিকরনের দাবি করার সুযোগ পায়। এই দাবি চলমান প্রক্রিয়া হিসেবে টানা ১৭ দিন যাবত লং মার্চ, সমাবেশ, ঢাকার রাজপথে অবস্থান, ভুখামিছিল সবই হচ্ছে।
অন্তর্বর্তী সরকার আসার পর সরকারি অনুদান প্রাপ্ত মাদ্রাসার মধ্যে থেকে বাছাই করে এক হাজর ৯০টি এমপিওভুক্ত করার জন্য তালিকাভুক্ত করে। কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ দু’দফা আশ্বাস দেওয়া স্বত্বে ও আমলাতান্ত্রিক জটিলতায় তা আটকে যায়। গত ৫ মার্চ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব ছাড়ার আগে স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদ্রাসাগুলো এমপিও ভূক্তির প্রস্তাবে অনুমোদন দেন সাবেক শিক্ষা উপদেষ্টা ওয়াহিদ উদ্দিন মাহমুদ। এরপর এ প্রস্তাব প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে পাঠানো হয়। স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদ্রাসা শিক্ষক ঐক্যজোটের মহাসচিব শামসুল আলম মিডিয়াকে জানান ‘প্রথম যখন প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে পাঠানো হয় সেখানে সংযুক্ত এবতেদায়ী মাদ্রাসার তথ্য ও পাঠানো হয়েছিল। তবে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয় থেকে পুনঃরায় নথি যাচাইয়ের জন্য ফেরত পাঠানো হয়।
তিনি আরও বলেন স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদ্রাসা এমপিও ভুক্তি ধাপে ধাপে সরকারিকরণ করার আশ্বাস দিলেও সংযুক্ত মাদ্রাসা নিয়ে কোন ঘোষণা ছিল না। অথচ মন্ত্রণালয়ের কোন কোন আমলা সংযুক্ত এবতেদায়ী মাদ্রাসাগুলোকে এর সঙ্গে যুক্ত করেন। ফলে টাকার অংক অনেক বড় হয়ে যায়। নথি অনুমোদনের প্রক্রিয়াও দীর্ঘায়িত হয়। এমনটা না হলে মে মাসের শুরুতে আমরা এমপিও সুবিধা পেতাম।’
তবে মাদ্রাসার এমপিওভুক্তির কাজ চলছে। জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে তথ্য নিয়ে অনুদানভুক্ত এবতেদায়ী মাদ্রাসাগুলোর মধ্যে প্রাথমিকভাবে এক হাজার ৯০টি এমপিওভুক্ত করতে অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব পাঠিয়েছে। এ জন্য একটি নীতিমালার খসড়া ও তৈরি করা হয়েছে। এসব মাদ্রাসার জনবল কাঠামো ও বেতন ভাতার জন্য অবশ্য ২০১৮ সালে প্রথম নীতিমালা করেছিল কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ। যদি ও সে নীতিমালা অনুযায়ী সুযোগ সুবিধা পাননি। এখন নতুন করে নীতিমালা হয়েছে এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ে গেছে।
এ নীতিমালায় এবতেদায়ী মাদ্রাসার প্রধানের বেতন ১১তম গ্রেড এবং শিক্ষক কারি মৌলভি পদে ১৩তম গ্রেড দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে। সূত্র মতে জানা যায় এবতেদায়ী মাদ্রাসায় প্রতিটিতে পদ থাকবে সাতটি। এর মধ্যে একটি পদ এবতেদায়ী প্রধানের এবং সহকারী ৫টি এর মধ্যে দুইজনের পদবি শিক্ষক একজন মৌলভী আরেকটি পদের নাম কারি। বাকি পদটি অফিস সহায়কের যার বেতন হবে ২০তম গ্রেডে।
শিক্ষা মন্ত্রণালয় বলেছে এবতেদায়ী মাদ্রাসা এমপিওভুক্তি প্রক্রিয়া অনেকটাই গুছিয়ে আনা হয়েছে। এমপিওভুক্তির নীতিমালার খসড়াও প্রস্তত। এ প্রক্রিয়ায় বেতন দিতে ৯ কোটি ৮৪ লাখ টাকা লাগবে। অনুদানভুক্ত স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদ্রাসার সংখ্যা এক হাজার ৫১৯টি হলে ও বর্তমানে অনুদান পাচ্ছেন এক হাজার ৩৩৮টি মাদ্রাসার চার হাজার ৪৩৭ শিক্ষক। ১৮১ স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদ্রাসার শিক্ষকরা অনুদান নেন না।সেগুলো বেশিরভাগ নিজস্ব অর্থায়নে পরিচালিত হয়।
বর্তমানে চার হাজার ৪৩৭ শিক্ষককে অনুদান দিতে মাসে ১ কোটি ৪৮ লাখ ৩৭ হাজার টাকার প্রয়োজন হয়। এমপিওভুক্ত হলে সরকারকে প্রতি মাসে গুনতে হবে ৯ কোটি ৮৪ লাখ টাকা। কিন্তু এই মুহূর্তে সরকারের সক্ষমতা আছে কিনা তাও ভেবে দেখা উচিত। দেশের আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো বেহাল অবস্থা, গার্মেন্টস কারখানা বন্ধ হয়ে বেকারত্ব সৃষ্টি, দেশে বিনিয়োগে মন্দাভাবে কোন কর্মসংস্থান হচ্ছে না। অর্থযোগানের সীমাবদ্ধতায় এখন কি দাবি দাওয়া বাস্তবায়নের সময়? তারপরও যেহেতু স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদ্রাসার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন সেটার সমাধান হয়ত হয়ে যাবে। তাছাড়া দেশে নৈতিক শিক্ষার আলো ছড়াতে ইসলামিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর অবদান অস্বীকার করা যাবে না। আগামী প্রজন্মের নৈতিক শিক্ষা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদ্রাসার দাবীগুলো আমলাতান্ত্রিক জটিলতা কাটিয়ে সমাধান হউক…এই প্রত্যাশাটুকু সরকারের প্রতি থাকবেই।
লেখক: কলামিস্ট ও সাবেক ব্যাংকার।

১ নভেম্বর ২০২৫ সমবায় দিবস। আর এটি ৫৪তম জাতীয় সমবায় দিবস। এবার এর প্রতিপাদ্য স্লোগান হলো ‘সাম্য ও সমতায়, দেশ গড়বে সমবায়’। যেভাবেই বলি না কেন, জীবজগত টিকে থাকার জন্য অন্যতম নিয়ামক হলো সমবায়। আর সমবায়ী মনোভাব যেখানে অনুপস্থিত, সেখানেই বিশৃঙ্খলা এবং এর ফলশ্রুতিতে মূল উদ্দেশ্য গতিহারা হয়ে মাঝ পথেই ভরাডুবি হয়ে থাকে, যার ভুড়ি ভুড়ি উদহারণ বাস্তবে পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। আর এই বিশ্বে অদ্যাবধি আবিস্কৃত পর্যায় সারনিতে ১১৮টি মৌলের মধ্যে কোনটি এককভাবে তেমন কার্যকরী নয়; সেখানে যৌগিকতার প্রশ্ন উঠে আসে, যা বৈজ্ঞানিকরা চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন। এদিকে মনূষ্যকুল আদিমযুগে যখন টোটেম গ্রুপের আওতায় সমাজবদ্ধ হতে শুরু করে; সেই সময়ে সমবায়ী দর্শন বলতে গেলে স্টেম সেল হিসেবে ভূমিকা রেখেছে বলেই আমরা মানুষ আজ এ পর্যায়ে পৌছিয়েছি। তাছাড়া সামষ্টিক দিক দিয়ে সমস্যা সংকুল ও জটিল বিশ্ব সংসারে নিজেদের সংরক্ষিত রাখার পথ সুগম করেছে। আর এরই ধারাবাহিকতায় সংঘ বা সমিতি সৃষ্টি হওয়ার পথে এগিয়ে দিয়েছে। এদিকে ব্যষ্টিক দিক দিয়ে ছোট বেলার সেই গল্পের কথা আপনাদের হয়তো স্মরণে আছে। এ সূত্র ধরে উল্লেখ্য যে, যিশুখৃষ্টের জন্মের অনেক আগে গ্রীসের ঈশপ নামক লেখকের বিখ্যাত গল্পের আড়ালে বৃদ্ধ পিতার অবাধ্য সন্তানদের একত্রে থাকার ব্যাপারে একতাই বল সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছিলেন, যা অমোঘ সত্য বলে প্রতিষ্ঠিত।
আর এই তো ৫ আগস্ট (২০২৪) বৈষম্যবিরোধী গণঅভ্যুত্থান বা বিপ্লব ঘটে গেলো। এতে বহু ছাত্র জনতা হতাহত হয়। চারিদিকে নৈরাজ্য, কেবল দাবি দাওয়া নিয়ে একের পর এক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছে। সেই মুহূর্তে হাল ধরেন প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে বিশ্ব বরেণ্য নোবেল বিজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূস। এক পর্যায়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তার প্রথম কথা ছিল, ‘আমি কিছু চাই না, চাই শুধু একতা; তাহলে সব সমাধান হয়ে যাবে এবং দেশ উত্তরোত্তর উন্নতির দিকে চলে যাবে এবং বিশ্ব দরবারে বাংলাদেশ সম্মানিত আসন নিয়ে অবস্থান নিয়ে থাকতে পারবে’
মূলত অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে কতিপয় লোকের সংঘবদ্ধ হওয়ার পদ্ধতিকে ‘সমবায়’ ব্যবস্থা বলে অভিহিত করা হয়। আর মানবজীবনে এই সম্মিলিত প্রয়াস বয়ে আনে বিপুল সম্ভাবনা। সাধারণত যেখানে একক প্রচেষ্টায় কোনো উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জণ করা সম্ভবপর হয় না; সেক্ষেত্রে সমবেত প্রচেষ্টার আবশ্যকতা দেখা দেয়। আর সকলে সম্মিলিতভাবে যে কাজটি যত সহজে সম্পাদন করতে পারে, পৃথক পৃথকভাবে তথা এককভাবে তা বাস্তবায়িত করা ততটা সহজ নয়। সকলে মিলে কাজ করতে পারলে, তাতে সাফল্য অনিবার্য হয়ে ওঠে। এ পরিপ্রেক্ষিতে প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ কালভার্টের মতে, ‘কিছুসংখ্যক লোক যখন কোনো অর্থনৈতিক স্বার্থ সুসম্পন্ন করার লক্ষ্যে স্বেচ্ছায় সম্মিলিত হয়, তখন তাকে ‘সমবায়’ বলা হয়’। আর এর ওপর ভিত্তি করেই সমবায় আন্দোলনের উদ্ভব এবং কালক্রমে বিকাশ সাধিত হয়েছে।
এ প্রেক্ষাপটে উল্লেখ্য যে, ১৮৪৪ সালে প্রতিষ্ঠিত ইংল্যান্ডের রচডেল গ্রামের প্রথম সফল সমবায় সমিতির কথা হয়তো অনেকেই জানেন এবং বলতে গেলে সেখানেই অংকুরোদগম হয়। এদিকে সমবায় আন্দোলনের ক্ষেত্রে জার্মানীর ভূমিকা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। এক্ষেত্রে যে পুরোধার কথা উঠে আসে; তিনি হলেন অর্থনীতিবিদ রাইফিজেন। এই মহান-হৃদয়বান জার্মান সমাজ-সংস্কারক মহাজনদের নির্মম শোষণ থেকে কৃষককুলকে রক্ষার জন্যে সমবায় আন্দোলনের সূত্রপাত করেন। আর সেই থেকে সমবায়ী ধারা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। আর আমাদের এই উপমহাদেশে উইলিয়াম নিকলসন সমবায়ের নীতি গ্রহণ করেন এবং একটি ঋণদান সমিতি আইন পাস করেন। আর এই আইনের ভিত্তিতে শহরে-গ্রামে-বন্দরে কৃষক, কারিগর ও স্বল্পবিত্ত মানুষের মধ্যে সমবায়িক কর্মপ্রচেষ্টা প্রসারের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯০৪ সালে কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটিজ অ্যাক্ট পাস করে সমবায়ী কার্যক্রম শুরু করা হয়। শুধু তাই নয়, সমবায় আন্দোলনকে ব্যাপকতর করার জন্যে ১৯১২ সালে নতুন কো-অপারেটিভ অ্যাক্ট জারি করা হয় এবং এই আইনে ঋণদান সমিতি ব্যতীত ক্রয়-বিক্রয়, উৎপাদন প্রভৃতি ক্ষেত্রে কার্যরত অনুরূপ সমিতিগুলোকেও সমবায় সমিতিরূপে স্বীকৃতি দেয়া হয়। এই সময় কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সমবায় ব্যাঙ্ক স্থাপন করা হয়। ১৯১৯ সালে ভারত শাসন আইনের মাধ্যমে সমবায়কে পুরাপুরি প্রাদেশিক সরকারের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সময়ের পরিক্রমায় দিনের পর দিন এগিয়ে যেতে থাকে। পাকিস্তান আমল এসে যায়। সেই সময়ে সমবায় কৃষি ব্যাংক, সমবায় বিমা সমিতি, সমবায় ঋণদান সংস্থা, বিক্রেতা সমবায় সমিতি, ইত্যাদি গড়ে ওঠে। তবে তখন সরকারি কার্যোদ্যোগের অভাবে জনগণের মধ্যে সমবায় আন্দোলনের ভিত মজবুত না হলেও এর প্রসার ঘটেছিল। তৎপর বাংলাদেশে এর উপর গুরুত্ব দেয়া হয় এবং বিভিন্ন আঙ্গিকে প্রসার লাভ করে।
(ই) দুঃখের বিষয় হলো যে বিগত প্রায় দেড়যুগ অগণতান্ত্রিক পরিবেশে অনেক লম্বা লম্বা কথা বলা হলেও, বাস্তবে আমরা এক্ষেত্রে অনেকাংশে পিছিয়ে ছিলাম। দেশে খেয়ালখুশী মতো সিদ্ধান্ত ও নৈরাজ্যর জন্য সমবায় সহ অনেক সেক্টর বলতে গেলে থমকে দাঁড়িয়েছিল। উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশ তৃতীয় বিশ্বের একটি কৃষিনির্ভর দেশ। সবে অনুন্নত থেকে উন্নয়নশীল দেশের কাতারে সামিল হয়েছে, কাজেই বাংলাদেশের মতো অর্থনৈতিক দিক দিয়ে একটি পশ্চাৎপদ দেশের পক্ষে সমবায় নীতি খুবই ফলপ্রসূ ও কার্যকর ব্যবস্থা। বাংলাদেশে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে, বিশেষ করে কৃষিক্ষেত্রে সমবায়ের প্রয়োজনীয়তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের দেশের দরিদ্র, অসহায় কৃষককুল সারাদিন প্রাণপাত পরিশ্রম করে তাদের ক্ষুধার অন্ন সংগ্রহ করতে পারেন না। তদুপরি ঋণভারে তারা জর্জরিত। কৃষি জমি পুরুষানুক্রমে খণ্ডীকৃত হয়ে আসছে। হাড়ভাঙা খাটুনির ফসল মহাজনের গোলায় ওঠে ঋণের দায়ে। কৃষিজাতপণ্য বাজারজাতকরণের ব্যবস্থাও ত্রুটিপূর্ণ। সত্যিকারার্থে যে দেশের অর্থনীতি কৃষিনির্ভর এবং শতকরা ৮৫ ভাগ মানুষ কৃষির উপর নির্ভরশীল, সে দেশে সমবায়ের গুরুত্ব অপরিসীম। কেননা সমবায়ের মাধ্যমে উন্নত বীজ, সার, ইত্যাদি প্রয়োগের দ্বারা চাষাবাদে অধিক ফসল উৎপন্ন করা সম্ভব। তাই বাংলাদেশে সমবায় আন্দোলন জনপ্রিয় করে সমবায়ের মাধ্যমে উন্নত ধরনের বৈজ্ঞানিক চাষাবাদ, কুটিরশিল্পের প্রসার, মূলধন সংগ্রহ, কাঁচামাল সংগ্রহ, কৃষিপণ্য বিক্রি প্রভৃতি ক্ষেত্রে সমবায়ের প্রয়োগ অপরিহার্য। সমবায় মানুষের অর্থনৈতিক উন্নয়নের মুক্তিদাতা। আর সমবায়ের পরিধি ছোট থেকে অনেক বড় হতে পারে। আদর্শ সমবায় সংগঠন সমাজের অবকাঠামোর পরিবর্তন করে অর্থনৈতিক সচ্ছলতা দান করে। বস্তুত সমবায় গড়ে ওঠে কতিপয় মূলনীতির ওপর ভিত্তি করে, যেমন- সহযোগিতামূলক মনোভাব, একতা, সাম্য, সততা, নৈকট্য, গণতন্ত্র, স্বাধীনতা, মিতব্যয়িতা, ঐক্যমত্ততা, স্বচ্ছতা, শৃঙ্খলা, বিশ্বস্ততা, সম্প্রীতি, বিশ্বাস ইত্যাদি। মূলত অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোন থেকে মানুষ ও সমাজে কল্যান সাধনই এর মূলমন্ত্র।
আরেকটি কথা বলছি, যা হয়তো আমরা ততটুকু তলিয়ে দেখি না। এ সূত্র ধরে উল্লেখ্য যে, বাঘ যখন শিকার ধরার জন্যে সচেষ্ট হয়। তখন হরিণ বা মহিষ বা শুকরের দল থেকে বুদ্ধি খাটিয়ে একটিকে আলাদা করে ফেলবার পর সহজে শিকার ধরে থাকে। তবে যদি দল থেকে এককভাবে আলাদা না করতে পারে, তাহলে শিকার ধরা কঠিন হয়ে দাঁড়ায় এবং অনেক সময় বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে যেতে হয়। তাই এতে প্রতীয়মান হয় যে, সমবায়ী হয়ে দলগতভাবে চলে নিরাপত্তার বলয়ের মধ্যে থেকে মৃত্যু ঝুঁকির মতো অবস্থা থেকে মুক্ত থাকা যায়। সেহেতু জীবন চলার পথে সমবায় কতখানি গুরুত্বপূর্ণ, তা সহজেই অনুমেয়। পরিশেষে এই বলে ইতি টানছি যে, দুই বছর আগে একটি সমবায় সংক্রান্ত দুই দিনের সেমিনারে যাওয়ার সুযোগ হয়েছিল, সেই সেমিনারে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন একজন লেকচারার বলেছিলেন যে বাংলাদেশে ছোট বড় মিলে লক্ষাধিক সমবায় সমিতি আছে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, কিছু সমিতি কয়েক বছর ভালভাবে চলে পরবর্তীতে মধ্য পথে বন্ধ হয়ে যায়। এর কারণ সম্পর্কে তিনি বিশেষভাবে উল্লেখ করেণ যে, সদস্যদের আচরণগত নেতিবাচক অনুদার মনোভাব এবং আর্থিক দিক দিয়ে ত্যাগের ছন্দপতন। তাই এ ব্যাপারে প্রতিষ্ঠিত সমিতিতে যাতে আত্মকলহ এবং ভুল বুঝাবুঝি না হয়, সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখা সমীচীন। আর এটি সত্য যে, এই কৃষি নির্ভরশীল বাংলাদেশে সমবায় সমিতির ব্যাপারে না দিক দিয়ে পটেনশিয়ালিটি বিদ্যমান। তাই সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষসহ সবাইকে ত্যাগ ও সহমর্মিতার সারথি ধরে এগিয়ে আসতে হবে।
লেখক : গবেষক, অর্থনীতিবিদ এবং লেখক হিসেবে মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সম্মাননা ও পদকপ্রাপ্ত।

যার জীবনে দুর্দশার ঝড় আসে, সে-ই জানে তার প্রচণ্ডতা। সুখের মজবুত ঘরের ভিত নড়ে ওঠে। জানালাগুলো উম্মাদের মতো অস্থির হয়। কোনো দরোজা আর খোলা মনে হয় না। মনে হয়, আনন্দের আকাশজুড়ে কোনোদিনই সূর্য ছিল না। এমন বিষাদপূর্ণ অনুভবে সব মুহূর্ত ভরে থাকে।
জীবনে নতুনত্ব আনার শত চেষ্টা করলেও যাপিত পুরনো মুহূর্তগুলো কখনোই পিছু ছাড়ে না। তখন এই কথার প্রতিধ্বনি আসে মনে বার বার, যেমন অনুভব করেছেন কবি মেরি অলিভার, I also know the way the old life haunts the new.” (আমি এও জানি, কীভাবে পুরনো জীবন, নতুন জীবনকে তাড়া করে ফেরে)। কোনো কোনো ক্ষেত্রে, অভিজ্ঞতা শক্তিতে পরিণত হয়ে জীবন অঢেল ফুল ফসলে ভরে তোলে। এজন্য অত্যন্ত ধৈর্য, সঠিক ও সুষম ভাবনার স্থিরতা চাই। অন্যথায়, সময়ের সাম্পান ভুল নদীতে গিয়ে পড়তে পারে। তার উত্তাল ঢেউয়ে তলিয়ে যেতে পারে পালতোলা সুবাতাসে বয়ে যাওয়া জীবন-নৌকা।
আমাদের জীবনকাল নানারকম মোহের মাকাল ফলে ভরা। প্রয়োজনটুকু ব্যক্তি, সমাজ ও পরিপার্শ্ব অনুযায়ী ভিন্ন। তবু ন্যুনতম মৌলিক চাহিদা পূরণের উপকরণ না হলে চলাও তো কঠিন হয়ে পড়ে। এই চাহিদারও সীমা আকাশ সমান। দৃষ্টি দিয়ে দেখবার চেষ্টা করা যায়, কিন্তু দিগন্তের আভাররশ্মির মতো কিছু একটার আড়ালে গিয়ে থামে চোখ। ক্লান্তিতে ভরে ওঠে, তবু দেখবার বাসনা যায় না। চাওয়া-পাওয়া বা কামনা-বাসনার লাগাম টেনে ধরতে নিজেদেরকেই পয়লা শিখতে হয়, অনুশীলন করতে হয়, তবেই পরিবারের অন্যান্যদেরকে সেই অনুযায়ী শিক্ষা বা পরামর্শ দেয়া সম্ভব হয়। তা না হলে আরও বড় ভুল হয়ে যায় প্লেটো’র কথাটা খাটে এখানে, “If one has made a mistake, and fails to correct it, one has made a greater mistake.। ভুল ধরিয়ে দেয়া বা শুধরে নেবার ক্ষমতা সবার থাকে না। হতাশা, নিরাশা বা প্রাপ্তির প্রচ্ছন্নতা ব্যক্তির অন্তরে ঘন হয়ে ওঠে। আদীগন্ত হতাশার কুয়াশায় তার আকাশ ছেয়ে যায়। হতে পারে, এটা এমন এক চাওয়ার ফল, যা ঝুলে আছে এমন উঁচু গাছের মগডালে, তার নাগালের কোনো উপায় তার হাতে নেই। মনের গহন কথাটা কাউকে বলতেও পারে না, বা প্রকাশ করতে চায় না। মা অথবা বাবা’র কাছ থেকে পরামর্শ নেবে, সে ভরসাও পায় না। অনেক ক্ষেত্রে সবসময়ের প্রজন্ম ভাবে, তাদের মন বুঝবার মতো ক্ষমতা, সামর্থ মা-বাবা’র নেই। কবি আলেক্সানডার পোপ চমৎকার করে বলেছেন, “We think our Fathers Fools, so wise we grow; Our Wiser Sons, no doubt, will think us so,” কিন্তু সত্যকে মেনে নেয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ। আর তার বিপরীত মেরুতে থাকে বোকামী। “There are two ways to be fooled, One is to believe what isn’t true; the other is to refuse to believe what is true.” (Soren Kierkegaard)।
ক’দিন আগে কুড়ি বছরের একটি মেয়ের আত্মহনন এবং অভাবনীয় অপ্রীতিকর ঘটনায় বিবেকবান মানুষের অন্তর ব্যথিত হয়েছে দারুণ। মেয়েটি তার মৃত্যুর জন্য কাউকে দায়ী করেনি। করেছে, জীবনের প্রতি তার অনাগ্রহকে। ছোট্ট আত্মহনন-চিঠিটা কম্পিত চোখ ও হৃদয়ে পড়েছি কয়েকবার। বার বার ভেসে উঠেছে, একজন প্রতিশ্রুতিময়, ফুলের মতো মেয়ের মুখ। যে কিনা পড়াশোনা শেষে, সুন্দর এক জীবন শুরু করতে পারত। কি এমন বেদনায় ডুবে গিয়েছিল সে, যেখান থেকে আর উঠতে পারলো না কিনারায়! আমাদের তা জানা নেই। তবে, জীবনের মানে যদি জানতে পেত, আর সেই মানেটাকে, সেই অতি মূল্যবান অর্থটাকে আরও অর্থময় করে তোলার পথে নেমে যেত, প্রতিটি পদক্ষেপে ছোট ছোট হোঁচট সামলে সোজা হয়ে চলত, পথের পাথরগুলোকে ফুলের তোড়া ভেবে, কাঁটাগুলো উপেক্ষা করত, ঝোড়ো বাতাসে নুয়ে আসা ডাল দুহাতে সরিয়ে দৃষ্টি দিত দূরে, গন্তব্যে,--- তবে হয়ত আমাদের আর এমন সংবাদ শুনতে হত না।
অনাগ্রহ নিয়ে আত্মহনন ভাবনার পর্যায়ে না গেলেও কারও কারও বেলায়, নিভৃতে, নির্জনে, নিরালায়, অতিগোপন মন-প্রকোষ্টে নিশ্বাস নেবার অনীহা জন্মায়। এমন হতে পারে, সুন্দর চেহারার, সচ্ছল, শিক্ষিত কিংবা সুখের সবরকম উপাদান, উপাচারে পরিপূর্ণ মানুষের জীবনেও। আজকাল, সোসাল মিডিয়ার যুগে, ব্যক্তি জীবনের নানাকথা আর তেমন আড়ালে রাখবার উপায় নেই। নেশার আকারে জুড়ে বসেছে এই জামানার মানুষের দৈনিক-জীবনে। ভরা সংসারেও হাজার হাসি-আলোর মাঝখানেও আঁধার ছেয়ে আসে। সেই আত্ম-অসুখের কথামালা উজাড় করে দেয়, মিডিয়ার আলো’র পর্দায়। কেউ সেগুলোকে সত্যি হিসেবে নেয়, কেউবা ভাবতে পারে মূল্যহীন প্রলাপ বা সময় কাটানোর চটকদার কৌশল। অজানা দুঃখের ভারে পথ চলতে চলতে জীবন থেকে পালিয়ে যাবার উচ্চারণটাই উচ্চকিত হয়ে দেখা দেয় পরিবেশের অনিরাপত্তার কারণে। সেদিনের মেট্রোরেল-পাতের ছুটে যাওয়া কোনো অংশের আঘাতে নিহত দুসন্তানের জনক, যুবকের মৃত্যু, ব্যথায় নির্বাক করেছে আমাদেরকে।
জীবনের প্রতি অপার আকাক্সক্ষা থাকা সত্ত্বেও এর অবসান নেমে আসতে পারে। অমিত সম্ভাবনার দ্বার যার পথের প্রান্তে হা-খোলা হয়ে আছে, তেমন কারো মরণ আসে হঠাৎ। মৃত্যুকে সে ভাবেনি। তেমন করে দেখেওনি আত্মার উড়ান। আপনজনের মৃত্যুর পরপরই তার নিজের জীবনের উজ্জ্বলতাই ঝলসে উঠেছে চোখে। একটিমাত্র সময়কাল আমাদের হাতে। জন্মের পরেই আয়ুর বালুর পটে, ফুরিয়ে আসা বালুকণা ঝরে পড়ছে অবিরাম। সেই ক্ষয়ে আসা সময়পাত্র, সেই তীর ভাঙা নদীর ঢেউয়ে বয়ে যাওয়া নিশ্বাসের হাওয়া কোন্ নিঃশেষের সমুদ্রে পড়ে যাওয়ার আয়োজন করছে, জানি না আমরা। আমাদের আবেদন সীমার মধ্যে থেকে জীবনের সীমানা ফুরিয়ে যায়। তবে, অযথা, অনুচিত ও সীমার অতীত আশা, নিরাশার জন্ম দিতে সহায়তা করে। কেউ একজন বলেছেন যে, ‘মানুষের মন একটা হিজিবিজি জিনিস’। আসলে, এর স্বচ্ছতা সংজ্ঞাহীন। বলা শক্ত যে, মন হলো এই। ‘এই’ জিনিসটা অমাবস্যার চেয়েও অন্ধকার। আলোহীন হাতে পথ চলা কিংবা অন্ধচোখে আকাশে আলোর প্রদীপমালা দেখবার বাসনার নামান্তর। কবি এডগার অ্যালান পো’র কথা মনে হয়, “All suffering originates from craving, from attachment, from desire.”। শেষ নবী (সা.) এমন বলেছেন যে, ‘আদম সন্তান যদি একটি সোনার উপত্যকা পায়, সে আরেকটা চাইবে। তার মুখ মাটি ছাড়া ভরবে না।” তাই, চাওয়া শুধু নয়, --- বিপরীত, বৈরী পরিবেশে স্বর্ণকারের আগুনের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ অলংকারের মতো হতে পারলেই সত্যিকার মানুষ হওয়া যায়। আর যদি স্বাচ্ছন্দ্য, অঢেল অর্থ, অযাঞ্চিত শক্তি-সামর্থ্য, --- এসবের অনুচিত প্রভাববলয়ে বন্দী হয়ে পড়ে কেউ, তাতেই তার সর্বনাশ। ভিকটর হুগো বলেছেন, “Adversity makes men, and prosperity makes monsters.” ।
জীবনের একটা স্বাভাবিক সুখময় দৃশ্য, ছন্দ ও সংগীত আছে। তা দেখবার চোখ খুলে রাখতে হয়। শুনবার কান তৈরি করতে হয়। প্রতিদিন সকালে আঙিনার পাতাবাহারের কোলে, ছোট্ট ছায়ার তলে যে শুভ্ররোদ শুয়ে আছে, --- বাড়ির নিরিহ বেড়ালের মতো; তা দেখতে পারা কি কম আনন্দের? রাতের আকাশের তারা, পূর্ণচাঁদ, ঝিকিমিকি চিত্রল অন্ধকার, এমন মনোহর দৃশ্যে ভরে আছে আমাদের দিনরাত। গ্রীষ্মের দুপুরে, অনেক রোদের পরে, হঠাৎ আকাশের আলো মিলিয়ে মেঘ জমে যায়। একে অপরের গায়ে মিশে মিশে ঘন হয়। একে অন্যের চোখে ঘন কাজল মাখিয়ে দেয়। আনন্দে, মেঘেদের চোখজুড়ে অশ্রু নামে। আর আমরা বলি, বৃষ্টি নামছে। বৃষ্টির সংগীতে মুখর হয় বন, আঙিনার আমড়া গাছ, মাধবীলতা, গন্ধরাজ, আর বাতাবীলেবুর ঘ্রাণপূর্ণ ঘন-সবুজ পাতা। বৃষ্টির মধুর হাতের আদরে আশা ও উচ্ছ্বাসের খই ফোটে শুকনো উঠোনে। এমন সংগীতের কথা বলেছেন, কবি মেরি অলিভার। গল্পধর্মী কবিতায় বর্ণনার বাহারে মন উচাটন হয়। কাহিনিও বেদনাময়। তাঁর পোষা প্রিয় কুকুরের মৃত্যু হয়েছে। চারজন মিলে কবর দিতে নিয়ে যাচ্ছেন বনে। সে যাত্রাটা এমন অন্তর-হরণকারী কথায় সাজানো :
“It took four of us to carry her into the woods.
We did not think of music,
but anyway, it began to rain slowly.”
(Mary Oliver : Her Grave)
অনাগ্রহ নয়, আশাবাদী হয়ে আমরা যেন জীবনের গান শুনতে পারি। প্রকৃতির নির্মল, স্নেহার্দ্র, সুভদ্র সুরগুলো তুলে নিতে পারি আমাদের অজর কণ্ঠে। এই আত্মা অমর। দেহকাঠামো দিয়ে রুখে রাখা। দেহ জীর্ণ হবেই। আজ না হয়, দুদিন পরে। যৌবনের মৃত্যুতে অথবা বয়সের কিনারে এসে। তাই একটিমাত্র জীবনকালের প্রকৃত মানে বুঝে নিই। অমর করে তুলি ধরণীর ধুলিমাখা, অমূল্য অভিনব জীবনটাকে।
লেখক : কবি, কথাসাহিত্যিক, অনুবাদক, প্রবন্ধকার।
প্রাক্তন প্রভাষক, ইংরেজি বিভাগ, ঝিকরগাছা মহিলা কলেজ, যশোর।

দুটি প্রতিবেশী দেশ পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের মধ্যে সাম্প্রতিক সীমান্ত সংঘর্ষ দক্ষিণ এশিয়ার ভূ-রাজনৈতিক স্থিতিশীলতাকে এক নতুন সংকটের মুখে দাঁড় করিয়েছে। উভয় পক্ষের মধ্যেই হতাহতের ঘটনা ঘটেছে এবং উত্তেজনা এখনো চরমে। ইতোমধ্যে এই উত্তাপ নিরসনের জন্য বার কয়েক আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টা হলেও বারবার তা ভেঙে গেছে। যা এই সংকটকে আরও ঘনীভূত করেছে। এই সংঘাত শুধু সীমান্ত পারাপার বা নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয় নয়, এটি দুই দেশের মধ্যে অবিশ্বাস, আস্থার অভাব, দীর্ঘদিনের ঐতিহাসিক টানাপড়েন, সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলায় ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি এবং বহির্বিশ্বের অন্যান্য দেশের ষড়যন্ত্রের শিকার।
পাকিস্তান এবং আফগানিস্তানের সাম্প্রতিক সীমান্ত সংঘাতের একটি বিস্তীর্ণ পটভূমি রয়েছে। যার ভিত্তি মূলত ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক। ডুরান্ড লাইন ১৮৯৩ সালে ব্রিটিশ ভারতের তরফে স্যার হেনরি মর্টিমার ডুরান্ড ও আফগানিস্তানের এমীর আব্দুর রহমান খান এর মধ্যে চুক্তি চিহ্নিত হয়েছিল মূলত ব্রিটিশ ভারতের প্রতিযোগী হিসাবে রাশিয়া-অধিষ্ঠিত ‘গ্রেট গেম’ পরিচালনায়। স্বাধীন পাকিস্তান (১৯৪৭) ওই সীমান্ত লাইন উত্তরাধিকার সূত্রে গ্রহণ করেছিল, কিন্তু আফগানিস্তান আরও পরবর্তী বিভিন্ন সরকারের সময় থেকে এটিকে আন্তর্জাতিক বৈধ সীমান্ত হিসেবে স্বীকার করেনি। এই সীমান্তবর্তী অঞ্চলে বহুয়ান পশতুন জনগোষ্ঠীর বসবাস; যারা ঐতিহ্যগতভাবে পাকিস্তান এবং আফগানিস্তান দুই দেশভুক্ত। এই সমাজে ঐতিহ্য, জনসংখ্যা ও ভাষাগত বন্ধন রয়েছে; যে কারণে সীমান্ত সমস্যা আজও জিইয়ে আছে।
পাকিস্তান-আফগানিস্থান সীমান্ত বরাবর বিশেষত পশ্চিম পাকিস্তানের খাইবার পাখতুনখোয়া ও বালুচিস্তান অঞ্চলে তেহরিক- ই- তালেবান পাকিস্তান (টিটিপি) ও অন্যান্য সশস্ত্র গোষ্ঠীর পাকিস্তানভিত্তিক কার্যক্রমের জন্য আফগান ভূখণ্ড ব্যবহার হয়; যেটি পাকিস্তানের নিরাপত্তার জন্য বড় হুমকি হিসেবে গণ্য।
পাকিস্তান এসব গ্রুপের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নিচ্ছে। সীমান্ত রক্ষা, বেআইনি চাপা প্রবেশ প্রতিরোধ এবং ২০১৭ সাল থেকে সীমান্তরোধ বাঁধ নির্মাণ শুরু করে।
সম্প্রতি পাকিস্তান-আফগানিস্তান সীমান্তে যে সংঘর্ষ শুরু হয়েছে, তা বিগত কয়েক দশকের মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক। সংঘর্ষের সূত্রপাত হয় আফগানিস্তানে পাকিস্তানের বিমান হামলাকে কেন্দ্র করে। ইসলামাবাদ অভিযোগ করে যে, আফগানিস্তানের ভূমি ব্যবহার করে তেহরিক- ই- তালেবান পাকিস্তান (টিটিপি) জঙ্গিরা পাকিস্তানের ভেতরে হামলা চালাচ্ছে, বিশেষত খাইবার পাখতুনখোয়া প্রদেশে। জঙ্গিদের সেই হামলায় পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বেশ কয়েকজন জওয়ান শহীদ হয়েছে। সেই জঙ্গি আস্তানা লক্ষ্য করেই পাকিস্তান তাদের বিমান হামলা চালায়।
পাল্টা হিসেবে আফগান তালেবান বাহিনী সীমান্তে পাকিস্তানের সামরিক চৌকি লক্ষ্য করে হামলা চালায়, যার ফলে উভয় পক্ষেই সেনা হতাহত হয়। আফগানিস্তান এই হামলাকে তাদের সার্বভৌমত্বের লঙ্ঘন বলে অভিহিত করে। এই সংঘর্ষের তীব্রতা এতটাই ছিল যে চামান ও স্পিন বলদাকের মতো গুরুত্বপূর্ণ সীমান্ত ক্রসিংগুলো বন্ধ করে দিতে হয়, যার ফলে সাধারণ মানুষের যাতায়াত ও বাণিজ্যিক কার্যক্রম ব্যাহত হয়। এমনকি আফগানিস্তান পাকিস্তানের সাথে অনুষ্ঠিতব্য ক্রিকেট সিরিজও বাতিল করে।
এত সবকিছুর মূল কারণ পারস্পরিক অবিশ্বাস এবং আন্তর্জাতিক ইন্দন। এই সংঘাতের মূলে রয়েছে পাকিস্তানের অভিযোগ আফগানিস্তানের তালেবান সরকার টিটিপি-কে আশ্রয়-প্রশ্রয় দিচ্ছে। টিটিপি, যা পাকিস্তানি তালেবান নামেও পরিচিত, পাকিস্তানের জন্য এরা বড় নিরাপত্তা হুমকি। ২০২১ সালে আফগানিস্তানে তালেবান ক্ষমতা দখলের পর থেকে পাকিস্তানের অভ্যন্তরে জঙ্গি হামলা বহুগুণে বেড়ে গেছে। পাকিস্তান মনে করে, আফগান তালেবান তাদের মিত্র হওয়া সত্ত্বেও টিটিপি-র বিরুদ্ধে কার্যকর কোনো ব্যবস্থা নিচ্ছে না, বরং তাদেরকে পাকিস্তানবিরোধী কার্যক্রমে উৎসাহ দিচ্ছে। অতিসম্প্রতি আফগানিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর ভারত সফর এবং বিবৃতি প্রদান এই অবিশ্বাসকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে।
অন্যদিকে, আফগান তালেবান সরকার পাকিস্তানের এই অভিযোগ অস্বীকার করে। তাদের দাবি, তারা কারো বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী কার্যক্রম পরিচালনার জন্য আফগান ভূমি ব্যবহার করতে দেয় না। তারা উল্টো পাকিস্তানকে বিমান হামলা চালিয়ে নিরপরাধ বেসামরিক নাগরিক হত্যার জন্য দায়ী করে। এই পাল্টা-অভিযোগ এবং পরস্পরকে দোষারোপ করার প্রবণতা দুই দেশের মধ্যে আস্থার সংকটকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে।
এছাড়াও দুই দেশের মধ্যে ডুরান্ড লাইনকে আন্তর্জাতিক সীমান্ত হিসেবে আফগানিস্তানের স্বীকৃতি না দেওয়াও একটি দীর্ঘদিনের বিবাদের কারণ। যদিও পাকিস্তান এটিকে আন্তর্জাতিক সীমান্ত মনে করে, আফগানিস্তানের তালেবান সরকারসহ পূর্বের সরকারগুলোও এটিকে মানতে নারাজ। এই অচিহ্নিত ও বিতর্কিত সীমান্ত বরাবরই সংঘাতের জন্ম দিয়েছে।
প্রাথমিকভাবে সংঘর্ষ মারাত্মক আকার ধারণ করার পর কাতার এবং সৌদি আরবের মতো মধ্যস্থতাকারীদের উদ্যোগে দুই দেশ ৪৮ ঘণ্টার যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হয়। এই যুদ্ধবিরতির উদ্দেশ্য ছিল উত্তেজনা প্রশমিত করা এবং আলোচনার মাধ্যমে সমাধানের পথ খোঁজা। তবে এই যুদ্ধবিরতির মধ্যেই উত্তর ওয়াজিরিস্তানে পাকিস্তানি সেনা ক্যাম্পে টিটিপি-র আত্মঘাতী হামলা এবং এরপর আফগানিস্তানের অভ্যন্তরে পাকিস্তানের নতুন করে বিমান হামলা চালানো এই সবই যুদ্ধবিরতিকে ভঙ্গুর করে তুলেছে।
এসব ঘটনা স্পষ্ট করে যে, সীমান্ত সংঘর্ষ শুধুমাত্র সামরিক উত্তেজনা নয়, এটি অভ্যন্তরীণ রাজনীতি এবং জঙ্গিগোষ্ঠীর কৌশলের সাথেও গভীরভাবে সম্পর্কিত। টিটিপি যেন এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে দুই দেশের মধ্যে স্থায়ী শান্তি স্থাপনের সম্ভাবনাকে নস্যাৎ করতে চায়।
সংলাপের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে, এই সংকটই হতে পারে শান্তি প্রক্রিয়ার নতুন ট্রিগার: আগের তুলনায় বিশ্বের আনুগত্য ও মধ্যস্থতার আগ্রহ রয়েছে। তবে যদি দ্রুত নিয়ন্ত্রণ না করা হয়, তাহলে এটি আবার বৃহত্তর সামাজিক, অর্থনৈতিক ও নিরাপত্তাগত সঙ্কটে রূপ নিতে পারে — যেমন জঙ্গি পুনরুজ্জীবন, বিএসএম প্রবাহ বৃদ্ধি, মানুষের দুর্দশা বৃদ্ধি ইত্যাদি।
পাকিস্তান-আফগানিস্তানের এই সংঘাত আঞ্চলিক স্থিতিশীলতার জন্য একটি বড় উদ্বেগের কারণ। এই অঞ্চলে শান্তি বজায় রাখার জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় এবং বিশেষত চীন, ইরান ও মধ্য এশিয়ার দেশগুলো গভীরভাবে আগ্রহী। তারা প্রত্যেকেই এই সংঘাতের অবসানের জন্য সংলাপের গুরুত্বের ওপর জোর দিয়েছে। পাকিস্তানের প্রধান মিত্র চীন, যারা আফগানিস্তানের সাথেও সুসম্পর্ক বজায় রাখতে আগ্রহী, তারা উভয় পক্ষকে সংযম দেখানোর আহ্বান জানিয়েছে। আবার, আমেরিকার মতো পশ্চিমা শক্তি যারা সন্ত্রাসবাদ দমনে আগ্রহী, তারাও পরিস্থিতির দিকে নজর রাখছে। তবে, এই সংঘাতের ফলে সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং সীমান্ত এলাকার গ্রামগুলো থেকে শত শত পরিবারকে নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে পালাতে হচ্ছে।
এই জটিল পরিস্থিতিতে সামরিক পদক্ষেপের মাধ্যমে দীর্ঘস্থায়ী শান্তি অর্জন করা প্রায় অসম্ভব। দুই দেশের মধ্যে একমাত্র পথ হলো অর্থপূর্ণ ও টেকসই সংলাপ। আর এই সংলাপের ভিত্তি হবে পারস্পরিক আস্থা এবং বিশ্বাস। টিটিপির মতো জঙ্গিগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সমন্বিত ব্যবস্থা নিতে উভয়কে একমত হতে হবে। আফগানিস্তানকে নিশ্চিত করতে হবে যে তাদের ভূমি থেকে কোনো সন্ত্রাসী গোষ্ঠী পাকিস্তানের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করবে না। ডুরান্ড লাইন ইস্যুতে একটি বাস্তবসম্মত ও গ্রহণযোগ্য সমাধান খুঁজে বের করা জরুরি। সীমান্তকে সুরক্ষিত ও নিয়ন্ত্রিত করার জন্য যৌথ নজরদারি ব্যবস্থা বা সমন্বিত সীমান্ত টহল চালু করা। তদুপরি সংঘাতের কারণে যে সমস্ত বেসামরিক মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, তাদের সুরক্ষা ও মানবিক সহায়তা নিশ্চিত করতে হবে। তবে এই সংকট নিরসনের জন্য কূটনৈতিক পর্যায়ে দোহা-র মতো স্থানে দুই দেশের প্রতিনিধিদের মধ্যে বৈঠক অত্যন্ত জরুরি। শুধুমাত্র রাজনৈতিক সদিচ্ছা এবং পারস্পরিক সহযোগিতা-র মাধ্যমেই এই সংঘাতের স্থায়ী সমাধান সম্ভব। অন্যথায়, এই সীমান্ত সংঘাত শুধু দুই দেশের মধ্যেই নয়, সমগ্র দক্ষিণ এশিয়ায় অস্থিরতা আরও বাড়িয়ে তুলবে। তাছাড়া সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হবে দুই দেশের সাধারণ মানুষ। কেননা সীমান্ত চেকপয়েন্ট বন্ধ হলে সাধারণ বাণিজ্য, মানুষের চলাচল ও সামুদ্রিক সরবরাহ লাইন ব্যাহত হয়। এতে স্থানীয় অর্থনীতি একেবারে ধ্বংস হয়ে যায়।
সর্বোপরি আমি মনে করি, দুই দেশের সীমান্তের উত্তেজনা শুধুই দুদেশের মধ্যকার বিষয় নয়—এটি দক্ষিণ এশিয়ার বৃহত্তর ভূ-রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকেও গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এখানে রয়েছে বড় জঙ্গি সংগঠন, আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্ক এবং শক্তির সমীকরণ। যেমন: পাকিস্তান-চিন-ইরান-মধ্য এশিয়ার দেশগুলো এ অঞ্চলে স্থিতিশীলতার স্বার্থ রাখে; অপর দিকে আফগানিস্তানে যুক্তরাষ্ট্রেরও নেটওয়ার্ক ভিত্তিক যোগাযোগ রয়েছে। ভারত, যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন ভুক্ত অনেক দেশই নিজেদের স্বার্থ রক্ষায় এই সংঘর্ষের আগুনকে আরো প্রজ্জ্বলিত করার জন্য ঘি ঢালতে প্রস্তুত। তাছাড়া পাকিস্তান এবং আফগানিস্তান উভয়েই মুসলিম দেশ হওয়ার তাদের মধ্যে অনৈক্য এবং বিভেদ সৃষ্টির সুযোগ অনেকেই হাতছাড়া করতে চাইবে না। মুসলিম বিশ্ব এমনিতেই সমগ্র বিশ্ব জুড়ে নানাবিধ সমস্যায় জর্জরিত। তাই আমি মনে করি, কিছুটা ছাড় দিয়ে হলেও মুসলিম উম্মাহর বৃহত্তর কল্যাণে এই সংঘাত যত দ্রুত সম্ভব মিটিয়ে ফেলা উচিত। অন্যথায় এই আগুনে কেবল পাকিস্তান এবং আফগানিস্তান পুড়বে না; জাতি হিসাবে মুসলমানদের মধ্যে অনৈক্য এবং বিভেদ চূড়ান্ত মাত্রায় ছড়িয়ে পড়বে। মুসলিম বিশ্বের জন্য যার পরিণতি হবে অত্যন্ত মারাত্মক।
লেখক; জসীম উদ্দীন মুহম্মদ, কবি, কথাসাহিত্যিক, প্রাবন্ধিক, কলামিস্ট এবং সহযোগী অধ্যাপক, সরকারি আনন্দ মোহন কলেজ, ময়মনসিংহ।

António Guterres ২০২৬ সালের শেষ দিন (৩১ ডিসেম্বর ২০২৬) তার দ্বিতীয় পাঁচ বছরের মেয়াদ শেষ করবেন।
জেনারেল অ্যাসেম্বলি ও নিরাপত্তা পরিষদে নতুন রুল-বিধি গৃহীত হয়েছে মহাসচিব নির্বাচন প্রক্রিয়ায় — উদাহরণস্বরূপ, প্রার্থীদের অবশ্যই তাদের ফান্ডিং উৎস প্রকাশ করতে হবে, নির্বাচনী সময়সূচি নির্ধারণ করা হয়েছে, এবং “নারীর সম্ভাব্যতা” উদ্দিষ্ট করা হয়েছে।
ইতোমধ্যে কয়েকজন প্রার্থী নাম ঘোষণা করেছে:
Latin America অঞ্চলের দেশগুলো দীর্ঘদিন ধরে দাবি করে আসছে যে এবার এই জায়গাটি তাদের পালা, কারণ গত কয়েকবার হয় অন্যান্য অঞ্চলের নাগরিকই হয়েছে মহাসচিব।
যুক্তরাষ্ট্র জানিয়ে দিয়েছে তারা ‘বিশ্বব্যাপী’ প্রার্থীর খোঁজে, শুধুই নির্দিষ্ট অঞ্চলের নয় — তবে এই বক্তব্যকে ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলো ‘আমাদের পালা’ দাবি হিসেবে দেখছে। সংক্ষেপে বিশ্লেষণ করার চেস্টা করছি,
দেশগুলোর বিন্যাস বিবেচনায় গুরুত্বপূর্ণ।
বাংলাদেশের জন্য এর অর্থ
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ ধ্বংসযজ্ঞের পর মানবসভ্যতা যখন টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছিল, তখনই ১৯৪৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় জাতিসংঘ— মানবতার শান্তি ও ন্যায়ের পতাকা হাতে। উদ্দেশ্য ছিল, ভবিষ্যতে যেন আর কোনো বিশ্বযুদ্ধ না ঘটে, যেন আলোচনা ও সহযোগিতার মাধ্যমে রাষ্ট্রগুলো পার্থক্য মিটিয়ে নিতে পারে। কিন্তু আট দশক পার হয়ে আজ বিশ্ববাসীর মুখে একটাই প্রশ্ন— জাতিসংঘ আসলেই কি সেই নিরপেক্ষ ন্যায়বিচারের মঞ্চ, নাকি এটি পরিণত হয়েছে বিশ্বশক্তির স্বার্থরক্ষার একটি কূটনৈতিক পর্দায়?
🔹 নিরাপত্তা পরিষদ: ভেটোর ফাঁদে ন্যায়বিচার
জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ (UNSC) হলো সংস্থাটির সবচেয়ে ক্ষমতাধর অঙ্গ। এখানে পাঁচ স্থায়ী সদস্য— যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, রাশিয়া, চীন ও ফ্রান্স— এককভাবে প্রস্তাব ভেটো করতে পারে। এই এক ‘ভেটো’ শব্দটাই আজ জাতিসংঘের সবচেয়ে বড় সংকটের প্রতীক।
কোনো যুদ্ধবিরতি, মানবাধিকার তদন্ত, কিংবা অস্ত্রবিরোধী প্রস্তাব— এসব কিছুই প্রায়ই আটকে যায় এই পাঁচ দেশের রাজনৈতিক স্বার্থে।
সিরিয়া যুদ্ধ, ইউক্রেন সংঘাত কিংবা গাজা উপত্যকার গণহত্যা— প্রতিটি ক্ষেত্রেই দেখা গেছে, নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাব শক্তিধরদের ভেটোতে থমকে গেছে। রাশিয়া যেমন ইউক্রেন প্রসঙ্গে নিজের অবস্থান রক্ষায় ভেটো দিয়েছে, তেমনি যুক্তরাষ্ট্র ইসরায়েল ইস্যুতে বহুবার ভেটো ব্যবহার করেছে।
ফলাফল— নিরীহ মানুষের মৃত্যু, ধ্বংস আর নির্বিকার জাতিসংঘ।
🔹 সাধারণ পরিষদের সীমাবদ্ধতা
জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে ১৯৩টি সদস্য রাষ্ট্রের সমান ভোটাধিকার থাকলেও, এখানকার সিদ্ধান্তগুলো বাধ্যতামূলক নয়। তাই বাস্তব প্রভাব খুব সীমিত।
উদাহরণস্বরূপ, গাজা যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব সাধারণ পরিষদে পাস হলেও তা বাস্তবায়িত হয়নি, কারণ নিরাপত্তা পরিষদের অনুমোদন ছাড়া কোনো পদক্ষেপ নেওয়া যায় না।
এভাবে ছোট দেশগুলোর কণ্ঠস্বর প্রায়ই হারিয়ে যায় বড় শক্তির স্বার্থের কাছে।
জাতিসংঘের মূল মঞ্চে ‘সবার সমান অধিকার’ থাকলেও বাস্তবে ক্ষমতা নিয়ন্ত্রিত থাকে কিছু রাষ্ট্রের হাতে।
🔹 মহাসচিব নির্বাচন: নেপথ্যের কূটনীতি
জাতিসংঘের মহাসচিবকে বলা হয় ‘বিশ্বের নৈতিক নেতা’। কিন্তু এই পদটিও রাজনীতির জটিল হিসাবের বাইরে নয়। নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যদের অনুমোদন ছাড়া কেউ মহাসচিব হতে পারেন না।
অতএব, প্রার্থীকে হতে হয় কূটনৈতিকভাবে ‘নিরাপদ’— এমনভাবে কথা বলতে হয় যেন কোনো বড় শক্তি ক্ষুব্ধ না হয়।
আগামী মহাসচিব নির্বাচনের আলোচনাতেই এটি স্পষ্ট। চিলির মিশেল ব্যাচেলেট, আর্জেন্টিনার রাফায়েল মারিয়ানো গ্রোসি, বুলগেরিয়ার ইরিনা বোকোভা, এবং লাইবেরিয়ার এলেন জনসন স্যারলিফ— এদের প্রত্যেকেই আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্য, কিন্তু কাউকেই ‘অতি নিরপেক্ষ’ বলা যায় না।
কারণ, একেকজনের পেছনে একেকটি ব্লকের সমর্থন রয়েছে। ফলে যিনি নির্বাচিত হবেন, তাকেও সেই ভারসাম্য রক্ষা করতে হবে— মানবতার জন্য নয়, বরং রাজনীতির ভারসাম্যের জন্য।
🔹 উন্নয়ন ও অনুদানের রাজনীতি
জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থা যেমন UNDP, WHO, UNESCO, UNICEF— এসবই মানবিক উন্নয়নের প্রতীক। কিন্তু বাস্তবে এসব তহবিলের বড় অংশ আসে ধনী দেশগুলোর অনুদান থেকে। ফলে অনুদানদাতা দেশের রাজনৈতিক অগ্রাধিকারই অনেক সময় নির্ধারণ করে কোন অঞ্চলে প্রকল্প হবে, কোথায় হবে না।
আফ্রিকার দারিদ্র্য, ইয়েমেনের দুর্ভিক্ষ, কিংবা রোহিঙ্গা সংকট— অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়, সাহায্যের প্রতিশ্রুতি থাকলেও কার্যকর সহায়তা আসে না।
এভাবেই মানবিকতার চেয়ে রাজনীতি বড় হয়ে দাঁড়ায়, এবং জাতিসংঘের নৈতিক অবস্থান প্রশ্নবিদ্ধ হয়।
🔹 যুদ্ধ বন্ধে জাতিসংঘের ভূমিকা: আশার চেয়ে হতাশা বেশি
বর্তমানে ইউক্রেন ও গাজা— এই দুই যুদ্ধই জাতিসংঘের সক্ষমতার কঠিন পরীক্ষা।
ইউক্রেনে রাশিয়ার আগ্রাসনের পর একাধিক প্রস্তাব আনা হলেও রাশিয়ার ভেটো ব্যবহারে সব থেমে যায়। অপরদিকে গাজা উপত্যকায় ইসরায়েলের বোমা হামলায় হাজারো বেসামরিক নিহত হলেও নিরাপত্তা পরিষদ কার্যকর কোনো পদক্ষেপ নিতে পারেনি।
সাধারণ পরিষদের বিবৃতিতে যুদ্ধবিরতির আহ্বান এসেছে, কিন্তু তা বাস্তবে প্রভাব ফেলেনি।
বিশ্ববাসী তাই এখন প্রশ্ন করছে— জাতিসংঘ কি কেবল বিবৃতি দেয়ার সংস্থা?
যদি যুদ্ধ থামাতে না পারে, যদি মানবতা রক্ষা করতে না পারে, তবে এই সংস্থার প্রয়োজনীয়তা কোথায়?
এক জরিপে দেখা গেছে, ইউরোপ ও লাতিন আমেরিকার মাত্র ৪৫ শতাংশ মানুষ জাতিসংঘের প্রতি ‘পূর্ণ আস্থা’ রাখে। আফ্রিকায় এই হার কিছুটা বেশি, প্রায় ৬০ শতাংশ। কিন্তু মধ্যপ্রাচ্য ও দক্ষিণ এশিয়ায় আস্থার হার নেমে এসেছে ৩০ শতাংশে। অর্থাৎ, জাতিসংঘের নৈতিক অবস্থান ক্রমেই দুর্বল হচ্ছে।
🔹 বাংলাদেশের দৃষ্টিকোণ থেকে জাতিসংঘ
বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্য হয় ১৯৭৪ সালে। প্রতিষ্ঠার পর থেকেই শান্তি, উন্নয়ন ও মানবতার পক্ষে জাতিসংঘে সক্রিয় ভূমিকা রেখে আসছে।
বাংলাদেশ জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা মিশনে অন্যতম শীর্ষ অবদানকারী দেশ। বর্তমানে প্রায় ৭,০০০ বাংলাদেশি সেনা ও পুলিশ সদস্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশে শান্তিরক্ষায় নিয়োজিত।
এটি শুধু বাংলাদেশের ভাবমূর্তি বাড়ায়নি, বরং জাতিসংঘে দেশের কণ্ঠস্বরকে জোরালো করেছে।
তবে বাংলাদেশের জন্য জাতিসংঘের ভূমিকা অনেক সময় হতাশাজনকও হয়েছে।
রোহিঙ্গা সংকটে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের নিষ্ক্রিয়তা, জলবায়ু অর্থায়নের বিলম্ব, কিংবা গাজা যুদ্ধের নীরবতা— এসবই জাতিসংঘের সীমাবদ্ধতাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখায়।
বাংলাদেশ চায়, জাতিসংঘ যেন উন্নয়নশীল দেশগুলোর প্রকৃত কণ্ঠস্বর হয়ে ওঠে, শুধুমাত্র বড় শক্তির মঞ্চ না থাকে।
🔹 সংস্কারের দাবি ও ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জ
বিশ্ব এখন বহুমেরুকেন্দ্রিক— শুধু পশ্চিমা দুনিয়া নয়, চীন, ভারত, ব্রাজিল, দক্ষিণ আফ্রিকা প্রভৃতি দেশও বৈশ্বিক প্রভাবশালী শক্তি।
তাই জাতিসংঘের কাঠামোতে পরিবর্তন সময়ের দাবি হয়ে উঠেছে। আফ্রিকা, এশিয়া ও লাতিন আমেরিকার দেশগুলো দীর্ঘদিন ধরে বলছে— নিরাপত্তা পরিষদে নতুন স্থায়ী সদস্য যুক্ত করতে হবে, ভেটো ক্ষমতা সীমিত করতে হবে, এবং সংস্থার নেতৃত্বে বৈচিত্র্য আনতে হবে।
এই সংস্কার ছাড়া জাতিসংঘ আর বিশ্ববাসীর আস্থা ফেরাতে পারবে না।
🔹 জাতিসংঘের সামনে পথচলা
জাতিসংঘের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে তিনটি বিষয়ের ওপর—
যদি এই তিনটি ক্ষেত্রে জাতিসংঘ কার্যকর হতে না পারে, তাহলে সংস্থাটির অস্তিত্ব শুধু নামমাত্র হয়ে যাবে। বিশ্বকে তখন নতুন কোনো সমন্বিত কাঠামোর প্রয়োজন পড়বে, যেমনটা জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার আগের যুগে দেখা গিয়েছিল।
জাতিসংঘের রাজনীতি আজ ন্যায়বিচার ও বাস্তবতার সংঘাতে দাঁড়িয়ে। একদিকে বিশ্বজুড়ে যুদ্ধ, শরণার্থী সংকট, জলবায়ু বিপর্যয়; অন্যদিকে ভেটো আর কূটনীতির দেয়াল।
তবুও জাতিসংঘ ছাড়া মানবজাতির বিকল্প কোনো বৈশ্বিক কাঠামো এখনো নেই।
বিশ্ববাসী তাই আশা ছাড়তে চায় না— একদিন হয়তো জাতিসংঘ সত্যিই তার মূল প্রতিশ্রুতির জায়গায় ফিরে যাবে।
যুদ্ধ নয়, আলোচনাই সমাধান— এই মূলমন্ত্র যদি আবার সক্রিয়ভাবে বাস্তবায়িত হয়, তবে জাতিসংঘ আবার হতে পারে ন্যায় ও মানবতার প্রকৃত আশ্রয়স্থল।
আর যদি তা না হয়, তবে শান্তির প্রতীক এই সংস্থাই একদিন হয়ে উঠবে শক্তির প্রতীক— ইতিহাস তখন সেটাকেই কঠিনভাবে বিচার করবে।
লেখক: ড. আজিজুল আম্বিয়া, কলাম লেখক ও গবেষক।