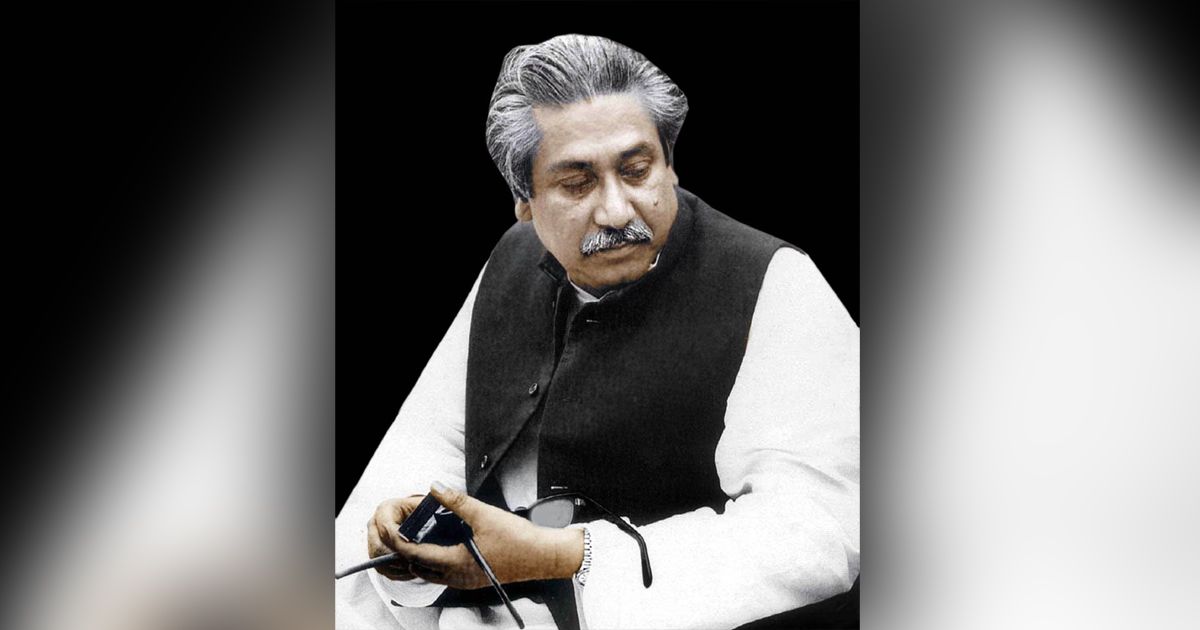
স্বাধীন বাংলাদেশের যাত্রা যখন শুরু হয়, সেই সময় বাংলাদেশের অর্থনীতিসহ সবকিছুই ছিল বিধ্বস্ত। দেশের অবকাঠামো ছিল ধ্বংসপ্রাপ্ত, কৃষি খাত স্থবির ও শিল্পকারখানা বন্ধ। উল্লেখ্য, শিল্পের ক্ষেত্রে বেশির ভাগ শিল্পের মালিকরা ছিল পাকিস্তানি, যারা যুদ্ধকালীন অথবা বিজয়ের প্রাক্কালে এ দেশ ছেড়ে চলে যায়। বাংলাদেশি মালিকানাধীন শিল্পকারখানাগুলোও যুদ্ধের কারণে বন্ধ ছিল। পাশাপাশি বাংলাদেশের প্রশাসনিকব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে ভেঙে পড়েছিল। একই সঙ্গে দেশের উন্নয়নের প্রয়োজনে ব্যয় করার মতো অর্থ ব্যাংকে ছিল না। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ছিল শূন্যের কোঠায়। সেই বিধ্বস্ত অবস্থা থেকে দেশের উন্নয়নের জন্য কার্যকর এবং সঠিক পরিকল্পনার খুবই প্রয়োজন ছিল।
বঙ্গবন্ধু রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব গ্রহণের পর দেশ পুনর্গঠনের কাজ শুরু করেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল যত দ্রুত সম্ভব অর্থনৈতিকভাবে দেশকে ঘুরে দাঁড়ানোর ব্যবস্থা করা। সেই সময় দেশের দারিদ্র্য পরিস্থিতি ছিল ভয়াবহ। শরণার্থী হিসেবে ভারতে গমনকারী প্রায় এক কোটি মানুষ বিপন্ন অবস্থায় দেশে ফিরে আসে। তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করাও সরকারের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ ছিল। যুদ্ধকালীন দেশের অভ্যন্তরে অসংখ্য মানুষের আর্থিক অবস্থাও ভেঙে পড়েছিল। রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব গ্রহণের পর বঙ্গবন্ধুর প্রথম কাজই ছিল এই অবস্থা থেকে দেশ ও দেশের মানুষের উত্তরণ ঘটানো। অবশ্যই দেশ পরিচালনার জন্য একটি আইনি কাঠামো জরুরি ছিল তাই তিনি সংবিধান রচনায় মনোযোগ দেন এবং বিজয়ের মাত্র ৯ মাসের মধ্যে একটি জনকেন্দ্রিক দূরদর্শী সংবিধান জাতিকে উপহার দেন। প্রণীত সংবিধানে রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য ৪টি মৌল নীতিনির্ধারণ করা হয়। এগুলো হচ্ছে: (১) বাঙালি জাতীয়তাবাদ, (২) গণতন্ত্র, (৩) সমাজতন্ত্র ও (৪) ধর্ম নিরপেক্ষতা বা অসাম্প্রদায়িকতা। এই ৪টি মৌল নীতিকে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলভিত্তি হিসেবে চিহ্নিত করা হলো। তিনি প্রশাসনিকব্যবস্থা, নীতিনির্ধারণী ব্যবস্থা এবং অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিকব্যবস্থা গড়ে তোলার দিকে নজর দিলেন এবং একই সঙ্গে দেশের অবকাঠামো পুনর্বাসন এবং অর্থনৈতিক পুনর্গঠনে হাত দিলেন। অবকাঠামোগত উন্নয়ন, কৃষি উন্নয়ন, দারিদ্র্য নিরসন, ব্যাপকভিত্তিক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা, এসব বিষয়ে অগ্রাধিকার দেয়া হলো। অর্থাৎ সাধারণ মানুষের পুনর্বাসন ও উন্নয়নে জোর দেয়া হলো। পাশাপাশি অবশ্য অন্যান্য খাতের পুনর্বাসন ও উন্নয়নে পদক্ষেপ নেয়া হলো। ১৯৭০ সালের নির্বাচনী ইস্তেহারের ঘোষণা অনুসারে তিনি বড় বড় শিল্পকারখানা, ব্যাংক ও বিমা রাষ্ট্রীয়করণ করেন। তবে কুটির ও অতিক্ষুদ্র শিল্প ও ব্যবসায় ব্যক্তি খাতে সম্প্রসারণের উদ্যোগ নেয়া হয়। তবে এসব কর্মকাণ্ড হতে হবে পরিকল্পিত অন্যথায় অগ্রগতি সমন্বিত ও সবার জন্য, বিশেষ করে পিছিয়েপড়া মানুষের জন্য যথাযথ সুফল বয়ে আনবে না। তাই তিনি পরিকল্পিত উন্নয়নের ব্যবস্থা করার লক্ষ্যে পরিকল্পনা কমিশন গঠন করে একটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা তৈরির দায়িত্ব দিলেন।
পরিকল্পনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যানকে মন্ত্রীর পদমর্যাদা দেয়া হয়। সদস্যদের প্রতিমন্ত্রীর মর্যাদা দেয়া হয়। ডেপুটি চেয়ারম্যান ছিলেন অধ্যাপক নুরুল ইসলাম আর সদস্য ছিলেন অধ্যাপক মোশাররফ হোসেন, অধ্যাপক রেহমান সোবহান এবং অধ্যাপক আনিসুর রহমান। গঠিত কমিশনকে দায়িত্ব দেয়া হলো সংবিধানে বিধৃত চার মূলনীতির আলোকে খুব দ্রুততার সঙ্গে পাঁচ বছর মেয়াদি একটি উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে। প্লানিং কমিশনে যাদের দায়িত্ব দেয়া হলো তারা সবাই দেশের খ্যাতিমান অর্থনীতিবিদ এবং কোনো না কোনোভাবে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন। প্লানিং কমিশনের সদস্যরা বঙ্গবন্ধুর চিন্তা-ভাবনা সম্পর্কে অনেকটাই অবহিত ছিলেন। বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক দর্শন এবং চাওয়া তাদের জানা ছিল। ফলে তাদের পক্ষে বঙ্গবন্ধুর চাওয়ার মতো পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের কাজটি সহজ হয়। আমাকেও কোনো কোনো কাজে সম্পৃক্ত করা হয়েছিল। আমি মুক্তিযুদ্ধ থেকে ফিরে বিআইডিএসে কর্মরত ছিলাম।
বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন দর্শনের মূল ভিত ছিল এই যে উন্নয়ন হতে হবে মানবকেন্দ্রিক। অর্থাৎ উন্নয়ন হতে হবে দেশের সব শ্রেণি-পেশার মানুষকে উপলক্ষ করে। তবে বিশেষ নজর দিতে হবে দুঃখী মানুষের দিকে। দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে হবে। স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে বলা হয়েছিল, সবার সব মানবাধিকার নিশ্চিত, বৈষম্যহীন সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা এবং সব মানুষের মানব-মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করা হবে, সেই কথাও তিনি সংশ্লিষ্ট সবাইকে স্মরণ করিয়ে দেন। চূড়ান্ত পর্যায়ে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করাই ছিল বঙ্গবন্ধুর মূল উদ্দেশ্য। কিন্তু সেই সময়ে দেশে বিরাজমান বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কাজটি খুব একটা সহজ ছিল না। তৎকালীন সমাজব্যবস্থা, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিক বাস্তবতা যে স্তরে ছিল সেই অবস্থায় সরাসরি সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা কঠিন ছিল, বলা চলে অসম্ভবই ছিল। তাই জোর দেয়া হয় সমাজতন্ত্রের পথ রচনা করার দিকে।
উন্নয়ন পরিকল্পনা রচনা করতে একদিকে যেমন রাজনৈতিক লক্ষ্য ও দিকনির্দেশনা প্রয়োজন তেমনি তথ্য ও বাস্তবতা বিশ্লেষণের প্রয়োজন। রাজনৈতিক চাহিদা বঙ্গবন্ধুর কাছ থেকে বিশদভাবে পাওয়া যায়। তবে তথ্য ও বাস্তবতার বিশ্লেষণে নানা রকম ঘাটতি ছিল। পরিকল্পনা কমিশন এ ক্ষেত্রে সম্ভাব্য সব পদক্ষেপ গ্রহণ করে। যেহেতু পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা দ্রুত তৈরি করতে হবে, তাই দীর্ঘমেয়াদি কোনো গবেষণা কাজ হাতে নেয়া সম্ভব ছিল না। কেননা, তাতে দীর্ঘ সময় ব্যয় করতে হতো। আর সেরকম সময় হাতে ছিল না। তবে অবশ্যই পরবর্তী সময়ে প্রয়োজনে নতুন তথ্য ও বিশ্লেষণপ্রাপ্তি সাপেক্ষে পরিবর্তন করার সুযোগ সব সময় থাকে। তাই নজর দেয়া হয় যে সব তথ্য জোগাড় করা সম্ভব সেগুলো সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করার দিকে। এভাবেই একটি গ্রহণযোগ্য তথ্য ও বিশ্লেষণ ভিত্তি দাঁড় করিয়ে সেই ভিত্তিতে বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক দিকনির্দেশনা অনুযায়ী একটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা দেড় বছরের মধ্যে তৈরি করা হয়। দলিলটি বিশ্লেষণ, বিন্যাস এবং প্রাপ্ত রাজনৈতিক দিকনির্দেশনা অনুযায়ী দেশের বিধ্বস্ত আর্থসামাজিক অবস্থা থেকে উত্তরণ এবং এগিয়ে চলার কর্মপন্থা ও কর্মসূচি তুলে ধরা হয়। দলিলটি সুলিখিত ও সুবিন্যস্ত।
সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে, সেই লক্ষ্য সামনে রেখে একটি গুরুত্বপূর্ণ্ দিকে বিশেষ নজর দেয়া হয়। বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, সোনার বাংলা গড়তে হলে সোনার মানুষ চাই। বস্তুত সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার জন্য চিন্তা-চেতনা ও মননে সেই দর্শন ধারণ করে এমন প্রয়োজনীয় সংখ্যক ক্যাডারের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু তখন সেরকম ক্যাডারের সংখ্যা ছিল নগণ্য। তাই প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এমন ক্যাডার গড়ে তোলার দিকে বিশেষ গুরুত্ব দেয় ও দিকনির্দেশনা প্রদান করেন।
এই প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আকার ছিল ৪ হাজার ৪৫৫ কোটি টাকা এবং অ-আর্থিক বিনিয়োগ ধরা হয়েছিল আরও ৫৮৫ কোটি টাকা। পাকিস্তান আমলে ১৯৬৫-৭০ সালভিত্তিক তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের জন্য পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আকার থেকে ১৫ শতাংশের মতো বেশি ধরা হয় বিরাজমান বাস্তবতা বিবেচনায় নিয়ে। অবশ্যই দলিলটি সমাজতন্ত্রে উত্তরণকে সামনে রেখে তৈরি করা হয়। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে মোট ব্যয়ের ৪০ শতাংশ বৈদেশিক সাহায্য থেকে আসবে বলে ধরা হয়েছিল। তবে এ কথা জোর দিয়ে বলা হয়েছিল যে, ক্রমান্বয়ে অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণ বাড়ানো হবে এবং বিদেশ-নির্ভরতা কমিয়ে আনা হবে এবং সেভাবে স্বনির্ভরতার দিকে দেশ এগিয়ে চলবে। সেই লক্ষ্যে পরিকল্পনা দলিলে দিকনির্দেশনা ও পদক্ষেপ অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সমাজতন্ত্রের পথে এগিয়ে চলার অভীষ্টের পরিপ্রেক্ষিতে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মোট ব্যয়ের ৮৯ শতাংশ রাষ্ট্রীয় খাতে বরাদ্দ ছিল।
একদিকে প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা রচিত হতে থাকল কিন্তু বঙ্গবন্ধু তাঁর মানুষকেন্দ্রিক উন্নয়ন দর্শনের আলোকে দেশটির বিধ্বস্ত আর্থসামাজিক অবস্থার পুনর্গঠন ও জাগরণ-প্রক্রিয়া এগিয়ে নিতে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করলেন।
অবকাঠামো পুনর্বাসন ও উন্নয়নে অগ্রাধিকার দিয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। যে অসংখ্য রাস্তাঘাট, সেতু, কালভার্ট যুদ্ধের সময় বিধ্বস্ত হয়েছিল সেগুলোর দ্রুত পুনর্বাসন করা হয়। দুই-আড়াই বছরের মধ্যে সড়ক, নৌ ও রেল যোগাযোগব্যবস্থায় উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন করা হয়।
লক্ষণীয়, কৃষি খাতের জন্য বঙ্গবন্ধু নানা ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। জমির সর্বোচ্চ সিলিং পরিবারপ্রতি ১০০ বিঘা নির্ধারণ করে দেয়া হয়। একই সঙ্গে ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মওকুফ করা হয়। পাকিস্তান আমলে কৃষকদের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত প্রায় ১০ লাখ সার্টিফিকেট মামলা প্রত্যাহার করা হয়। কৃষকদের নতুন করে ঋণ দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়। টেস্ট রিলিফ ১৬ কোটি এবং তাকাবি ঋণ ১০ কোটি টাকা দেয়া হয়। আরও ৫ কোটি টাকা দেয়া হয় সমবায় ঋণ হিসেবে। বীজ সরবরাহ ও কৃষি যান্ত্রিকরণেও পদক্ষেপ নেয়া হয়।
প্রায় সব বড় শিল্প, ব্যাংক ও বিমা রাষ্ট্রীয়করণ করা হয়। সমাজতান্ত্রিক উন্নয়নের একটি করণীয় হিসেবেই। পাকিস্তানি মালিকাধীন যে প্রতিষ্ঠাগুলো তারা ফেলে চলে গিয়েছিল সেগুলো তো বটেই। বাঙালি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানগুলোও রাষ্ট্রীয়করণ করা হয়। কুটির ও অতিক্ষুদ্র শিল্প ও ব্যবসায় ব্যক্তিমালিকানায় সম্প্রসারণে সহযোগিতা করা হয়। এ ছাড়া পাট ও পাটজাত দ্রব্যাদির রপ্তানি পুনর্বাসন ও সম্প্রসারণে জোরালো পদক্ষেপ নেয়া হয়।
আন্তজার্তিক পরিমণ্ডলে অন্যান্য দেশের স্বীকৃতি আদায়ে বঙ্গবন্ধু দ্রুত অগ্রগতি সাধন করেন। মাত্র সাড়ে তিন বছরে তিনি শতাধিক রাষ্ট্রের স্বীকৃতি অর্জন করেন। তা সম্ভব হয়েছিল প্রধানত তাঁর ক্যারিসমা, ব্যক্তিত্ব ও রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতার ফলে।
তিনি ১৯৭৫ সালের প্রথম দিকে সবাইকে ন্যায্যভাবে অন্তর্ভুক্ত করে উন্নয়ন-প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে সারা দেশে সমবায়ভিত্তিক উন্নয়ন সাধনের পরিকল্পনা ঘোষণা করেন। প্রত্যেক গ্রামে একটি করে সমবায় গঠন করা হবে। গ্রামের সবাইকে এতে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। ঘোষণা করা হয় কারও জমি কেঁড়ে নেয়া হবে না, যারা জমির মালিক তারা আয় থেকে একটি অংশ পাবেন। যারা জমিতে চাষাবাদ করবেন তারা আয়ের একটি অংশ পাবেন। আর রাষ্ট্র একটি অংশ পাবে। এসবই হবে সমবায়ের মাধ্যমে। সবার অধিকার নিশ্চিত করে গ্রামের সার্বিক উন্নয়নই ছিল লক্ষ্য। এটা ছিল এক যুগান্তকারী পরিকল্পনা। কিন্তু এর বাস্তবায়ন পদ্ধতি নির্ধারণ করে এই লক্ষ্য বাস্তবে রূপ দেয়ার সময় তিনি পাননি।
সেই সময় দেশে দারিদ্র্যের হার ছিল ৮০ শতাংশের মতো। তাই প্রতিটি কর্মসূচিকে দারিদ্র্য বিমোচনকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়া হয়। বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন দেশে অতি ধনি কেউ হবে না এবং অনেক পিছিয়েও কেউ থাকবে না। দেশে সাম্য প্রতিষ্ঠা করা হবে, ন্যায্যতা নিশ্চিত করা হবে, দেশ উন্নতির পথে এগিয়ে চলবে এবং প্রত্যেক মানুষ মানব-মর্যাদায় জীবনযাপন করবে। পরিকল্পিত পথ-পরিক্রমায় সমাজতন্ত্রের লক্ষ্য অর্জন নিশ্চিত করা হবে।
ঘাতকরা বঙ্গবন্ধুকে তাঁর জনকল্যাণে মহৎ কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করার সময় দেয়নি। আমি তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে গভীর শ্রদ্ধা জানাই এবং তাঁর মাগফিরাত কামনা করি।
অনুলিখন: এম এ খালেক
লেখক: অর্থনীতিবিদ, উন্নয়ন চিন্তাবিদ, সভাপতি; ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবিধানিক ইনস্টিটিউট ঢাকা স্কুল অব ইকোনমিক্স ও সভাপতি; পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন।

সঙ্গত কারণেই বর্তমানে মর্মস্পর্শী ও হৃদয় ছোঁয়া বিষয়কে ঘিরে এলিজা কার্সনকে নিয়ে লিখতে বসেছি। এ মেয়েটি আমাদের পৃথিবীর প্রথম অভিযাত্রী, যে ২০৩৩ সালে মঙ্গলগ্রহের উদ্দেশ্যে রওনা হবে। সে ভালো করে জানে, হয়তো আর ফিরে আসবেনা এই প্রিয় জন্মভূমি পৃথিবীতে। আর মাত্র ৯ বছর পরে একমাত্র নিঃসঙ্গ মানুষ হিসেবে কোটি কোটি মাইল দূরের লোহার লালচে মরিচায় ঢাকা প্রচণ্ড শীতল নিষ্প্রাণ গ্রহের ক্ষীয়মাণ নীল নক্ষত্রের মধ্যে হারিয়ে যাবে। তবে তাতে ভীত নয় সে। ভাবতে অবাক লাগে, মানুষের স্বপ্ন কত বিশাল! এলিজা কার্সন নিজে সেই দুঃসাহসিক স্বপ্ন দেখে এবং একই সঙ্গে মানুষকে স্বপ্ন দেখাতে শেখায়। সে বলে- ‘সর্ব সময় আপনার লালিত স্বপ্ন ভিত্তি করে চলুন এবং এমন কিছুকে প্রশ্রয় দেবেন না, আপনার স্বপ্ন থেকে হেলাতে পারে বা নষ্ট করে দিতে পারে।
আসলেই মা জননীবিহীন সিঙ্গেল প্যারেন্ট হিসেবে কেবল বাবা বার্ট কার্সনের আদরেই বড় হয়ে উঠেছে এলিজা। এই ছোট মেয়েটি হয়তো মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে, এ পৃথিবীতে আগমন কেবল খাওয়া ও ঘুমানোর জন্য নয়। আরও অনেক কিছু মহৎ কাজ আছে, যা মানব কল্যাণকে ঘিরে করতে হয়। আর তাই ঝুঁকিপূর্ণ কাজ সামনে রেখে জীবন অতিবাহিত করে থাকেন মহামানবরা। অথচ সাধারণ মানুষ তা করে না। কারণ সাধারণ মানুষ আন্তঃকেন্দ্রিক এবং নিজেদের চাওয়া-পাওয়া ও ভোগবিলাসের মধ্যে ব্যতিব্যস্ত রাখে। সত্যি কথা বলতে কি, এ বিশ্বের সৃষ্টির গোড়া থেকে মানব কল্যাণার্থে এ ধরনের কতিপয় অধিমানব জীবন উৎসর্গ করে এগিয়ে এসেছেন বলেই আমরা আজ নানা রকম সুযোগ-সুবিধা ভোগ করছি। অথচ দুঃখের বিষয় হলো, আমরা সাধারণ মানুষের খুব কম সংখ্যকই তাদের শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি এবং কৃতজ্ঞতাভরে মনে করি। স্মরণকাল থেকে এ ধরনের এরকম অনেক অধিমানব বা মহামানব থাকলেও আমি অত্র প্রবন্ধের কলেবরের স্বার্থে নিম্নে কেবল জনাকয়েক অধিমানবের কথা তুলে ধরছি, যারা সৃষ্টি জগৎ তথা মানুষের জন্য জীবন বাজি রেখে তথা জীবন দিয়েও অবদান রেখে গেছেন।
প্রথমে যার কথা দিয়ে শুরু করছি। তিনি হলেন- গ্রিক পণ্ডিত আর্কিমিডিস। প্রাচীন গ্রিকের এই গাণিতিক ও বিজ্ঞানী জন্মেছিলেন ইতালির ভূমধ্যসাগরীয় দ্বীপ সিসিলির সাইরাকিউস নামে একটি ছোট রাজ্যে। পাটিগণিত, জ্যামিতি এবং হাইড্রলিক্সে তার অবদানের জন্য আজও স্মরণীয়। অথচ গবেষণারত অবস্থায় তার করুণ মৃত্যু হয় মাথামোটা একজন রোমান সৈনিকের ধারাল তরবারির আঘাতে। দ্বিতীয়ত, যার কথা উঠে আসে, তিনি হলেন মহান জ্যোতির্বিজ্ঞানী জিওদার্নো ব্রুনো। অতি সত্যি কথা বলায় তাকে হাত-পা বেঁধে রোমের রাজপথে নির্মমভাবে পুড়িয়ে মারা হয়েছিল। কি বলেছিলেন ব্রুনো? কি ছিল তার অপরাধ? তিনি বলেছিলেন, পৃথিবী সূর্যের চারপাশে ঘুরছে। এই পৃথিবী সৌরজগতের কেবল তুচ্ছ গ্রহ ছাড়া আলাদা কোনো গুরুত্ব নেই। আর পৃথিবী ও বিশ্বজগৎ চিরস্থায়ী নয়, এক দিন এসব ধ্বংস হয়ে যাবে। অথচ অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে, ব্রুনোর সেই চিরসত্যর ওপরই ভিত্তি করে সূর্যের চারদিকে ঘূর্ণায়মান আমাদের সাধের পৃথিবী। তৃতীয়ত, যার কথা বলছি তিনি হলেন মধ্যযুগের জগদ্বিখ্যাত বিজ্ঞানী গ্যালিলিও, যিনি আট বছর ধরে বন্দিদশায় অন্ধ হয়ে পড়েছিলেন এবং আশি বছর বয়সে দীর্ঘ সময় ধরে কারাগারে ধুঁকে ধুঁকে মারা যান। কী এমন দোষ করেছিলেন সর্বকালের অন্যতম সেরা এই বিজ্ঞানী? তিনি শুধু কোপার্নিকাসের মতবাদ প্রচার করেছিলেন এবং যুগপৎ বলেছিলেন, ব্রুনোকে অন্যায়ভাবে হত্যা করেছে মূর্খ যাজকেরা। এ জন্য তাকে একবার মাফ চাইতে হয়েছিল। ওয়াদা করতে হয়েছিল, চার্চ ও বাইবেলবিরোধী কিছু বলবেন না; কিন্তু সে কথা রাখতে পারেননি গ্যালিলিও। জ্বলজ্বলে তারার মতো সত্যকে উপেক্ষা করে তিনি কীভাবে মিথ্যা বলবেন? কীভাবে অন্ধকারকে আলো বলে চালিয়ে দেবেন। আর তাই গ্যালিলিও সত্যের এ জয়গান করে গেয়েছিলেন আজীবন এবং বলেছিলেন যে সূর্য নয়, পৃথিবীই সূর্যের চারপাশে ঘোরে। তারপর যার কথা উঠে আসে, তিনি ইতিহাসখ্যাত নারী বিজ্ঞানী ম্যারি কুরি, যে সময়টাতে সারা পৃথিবীতেই মেয়েরা ছিল অনেক পিছিয়ে। অথচ সে সময় ম্যারি কুরি বিশ্ববাসীকে এনে দিয়েছেন অসংখ্য অর্জন। পোলান্ডে জন্ম নেওয়া ম্যারি দুটি উপাদানের আবিষ্কারের জন্য নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন। তবে প্রথমবার নোবেল পেয়েছিলেন পদার্থবিজ্ঞানে (রেডিওঅ্যাক্টিভিটি বা তেজস্ক্রিয়তা নিয়ে গবেষণার জন্য) আর এর মাত্র ৮ বছরের মাথায় দ্বিতীয় নোবেল পুরস্কার পান রসায়নে। অথচ এই আবিষ্কার ছিল মারাত্মকভাবে স্বাস্থ্যের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ ও বিপজ্জনক। এই আবিষ্কারে ম্যারি কুরি এবং তার স্বামী পেয়েরি কুরি এতটাই স্বাস্থ্যগত ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছিলেন, এই পৃথিবী থেকে অচিরেই বিদায় নিতে হয়েছিল। এ ছাড়া এ ধরনের অনেক প্রতিভাধর সৃষ্টিধর্মী ও উদ্যোগী মহৎপ্রাণ, এভাবে পৃথিবী থেকে অকালেই চির বিদায় নিয়েছেন। যারা হলেন রবার্ট ককিং, অটো লিলিয়েনথাল, অরেল ভিলাইকু, উইলিয়াম বুলোক, আলেকজান্ডার বগডানোভ, হেনরি থুআইল, ম্যাক্স ভ্যালিয়ার, প্রমুখ। এরা কেবল মানুষের কল্যাণে জীবন উৎসর্গ করেছেন। সত্যি কথা বলতে কি, এসব অধিমানব মানবজাতির মঙ্গলের জন্য আবিষ্কার করতে গিয়ে নির্দ্বিধায় জীবন দিয়েছেন। আশ্চর্যর বিষয় হলো, আমরা তাদের আবিষ্কারের ফল ভোগ করে চলেছি। অথচ তাদের কথা এতটুকু ভাবী না এবং মনেও রাখি না।
এবার আসুন আমাদের প্রতিপাদ্য বিষয় এলিজা কার্সনের কথায় ফিরে আসি। এই ছোট মেয়েটি নাসার কনিষ্ঠতম সদস্য। ৭ বছর বয়সে বাবা তাকে নিয়ে গিয়েছিলেন আলবামার একটি স্পেস ক্যাম্পে। সেই ক্যাম্পের অভিজ্ঞতা তাকে এমনভাবে নাড়িয়ে দিয়েছিল যে তার ভাবনার জগৎটাই অন্য শিশুদের চেয়ে আলাদা হয়ে যায়। এদিকে এলিজার যখন ৯ বছর বয়স, তখন তার সঙ্গে দেখা হয় নাসার এক মহাকাশচারী সান্ড্রা ম্যাগনাসের সঙ্গে। এই নারী মহাকাশচারী তাকে জানিয়েছিলেন ছোটবেলাতেই তিনি মহাকাশে যাওয়ার স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিলেন বলেই বর্তমানে এ অবস্থায় এসে পৌঁছেছেন। এই কথাটি ছোট্ট এলিজার মনে দাগ কেটে যায়। এতে মহাকাশে যাওয়ার স্বপ্ন তার অন্তরে আরও শেকড় গেড়ে বসে। উল্লেখ্য, মাত্র ১২ বছর বয়সেই এলিজা আলবামা, কানাডার কুইবেক ও তুরস্কের ইজমিরে নাসার তিনটি ভিন্ন ভিন্ন স্পেস ক্যাম্পে অংশ নেন। এর মধ্যে মহাকাশের বেসিক জ্ঞান অর্জনের পাশাপাশি বিভিন্ন মিশন কীভাবে পরিচালিত হয়, তা সে রপ্ত করে ফেলে। এ ক্ষেত্রে মহাকর্ষ-শূন্য স্থানে চলাচল করার পদ্ধতি, ভারহীন স্থানে থাকার উপায়, রবোটিক্স সম্পর্কে জ্ঞান এবং বিশেষ মুহূর্তে জরুরি সিদ্ধান্ত নেওয়ার দক্ষতা ইত্যাদি অর্জন করে। মজার ব্যাপার হলো, তার এই অভাবনীয় কাজের জন্য নাসার পক্ষ থেকে তাকে একটি ‘কল নেম’ও দেওয়া হয়, যা হলো ‘ব্লুবেরি’।
যেহেতু সে মঙ্গলে গেলে ফিরে আসার সম্ভাবনা খুবই কম। সোজা কথায় সে ফিরে আসতে চাইলেও আর আসতে পারবে না। তাই নাসার কাছে সে কোনো প্রকার যৌনতা, বিয়ে বা সন্তানধারণের নিষেধাজ্ঞাপত্রতে স্বাক্ষর করেছে। এদিকে অফিসিয়ালি নাসা ১৮ বছরের আগে কাউকে নভোচারী হিসেবে আবেদন করার সুযোগ দেয় না। তবে এলিজার ক্ষেত্রে এ নিয়ম মানা হয়নি। ১১ বছর বয়সেই তাকে মনোনীত করা হয়েছে। প্রথম থেকেই প্রতিষ্ঠানটি এলিজাকে মানুষের ভবিষ্যতে মঙ্গলগ্রহে অভিযানের জন্য জোর সমর্থন করে তৈরি করতে সচেষ্ট হয়েছে। উল্লেখ্য, ২০৩৩ সালে যখন মঙ্গলগ্রহে প্রথমবার মানুষ পাঠানোর অভিযান শুরু হবে, তখন এলিজার বয়স হবে ৩২, যা একজন নভোচারীর জন্য যথাযথ বয়স। অবশ্য এলিজার মঙ্গলগ্রহে অভিযান নিয়ে নেতিবাচক কথাও শোনা যাচ্ছে। পরিশেষে এই বলে ইতি টানছি, সত্যিই যদি ২০৩৩ সালে এলিজা মঙ্গলগ্রহের উদ্দেশে রওনা হয় সে ক্ষেত্রে প্রায় ৮০০ কোটি পৃথিবীবাসীর পক্ষ থেকে আগাম মোবারকবাদ জানাচ্ছি। আর অবস্থাদৃষ্টে প্রতীয়মান হয়, সে হয়তো আর এই পৃথিবীতে ফিরে আসতে পারবে না। তথাপিও পৃথিবীবাসীর জন্য যে উদ্দেশে যাচ্ছে, সেটা যেন পূরণ হয়। তা হলে তার আত্মা পরিপূর্ণতার শান্তিতে ভরে উঠবে।
লেখক: বিশিষ্ট গবেষক, অর্থনীতিবিদ এবং লেখক হিসেবে মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সম্মাননা ও পদকপ্রাপ্ত

বাংলাদেশে বর্তমান সরকার টানা চতুর্থবারের মতো ক্ষমতায় এসেছে। মন্ত্রিপরিষদে ব্যাপক রদবদল হয়েছে। অর্থমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রী দুজনই নতুন এসেছেন এবং তাদের যথেষ্ট ইতিবাচক ভাবমূর্তি রয়েছে, যা গত কিছুদিনের মধ্যেই তারা প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছেন। আওয়ামী লীগ সরকারের গত মেয়াদের শেষের দিকে নতুন কারিকুলাম এসেছে। এই কারিকুলামকে বাস্তবায়ন করতে এখন দরকার যথাযথ পদক্ষেপ ও নীতিমালার। বিশেষ করে অবকাঠামোতে ব্যাপক পরিবর্তন করতে হবে। শিক্ষকদের জন্য আলাদা পে-স্কেল এখন সময়ের দাবি। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ‘ভিশন ২০৪১’ ঘোষণা করেছেন, যা ‘ডিজিটাল বাংলাদেশ’-কে ‘স্মার্ট বাংলাদেশে’ রূপান্তরিত করবে। ‘ডিজিটাল বাংলাদেশ’ এখন বাস্তব; কিন্তু ‘স্মার্ট বাংলাদেশ’ যদি সময়মতো করতে চাই তাহলে অর্থ বরাদ্দ শুধু বাড়ালেই হবে না, সেই অর্থের যথাযথ ব্যয় ও দুর্নীতি সর্বাংশে দমন করতে হবে। নতুন শিক্ষামন্ত্রী শপথ নেওয়ার পরের দিনই দুর্নীতি নিয়ে কথা বলেছেন। এর সঙ্গে ইউজিসির সুপারিশ কার্যকর করতে হবে।
বর্তমান ২০২৩-২৪ অর্থবছরের জন্য বাজেটে শিক্ষা এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে টাকার অঙ্কে বরাদ্দ বাড়লেও, শতকরা হারে তা কমেছে। শিক্ষাব্যবস্থার দেখভালকারী শিক্ষা এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন কার্যক্রমের জন্য এবার যে বরাদ্দ প্রস্তাব করা হয়েছিল, তা জাতীয় বাজেটের ১১ দশমিক ৫৭ শতাংশ, যা আগের অর্থবছরে ছিল ১২ শতাংশের মতো। অবশ্য শিক্ষার সঙ্গে প্রযুক্তি খাতের বরাদ্দ যোগ করলে এই হার দাঁড়ায় ১৩ দশমিক ৭ শতাংশ। শিক্ষাসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা দীর্ঘদিন ধরে জাতীয় বাজেটের প্রায় ২০ শতাংশ অর্থ শিক্ষা খাতে বরাদ্দের দাবি জানিয়ে আসছেন। তবে অতীতের মতো এবারও দাবিটি পূরণ হয়নি, বরং বরাদ্দের হার কমে ২০ শতাংশ থেকে বেশ দূরেই আছে। উন্নত বিশ্বে এই বরাদ্দ ২০ শতাংশের আশপাশে। কোনো কোনো দেশে এর পরিমাণ আরও বেশি। বিশেষ করে ইউরোপের দেশগুলোতে। পৃথিবীর উন্নয়নশীল দেশ থেকে যারা উন্নত দেশে পরিণত হয়েছে বা হওয়ার পথে; তাদের বেশির ভাগেরই শিক্ষা খাতের বরাদ্দ অনেক বেশি। এদিকে জাতিসংঘের মতে, কোনো দেশের বাজেটের ২০ শতাংশ বা জিডিপির ৬ শতাংশ শিক্ষা খাতে বরাদ্দ করা উচিত। বিপরীতে আমাদের দেশের শিক্ষা খাতে জিডিপির ২ দশমিক ৬ থেকে ৭ শতাংশের বেশি বরাদ্দ দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না।
আশার কথা, ইতোমধ্যেই ২০০৯ থেকে ২০২৩ পর্যন্ত সময়ে ৩৫১টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও ৩৭১টি কলেজ জাতীয়করণ, সরকারি বিদ্যালয়বিহীন ৩১৫টি উপজেলা সদরে অবস্থিত বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে মডেল স্কুলে রূপান্তরণ, জেলা সদরে অবস্থিত সরকারি পোস্ট গ্র্যাজুয়েট কলেজে ১৮০টি ভবন নির্মাণ করাসহ নানামুখী উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। আশা করা যায়, সরকারের নেওয়া চলমান উদ্যোগগুলো রূপকল্প ২০৪১ এবং জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার চতুর্থ লক্ষ্য, ‘সবার জন্য মানসম্মত শিক্ষা’ অর্জনে সহায়ক হবে।
প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, ‘আমাদের শিক্ষার মান অনেক উন্নত হয়েছে। শিক্ষার মান আরও উন্নত করে আমরা বিশ্বমানের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে চাই। এটা আমাদের লক্ষ্য এবং এটি অর্জনে আমাদের কাজ করতে হবে।’ প্রধানমন্ত্রীর উদ্যোগ, শিক্ষাকে বহুমাত্রিক করার অংশ হিসেবে প্রতিটি জেলায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা, চারটি বিভাগীয় সদরে চারটি মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা, ইসলামিক আরবি বিশ্ববিদ্যালয়, ডিজিটাল বিশ্ববিদ্যালয়, অ্যারোস্পেস এবং এভিয়েশন বিশ্ববিদ্যালয় এবং মেডিকেল কলেজের পাশাপাশি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।
সরকারকে কিছু ক্ষেত্রে ধীরে চলো নীতিতে চলতে হচ্ছে। তার মধ্যে শিক্ষাও একটি। কারণ বিশ্ববাজার অস্থির। সবার আগে দ্রব্যমূল্য ঠিক রাখতে হবে। সবকিছু আমাদের হাতেও নেই। ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধ। ইসরাইলে-ফিলিস্তিনির সঙ্গে আরব বিশ্বের বর্তমান অবস্থা। এই টালমাটাল সময়ে, যেখানে সারা বিশ্বের বেশির ভাগ দেশেই শিক্ষার্থীদের বিরাট একটি অংশ, বিশেষ করে উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা মানবিকতার জয়গান গাইছেন। সব ধরনের যুদ্ধ বন্ধের জন্য বিক্ষোভ করছেন। সেই সময়ে বাংলাদেশে শিক্ষকের বিচার করতে হচ্ছে।
যৌন হয়রানির কারণে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্রীর আত্মহত্যা অসংখ্য যৌন হয়রানির ঘটনাকে সামনে এনেছে। এখন অনেক ছাত্রীই মুখ খুলছে। অনেকগুলোর তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেওয়া হলেও প্রশ্নটা হলো, যেসব শিক্ষক এর সঙ্গে জড়িত তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হওয়ার কোনো যোগ্যতা রাখেন কী? সুষ্ঠু তদন্ত হলে এমন শত শত কেস সামনে এসে হাজির হবে। যদি ইউজিসির সুপারিশ কার্যকর করা হতো তবে এমন ঘটনা ঘটার সুযোগ কম থাকত। কারণ নিয়োগ প্রক্রিয়া খুব গুরুত্বপূর্ণ।
বুয়েটে রাজনীতি থাকবে নাকি থাকবে না? এই নিয়ে শুধু বুয়েট নয় বাংলাদেশের এ বিষয়ে খোঁজখবর যারা রাখেন তারা দুই ভাগে ভাগ হয়ে গেছেন। পড়ার বদলে সেখানে আন্দোলন হচ্ছে। প্রশ্ন হলো- বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পেছনে রয়েছে ছাত্র রাজনীতি। বুয়েটে আবরার ফাহাদকে হত্যা করা হয়েছিল এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। ছাত্রলীগের নেতা-কর্মী এ ঘটনা ঘটিয়েছিল এটি নিয়েও সন্দেহের অবকাশ নেই। সেই থেকে সেখানে ছাত্র রাজনীতি বন্ধ। পোকা ধরা ফলের জন্য কী গাছটাই কেটে ফেলতে হবে? বরং ছাত্র রাজনীতি না থাকার কারণে বুয়েট এখন মৌলবাদের আঁতুরঘরে পরিণত হয়েছে। টাঙ্গুয়ার হাওরের ঘটনা আপনাদের মনে আছে?
এবার একটু ইতিবাচক কথায় আসা যাক। আমাদের সমস্যা অনেক। এই সমস্যার সমাধান আমাদেরই করতে হবে। ইউজিসির কথামতো যদি বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগটা হতো তাহলে এ সমস্যাগুলোর বেশির ভাগই সমাধান হয়ে যেত। ছাত্র রাজনীতিকে জাতীয় রাজনীতির সঙ্গে মিশে যাওয়াটাই সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে।
‘স্মার্ট বাংলাদেশে’ শিক্ষা থেকে শুরু করে সব বিষয়ের আধুনিক পরিবর্তন বাংলাদেশকে বঙ্গবন্ধুর কাঙ্ক্ষিত ‘সোনার বাংলা’ করে গড়ে তুলতে সক্ষম হবে। সংবিধানে স্পষ্টত উল্লেখ আছে সমাজের প্রয়োজনের সঙ্গে শিক্ষাকে সঙ্গতিপূর্ণ করার কথা এবং সেই প্রয়োজন পূরণ করার উদ্দেশ্যে যথাযথ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও সদিচ্ছাপ্রণোদিত নাগরিক সৃষ্টির কথা- যেখানে জড়িত রয়েছে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন। বর্তমানে বাংলাদেশে সময়ের সঙ্গে উচ্চশিক্ষা বিস্তারের পথ বৃদ্ধি পাচ্ছে। দ্রুতগতিতে বেড়ে উঠছে স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়। বর্তমানে বাংলাদেশের প্রায় প্রত্যেকটি জেলাতেই উচ্চশিক্ষা বিস্তারে অন্ততপক্ষে একটি করে বিশ্ববিদ্যালয় তৈরির কথা আমাদের প্রধানমন্ত্রী সব সময় বলে আসছেন এবং বাস্তবায়ন করছেন যা অত্যন্ত সম্ভাবনাপূর্ণ ও আশাব্যঞ্জক। পৃথিবীর আর অন্যকোনো দেশে উচ্চশিক্ষার এমন প্রসার সহজেই চোখে পড়ে না। যার জন্য আমরা সব সময় গর্বিত। তবে একটি বিষয় আমাদের একটু খেয়াল রাখতে হবে এই বিপুল পরিমাণ উচ্চশিক্ষিত সমাজকে কীভাবে সম্পদে পরিণত করা যায়, যা দেশের জন্য মঙ্গল বয়ে আনবে।
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশে একটি জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতি গড়ে তুলতে মানসম্মত উচ্চশিক্ষার গুরুত্বকে অনুধাবন করেছিলেন। সে লক্ষ্যে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন ১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর প্রতিষ্ঠিত হয়, যা পরবর্তীকালে ১৯৭৩ সালে রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ১০-এর মাধ্যমে উচ্চশিক্ষার সর্বোচ্চ স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসাবে বিধিবদ্ধ হয়। সেই সময়ে ইউজিসির কার্যক্রম ছিল তৎকালীন ছয়টি বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক প্রয়োজনীয়তা ও চাহিদা নিরূপণ। সময়ের সঙ্গে বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষার পরিধি ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করেছে। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার আগে চারটি বিশ্ববিদ্যালয় (সাধারণ ক্যাটাগরির) প্রতিষ্ঠিত হয়: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (১৯২১), রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৫৩), চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৬৬) ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৭০)। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর প্রতিষ্ঠিত প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৮০)। বিশেষ ক্যাটাগরির দুটি বিশ্ববিদ্যালয় দেশ স্বাধীন হওয়ার আগে প্রতিষ্ঠিত হয়: বর্তমান বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৬১) ও বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৬২)। বর্তমানে বাংলাদেশে সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ৫৬। কিন্তু বিশাল জনবহুল দেশে এই সংখ্যাটা প্রয়োজনের তুলনায় কম। আর এ জন্যই সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এবং বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এখন পর্যন্ত দেশে অনুমোদিত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ১১৪। ১৪টি বিশ্ববিদ্যালয় নানা কারণে শিক্ষা কার্যক্রম শুরু না করতে পারলেও ৯৯টি বিশ্ববিদ্যালয় তাদের শিক্ষা কার্যক্রম অব্যাহত রেখে চলেছে।
বর্তমানে বাংলাদেশে শিক্ষার হার ৭৪ দশমিক ৬৫ শতাংশ, যেখানে পুরুষ ৭৬ দশমিক ৫৬ শতাংশ এবং নারী ৭২ দশমিক ৪২ শতাংশ রয়েছে। পরিসংখ্যানে দেখা যায়, শিক্ষায় নারীরাও পুরুষের তুলনায় পিছিয়ে নেই। ২০২৩ সালের গ্লোবাল ইনডেক্স অনুযায়ী সমগ্র বিশ্বে উচ্চশিক্ষায় বাংলাদেশের অবস্থান ১১২তম। শিক্ষক সংখ্যা, শিক্ষার হার ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান যাই হোক না কেন, শিক্ষার গুণগত মানই স্মার্ট বাংলাদেশ গঠনে সাহায্য করতে পারে।
এই গুণগতমান বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকার অনকেগুলো সময়োপযোগী ও প্রশংসনীয় পদক্ষেপ নিয়েছে। এ ক্ষেত্রে কিছু চ্যালেঞ্জও রয়েছে। প্রাথমিক থেকে উচ্চমাধ্যমিক পর্যন্ত নতুন কারিকুলামের যথাযথ বাস্তবায়ন করতে হবে। অবকাঠামো বৃদ্ধি করতে হবে। যথাযথভাবে জাতীয়করণ করতে হবে। শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধি করতে হবে। প্রয়োজনে শিক্ষকদের জন্য আলাদা বেতনকাঠামো করতে হবে। যা সময়ের দাবিও। এই কারিকুলামের জন্য যোগ্য ও দক্ষ শিক্ষক আমাদের কমই আছে। যথাযথ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিটি প্রতিষ্ঠানকেও নিজ উদ্যোগে ইনহাউস প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। ক্লাসরুম থেকে ল্যাবের সংখ্যার দিকে গুরুত্ব দিতে হবে। উপাচার্য নিয়োগে আরও দূরদর্শী হওয়া প্রয়োজন। উপাচার্য থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয়ে সব ধরনের নিয়োগে ইউজিসির সুপারিশ বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে সহায়ক গুণগত ও মানসম্পন্ন উচ্চশিক্ষার পরিবেশ নিশ্চিতকল্পে সরকারের পাশাপাশি আমাদের সবার দায়িত্ব রয়েছে।
বিশ্ববিদ্যালয় হলো নতুন নতুন জ্ঞান সৃজন ও বিতরণের কেন্দ্র। আমি মনে করি সরকার, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ইউজিসি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ এবং ইন্ডাস্ট্রিগুলো সম্মিলিতভাবে কাজ করলে বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন জ্ঞান সৃষ্টি, উদ্ভাবন, প্রায়োগিক গবষেণা ও দক্ষ গ্র্যাজুয়েট তৈরির মাধ্যমে ভিশন ২০৪১ সহজেই বাস্তবায়ন করা সম্ভব। কোনো ধরনের অপপ্রচার ও গুজবে কান না দিয়ে এবং প্রধানমন্ত্রীর প্রতি আস্থা রেখে আমাদের নিজ নিজ ক্ষেত্রে সততা ও নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করলে বাংলাদেশ অচিরেই হবে জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা। আমাদের মেধাবী তরুণরাই হবে সোনার মানুষ। আর সেই সোনার মানুষ তৈরির সূতিকাগার হবে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো।
লেখক: সদস্য, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি)

সারা বিশ্বে মানুষের মধ্যে কায়িক পরিশ্রমের প্রবণতা কমছে। আর রোগ-ব্যাধির প্রবণতা বাড়ছে। যেকোনো বয়সের মানুষের শরীর ঠিক রাখতে ব্যায়ামের কোনো বিকল্প নেই। তবে সব ব্যায়াম সব বয়সের জন্য উপযোগী নয় এবং সব বয়সে সব ধরনের ব্যায়াম সম্ভবও নয়; কিন্তু হাঁটা এমন একটি ব্যায়াম, যা যেকোনো বয়সের নারী-পুরুষের জন্য সহজেই সম্ভব, মানানসই, উপযোগী এবং এর মতো সহজ, ভালো ব্যায়াম আর নেই। হাঁটার উপকারিতাও অনেক। উপযুক্ত পোশাক এবং এক জোড়া ভালো জুতা ছাড়া কোনো অতিরিক্ত খরচের প্রয়োজন পড়ে না, ঘরে-বাইরে যেকোনো জায়গায় করা যায়। ব্যক্তির শারীরিক ক্ষমতা অনুযায়ী এর সময় এবং তীব্রতা বাড়ানো-কমানো যায়।
হাঁটা নিয়ে হয়েছে বিস্তর গবেষণা, যার ফলাফল চমকপ্রদ। যারা নিয়মিত হাঁটা-চলার মধ্যে থাকেন, তাদের আলাদা ব্যায়ামের দরকার হয় না, যদিও সম্ভব হলে অন্যান্য ব্যায়াম করা উচিত। যারা সারা দিন অনেকক্ষণ ধরে এক জায়গায় বসে বসে কাজ করেন এবং অলস জীবনযাপন করেন, তাদের অবশ্যই কিছু সময় হলেও একটু একটু করে হাঁটা-চলা এবং ব্যায়াম করা দরকার। শীতকালে এটা আরও বেশি জরুরি। এতে শরীরের রক্ত চলাচল বাড়ে, উচ্চরক্তচাপ, শারীরিক স্থূলতা, ডায়াবেটিস, স্ট্রোক, এমনকি হৃদরোগের ঝুঁকি কমাতেও সহায়তা করে, শরীর থাকে সচল আর মন-মেজাজ থাকে ফুরফুরে।
ডায়াবেটিস রোগীর উপকার: ডায়াবেটিস রোগীর ব্যায়ামের বিকল্প নেই। সকাল-সন্ধ্যা নিয়মিত হাঁটা-চলা, হাট-বাজারে বা অল্প দূরত্বে রিকশা বা গাড়ি ব্যবহার না করা, অল্প কয়েক তলার জন্য লিফট ব্যবহার না করে হেঁটে ওঠা বা নামা ইত্যাদির মাধ্যমে ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ সম্ভব। প্রতিদিন ৩০ মিনিট করে সপ্তাহে পাঁচ দিন বা সপ্তাহে মোট ১৫০ মিনিট হাঁটলে এবং শরীরের ওজন ৭ শতাংশ কমালে টাইপ টু ডায়াবেটিস হওয়ার আশঙ্কা কমে প্রায় শতকরা ৫৮ ভাগ। আর যদি ডায়াবেটিস হয়েই থাকে, তবে তা নিয়ন্ত্রণে রাখতেও হাঁটা বিশেষ কার্যকর। হাঁটাহাঁটি করলে শরীরের পেশিতে ইনসুলিনের কার্যকারিতা বাড়ে এবং রক্তের সুগার কমে, ওষুধ লাগে কম।
ওজন নিয়ন্ত্রণ: নিয়মিত হাঁটলে শরীরে জমে থাকা মেদ কমে, ওজন কমাতে সহায়ক হয়। অনেকেই শরীরের ওজন কমাতে শুধু ডায়েটিং করেন; কিন্তু হাঁটাহাঁটি না করে বা অলস জীবনযাপন করে শুধু ডায়েট কন্ট্রোলের মাধ্যমে ওজন কমানো সম্ভব নয়, উচিতও নয়। দীর্ঘমেয়াদি ওজন নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচির মূল চাবিকাঠি স্বাস্থ্যকর, সুষম খাবার এবং নিয়মিত হাঁটা-চলা ও ব্যায়াম।
হৃদযন্ত্রের কার্যকারিতা: নিয়মিত হাঁটলে হৃদযন্ত্রের কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি পায়, ফলে স্বল্প চেষ্টায় শরীরে বেশি পরিমাণে রক্ত সরবরাহ করতে পারে এবং ধমনির ওপরও চাপ কম পড়ে। উচ্চ রক্তচাপ হওয়ার আশঙ্কা থাকে কম। এ ছাড়া রক্তনালির দেয়ালে চর্বি জমে কম। ফলে রক্তনালি সরু হয় না, সহজে ব্লক হয় না, রক্তনালির দেয়াল শক্ত হয় না। তাই হৃদরোগের কারণে মৃত্যুর ঝুঁকি কমে প্রায় ৩৫ থেকে ৫০ শতাংশ। কমে যায় স্ট্রোকের ঝুঁকিও, উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণেও সহায়ক।
উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ: রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণের অন্যতম চাবিকাঠি হচ্ছে নিয়মিত ব্যায়াম বা হাঁটা। রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতে হাঁটা-চলা অনেকটা উচ্চ রক্তচাপরোধী ওষুধের মতো কাজ করে। হাঁটার ফলে উচ্চ রক্তচাপ হওয়ার ঝুঁকি কম থাকে, আর আগে থেকেই থাকলে তা নিয়ন্ত্রণে রাখে।
রক্তের চর্বি বা কোলেস্টেরল: নিয়মিত হাঁটার ফলে ভালো কোলেস্টেরল বা এইচডিএল বাড়ে। হাঁটা-চলা না করলে মন্দ কোলেস্টেরল বা এলডিএলের পরিমাণ বেড়ে, তা ধমনির গায়ে জমা হয়ে হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি বাড়িয়ে তোলে। যারা সপ্তাহে অন্তত তিন ঘণ্টা অথবা দৈনিক আধা ঘণ্টা করে হাঁটেন, তাদের রক্তে এলডিএল কমে যায় এবং হৃদরোগ হওয়ার ঝুঁকি অন্যদের চেয়ে ৩০ থেকে ৪০ শতাংশ কমে।
স্ট্রোকের ঝুঁকি হ্রাস: মস্তিষ্কের রক্তক্ষরণ বা স্ট্রোকের অন্যতম একটি রিস্ক ফ্যাক্টর হচ্ছে অলস জীবনযাপন করা, স্থূলতা বা অতিরিক্ত মোটা হওয়া। হাঁটা-চলা বা ব্যায়ামের মাধ্যমে শরীরের মেদ কমে যায়, ওজন নিয়ন্ত্রণে আসে। ফলে স্ট্রোকের ঝুঁকিও কমে আসে। দৈনিক এক ঘণ্টা করে সপ্তাহে পাঁচ দিন হাঁটার মাধ্যমে স্ট্রোকের ঝুঁকি শতকরা ৫০ ভাগ কমে যায়।
কর্মক্ষমতা: হাঁটার সময় হৃদস্পন্দন ও শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি এবং রক্ত সরবরাহ বাড়ে, এগুলো বেশি কর্মক্ষম থাকে। হাঁটার ফলে পেশিতে রক্ত সরবরাহ বাড়ে এবং পেশির শক্তি বাড়ে। শরীরের ওজন কমে। শরীর থাকে ফিট। নিজেকে মনে হয় বেশি শক্তিশালী, মন থাকে প্রফুল্ল এবং সার্বিকভাবে বেড়ে যায় শরীরের কর্মক্ষমতা।
ক্যানসারের ঝুঁকি: কিছু কিছু ক্যানসারের ঝুঁকি হাঁটা-চলার মাধ্যমে কমানো সম্ভব বলে অনেক গবেষণায় দেখা গেছে। ব্রিটিশ জার্নাল অব ক্যানসার স্টাডিতে প্রকাশিত এক গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, হাঁটার ফলে খাদ্যনালির নিম্নাংশের ক্যানসারের ঝুঁকি ২৫ শতাংশ হ্রাস পায়, দীর্ঘমেয়াদি কোষ্ঠকাঠিন্য দূর হয়, কমে যায় কোলন বা বৃহদান্ত্রের ক্যানসারের আশঙ্কাও।
অস্টিওপোরোসিস বা হাড়ের ক্ষয়রোগ: বয়স্ক পুরুষদের এবং পোস্ট-মেনোপজাল বা মাসিক বন্ধের পর নারীদের সাধারণ রোগ হচ্ছে অস্টিওপোরোসিস বা হাড়ের ক্ষয়রোগ। এই রোগে হাড় দুর্বল ও ভঙ্গুর হয়ে যায়। সামান্য আঘাত বা অল্প উচ্চতা থেকে পড়ে গিয়ে ভেঙে যেতে পারে হাড়। নিয়মিত হাঁটা-চলা এ ক্ষেত্রে উপকারী ভূমিকা রাখতে পারে। গবেষণায় দেখা গেছে, যেসব পোস্ট-মেনোপজাল নারী প্রতিদিন অন্তত এক মাইল হাঁটেন, তাদের হাড়ের ঘনত্ব কম হাঁটা নারীদের তুলনায় বেশি। হাঁটার ফলে যেমন হাড় ক্ষয়ের প্রবণতা হ্রাস পায়, তেমনি আর্থ্রাইটিসসহ হাড়ের নানা রোগ হওয়ার আশঙ্কাও কমে যায়।
মানসিক স্বাস্থ্য: হাঁটলে মস্তিষ্কে ভালো লাগার কিছু পদার্থ যেমন এনডর্ফিন, ডোপামিন, সেরোটোনিন নিঃসরণ হয়। ফলে মনমেজাজ থাকে ভালো। হাঁটার ফলে মনে ভালো লাগার অনুভূতি জাগে, মানসিক চাপ বোধ কম হয়। এনডর্ফিন নামক রাসায়নিকের ক্রিয়া বেড়ে গেলে ঘুম আরামদায়ক হয়। প্রতিদিন ৩০ মিনিট করে সপ্তাহে তিন থেকে পাঁচ দিন হাঁটার ফলে বিষণ্নতার উপসর্গ ৪৭ শতাংশ হ্রাস পায়। অপর এক গবেষণায় দেখা গেছে, যে নারীরা সপ্তাহে অন্তত দেড় ঘণ্টা হাঁটেন, তাদের বোধশক্তি সপ্তাহে ৪০ মিনিটের কম হাঁটা নারীদের তুলনায় বেশি।
হাঁটার আরও কিছু উপকার:
(১) যারা সকালে হাঁটতে অভ্যস্ত, তাদের শরীর ঝরঝরে হয়ে যায়। সার্বিকভাবে শরীর থাকে ফিট, বেড়ে যায় শরীরের কর্মক্ষমতা।
(২) শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়, সাধারণ অসুখ-বিসুখ কম হয়। অনেক সময় ইনফ্লেমেশন হলে শরীরের রোগ-প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে সক্রিয় করতে সাহায্য করে।
(৩) হাঁটার সময় হৃদস্পন্দন আর শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি বেড়ে এ দুটি ভাইটাল অঙ্গের রক্ত সরবরাহ বাড়ায়।
(৪) হাঁটার ফলে পেশিতে রক্ত সরবরাহ বাড়ে, পেশির শক্তি বাড়ে, শরীরের ওজন থাকে গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে।
(৫) দুশ্চিন্তা কমায় ও মানসিক প্রশান্তি বাড়ায়, শরীর মন চাঙ্গা রাখে।
(৬) অসংক্রামক রোগ-প্রতিরোধে কার্যকর ভূমিকা রাখে।
(৭) ফুসফুসের অক্সিজেন ধারণ সক্ষমতা বৃদ্ধি করে।
জেনে রাখা ভালো: হাঁটার উপকার পেতে প্রতিদিন, ৩০ থেকে ৪৫ মিনিট ধরে হাঁটতে হবে। সম্ভব হলে হাঁটতে হবে যথেষ্ট দ্রুতগতিতে যেন শরীরটা একটু ঘামে। নিম্নে কিছু টিপস দেওয়া হলো :
(১) হাঁটা শুরু করার প্রথম ও শেষের ৫-১০ মিনিট আস্তে হেঁটে শরীরকে ওয়ার্মআপ এবং ওয়ার্ম ডাউন করা উচিত।
(২) হাঁটার আগে এবং পরে একটু পানি পান করুন।
(৩) খাওয়ার পর পরই হাঁটবেন না। ৪৫ মিনিট থেকে ৬০ মিনিট অপেক্ষা করুন।
(৪) দুপুরের ভরা রোদে হাঁটবেন না। সকাল বা বিকেলের একটি সময় বেছে নিন।
(৫) হাঁটা শেষ করে এক থেকে দুই ঘণ্টার মধ্যে কিছু খেয়ে নিন।
(৬) অনেককে দেখা যায় অনেকক্ষণ হেঁটে বা ব্যায়াম করার পর ক্লান্ত হয়ে কোক, পেপসি, কেক বা মিষ্টিজাতীয় খাদ্য খেয়ে ফেলেন। এগুলো ওজন কমানোর সহায়ক কিছু হয় না।
কখন হাঁটবেন: সকালে হাঁটবেন, নাকি বিকেলে বা সন্ধ্যায়, এ নিয়ে কিছুটা বিতর্ক আছে। কেউ বলেন, সকালের চেয়ে বিকেলে হাঁটা হৃদযন্ত্রের জন্য ভালো। তবে কারও কারও মতে ভোরে খালি পেটে হাঁটা ওজন এবং রক্তে চর্বির মাত্রা কমাতে বেশি সহায়ক। তবে একটি বিষয়ে সবাই একমত, হাঁটার প্রকৃত সুফল পাওয়ার জন্য প্রতিদিন ৩০ মিনিট করে সপ্তাহে পাঁচ দিন বা মোট ১৫০ মিনিট হাঁটতে হবে, তা সকালেই হোক বা বিকেলেই হোক। তবে নির্দিষ্ট করে প্রতিদিন একই সময় বেছে নিলেই ভালো।
হাঁটার উপকারিতা অনেক এবং যেকোনোভাবে হাঁটা-চলা করলে কিছু না কিছু উপকার অবশ্যই হবে। তবে শারীরিক অসুস্থতা থাকলে কতটুকু হাঁটা যাবে, তা চিকিৎসকের সঙ্গে পরামর্শ করে জেনে নেওয়া উচিত। সমাজের সব মানুষের শারীরিক, মানসিক সুস্থতা ও রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানো, অসংক্রামক ব্যাধি প্রতিরোধ এবং মাদক ও স্মার্টফোন আসক্তি থেকে দূরে রাখতে হাঁটার কোনো বিকল্প নেই। তাই সব বয়সের, নারী-পুরুষ সবাই কম-বেশি হাঁটুন, সুস্থ থাকুন।
লেখক: প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত চিকিৎসক

তারুণ্যের হাত ধরে সৃষ্টি হয়েছে মুক্তির বরাভয়, জাগরণের নব ইতিহাস। তরুণরা হলো চেতনা আর বিপ্লবের হংসদূত। সুপ্রাচীন কাল থেকে কৃষি এবং বাণিজ্যের উর্বর ভূমি হিসেবে পরিচিত এই বাংলা দেখেছে বহু বিজাতি,বিভাষী, বিদেশিদের শাসন-শোষণ। লালসায় তুষ্ট বিদেশি বণিকদের দ্বারা শোষিত এই বাংলার ভূমি। সর্বশেষ ইংরেজ কর্তৃক নবাব সিরাজদ্দৌলাকে পরাজয়ের মধ্যে দিয়ে বাংলার স্বাধীনতার সূর্যকে ১৯০ বছরের জন্য অস্তমিত করে রাখা হয়েছিল।
ইংরেজরা বিতাড়িত হওয়ার পর ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর বাঙালির বহু আশা,আকাঙ্ক্ষা, প্রত্যাশা আরও ম্লান হতে থাকে পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর দ্বারা। দিনের পর দিন শাসন,শোষণ আর লাঞ্ছনা,বঞ্চনা বয়ে বেড়াতে হয়েছে বাঙালিকে। সবকিছু ছিনিয়ে নেওয়ার প্রতিযোগিতায় পশ্চিম পাকিস্তানিরা যখন বাংলার মানুষের মুখের ভাষা ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য তৎপর হয় এদেশের বিপ্লবী ছাত্রজনতা তখন বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠে অর্থাৎ সেদিন তরুণরা তাদের মায়ের ভাষাকে কেড়ে নিতে দেয়নি। ১৯৫২ সালে সংগ্রাম আর অকুতোভয় দুঃসাহস আর বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দিয়ে মাতৃভাষাকে রক্ষা করেছে।
১৯৫২ সাল থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত এদেশের তরুণ প্রজন্ম তথা ছাত্রসমাজ রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম আর যুদ্ধের মধ্যে দিয়ে দেশের প্রয়োজনে, মাতৃভূমির প্রয়োজনে সংগ্রাম চালিয়ে গিয়েছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশের সংকটকালীন সময়ে ১৯৪৮ সালের ৪ঠা জানুয়ারি ছাত্রলীগ প্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়ে দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছিলেন। কারণ তিনি জানতেন তারুণ্যের শক্তির কাছে সকল অপশক্তি ম্লান হয়ে যায়, বিনাশ হয়ে যায়। বঙ্গবন্ধু তরুণ প্রজন্মকে দেশের প্রয়োজনে নিজেকে বিলিয়ে দেওয়ার জন্য ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের দিয়ে ছাত্রসমাজকে ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা করেছেন এবং সময়ের তাগিদে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশনায় তরুণরা দেশমাতৃকার প্রয়োজনে পরাধীনতার শৃঙ্খল বেধ করতে সচেষ্ট থেকেছে। ১৯৭৫ সালে এদেশ গড়ার কারিগর বঙ্গবন্ধুকে হত্যার মধ্যে দিয়ে বাঙালির ললাটে যে কালো টীকা এঁকে দেওয়া হয়েছিলো তার উদ্দেশ্য ছিল ঐ পরাজিত পাকিস্তানিদের একটি অন্যতম অ্যাজেন্ডা! পাকিস্তানিরা যা করতে পারেনি তাদের একটি বিপথগামী দালাল গোষ্ঠী সেটি করতে সক্ষম হয়েছে। দেশকে পিছিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য এর থেকে জঘন্যতম হত্যাকাণ্ড পৃথিবীর ইতিহাসে আর একটিও যোগ হয়নি। স্বৈরশাসনে অতিষ্ঠ বাঙালিকে পুনরায় গণতন্ত্রের স্বাদ ফিরে দিতে ৯০ স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে এদের তরুণ প্রজন্ম তথা ছাত্রসমাজ।
তরুণদের হাত ধরেই রাষ্ট্রে ঘটেছে পরিবর্তন, উন্নয়ন। তারুণ্যের এই শক্তিকে যথাযথভাবে পরিচর্যা এবং তরুণদেরকে আগামীর বাংলাদেশ বিনির্মাণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করার জন্য সুগম পথ তৈরি পাশাপাশি তাদের মধ্যে নেতৃত্ব তৈরির ব্যাপারে ইতিবাচক নির্দেশনা দিয়েছেন বর্তমান বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনা। ২০০৮ সালে আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারে উল্লেখযোগ্য বিষয় ছিল ‘ডিজিটাল বাংলাদেশ’ গঠন,যেখানে মূলত তরুণদের প্রাধান্য দেওয়া হয়েছিল। ‘ডিজিটাল বাংলাদেশ’ রূপকল্পের অনেকাংশ বাস্তবায়নের পাশাপাশি দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি ঘটেছে, দেশ এগিয়ে যাচ্ছে বৈশ্বিক সূচকে। এর পেছনে অন্যতম চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করছে তরুণদের উদ্যম। এ কারণে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তরুণদের কথা শুনতে চান, নিজের ভাবনার কথাও তাদের জানাতে চান।তরুণদের নিয়ে অনুষ্ঠিত ‘লেটস টক’-এ ‘স্মার্ট বাংলাদেশ’ গড়ে তোলার ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার দৃষ্টিভঙ্গি বর্ণনা করেছেন। এটি বাস্তবায়নে স্মার্ট নাগরিক, স্মার্ট অর্থনীতি, স্মার্ট সরকার ও স্মার্ট সমাজ রূপরেখার ওপর জোর দিয়েছেন তিনি। এছাড়াও তরুণ প্রজন্মকে একটি সুখী সমৃদ্ধ বাংলাদেশ উপহার দেওয়ার জন্য তিনি তার বর্তমানকে ত্যাগ করে চলেছেন এবং তিনি প্রায়ই বলে থাকেন আমার বর্তমানকে তরুণ প্রজন্মের সুন্দর ভবিষ্যতের জন্য আমি উৎসর্গ করেছি, তারাই ভবিষ্যতের বাংলাদেশ গড়বে। যতক্ষণ ক্ষমতায় আছি পরিবর্তিত বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার জন্য প্রয়োজনীয় সব ধরনের পদক্ষেপই গ্রহণ করব। তরুণ প্রজন্মের শিক্ষার পথকে গতিশীল এবং শিক্ষার মানকে বৃদ্ধি করার জন্য যুগোপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থা, আধুনিক টেকনোলজি ব্যবহার,কারিগরি প্রশিক্ষণ ইত্যাদি বৃদ্ধির লক্ষ্যে শেখ হাসিনা সরকার প্রচুর অর্থ ব্যয় করছে প্রতিবছর। এছাড়া পড়াশোনা করে শুধু চাকরির পেছনে সময় ব্যয় না করে নিজে উদ্যোক্তা হয়ে অন্যের জন্য আয়ের পথ তৈরি করার ব্যাপারে নির্দেশনা দিয়েছেন। আর সেজন্য তরুণদের জন্য সহজলভ্য ঋণের ব্যবস্থা করেছেন তিনি।
একটি সময় এদেশের বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলোর শিক্ষার্থীদের হাতে হাতে অস্ত্র থাকতো, খুনাখুনি, হানাহানি এসব ছিল নিত্যদিনের ঘটনা।শেখ হাসিনা ক্ষমতায় আসার পর শিক্ষার্থীদের হাতে হাতে বই, খাতা-কলম তুলে দিয়েছেন,অস্ত্রের বদলে কলম চালানোর উপর তাগিদ দিয়েছেন। তিনি নতুন করে শিখিয়েছেন ‘অসির চেয়ে মসি বড়’। আগামীর সুখী,সমৃদ্ধ বাংলাদেশ নির্ভর করছে তারুণ্যের উদ্ভাবনী শক্তি ও সৃজনশীলতার উপর। আর শেখ হাসিনা এই শক্তি ও সৃজনশীলতাই প্রত্যাশা করেন তরুণদের কাছে।। এজন্যই বলা হয় একজন শেখ হাসিনা,তারুণ্যের কলমে যিনি সফলতার গল্প লিখেন।
লেখক: ছাত্র রাজনৈতিক, বাংলা বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

প্রতি বছর সাতই জুন, ’ছয় দফা দিবস’ যথাযোগ্য মর্যাদায় আমরা পালন করি। জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসে ছয় দফা ও সাতই জুন অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে আছে। জাতীয় জীবনে ছয় দফা ও সাতই জুনের গুরুত্ব অপরিসীম। বাংলার গণমানুষ ১৯৬৬-এর সাতই জুন স্বাধিকার ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবসহ সব রাজবন্দির মুক্তির দাবিতে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে পাকিস্তান শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সর্বব্যাপী হরতাল পালন করেছিল। এই দিনে মনু মিয়া, মুজিবুল্লাহসহ অসংখ্য শহীদের রক্তে রঞ্জিত হয় ঐতিহাসিক ছয় দফা। পরবর্তীতে ’৬৯-এর গণআন্দোলনের সূচনালগ্নে ছয় দফা দাড়ি-কমা-সেমিকোলনসমেত এগারো দফায় ধারিত হয়ে, ’৭০-এর ঐতিহাসিক নির্বাচনে জনগণের ম্যান্ডেট নিয়ে এক সাগর রক্তের বিনিময়ে আমরা এক দফা তথা স্বাধীনতা অর্জন করেছি।
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিচক্ষণ ও দূরদর্শী নেতা ছিলেন। জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের অভিপ্রায় থেকেই তিনি জাতির উদ্দেশে ছয় দফা কর্মসূচি প্রদান করেছিলেন। যে জন্য ছয় দফাকে বলা হয় জাতির মুক্তিসনদ। বঙ্গবন্ধুর হৃদয়ের গভীরে সততই প্রবহমান ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতা। প্রিয় মাতৃভূমির স্বাধীনতার বাইরে অন্য কোনো চিন্তা তার ছিল না। জেল-জুলম-অত্যাচার-নির্যাতন সহ্য করে পরাধীনতার নাগপাশ থেকে বাংলাদেশকে তিনি স্বাধীন করেছেন। বঙ্গবন্ধু ছিলেন গণতান্ত্রিক-অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির প্রবক্তা। আওয়ামী মুসলিম লীগ থেকে ‘মুসলিম’ শব্দটি বাদ দিয়ে সর্বধর্মের, সর্ববর্ণের, সর্বশ্রেণির মানুষের জন্য তিনি আওয়ামী লীগের দরোজা উন্মুক্ত করেছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন বাংলাদেশ হবে বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। যার যার ধর্ম সেই সেই পালন করবে। কারও ধর্ম পালনে কেউ হস্তক্ষেপ করতে পারবে না।
স্বৈরশাসক আইয়ুব খান এ দেশের গণতান্ত্রিক শক্তিকে নিশ্চিহ্ন করে সংখ্যাগুরু বাঙালি জাতিকে গোলামির শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত করার জন্য ষড়যন্ত্র করেছিল। এর বিপরীতে বাংলার প্রাণপ্রিয় নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ’৬৬-এর ৫ ফেব্রুয়ারি লাহোরে সম্মিলিত বিরোধী দলসমূহের এক কনভেনশনে বাংলার গণমানুষের আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের দাবি সংবলিত বাঙালির ‘মুক্তিসনদ’ খ্যাত ঐতিহাসিক ‘ছয় দফা দাবি’ উত্থাপন করে তা বিষয়সূচিতে অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব করেন। কিন্তু সভার সভাপতি চৌধুরী মোহাম্মদ আলী ‘ছয় দফা দাবি’ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনায় অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করলে ১১ ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধু দেশে ফিরে ঢাকা বিমানবন্দরে সংবাদ সম্মেলনে এ বিষয়ে বিস্তারিত তুলে ধরেন। ২০ ফেব্রুয়ারি আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে ‘ছয় দফা’ দলীয় কর্মসূচি হিসেবে গৃহীত হয়। ‘ছয় দফা’ ঘোষণার পর জনমত সংগঠিত করতে বঙ্গবন্ধু তার সফরসঙ্গীসহ ’৬৬-এর ২৫ ফেব্রুয়ারি, চট্টগ্রামের লালদিঘি ময়দানের জনসভায় ‘ছয় দফা’কে ‘নূতন দিগন্তের নূতন মুক্তিসনদ’ হিসেবে উল্লেখ করে চট্টগ্রামবাসীর উদ্দেশে বলেন, ‘এক দিন সমগ্র পাক-ভারতের মধ্যে ব্রিটিশ সরকারের জবরদস্ত শাসনব্যবস্থাকে উপেক্ষা করে এই চট্টগ্রামের জালালাবাদ পাহাড়েই বীর চট্টলার বীর সন্তানরা স্বাধীনতার পতাকা উড্ডীন করেছিলেন। আমি চাই যে, পূর্ব পাকিস্তানের বঞ্চিত মানুষের জন্য দাবি আদায়ে সংগ্রামী পতাকাও চট্টগ্রামবাসী চট্টগ্রামেই প্রথম উড্ডীন করুন।’ চট্টগ্রামের জনসভার পর দলের আসন্ন কাউন্সিল সামনে রেখে ‘ছয় দফা’র যৌক্তিকতা তুলে ধরতে তিনি একের পর এক জনসভা করেন। এরই অংশ হিসেবে ২৭ ফেব্রুয়ারি, নোয়াখালীর মাইজদী, ওই দিনই বেগমগঞ্জ, ১০ মার্চ ময়মনসিংহের মুক্তাগাছা, ১১ মার্চ ময়মনসিংহ সদর ও ১৪ মার্চ সিলেটে অনুষ্ঠিত জনসভায় জনতার দরবারে তার বক্তব্য পেশ করেন।
‘ছয় দফা’ প্রচার ও প্রকাশের জন্য বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে ছয় সদস্যবিশিষ্ট ‘উপ কমিটি’ গঠন এবং তারই নামে ‘আমাদের বাঁচার দাবি : ছয় দফা কর্মসূচি’ শীর্ষক একটি পুস্তিকা মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। একই বছরের ১৮, ১৯ ও ২০ মার্চ ছিল আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশন। এ দিন কাউন্সিল সভায় পুস্তিকাটি বিলি করা হয়। দলের সিনিয়র সহসভাপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামের সভাপতিত্বে সম্মেলনের উদ্বোধনী অধিবেশনে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি’ গীত হয়। বাঙালির বাঁচার দাবি ‘ছয় দফা’কে উপলক্ষ করে ’৬৬-এর মার্চে অনুষ্ঠিত আওয়ামী লীগের তিন দিনব্যাপী কাউন্সিল অধিবেশনটি ছিল সবিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। সে দিনের সেই কাউন্সিল সভায় আগত ১৪৪৩ জন কাউন্সিলর বঙ্গবন্ধুকে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি, তাজউদ্দীন আহমদকে সাধারণ সম্পাদক ও মিজানুর রহমান চৌধুরীকে সাংগঠনিক সম্পাদক পদে নির্বাচিত করে। ‘ছয় দফা’র ভিত্তিতে সংশোধিত দলীয় গঠনতন্ত্রের একটি খসড়াও অনুমোদন করা হয়। ‘ছয় দফা’ কর্মসূচি প্রদানের সঙ্গে সঙ্গে ‘ছয় দফা’র ভিত্তিতে দলীয় গঠনতন্ত্র এবং নেতৃত্ব নির্বাচনে যে পরিবর্তন সাধিত হয় তা পরবর্তীকালে ‘ছয় দফা’র চূড়ান্ত পরিণতি এক দফা তথা স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ গঠনের ইঙ্গিতবাহী ছিল। ‘ছয় দফা কর্মসূচি’ দলীয় কর্মীদের মধ্যে বিশেষ করে আমাদের মতো অপেক্ষাকৃত তরুণ ছাত্রলীগ নেতৃত্বের মধ্যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। পরবর্তীতে ‘ছয় দফা’ এতই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল যে, বাংলার প্রায় প্রতি ঘরে ঘরে এই পুস্তিকা সযত্নে রক্ষিত হয়েছিল। ‘ছয় দফা’ সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু বলতেন, ‘সাঁকো দিলাম, স্বাধিকার থেকে স্বাধীনতায় উন্নীত হওয়ার জন্য।’ বস্তুত, ‘ছয় দফা’ ছিল স্বাধীনতা সংগ্রামের বীজমন্ত্র তথা অঙ্কুর। কাউন্সিল অধিবেশনের শেষ দিন অর্থাৎ ২০ মার্চ চরম প্রতিকূল আবহাওয়ার মধ্যে ঢাকার পল্টন ময়দানের জনসভায় দলীয় নেতা-কর্মী ও দেশবাসীর উদ্দেশে উদাত্ত আহ্বান জানিয়ে বঙ্গবন্ধু বলেন, ‘চরম ত্যাগ স্বীকারের এই বাণী লয়ে আপনারা দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ুন। পূর্ব পাকিস্তানের প্রত্যন্ত প্রদেশের প্রতিটি মানুষকে জানিয়ে দিন, দেশের জন্য, দশের জন্য, অনাগতকালের ভাবী বংশধরদের জন্য সবকিছু জেনে-শুনেই আওয়ামী লীগের নেতা ও কর্মীরা এবার সর্বস্ব পণ করে নিয়মতান্ত্রিক পথে ছয় দফার ভিত্তিতে দেশব্যাপী আন্দোলনের জন্য এগিয়ে আসছে।’
আওয়ামী লীগের এই কাউন্সিল অধিবেশনটি ছিল বাঙালির ইতিহাসে বাঁক পরিবর্তন, যা ’৬৯-এর মহান গণঅভ্যুত্থান, ’৭০-এর ঐতিহাসিক নির্বাচন ও ’৭১-এর মহত্তর মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি তৈরি করেছিল। কাউন্সিল সভার সমাপনী জনসভায় বঙ্গবন্ধু মুজিব বলেছিলেন, ‘ছয় দফার প্রশ্নে কোনো আপস নেই। রাজনীতিতেও কোনো সংক্ষিপ্ত পথ নেই। নেতৃবৃন্দের ঐক্যের মধ্যেও আওয়ামী লীগ আর আস্থাশীল নয়। নির্দিষ্ট আদর্শ ও সেই আদর্শ বাস্তবায়নের জন্য নিবেদিতপ্রাণ কর্মীদের ঐক্যেই আওয়ামী লীগ বিশ্বাস করে। আওয়ামী লীগ নেতার দল নয়- এ প্রতিষ্ঠান কর্মীদের প্রতিষ্ঠান। শান্তিপূর্ণ ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মাধ্যমে এই ছয় দফা আদায় করতে হবে। কোনো হুমকিই ছয় দফা আন্দোলনকে প্রতিরোধ করতে পারবে না। ছয় দফা হচ্ছে বাঙালির মুক্তি সনদ।’ স্বভাবসুলভ কণ্ঠে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের, ‘যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলো রে’ উদ্ধৃত করে বলেছিলেন, ‘এই আন্দোলনে রাজপথে যদি আমাদের একলা চলতে হয় চলব। ভবিষ্যৎ ইতিহাস প্রমাণ করবে বাঙালির মুক্তির জন্য এটাই সঠিক পথ।’ বঙ্গবন্ধু জানতেন, ‘ছয় দফা’ই কেবল বাঙালির স্বাধিকার তথা পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন নিশ্চিত কর অখণ্ড পাকিস্তানের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পারে। পক্ষান্তরে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর একটি অতি ক্ষুদ্র অংশ পাঞ্জাবিরা ‘ছয় দফা’ বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে সংখ্যাগুরু বাঙালির রাষ্ট্র ক্ষমতায় আরোহণ ঠেকাতে সর্বশক্তি নিয়োগ করে- যা পরিণামে স্বাধীন বাংলাদেশের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। সফলভাবে সমাপ্ত আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশনের পর বঙ্গবন্ধু সারা দেশ চষে বেড়ান। ২৬ মার্চ সন্দ্বীপ এবং ২৭ মার্চ সাতকানিয়ার বিশাল জনসভায় ‘ছয় দফা কর্মসূচি’ ব্যাখ্যা করে বক্তৃতা করেন। এরপর উত্তরাঞ্চল সফরে যান ’৬৬-এর ৭ এপ্রিল। ওই দিন পাবনা ও নগরবাড়ির জনসমাবেশে বক্তৃতা করেন। একই মাসের ৮ তারিখ বগুড়া, ৯ তারিখ রংপুর, ১০ তারিখ দিনাজপুর, ১১ তারিখ রাজশাহী, ১৪ তারিখ ফরিদপুর, ১৫ তারিখ কুষ্টিয়া, ১৬ তারিখ যশোর এবং ১৭ তারিখ খুলনায় বিশাল সব জনসভায় ছয় দফার বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণসহ বক্তৃতা করেন। এভাবে সারা দেশে ৩৫ দিনে মোট ৩২টি জনসভায় তিনি বক্তৃতা করেন। বিপুল সংখ্যক জনতার অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত লাগাতার জনসভায় প্রদত্ত বঙ্গবন্ধুর বক্তৃতায় ‘ছয় দফা’র সপক্ষে জনমত প্রবল হয়ে ওঠে। ফলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবসহ আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের ওপর নেমে আসে স্বৈরশাসক আইয়ুবের নির্মম গ্রেপ্তার-নির্যাতন। প্রত্যেক জেলায় অনুষ্ঠিত সভায় প্রদত্ত বক্তৃতার প্রতিপাদ্য বিষয়বস্তুর ওপর ভিত্তি করে বঙ্গবন্ধুকে প্রত্যেক জেলা থেকে জারিকৃত ওয়ারেন্ট বলে লাগাতার গ্রেপ্তার প্রক্রিয়া চলতে থাকে। ১৭ এপ্রিল রাত ৪টায় খুলনায় এক জনসভায় ভাষণদান শেষে ঢাকা ফেরার পথে রমনা থানার জারিকৃত ওয়ারেন্ট অনুযায়ী পাকিস্তান দেশরক্ষা আইনের ৪৭ (৫) ধারা বলে পুলিশ বঙ্গবন্ধুকে গ্রেপ্তার করে। যশোর মহকুমা হাকিমের এজলাস হতে তিনি জামিন পান। সে দিনই রাত ৯টায় সিলেটে গ্রেপ্তার, পুনরায় জামিনের আবেদন এবং ২৩ তারিখ জামিন লাভ। ২৪ এপ্রিল ময়মনসিংহে গ্রেপ্তার, ২৫ এপ্রিল জামিন। ‘ছয় দফা’ প্রচারকালে তিন মাসে বঙ্গবন্ধুকে সর্বমোট ৮ বার গ্রেপ্তার করা হয়। এভাবেই আইয়ুবের দমন নীতি অব্যাহত থাকে। একই বছরের ৮ মে নারায়ণগঞ্জের চাষাঢ়ায় ঐতিহাসিক ‘মে দিবস’ স্মরণে শ্রমিক জনতার এক বিরাট সমাবেশে শ্রমিকরা বঙ্গবন্ধুকে বিপুল সংবর্ধনা জ্ঞাপন করে এবং পাটের মালায় ভূষিত করে। ভাষণদান শেষে রাত ১টায় তিনি যখন বাসায় ফেরেন তখন পাকিস্তান দেশরক্ষা আইনের ৩২ (১) ‘ক’ ধারা বলে তাকেসহ তার ঘনিষ্ঠ রাজনৈতিক সহকর্মীদের গ্রেপ্তার করা হয়। ‘ছয় দফা’ দেওয়াকে অপরাধ গণ্য করে স্বৈরশাসক আইয়ুব বঙ্গবন্ধুকে ‘বিচ্ছিন্নতাবাদী’ হিসেবে অভিহিত করে দেশরক্ষা আইনের আওতায় আওয়ামী লীগের ওপর অব্যাহত গ্রেপ্তার-নির্যাতন চালায়। সামরিক সরকারের এহেন কার্যকলাপের বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগের আহ্বানে ১৩ মে সমগ্র প্রদেশে ‘প্রতিবাদ দিবস’ পালিত হয়। প্রতিবাদ দিবসের জনসভায় ‘ছয় দফা’র প্রতি গণমানুষের বিপুল সমর্থন প্রকাশ পায়। হাজার হাজার শ্রমিক এ দিন স্বতঃস্ফূর্ত হরতাল পালন করে এবং পল্টনে অনুষ্ঠিত জনসভায় উপস্থিত হয়ে সরকারের দমন নীতির তীব্র প্রতিবাদ করে। দলের নবনির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক তাজউদ্দীন আহমদকে গ্রেপ্তার করা হলে সাংগঠনিক সম্পাদক মিজান চৌধুরী অস্থায়ী সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। নেতৃবন্দের গ্রেপ্তার-নির্যাতনের বিরুদ্ধে ২০ মে আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে ‘সাতই জুন’ সর্বব্যাপী হরতাল আহ্বান করা হয়।
সাতই জুনের হরতালে সমগ্র পূর্ব বাংলা যেন অগ্নিগর্ভ। বিক্ষুব্ধ মানুষ স্বাধিকার ও বঙ্গবন্ধুসহ সকল রাজবন্দির মুক্তির দাবিতে সোচ্চার হয়। আমি তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, ছাত্রলীগের সার্বক্ষণিক কর্মী, ইকবাল হল (বর্তমানে শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হক হল) ছাত্র সংসদের নির্বাচিত ভিপি। সর্বজনাব শেখ ফজলুল হক মণি, সিরাজুল আলম খান, আব্দুর রাজ্জাক, আমীর হোসেন আমু, সৈয়দ মাজহারুল হক বাকী, আব্দুর রউফ, খালেদ মোহাম্মদ আলী, নূরে আলম সিদ্দিকীসহ আরও অনেকে আমরা সেদিন হরতাল কর্মসূচি পালনের সর্বাত্মক প্রস্তুতি গ্রহণ করি। সে দিনের হরতাল কর্মসূচিতে ধর্মঘটী ছাত্র-জনতাকে ছত্রভঙ্গ করার জন্য সরকারের নির্দেশে পুলিশ বাহিনী নির্বিচারে গুলিবর্ষণ করে। পুলিশের গুলিতে তেজগাঁয় শ্রমিক মনু মিয়া, আদমজীতে মুজিবুল্লাহসহ এগারো জন শহীদ হন এবং প্রায় আটশ লোককে গ্রেপ্তার করা হয়। তেজগাঁ শিল্পাঞ্চলে হরতাল সফল করার দায়িত্বে ছিলেন ছাত্রনেতা খালেদ মোহাম্মদ আলী ও নূরে আলম সিদ্দিকী। তারা সেখানে বক্তৃতা করেন। প্রকৃতপক্ষে সাতই জুন ছিল স্বাধিকার থেকে স্বাধীনতার পথের আরম্ভস্থল তথা যাত্রাবিন্দু। আর আমরা যারা ছাত্রলীগের কর্মী ছিলাম, আমাদের স্বাধীনতার চেতনার ভিত্তিও স্থাপিত হয়েছিল এ দিনটিতেই।
বায়ন্নের একুশে ফেব্রুয়ারি মহান ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে ’৬২-এর ১৭ সেপ্টেম্বর, ‘শিক্ষা আন্দোলন’; ‘৬৬-এর ৭ জুন, ‘ছয় দফা আন্দোলন’; ’৬৯-এর ১৭ থেকে ২৪ জানুয়রি, ‘গণআন্দোলন-গণঅভ্যুত্থান’; ৯ ফেব্রুয়ারি, ১১-দফা বাস্তবায়ন ও বঙ্গবন্ধুর মুক্তির দাবিতে ‘শপথ দিবস’ পালন; স্বৈরশাসক আইয়ুব খানের পদত্যাগ; আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার ও বঙ্গবন্ধুসহ সব রাজবন্দির নিঃশর্ত মুক্তির দাবিতে ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০ ও ২১ ফেব্রুয়ারি, লাগাতার সংগ্রাম শেষে ২৪ ঘণ্টার আলটিমেটাম প্রদান; অতঃপর ২২ ফেব্রুয়ারি, সব রাজবন্দির মুক্তির পর বঙ্গবন্ধুর মুক্তি লাভ এবং ২৩ ফেব্রুয়ারি ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) ১০ লক্ষাধিক মানুষের উপস্থিতিতে ‘মুক্ত মানব শেখ মুজিব’কে ‘বঙ্গবন্ধু’ উপাধি প্রদান। পঞ্চাশের দশক থেকে বাঙালির জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের লক্ষ্যে গড়ে তোলা সব আন্দোলন-সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়েছে ছাত্রলীগ। এসব মহিমান্বিত সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ছাত্রলীগ অর্জন করেছে গণতান্ত্রিক তথা নিয়মতান্ত্রিক আচরণ ও রাজনৈতিক সংস্কৃতি এবং জয় করে নিয়েছে বাংলার মানুষের হৃদয় আর সৃষ্টি করেছে ইতিহাস। অতীতে আমাদের সময়ে ছাত্রলীগের সম্মেলন গঠনতন্ত্র মোতাবেক প্রতি বছর ২১ মার্চের মধ্যে সম্পন্ন করার বাধ্যবাধকতা ছিল। তা না হলে তিন সদস্য বিশিষ্ট কমিটির কাছে নেতৃত্ব তুলে দিতে হতো। এটাই ছিল বিধান এবং গঠনতান্ত্রিক বিধি-বিধানের অন্যথা হওয়ার কোনো সুযোগ ছিল না। বিধান মোতাবেক ’৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানের পর আমি ছাত্রলীগের সভাপতি এবং আ স ম আব্দুর রব সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়ে এক বছর পর গঠনতন্ত্র অনুযায়ী ২১ মার্চের মধ্যে সম্মেলন করে নূরে আলম সিদ্দিকী এবং শাজাহান সিরাজের কাছে নেতৃত্বের দায়িত্বভার অর্পণ করে আমাদের কমিটি বিদায় নিই এবং ২২ মার্চ হল ত্যাগ করে গ্রিন রোডে ‘চন্দ্রশীলা’ নামে একটি বাসা ভাড়া করে আমি এবং রাজ্জাক ভাই বসবাস শুরু করি। আজ অতীতের সেই সোনালি দিনগুলোর দিকে যখন ফিরে তাকাই স্মৃতির পাতায় দেখি, সে দিনের ছাত্রলীগ ছিল বাংলার গণমানুষের অধিকার আদায় তথা ‘মুজিব আদর্শ’ প্রতিষ্ঠার ভ্যানগার্ড। মূলত বঙ্গবন্ধু মুজিবের নির্দেশে আওয়ামী লীগ-ছাত্রলীগের নেতৃত্বই সে দিন সারা দেশে সাতই জুনের কর্মসূচি সফলভাবে পালন করে স্বাধিকারের পথে এক অনন্য নজির স্থাপন করে। আর বাংলার মেহনতী মানুষ আত্মত্যাগের অপার মহিমার দৃষ্টান্ত স্থাপন করে পাকিস্তান শাসকগোষ্ঠীসহ সমগ্র বিশ্বকে জানিয়ে দেয় যে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব প্রদত্ত ‘ছয় দফা’ই হচ্ছে বাঙালির জাতীয় মুক্তির একমাত্র পথ।
‘ছয় দফা’কে প্রতিহত করার জন্য পাকিস্তান শাসকগোষ্ঠী বহু ষড়যন্ত্র করেছে। কিন্তু ‘ছয় দফা’র প্রতি বঙ্গবন্ধুর দৃঢ় স্থির-প্রতিজ্ঞাবোধ তাকে জনমনে জনগণমন অধিনায়কের আসনে অধিষ্ঠিত করে। ’৬৬-এর ৮ মে বঙ্গবন্ধুকে কারাগারে নিক্ষেপ করে তার বিরুদ্ধে একের পর এক মামলা দিয়েও ‘ছয় দফা’ আন্দোলনকে যখন রোধ করা যাচ্ছিল না, তখন বঙ্গবন্ধুকে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলিয়ে চিরতরে তার কণ্ঠ স্তব্ধ করে দেওয়ার জন্য স্বৈরশাসক আইয়ুব খান ‘রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিব ও অন্যান্য’ মামলা দেন। ‘ছয় দফা’ দাবি আদায়ে এবং বঙ্গবন্ধুকে কারামুক্ত করতে বাংলার সর্বস্তরের মানুষসহ আমরা যারা ছাত্র রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলাম তারা ’৬৯-এর ৪ জানুয়ারি ছাত্রলীগের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠন করে ছয় দফাকে এগারো দফায় অন্তর্ভুক্ত করে সারা বাংলার গ্রামে-গঞ্জে-শহরে-বন্দরে-কলে-কারখানায় ছড়িয়ে দিয়েছিলাম। ফলে এগারো দফা আন্দোলনের সপক্ষে সারা দেশে যে গণজোয়ার তৈরি হয় তাতে দেশে বৈপ্লবিক পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটে। শাসকশ্রেণি গণআন্দোলনকে নস্যাৎ করতে আমাদের ‘বিচ্ছিন্নতাবাদী’ হিসেবে চিত্রিত করে। তাদের এই অপপ্রয়াসের সমুচিত জবাব দিতে ’৬৯-এর ৯ ফেব্রুয়ারি ঐতিহাসিক পল্টন ময়দানে সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের শপথ দিবসের জনসমুদ্রে বলেছিলাম, ‘পূর্ব বাংলার মানুষ কোনোদিন বিচ্ছিন্নতাকে প্রশ্রয় দেয়নি এবং বিচ্ছিন্নতায় বিশ্বাসীও নয়। কারণ তারা সংখ্যায় শতকরা ৫৬ জন। যদি কারও পূর্ব বাংলার সঙ্গে থাকতে আপত্তি থাকে তবে তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারে।’ নেতার এই নির্দেশ আমরা শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত মেনে চলেছি। পাকিস্তান সেনাবাহিনী গণহত্যা চালানোর আগ পর্যন্ত কোনোরকম উগ্রতাকে অতি বিপ্লবীপনাকে আমরা প্রশ্রয় দিইনি। নিয়মতন্ত্রের মধ্যেই বঙ্গবন্ধু সংগ্রাম পরিচালনা করেছেন। বিচ্ছিন্নতাবাদের অভিযোগে আমাদের কখনোই অভিযুক্ত করা যায়নি। আমরা আমাদের মুক্তি সংগ্রামের ন্যায্যতা প্রমাণ করে মুক্তি সংগ্রামী হিসেবেই এগিয়ে গেছি। আর এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে সাতই জুনের কর্মসূচি পালনকালে শহীদদের বীরত্বপূর্ণ আত্মদান। সাতই জুন ছিল এর সূচনাবিন্দু। আমাদের জাতীয় জীবনে শত শহীদের রক্তে লেখা এ দিনটি চেতনায় জাতীয় মুক্তির যে অগ্নিশিখার জন্ম দিয়েছিল, তারই ধারাবাহিকতায় ’৭০-এর ২ জুন, বঙ্গবন্ধু ও জাতীয় নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে এবং তারই নির্দেশে আনুষ্ঠানিকভাবে আওয়ামী লীগে যোগদান করি।
আজ ৭ জুন, অতীতের অনেক স্মৃতি আমার মানসপটে ভেসে ওঠে। বিশেষ করে বঙ্গবন্ধুর স্মৃতি আমাকে ভীষণভাবে নাড়া দেয়। বঙ্গবন্ধুর স্নেহে আমার জীবন ধন্য। সাতই জুনের চেতনাবহ এই দিনটি আমার জীবনে অম্লান হয়ে আছে। সাতই জুনে যে সকল শহীদ ভাইয়েরা তাদের বুকের তাজা রক্ত দিয়ে, জীবন দিয়ে, বাংলার মানুষের মুক্তির পথকে প্রশস্ত করে গিয়েছেন তাদেরকে পরম শ্রদ্ধায় স্মরণ করি। তাদের অমর প্রাণের বিনিময়ে সংগ্রাম পরম্পরায় এক সাগর রক্তের বিনিময়ে জাতির পিতার নেতৃত্বে স্বাধীন ও সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে ঐতিহাসিক সাতই জুন ছিল আমাদের স্বাধিকার ও স্বাধীনতার চেতনার প্রারম্ভ বিন্দু। এই দিনটিতে সাতই জুনের শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন কর্তব্য বলে মনে করি।
লেখক: উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্য, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ; সদস্য, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

যানজট- বাংলাদেশের বহুল আলোচিত একটি শব্দ ও সমস্যা। আমাদের যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থাপনার এক যন্ত্রণাময় চিত্র। ঢাকাসহ দেশের বৃহত্তম নগরীগুলোয় যানজটে নাকাল হয়ে আমাদের মূল্যবান কর্মঘণ্টা নষ্ট হয়ে যেমন কাজের গতি ও উন্নয়নকে করছে ব্যাহত তেমনি ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক সম্পর্ককেও শিথিল করে তুলছে। যানজটে ক্লিষ্ট হওয়ার ভয়ে আমরা শারীরিকভাবে চলাফেরা কমিয়ে দিচ্ছি। বাধ্য হয়ে যারা রাস্তায় বা পরিবহনে উঠছি তারা সময়ের অপচয়ের পাশাপাশি বায়ু ও শব্দদূষণের শিকার হয়ে শারীরিক-মানসিক অসুস্থতাকে নির্বাদে আলিঙ্গন করছি। এই হচ্ছে আমাদের বাংলাদেশের যানজটের বাস্তবতা।
বাংলাদেশ- এক সময় জালের মতো ছড়িয়ে থাকা নদী-নালা ও মাটির মেঠো পথের একটি দেশ ছিল। এখন সেই অনেক নদী-নালা শুকিয়ে আর মাটির মেঠো পথে ইট বিছিয়ে তৈরি হয়েছে গ্রামীণ সড়ক নেট ওয়ার্ক। গ্রামীণ সড়কের মর্যাদা নাগরিক সভ্যতাকে টেনে নিয়ে গেছে গ্রামের জনপদে। নৌকা বা হাঁটার স্থলে যান্ত্রিক পরিবহন গ্রামীণ জনজীবনকে গতিশীল ও আরামদায়ক করেছে সন্দেহ নেই। জীবনযাত্রারমান ও স্টাইলেও এসেছে অপ্রত্যাশিত পরিবর্তন। নতুন নতুন পরিবহন তথা অটো, পিকআপ, টেক্সি, লেগুনা, নসিমন, বাস অনুপ্রবেশ করেছে গ্রামের সড়কে। যোগাযোগ উন্নত হওয়ার পাশাপাশি তাই সাধারণ বেকারদের হয়েছে কর্মসংস্থান, প্রসার ঘটেছে ব্যবসা-বাণিজ্যেরও। এক কথায় গ্রামীণ চিত্র পাল্টে গেছে উন্নয়নের ছোঁয়ায়।
সাম্প্রতিক গ্রামীণ ও শহরের সড়ক উন্নয়নকে যেমন স্বাীকার করতে হবে পাশাপাশি এর সমস্যা ও সম্ভাবনার হিসাবটিও আমাদের মাথায় রাখা দরকার। উন্নয়নকে অদম্য অগ্রযাত্রার সিঁড়ি হিসেবে ব্যবহার করার সময় এর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াগুলো চিহ্নিত ও পরিকল্পিত সমাধানের ব্যবস্থা না নিলে যেকোনো উন্নয়ন মুখ থুবড়ে পড়তে সময় নেবে না। বলা যায়- লেজে-গোবরে এক হয়ে যাওয়ার পরিস্থিতির উদ্ভব হবে। যেটা আমরা এখনই অত্যন্ত তিক্ততার সঙ্গে লক্ষ্য করছি আমাদের সড়ক ও যোগাযোগ ব্যবস্থাপনায়।
গ্রামীণ সড়ক উন্নয়ন ও যোগাযোগ ব্যবস্থাপনায় অভূতপূর্ব উন্নয়নের ফলে গ্রামের ও মফস্বল শহরের জীবনযাত্রা ও উন্নতির বিপরীতে জেলা, মহানগর আর রাজধানী ঢাকার চিত্র ঠিক উল্টো। এখানে পাকা রাস্তা বাড়েনি, অপরিকল্পিত নগরায়ণের ফলে আর বাড়ানোর সুযোগও নেই। অথচ বাড়ছে ব্যক্তিগত গাড়ি, বাস, পিকআপ, ট্রাক, মোটরসাইকেল, সরকারি-বেসরকারি পরিবহন সার্ভিস, যোগ হয়েছে অটোরিকশার লাগামহীন বহর। যার ফলে চিরায়ত, পুরোনো মাপের সড়কগুলো, গলির রাস্তাগুলো সব সময়ই অচল আর স্থির হয়ে থাকছে মাত্রাতিরিক্ত গাড়ির চাপে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা গাড়িতে বসে থেকে যন্ত্রণায় ভোগা, মূল্যবান কর্মঘণ্টার অপচয় আর জ্বালানি পোড়ানো ছাড়া আর কিছুই করার থাকে না। সেই সঙ্গে গাড়ির জ্বালানি থেকে নির্গত ধোঁয়া আর হর্নের তির্যক শব্দ ঢাকাসহ মহানগরগুলোর পরিবেশকে যেভাবে দূষিত করছে তার ক্ষতি পোশানোর কোনো কার্যকর ব্যবস্থা এখনো চোখে পড়ার মতো নয়।
২০১০ সালে ঢাকাসহ মহানগরগুলোর অভ্যন্তরীণ এবং মহানগরগুলোর সঙ্গে যুক্ত আন্তজেলা সড়কের পরিমাপ যা ছিল এখনো তাই আছে। হয়েছে সংস্কার, কোথাও কোথাও সরু সড়ক একটু চওড়া হয়েছে; কিন্তু বিআরটিএর ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত তথ্য থেকে দেখা যায়, গাড়ি চলার মতো উপযোগী সড়ক সেভাবে না বাড়লেও নিবন্ধিত গাড়ির সংখ্যা বেড়েছে আশঙ্কাজনকভাবে। কিছু উড়াল সড়ক এবং মেট্রোরেলের ব্যবস্থা সেই ঘাটতি পূরণে কোনো কার্যকর ভূমিকা রাখছে না। কারণ নিবন্ধিত গাড়িগুলো তো সড়ক ছাড়েনি। তাই যানজট মুক্ত হওয়ার কোনো সুলক্ষণ নগরবাসী দেখছে না। এ বিষয়ে একজন সাধারণ নাগরিক হিসেবে আমার কিছু ৭টি প্রস্তাবনা নিম্নে তুলে ধরলাম-
০১। অনিবন্ধিত সব যানবাহনকে বাধ্যতামূলকভাবে নিবন্ধন করাতে হবে।
০২। গাড়ির মান ও ধরন ভেদে সব গাড়ির মেয়াদকাল নির্ধারিত হওয়া দরকার। মেয়াদ শেষে সেই গাড়িগুলোকে ঢাকাসহ সব মহনগর ও জেলা শহরে চলাচল নিষিদ্ধ করে বিআরটিএর বিশেষ অনুমোদন সাপেক্ষে মফস্বলে চলার সুযোগ দেওয়া যেতে পারে।
০৩। প্রতি বছর যে পরিমাণ গাড়ি মেয়াদোত্তীর্ণ হবে সরকারি কর্মচারীদের অবসরে যাওয়ার মতো তাদেরও সড়ক নগর-মহানগরের সড়ক থেকে বিদায় জানিয়ে সেই স্থলে নতুন গাড়ির নিবন্ধন প্রথা চালু করা যেতে পারে।
০৪। গাড়ি নিবন্ধনের আগে কোন এলাকায় গাড়িটি চলবে সেই সড়কের ধারণক্ষমতা আছে কি না যাচাই করা যেতে পারে।
০৫। এক ব্যক্তি বা তার পরিবারের জন্য একের অধিক ব্যক্তিগত গাড়ি নিবন্ধন দেওয়া নিরুৎসাহিত করা যেতে পারে।
০৬। পরিকল্পিত নগরায়ণ ও সড়ক নেটওয়ার্কের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সড়ক নির্মাণে মনোযোগী হতে হবে।
০৭। অগ্রাধিকার দিতে হবে সড়ক উন্নয়ন এবং মেট্রোরেল ও উড়াল সড়কের প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নের কাজকে।
যথাযথ কর্তৃপক্ষ যদি একটু গভীর মনোযোগ দিয়ে সমাধানের উপায়গুলো নিয়ে কাজ করেন তাহলে আশা করা যায় আমাদের যানজট সমস্যা অনেকাংশে কমে গিয়ে একটি সুন্দর ও স্বস্থিকর সড়ক ব্যবস্থাপনা এ দেশেও আমরা প্রতিষ্ঠা করতে পারব। দেশ হবে যানজটের অপবাদ মুক্ত।
লেখক: কলামিস্ট

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে অপরিহার্য উপাদান হলো প্লাস্টিক ও পলিথিন যা প্রতিদিন ঘুমভাঙা থেকে ঘুমুতে যাওয়ার আগ পর্যন্ত সময়ে আমাদের জীবনে জড়িয়ে আছে।
এই প্লাস্টিকজাতীয় দ্রব্য যা পোড়ালে বাতাস দূষিত হয়, মাটিতে ফেলে রাখলে মাটি নষ্ট হয়, নদীতে বা সাগরে ফেলে দিলে সেখানেও পানিদূষণ হয়। এগুলো কখনো পচেও না বা গলেও না অর্থাৎ অপচনশীল দ্রব্য। এ দেশের ফসলি জমি, শহরের ড্রেন, নদ-নদী, খাল-বিলের মাটি, পানি ও পরিবেশকে ধ্বংসের দিকে ক্রমাগত ঠেলে দিচ্ছে এই প্লাস্টিক সুতরাং প্লাস্টিক ও পলিথিনের ব্যবহার যত দ্রুত সম্ভব ক্রমান্বয়ে বন্ধ করে দিতে হবে। এবং সবাইকে এর ভয়াবহতা বুঝতে হবে। এটা যে আমাদের পরিবেশ, জীববৈচিত্র্য ও মানবদেহের জন্য কতটা ক্ষতিকর বা ঝুঁকিপূর্ণ তার বাস্তবতা অনুধাবন করতে হবে। নদী কিংবা সমুদ্রগুলোতে অনেক বেশি প্লাস্টিক ও পলিথিন ফেলার কারণে তা পানির নিচে স্তূপাকারে জমা হচ্ছে। ফলে নদীর মাছ এই অপচনশীল দ্রব্য এবং সামুদ্রিক মাছও তা খায়। আমরা ওই মাছ খাওয়ার পর প্রায়ই নানারূপ শারীরিক সমস্যা হয়ে থাকে যা পরবর্তীতে টের পাই। প্রতি বছরে প্রায় ৯ লাখ টন প্লাস্টিক আমাদের সাগর কিংবা মহাসাগরে জমা হচ্ছে। এভাবে যদি জমার পরিমাণ বাড়তেই থাকে, তাহলে ২০৩০ সালের দিকে তার সংখ্যা দাঁড়াবে প্রায় ২ কোটি ২০ লাখ টন, তা কতটা ভয়াবহ হবে, কেউ কি একবার তা ভেবে দেখেছেন? এখনি একটু ভাবতে হবে।
বাংলাদেশে এক সময় মৃৎশিল্পের বা মাটির তৈরি জিনিসের ব্যাপক প্রচলন ছিল। শহরে চিনামাটির ও কাচের অ্যালুমিনিয়ামের তামা, কাঁসা, পিতলের তৈজসপত্রের ব্যবহার ছিল কিন্তু আধুনিকতার ছোঁয়ায় এসব শিল্প প্রায় হারিয়ে যেতে বসেছে। দেশে কামার ও কুমারের সংখ্যা অনেকটাই কমে গেছে। মানুষ এখন মাটির তৈরি জিনিস শৌখিন পণ্য হিসেবে ব্যবহার করে, ড্রয়িং রুমে সাজিয়ে রাখে কিন্তু আমাদের দৈনন্দিন জীবনচর্চায় এটি আবার ফিরিয়ে নিয়ে আসতে হবে। আমরা যদি পাট, কাঠ, বাঁশ, বেত ইত্যাদির তৈরি পণ্য ব্যবহার করতে পারি, তাহলে ব্যাপক কর্মসংস্থান হবে। সহজলভ্য হবে এবং আনন্দের বিষয় যে এসব পণ্য আবার পরিবেশবান্ধবও। এসব পণ্য আমরা আমাদের অফিস-আদালত, বাসা-বাড়ি থেকে শুরু করে সর্বত্র ব্যবহার করতে পারি। পানির বোতল, কাপ, প্লেট, চামচ ইত্যাদি অনেক পণ্যের বিকল্প কাগজের তৈরি পণ্যও রয়েছে। তবে আমরা হরহামেশাই ছোটখাটো সব কাজেই কমবেশি পলিথিনের ব্যাগ ব্যবহার করছি। পাটের তৈরি ব্যাগ পলিথিনের বিকল্প হতে পারে। অতীতে আমরা মাটির পাত্র, কাঁসার পাত্র, সিরামিক ও কাচের পাত্রের ব্যাপকহারে ব্যবহার করতাম; কিন্তু সময়ের পরিক্রমায় তা বরং কমে গেছে।
পলিথিনের মধ্য থেকে বিষফেনোল নামক বিষ নির্গত হয় এবং খাদ্যদ্রব্যের সঙ্গে মিশে যায়। পলিথিন মাটির সঙ্গে মেশে না, বরং মাটির উর্বরতা শক্তি নষ্ট করে। ডাস্টবিনে ফেলা পলিথিন বৃষ্টির পানির সঙ্গে ড্রেনে ঢুকে পড়ে। ফলে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি করে। পলিথিন নদীর তলদেশে জমা হয়ে নদীর তলদেশ ভরাট করে ফেলে। পলিথিন পোড়ালে তাতে বায়ুদূষণ ঘটে। বাংলাদেশে ১৯৮২ সাল থেকে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে পলিথিনের উৎপাদন শুরু হয়। পলিথিনের অতি ব্যবহারের কারণে ১৯৯৮ সালে রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন শহরে পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থা মারাত্মকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে।
পলিথিন দামে সস্তা কিন্তু এর বিকল্প পাটের তৈরি সোনালি ব্যাগ উদ্ভাবন হওয়া সত্ত্বেও শুধু সরকারি উদ্যোগ ও উদাসীনতার অভাবে পলিথিনের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হচ্ছে না। বর্জ্য পদার্থ রিসাইক্লিংয়ের মাধ্যমে উৎপাদিত পলিথিন ব্যাগ শুধু খাদ্যসামগ্রীকেই বিষাক্ত করছে তা নয়, প্রতি বছর বর্ষা মৌসুমে শহরগুলোতে যে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হচ্ছে তার প্রধান কারণ অনিয়ন্ত্রিতভাবে পলিথিন ব্যাগের ব্যবহার। কেননা শহরের নর্দমা ও বর্জ্য নির্গমনের পথগুলো পলিথিন দ্বারা পূর্ণ। পলিথিনের কারণে পানি আটকে সৃষ্টি হচ্ছে জলাবদ্ধতা। এক গবেষণায় বলা হয়েছে, শুধু ঢাকাতেই প্রতিদিন ১ কোটি ৪০ লাখ পলিথিন ব্যাগ জমা হচ্ছে। ব্যবহৃত পলিথিন গলিয়ে আবার ব্যবহার করায় এতে রয়ে যাচ্ছে বিষাক্ত কেমিক্যাল, যা থেকে ক্যানসার, চর্মরোগ, লিভার, কিডনি ড্যামেজসহ জটিল রোগের সৃষ্টি হচ্ছে।
পলিথিন ব্যাগের মূল উপাদান সিনথেটিক পলিমার তৈরি হয় পেট্রোলিয়াম থেকে। এই বিপুল পরিমাণ পলিথিন ব্যাগ তৈরিতে প্রতি বছর পৃথিবীজুড়ে মোট খনিজ তেলের ৪ শতাংশ ব্যবহৃত হয়। এক গবেষণায় দেখা গেছে, এক টন পাট থেকে তৈরি থলে বা বস্তা পোড়ালে বাতাসে ২ গিগা জুল তাপ এবং ১৫০ কিলোগ্রাম কার্বন ডাইঅক্সাইড ছড়িয়ে পড়ে। অন্যদিকে এক টন পলিথিন ব্যাগ পোড়ালে বাতাসে ৬৩ গিগা জুল তাপ এবং ১৩৪০ টন কার্বন-ডাইঅক্সাইড বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে। ঢাকা ওয়াসার মতে, শুধু ঢাকায় ১০০ কোটি পলিথিন ব্যাগ ভূপৃষ্ঠের নিচে পরিত্যক্ত অবস্থায় রয়েছে। ফলে মাটির নিচেও সৃষ্টি হচ্ছে নতুন নতুন স্তর, যা ভূপৃষ্ঠে স্বাভাবিক পানি ও অক্সিজেন প্রবাহকে বাধাগ্রস্ত করে জমির শস্য উৎপাদন ক্ষমতা ধ্বংস করছে। একই সঙ্গে রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে ভূপৃষ্ঠকে ক্রমাগত উত্তপ্ত করে তোলার নেপথ্যে রয়েছে পলিথিনের অবদান, যা থেকে ভূমিকম্প, বজ্রপাত, আল্ট্রা ভায়োলেট রেডিয়েশনের মতো ঘটনা ঘটছে। এসব ক্ষতির বিবেচনা করে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা খাদ্যশস্য ও চিনি মোড়কীকরণ করার জন্য পরিবেশবান্ধব পাটের বস্তা বা থলে ব্যবহারের সুপারিশ করেছে।
পরিবেশ দূষণের দায়ে কল-কারখানাকে জরিমানা কিংবা নদ-নদী ও জলাশয় দূষণ বা দখলকারীদের বিরুদ্ধে প্রশাসনের ভূমিকা চোখে পড়ার মতো হলেও পলিথিনের ব্যবহার রোধে আইনের কঠোর প্রয়োগ তেমন নেই বললেই চলে। এ কারণে সর্বত্র নিষিদ্ধ পলিথিনের ব্যবহার উদ্বেগজনক হারে বাড়ছে। যদিও এ অপরাধ বন্ধে সচেতনতারই বেশি দরকার। তবু আইনের প্রয়োগও বাড়াতে হবে। না হলে এর উৎপাদন, বিপণন ও ব্যবহার বন্ধ করা যাবে না। এ আইনের সঠিক বাস্তবায়ন না থাকায় অসাধু ব্যবসায়ীরা অবাধে নিষিদ্ধ পলিথিন উৎপাদন ও বাজারজাত করে আসছে। এ ছাড়া বর্তমানে পলিথিনের কাঁচামাল দিয়ে এক ধরনের টিস্যু পলিথিন উৎপাদন করা হচ্ছে। উৎপাদনকারীরা বলছে, এটা ‘পরিবেশবান্ধব’। কিন্তু বুয়েটের এক পরীক্ষায় দেখা গেছে, পলিথিনের মতোই টিস্যু পলিথিন পরিবেশের জন্য ‘মারাত্মক ক্ষতিকর’। অথচ, পলিথিনের বিকল্প হিসেবে নতুন উদ্ভাবিত পরিবেশবান্ধব পাটের সোনালি ব্যাগ সহজেই ব্যবহার করা যায়, দরকার শুধু সকলের উদ্যোগ ও সদিচ্ছা।
পলিথিনের উৎপাদন ও ব্যবহার রোধে প্রশাসন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয় বা অধিদপ্তরকে অধিক সতর্ক হতে হবে এবং পলিথিন ব্যাগ নিষিদ্ধকরণ আইন কঠোরভাবে প্রয়োগ করতে হবে।
বাংলাদেশসহ বিশ্বের ৭২টি দেশ পলিথিনের ব্যবহার নিষিদ্ধ করেছে। সব দেশই পলিথিনের ব্যবহার বন্ধে শাস্তির বিধান করলেও ব্যবহার বন্ধ করা যায়নি। কেনিয়া সরকার কারও হাতে পলিথিন দেখলেই গ্রেপ্তার করার বিধান জারি করেছিল। আয়ারল্যান্ড সরকার পলিথিন ব্যাগের ব্যবহার কমাতে বাড়তি করারোপ করেছে। পর্তুগাল, স্পেনও এ ধরনের পদক্ষেপ নিয়েছে। উগান্ডার বিমানবন্দরে পলিথিনসহ কাউকে পেলে তাকে গ্রেপ্তার করার বিধান রাখা হয়েছিল, কিন্তু পলিথিনের বিকল্প জানা না থাকায় তা বেশি দিন বাস্তবায়ন করা যায়নি।
পানিতে বর্জ্যের ৭০ শতাংশ পলিথিন ব্যাগ। এ কারণে ২০২০ সাল থেকে ইউরোপের দেশগুলোতে পলিথিন ব্যাগ নিষিদ্ধ করার আইন করছে ইউরোপীয় পার্লামেন্ট। ইউরোপেই বছরে ১০০ বিলিয়ন (১০ হাজার কোটি) পলিথিন ব্যাগ ব্যবহৃত হয়। এসব দেশ পলিথিন ব্যাগ বন্ধে আইন করলেও বিকল্প জানা না থাকায় এর ব্যবহার পুরোপুরি বন্ধ করতে পারছে না। প্রতি মাসে ৪ কোটি ১০ লাখ পিস পলিথিন ব্যাগ ব্যবহার করা হয়। বাংলাদেশে পলিথিনের বিকল্প সোনালি ব্যাগ তৈরি করে সাড়া ফেলার পর এখন বৃহৎ পরিসরে বাণিজ্যিক উৎপাদনে যেতে পারলে এটি দিয়েই দেশীয় বাজারের পাশাপাশি বিশ্ববাজার দখল করা সম্ভব।
পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর পলিথিনের ব্যাগ বিশ্বজুড়ে যখন উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে, তখন পাটের এই প্রাকৃতিক পলিব্যাগ বিশ্বের পরিবেশ দূষণ কমাতে সহায়তা করবে। দেশীয় চেইনশপগুলো এই সোনালি ব্যাগ ব্যবহার করতে আগ্রহ প্রকাশের পাশাপাশি বিশ্ববাজারে এর বিপুল চাহিদা রয়েছে। এ জন্য দরকার সরকারি উদ্যোগ ও সুষ্ঠু পরিকল্পনা ও বাজেটে বরাদ্দ বৃদ্ধি।
বছরে ৫০০ বিলিয়ন পচনশীল পলিব্যাগের বৈশ্বিক চাহিদা রয়েছে। বিশ্বের এই চাহিদাকে কাজে লাগিয়ে পাটের সোনালি ব্যাগ উৎপাদন করতে পারলে তা যেমন বাংলাদেশের অর্থনীতিতে নতুন ধারার সূচনা করবে, তেমনি রক্ষা পাবে আমাদের পলিথিন ব্যাগে কলুষিত পরিবেশ।
এখন কাগজ ও পাটের ব্যাগের ব্যবহারই আমাদের পলিথিনের ভয়াবহতা থেকে পরিবেশকে সুরক্ষা দিতে পারে। পাটের সোনালি ব্যাগ পরিবেশবান্ধব ও দামে সাশ্রয়ী। পলিথিনের উৎপাদন, বিপণন ও বাজারজাত বন্ধে সরকারের ব্যাপক নজরদারিসহ গণমাধ্যমগুলোতে (রেডিও, টেলিভিশন, পত্রিকা, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম) ব্যাপক প্রচারণা দরকার। পাশাপাশি পাটের ও কাগজের ব্যাগের ইতিবাচক দিক, সাশ্রয়ী দাম ও সহজে প্রাপ্তির বিষয়গুলো বিবেচনায় নিয়ে পরিবেশ সুরক্ষায় পলিথিনমুক্ত বাংলাদেশ গড়া দরকার।
তাই নিজেদের স্বার্থে এবং পরিবেশের সুরক্ষায় ক্ষতিকর পলিথিন ব্যাগের ব্যবহার বন্ধ করতে হবে। কারণ এগুলো অতিপ্রয়োজনীয় পানি এবং মাটি মারাত্মকভাবে দূষণ করছে। বিভিন্নভাবে মানুষের শরীরে প্রবেশ করে ক্যানসারের সৃষ্টি করছে। এর বিকল্প হিসেবে পাটের তৈরি সোনালি ব্যাগের ব্যবহার বাড়াতে হবে।
পলিথিন ব্যাগের মূল উপাদান সিনথেটিক পলিমার তৈরি হয় পেট্রোলিয়াম থেকে। এই বিপুল পরিমাণ পলিথিন ব্যাগ তৈরিতে প্রতি বছর পৃথিবীজুড়ে মোট খনিজ তেলের ৪ শতাংশ ব্যবহৃত হয়। এক গবেষণায় দেখা গেছে, এক টন পাট থেকে তৈরি থলে বা বস্তা পোড়ালে বাতাসে ২ গিগা জুল তাপ এবং ১৫০ কিলোগ্রাম কার্বন ডাইঅক্সাইড ছড়িয়ে পড়ে। অন্যদিকে এক টন পলিথিন ব্যাগ পোড়ালে বাতাসে ৬৩ গিগা জুল তাপ এবং ১৩৪০ টন কার্বন-ডাইঅক্সাইড বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে। ঢাকা ওয়াসার মতে, শুধু ঢাকায় ১০০ কোটি পলিথিন ব্যাগ ভূপৃষ্ঠের নিচে পরিত্যক্ত অবস্থায় রয়েছে। ফলে মাটির নিচেও সৃষ্টি হচ্ছে নতুন নতুন স্তর, যা ভূপৃষ্ঠে স্বাভাবিক পানি ও অক্সিজেন প্রবাহকে বাধাগ্রস্ত করে জমির শস্য উৎপাদন ক্ষমতা ধ্বংস করছে। একই সঙ্গে রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে ভূপৃষ্ঠকে ক্রমাগত উত্তপ্ত করে তোলার নেপথ্যে রয়েছে পলিথিনের অবদান, যা থেকে ভূমিকম্প, বজ্রপাত, আল্ট্রা ভায়োলেট রেডিয়েশনের মতো ঘটনা ঘটছে। এসব ক্ষতির বিবেচনা করে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা খাদ্যশস্য ও চিনি মোড়কীকরণ করার জন্য পরিবেশবান্ধব পাটের বস্তা বা থলে ব্যবহারের সুপারিশ করেছে।
প্রায় ২৫ বছর আগে করা পরিবেশ সংরক্ষণ আইনে ২০০২ সালে সংশোধনী এনে পলিথিনের উৎপাদন ও বাজারজাত নিষিদ্ধ করা হয়। সরকার এ ঘোষণা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫-এর ৬(ক) ধারাটি সংযোজন করা হয়। আইনের ১৫ ধারায় বলা হয়েছে, যদি কোনো ব্যক্তি নিষিদ্ধ পলিথিনসামগ্রী উৎপাদন, আমদানি বা বাজারজাত করে তাহলে ১০ বছরের কারাদণ্ড বা ১০ লাখ টাকা জরিমানা, এমনকি উভয় দণ্ডও হতে পারে। শুধু প্রশাসনের সদিচ্ছা থাকলেই পলিথিনের ব্যবহার রোধ করা সম্ভব। এজন্য পরিবেশ মন্ত্রণালয় বা অধিদপ্তরকে অধিক সতর্ক হতে হবে এবং পলিথিন ব্যাগ নিষিদ্ধকরণ আইন কঠোরভাবে প্রয়োগ করতে হবে।
বাংলাদেশসহ বিশ্বের ৭২টি দেশ পলিথিনের ব্যবহার নিষিদ্ধ করেছে। সব দেশই পলিথিনের ব্যবহার বন্ধে শাস্তির বিধান করলেও ব্যবহার বন্ধ করা যায়নি। কেনিয়া সরকার কারও হাতে পলিথিন দেখলেই গ্রেপ্তার করার বিধান জারি করেছিল। আয়ারল্যান্ড সরকার পলিথিন ব্যাগের ব্যবহার কমাতে বাড়তি কর আরোপ করেছে। পর্তুগাল, স্পেনও এ ধরনের পদক্ষেপ নিয়েছে। উগান্ডার বিমানবন্দরে পলিথিনসহ কাউকে পেলে তাকে গ্রেপ্তার করার বিধান রাখা হয়েছিল, কিন্তু পলিথিনের বিকল্প জানা না থাকায় তা বেশি দিন বাস্তবায়ন করা যায়নি।
পরিবেশ দূষণের দায়ে কল-কারখানাকে জরিমানা কিংবা নদ-নদী ও জলাশয় দূষণ বা দখলকারীদের বিরুদ্ধে প্রশাসনের ভূমিকা চোখে পড়ার মতো হলেও পলিথিনের ব্যবহার রোধে আইনের কঠোর প্রয়োগ তেমন নেই বললেই চলে। এ কারণে সর্বত্র নিষিদ্ধ পলিথিনের ব্যবহার উদ্বেগজনক হারে বাড়ছে। যদিও এ অপরাধ বন্ধে সচেতনতারই বেশি দরকার। তবু আইনের প্রয়োগও বাড়াতে হবে। না হলে এর উৎপাদন, বিপণন ও ব্যবহার বন্ধ করা যাবে না। এ আইনের সঠিক বাস্তবায়ন না থাকায় অসাধু ব্যবসায়ীরা অবাধে নিষিদ্ধ পলিথিন উৎপাদন ও বাজারজাত করে আসছে। এ ছাড়া বর্তমানে পলিথিনের কাঁচামাল দিয়ে এক ধরনের টিস্যু পলিথিন উৎপাদন করা হচ্ছে। উৎপাদনকারীরা বলছে, এটা ‘পরিবেশবান্ধব’। কিন্তু বুয়েটের এক পরীক্ষায় দেখা গেছে, পলিথিনের মতোই টিস্যু পলিথিন পরিবেশের জন্য ‘মারাত্মক ক্ষতিকর’। অথচ, পলিথিনের বিকল্প হিসেবে নতুন উদ্ভাবিত পরিবেশবান্ধব পাটের সোনালি ব্যাগ সহজেই ব্যবহার করা যায়, দরকার শুধু সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগ ও ব্যবসায়ীসহ আপামর জনসাধারণদের সদিচ্ছা।
পরিবেশের সৌন্দর্যবর্ধনে আমাদের ব্যক্তিপর্যায়ে প্রত্যেককে সচেতন হতে হবে। প্লাস্টিক ও পলিথিনের ব্যবহার কীভাবে রোধ করা যায়, তার পদ্ধতি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা নিতে হবে। বর্তমানে বিভিন্ন বাজার থেকে শুরু করে বাসাবাড়িতেও প্লাস্টিক ও পলিথিন ব্যবহারের মাত্রা বেড়েছে। সুতরাং এ বিষয়ে সবাইকে অনেক অনেক সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। পাশাপাশি যথাযথ বাস্তবায়নের মাধ্যমেই সম্ভব আমাদের পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্যকে টিকিয়ে রাখা। প্রধানমন্ত্রী পরিবেশ ও জলবায়ুর ভারসাম্য বজায় রাখতে আপামর জনসাধারণসহ প্রশাসনের সর্বত্র সজাগ দৃষ্টি রাখতে সবাইকে অনুরোধ করেছেন। আমাদের সবার উচিত প্রধানমন্ত্রীর ডাকে সাড়া দিয়ে দেশের সর্বত্র যতটুকু সম্ভব প্লাস্টিক ও পলিথিন যা আমাদের জন্য অবশ্যই ক্ষতিকর তা পরিহার করা ও এটার মর্মার্থ অনুধাবন করা প্রতিটি নাগরিকের আবশ্যিক কর্তব্য পালন করা।
লেখক: পরিবেশবিষয়ক গবেষক

বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ২ জুন তারিখে জাতীয় প্রেস ক্লাবে বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমানের এক স্মরণসভায় জামায়াতের রাজনীতির মধ্যে বৈজ্ঞানিক কৌশলের চর্চার ভূয়সী প্রশংসা করতে গিয়ে সেটিকে কমিউনিস্ট পার্টির রাজনৈতিক চর্চার অনুকরণের সঙ্গে তুলনা করেছেন। তার এই দুই মেরুর দুই আদর্শের রাজনীতির চর্চার সাদৃশ্যকরণ নিয়ে গণমাধ্যমে কিছু কিছু আলোচনা, সমালোচনা হচ্ছে। তবে কোনো কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে এ ধরনের তুলনাকরণ নিয়ে কোনো ধরনের প্রতিবাদ গণমাধ্যমের কোথাও চোখে পড়েনি। বিষয়টি নিয়ে অনেকের মধ্যেই বেশ বিভ্রান্তি রয়েছে। দৃশ্যত কমিউনিস্ট পার্টিগুলোর মধ্যে যেমন বইপুস্তক পড়ার একটি নিয়ম রয়েছে, জামায়াতে ইসলামের মধ্যেও তেমনি তাদের আদর্শের বইপুস্তক পড়ার প্রচলন রয়েছে বলে শোনা যায়। এটি যারা প্রত্যক্ষ করেছেন তারা মির্জা ফখরুলের বক্তব্যে হয়তো মিল খুঁজে পাবেন; কিন্তু মির্জা ফখরুল একজন বিএনপির মতো রাজনৈতিক দলের মহাসচিব হয়ে নিজের দলের নেতা-কর্মীদের রাজনৈতিক পড়াশোনার প্রয়োজনীয়তার কথা বলতে গিয়ে কেন জামায়াত শিবিরের অনুসৃত ব্যবস্থার শুধু উদাহরণই দিলেন না, এটিকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বলেও ভূয়সী প্রশংসা করলেন। এবং এটিকে কমিউনিস্ট পার্টির চর্চার সঙ্গে একাকার করে দেখলেন- তা বোঝা গেল না। রাজনীতিতে অবশ্যই নেতা-কর্মীদের পড়াশোনা করা দরকার আছে।
বিএনপির নেতা-কর্মীরা কি ধরনের বই পড়বেন বা চর্চা করবেন সেটি তাদের দলীয়নীতি আদর্শ বাস্তবায়নের সঙ্গে অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। জিয়াউর রহমানও তার জীবদ্দশায় যখন নতুন রাজনৈতিক দল বিএনপি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তখন তিনি বিএনপির একটি গবেষণা সেল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সেটি ১৯৭৮-৭৯ এর পর বেশ গুরুত্ব দিয়ে প্রচার করা হতো। বিএনপির সিনিয়র নেতাদের তখন এই গবেষণা সেলের প্রশিক্ষণ কোর্সে জিয়াউর রহমান সাহেবের বক্তৃতা শুনতে হতো এবং জিয়াউর রহমান সাহেব নেতাদের নানা ধরনের পরীক্ষা নিতেন, অনেকটা যেন হাতে-কলমে রাজনীতি শেখাতেন! জিয়াউর রহমান নিজে ছিলেন পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীর একজন ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চের কর্মকর্তা। রাজনৈতিক দল কিংবা দলীয় রাজনীতি করার কোনো সুযোগ না থাকলেও গোটা আইয়ুব আমলে তিনি তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানের সেনাবাহিনীতে বেশ দাপটের সঙ্গেই চাকরি করতেন। আইয়ুবের সামরিক শাসন তার চাকরিজীবনের সেই সময়ের দিনগুলোতেই কেটেছিল। সেখানে সেই সময়ে কর্মরত বেশ কয়েকজন বাঙালি সামরিক কর্মকর্তার সঙ্গে তার সখ্যতা কতটা ছিল তা জানা যায় তাদেরই লেখা বিভিন্ন স্মৃতিমূলক গ্রন্থে। এরপর ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে চট্টগ্রামে থাকার সুবাদে তিনি অংশ নিতে পেরেছিলেন। স্বাধীনতার পর সেনাবাহিনী তিনি গুরুত্বপূর্ণ পদে থেকে অবশেষে বঙ্গবন্ধু হত্যার পর প্রধান সেনাপতি পদ লাভ করেন। পরে তিনি সামরিক শাসক থেকে ১৯৭৮ সালে রাজনীতিবিদ হিসেবে পদার্পণ করেন। জিয়াউর রহমানের প্রতিষ্ঠিত ‘রাজনীতি ও সমাজ বিজ্ঞান শিক্ষা কেন্দ্রে’ যেসব বক্তৃতা তিনি দিতেন সেগুলো ১৯৯২ সালে ‘জিয়াউর রহমান, আমার রাজনীতির রূপরেখা’ শিরোনামে এ কে এ ফিরোজ নুনের সম্পাদনায় সংকলন আকারে প্রকাশিত হয়েছে। তাতে তিনি ১৯ দফা, জাতীয়তাবাদ, বাঙালি, বাংলাদেশি, ধর্মীয় মূল্যবোধ নানা বিষয়ে তার নিজের মতো করে কতগুলো বক্তৃতা দিয়েছেন। এসব বক্তৃতা অনেকটাই মেঠো বক্তৃতা ছিল। তাতে রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্যের কোনো জ্ঞানতাত্ত্বিক আলোচনাই খুঁজে পাওয়া যায় না। যেহেতু তিনি দলের প্রধান তাই বি চৌধুরীসহ অনেকেই যা বক্তৃতা শুনতেন সেগুলোর ওপর নানা কুইজ পরীক্ষাও হতো। জেনারেল জিয়াউর রহমান সাহেব সেই সব পরীক্ষায় নম্বরও দিতেন। অতীতে ডান-বাম রাজনীতি করা পরিচিত অনেক নেতাই জিয়াউর রহমানের এসব প্রশিক্ষণে অংশ নিতেন, তাদের প্রশ্ন-উত্তরে জিয়াউর রহমান সব সময় খুব একটা সদয় হতে পারেননি। সেটি সেই প্রশিক্ষণ পরীক্ষার নমুনাতে এখনো খুঁজলে পাওয়া যাবে। জিয়াউর রহমানের প্রবর্তিত রাজনৈতিক প্রশিক্ষণের ফলাফল বিএনপিকে কি দিয়েছে বা বিএনপি কি লাভ করেছে তা বোধহয় সেই সময়ের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অভিজ্ঞতা থেকেই বুঝে নেওয়া যেতে পারে।
মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এক সময় বাম রাজনীতি করতেন। বামদের সে রকম কিছু প্রশিক্ষণের নিয়ম বিভিন্ন সংগঠনে রয়েছে। এটিকে অনেকেই বলে থাকে লাল বই পাঠের চর্চা। সেগুলোতে চেয়ারম্যান মাও সে তুং, মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিনসহ আরও অনেক মার্কসবাদী নেতাদের লেখা কিংবা তাদের ওপর আলোচিত বই পাঠ করা হতো কিংবা কোনো কোনো নেতা আলোচনা করতেন। আমি এটিকে একেবারেই খারাপ কিছু বলি না। তবে এসব বই পড়ে কতজনই বা কমিউনিস্ট রাজনীতি ভালো করে বুঝেছেন। সেটি একটি ভিন্ন বিষয়, প্রশিক্ষণের দুই-চারটি বই পড়ে কিংবা লেকচার শুনে জটিল মার্কসবাদী লেনিনবাদী দর্শন, অর্থনৈতিক তত্ত্ব ও সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের ইতিহাস জানা বা বোঝা মোটেও খুব সহজ ব্যাপার বলে মনে করার কোনো কারণ নেই। কমিউনিস্ট আন্দোলনে এসব বইয়ের লেখা তাত্ত্বিক আলোচনা বোঝা না বোঝা থেকেই অনেক বিভ্রান্তি, বিভক্তি কমিউনিস্ট আন্দোলনের মধ্যেই জন্ম নিয়েছিল। সেখান থেকে বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টি, মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি, লেনিনবাদী, মাওবাদী, সর্বহারা ইত্যাদি অসংখ্য নামে শুধু পার্টিই নয়, দলের নেতারাও কেউ কেউ নিজেদের কর্মীদের মধ্যে সেভাবে উপস্থাপন করে, তাদের দেশীয় মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তাত্ত্বিক বলেই খেতাব দেওয়া হতে থাকে। অনেকটাই পীরতন্ত্রের প্রভাব এতে দেখা যেত। কমিউনিস্ট নেতাদের মধ্যে মতবিরোধ এবং তাত্ত্বিক তথাকথিত ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ নিয়ে যেসব দ্বন্দ্ব দেখা যেত তাতে দলীয় বহু নেতা-কর্মীরই জীবন বিপন্ন হতো, হত্যার শিকার হতেন, আদর্শের নামে অনেক মানবতাবিরোধী কর্মকাণ্ডও এতে চলত। এর প্রধান কারণ হচ্ছে- আদর্শের জন্য তারা সংগঠন গড়ে তুলেছিলেন সেই আদর্শ বোঝা ও ধারণ করা অনেকের পক্ষেই সম্ভব হতো না। এত কম পড়াশোনা জেনে কমিউনিস্ট মতাদর্শকে বোঝা যে সম্ভব নয় সেটি যারা মানতে চান না। তারা কমিউনিস্ট আন্দোলনের ব্যর্থতার কারণগুলোর ব্যাখ্যা নিজেরাই দিতেন তাহলে কমিউনিস্ট আন্দোলন হয়তো উপকৃত হতো। কমিউনিস্ট আন্দোলন অবশ্যই অনেক মহৎ উদ্দেশ্য, আদর্শ ও কর্মকাণ্ডকে সামনে নিয়ে গড়ে ওঠার চেষ্টা করেছিল; কিন্তু পৃথিবীর প্রায় কোনো দেশেই সেই আদর্শ বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি। লেনিনের মৃত্যুর পর স্টালিন যা করতে চাইলেন তাতে আর সমাজতন্ত্র আর মার্কসবাদী কিছুই খুঁজে পাওয়া যায়নি। এই প্রসঙ্গে আর বেশি কিছু বলার নেই। আমাদের দেশের কমিউনিস্ট পার্টি এখন অতি ক্ষুদ্র একটি দল; কিন্তু মার্কসবাদী বলে পরিচিত অনেকেই এখন বিভিন্ন দলে নিজেদের পরিচয় দিচ্ছেন। বাম রাজনৈতিক দল বললে এক ধরনের সম্মান পাওয়া যায়; কিন্তু বাম রাজনীতি কেন জনগণের আস্থা অর্জন করতে পারেনি সেই ব্যাখ্যা বামরাও দিতে পারবেন কি না সন্দেহ আছে। সুতরাং কমিউনিস্ট পার্টি দলীয় নেতা-কর্মীদের জন্য বইপুস্তক পড়া, প্রশিক্ষণ নেওয়া ইত্যাদির যে ধারা চালু করেছিল সেটি প্রশংসনীয় হলেও তার সুফল রাজনীতিতে কতটা প্রভাব ফেলেছে সেটি হাজারও বিতর্কের জন্ম দিতে পারে। সেই বিতর্কে নাই বা গেলাম।
অন্যদিকে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর জামায়াতে ইসলামের কৌশলকে বৈজ্ঞানিক বলে যে সনদ প্রদান করেছেন সেটি সম্পর্কে সংক্ষেপে বলা যায় যে ছাত্র সংঘ, ছাত্র শিবির, জামায়াত যেসব বইপুস্তক পড়ে বা পাঠ করায় সেগুলো তাদের দলীয় নেতাদের লেখা বইপুস্তক। গোলাম আযমের লেখা বই পড়ে ছাত্রশিবিরের একজন স্কুল, কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়পর্যায়ের নেতা বা কর্মী যদি নিজেকে রাজনৈতিক প্রাজ্ঞ, বিজ্ঞ ভাবতে শুরু করেন এবং দুনিয়ার তাবৎ গবেষণা গ্রন্থকে মিথ্যা কিংবা বিভ্রান্তিকর বলে মনে করেন। তাহলে বলতে হবে এসব প্রশিক্ষণ কিংবা বইপুস্তক পাঠের ফলাফল মোটের ওপর মগজধোলাই ছাড়া আর কিছুই না। পুরোপুরি অন্ধবিশ্বাস তৈরির বেশি কিছু তাদের কথিত বইয়ে বা প্রশিক্ষণে পাওয়া যায় না। ছাত্র সংঘের নেতা-কর্মীরা রাজনৈতিক প্রশিক্ষণ ও দীক্ষা নিয়ে ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি জান্তার সহযোগী হওয়ার বেশি কিছু নিজেদের ভাবেনি, আল-বদর, আল-শামস হয়ে এ দেশের মানুষকে হত্যা করেছে। বুদ্ধিজীবীদের বধ্যভূমিতে নিয়ে পশুর মতো জবাই করেছে। জিয়াউর রহমান সেই জামায়াতে ইসলামকে রাজনীতি করার অনুমোদন দিলে ছাত্রশিবির নামে তাদের ছাত্র সংগঠন মাঠে নামে। মির্জা ফখরুল সাহেবের স্মরণে কতটা আছে জানি না। ছাত্রশিবিরের কর্মীরাই নিজেদের সহপাঠীদের ভিন্ন আদর্শে বিশ্বাসের কারণে হত্যা করতে মোটেও দ্বিধা করেনি। চট্টগ্রাম কলেজের ছাত্রাবাসে ছাত্র ইউনিয়ন কর্মী শাহাদাতকে গলা টিপে হত্যা করেছে তার সহপাঠী ছাত্রশিবিরের কর্মী। কারণ ছাত্রশিবিরের কর্মীরা ছাত্র ইউনিয়ন এবং ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীদের তাদের আদর্শিক শত্রু হিসেবেই বিশ্বাস করতে শেখে, সেভাবেই শেখানো হয়েছিল। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের বেশির ভাগ বিশ্ববিদ্যালয়ে ৮০-এর দশকে ছাত্রশিবিরের নেতা-কর্মীরা কীভাবে অন্য সংগঠনের নেতা-কর্মী এমনকি শিক্ষককেও হত্যা করেছে সেটি মির্জা ফখরুলের ভুলে যাওয়ার কথা নয়। গোটা ৮০-এর দশকে জামায়াত ইসলামের শিশু সংগঠন ফুল কুড়ি এবং ছাত্র সংগঠন ছাত্রশিবির সারা দেশে স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ইসলামী বিপ্লবের স্বপ্ন দেখাতে নানা ধরনের পাঠচক্র গোপনে পরিচালিত করত। এই পাঠচক্রের ফসলই হচ্ছে স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, মুক্তিযুদ্ধ ইত্যাদির বিরুদ্ধে কিশোর, তরুণ শিক্ষার্থীদের মগজ ধোলাই করা। জামায়াতে ইসলাম যদিও পাকিস্তানের মওদুদি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত জামায়াতে ইসলামেরই অঙ্গসংগঠন কিন্তু এর মূলে রয়েছে মিসরে প্রতিষ্ঠিত ব্রাদারহুডের আদর্শ তথা সারাবিশ্বে ইসলামী বিপ্লব ও রাষ্ট্রব্যবস্থা তৈরি করা। সে আদর্শের বাইরে পৃথিবীর কোনো দর্শনচিন্তা, অর্থনৈতিক তত্ত্ব, বিজ্ঞানসহ আধুনিক জ্ঞানচর্চার কোনো রাজনীতি এই পাঠচক্রে মির্জা ফখরুল দেখাতে পারবেন না। বাংলাদেশে ছাত্রশিবির ও জামায়াত যেসব বইপুস্তক পাঠ করে তা আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানের রাষ্ট্রব্যবস্থা তৈরির জন্য নয়, তাদের উদ্দেশ্য ‘একটি ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা যা ইসলামী বিশ্বব্যবস্থা তৈরিতে ধাবিত হবে।’ সেই দর্শনই জামায়াতে ইসলামের পাঠচক্রের মূল বিষয়। মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এটিকে একটি বিজ্ঞানসম্মত রাজনৈতিক প্রক্রিয়া হিসেবে অভিহিত করেছেন। মির্জা ফখরুলের অভিহিতকরণ তাকে সন্তুষ্ট করতে পারে; কিন্তু যারা আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞান, রাষ্ট্রব্যবস্থা, রাজনীতি ইত্যাদির জটিল বিষয়গুলো নিয়ে পড়াশোনা ও গবেষণা করেন তাদের কাছে এগুলো কতটা মূল্যহীনই শুধু নয়- রাষ্ট্র ও সমাজের জন্য ক্ষতিকর, তাও বুঝতে হলে আরও অনেক কিছু পড়াশোনা করতে হবে।
লেখক: ইতিহাসবিদ ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক

বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এমপিওভুক্ত শিক্ষক নিয়োগের জন্য পঞ্চম গণবিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর শূন্য পদের তুলনায় আবেদনকারীর সংখ্যা অস্বাভাবিক কম হওয়ায় নানা রকম কথা শোনা যাচ্ছে। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে যেকোনো চাকরির বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করলে যেখানে শূন্য আসনের তুলনায় অনেকগুণ বেশি আবেদন পড়ে সেখানে আবেদনের তুলনায় শূন্য আসন চারগুণের বেশি থাকাটা অবশ্যই একটি ব্যতিক্রমী উদাহরণ। ৯৬ হাজার শূন্য আসনের বিপরীতে আবেদন জমা পড়েছে মাত্র ২৪ হাজার। বিভিন্ন যুক্তিযুক্ত কারণে এর থেকেও বাদ পড়তে পারেন দুই-তিন হাজার প্রার্থী। অর্থাৎ আবেদনকারী প্রায় সবার চাকরি হওয়ার সম্ভাবনা শতভাগ। যারা আবেদন করেছেন তারা নিবন্ধন পরীক্ষায় যত কম নম্বরই পেয়ে থাকুক না কেন সবাই যোগ্য বিবেচিত হবেন। অথচ এই চিত্রটি যদি এমন হতো যে শূন্য পদের সংখ্যা ২৪ হাজার আর আবেদনকারীর সংখ্যা ৯৬ হাজার। তাহলে নিশ্চয়ই তুলনামূলক আরও অনেক বেশি নম্বর প্রাপ্তরা যোগ্য বিবেচিত হতেন, শিক্ষক হতেন। অর্থাৎ আমরা আরও অধিক যোগ্য শিক্ষক পেতাম; যারা আগামী প্রায় ২৫-৩০ বছর অগণিত অধিক যোগ্য নাগরিক তৈরি করতেন; কিন্তু তেমনটি হলো না কেন?
সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বলেছেন, যাদের নিবন্ধন সনদের মেয়াদ ৩ বছরের বেশি হয়েছে এবং যাদের বয়স ৩৫ বছর এর বেশি হয়েছে তারা আবেদন করতে পারেননি বলে পঞ্চম গণবিজ্ঞপ্তিতে প্রার্থীর সংখ্যা অত্যন্ত কম হয়েছে। শুধু ১৬তম ও ১৭তম নিবন্ধনে উত্তীর্ণরাই আবেদন করতে পেরেছেন। এরমধ্যে ১৬তম নিবন্ধনে উত্তীর্ণ বেশির ভাগ নিবন্ধনধারীর চাকরি চতুর্থ গণবিজ্ঞপ্তিতে হয়ে গেছে। ফলে ১৭তম নিবন্ধনে উত্তীর্ণ ২৩ হাজার ৯৮৫ জনের মধ্যে যারা আবেদনের যোগ্য ছিল তারাই পঞ্চম গণবিজ্ঞপ্তিতে আবেদন করেছেন। তাই তিন-চতুর্থাংশ পদ আপাতত শূন্য থেকে যাবে! অত্যন্ত তথ্যবহুল এই বাস্তব চিত্রটি সম্পর্কে সংশ্লিষ্টদের পূর্বানুমান থাকাটাই স্বাভাবিক। এমতাবস্থায় কেউ কেউ সরাসরি আবার কেউ কেউ ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে মতামত দিচ্ছেন, যেহেতু নতুন তথা যোগ্যতা ও দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের জন্য শিক্ষকদের শূন্য পদ দ্রুত পূর্ণ করা আবশ্যক সেহেতু নিবন্ধন সনদের মেয়াদের ক্ষেত্রে ও প্রার্থীদের বয়সের ক্ষেত্রে ছাড় দিয়ে পঞ্চম গণবিজ্ঞপ্তিতে আবেদনের সুযোগ দিয়ে এখনই আরও বেশি সংখ্যক শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া উচিত। আদালতের নিষেধাজ্ঞা না থাকলে হয়তো এ দাবি আরও জোরাল হতো এবং তা বাস্তবায়নের জন্য কেউ কেউ সক্রিয় হতেন। আমি মনে করি, তেমন ছাড় দেওয়ার উদাহরণ তৈরি করা মোটেও উচিত নয়। আদালতের নিষেধাজ্ঞা না থাকলেও তেমনটি করা উচিত হতো না। বেসরকারি শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে বয়সে ও যোগ্যতায় ছাড় দেওয়া মানেই আমাদের প্রায় ৯৭ শতাংশ সন্তানকে ঠকিয়ে দেওয়া। সাময়িক সুবিধা/অসুবিধা বিবেচনা করে কিংবা বিশেষ প্রার্থীদের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে তড়িঘড়ি করে তুলনামূলক কম যোগ্য শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া মানেই দীর্ঘ মেয়াদে দেশ ও জাতির অপূরণীয় ক্ষতি করা!
বর্তমান তথ্যপ্রযুক্তির যুগে গত কত দিনে কতজন শিক্ষক নিয়োগ করা প্রয়োজন ছিল এবং আগামী কত দিনে কতজন শিক্ষক অবসরে যাবেন, কতটি পদ শূন্য হবে, কতটি পদ নতুন তৈরি হতে পারে, কতজন শিক্ষক নিয়োগ করা প্রয়োজন হবে এমন একটা সুনির্দিষ্ট ডেটা মেইন্টেন করা খুব একটা কঠিন হওয়ার কথা নয়। মাউশি, বেনবেইস ও এনটিআরসিএ এই তিনটি কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে ডেটা নিয়েই এটি করা সম্ভব। বিশেষ করে ইএমআইএস সেল থেকে শিক্ষকদের যোগদান, পদবি, জন্ম তারিখ ও অবসরের তারিখ সম্পর্কিত সব আপডেট তথ্য এবং এনটিআরসিএ থেকে নিবন্ধন পরীক্ষার ফলাফল, নিবন্ধন সনদধারীদের সংখ্যা, বিভিন্ন সময় যোগদানকারী শিক্ষকদের সংখ্যা ও অবশিষ্ট নিবন্ধনধারীদের সংখ্যাসংক্রান্ত আপডেট তথ্য সমন্বয় করা হলেই শিক্ষক চাহিদা ও যোগ্য প্রার্থীর সম্ভাব্য সংখ্যা নির্ধারণ করা সম্ভব। তেমন পরিকল্পিতভাবে শিক্ষক নিবন্ধন/নিয়োগ পরীক্ষা নিয়মিত সম্পন্ন করা হলে বর্তমান শূন্যতা তৈরি হতো না, ভবিষ্যতেও হবে না।
অন্যদিকে লক্ষণীয় যে, বেসরকারি শিক্ষকদের নিয়োগ যখন কমিটির হাতে ছিল তখন শিক্ষকদের ন্যূনতম মান নিশ্চিত করার প্রয়োজনে শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা প্রবর্তন করা হয়েছিল। সেটি তখন অবশ্যই প্রয়োজন ছিল। এখন যখন শিক্ষক নিয়োগের ক্ষমতা সরকারের হাতে, নিয়োগযোগ্য শিক্ষক বাছাই করা হয় কেন্দ্রীয়ভাবে, পদায়ন করা হয় প্রার্থীদের পছন্দ ক্রমানুসারে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে; তখন শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষার প্রয়োজনীয়তা কতটুকু বিদ্যমান তা ভেবে দেখার সময় এসেছে। একবার নিবন্ধন পরীক্ষা সম্পন্ন করা এবং আবার নিবন্ধিত শিক্ষকদের মধ্য থেকে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা প্রায় দ্বিগুণ সময় সাপেক্ষ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাস্তবে এ কারণেই শূন্য পদের তুলনায় চার ভাগের একভাগ আবেদন পাওয়ার উদাহরণ তৈরি হয়েছে! সরকারি স্কুল-কলেজে যেমন নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দিয়ে, অনূর্ধ্ব ৩০ বছর বয়সি যোগ্য প্রার্থীদের আবেদন নিয়ে, সরাসরি নিয়োগ পরীক্ষা নিয়ে, অধিক যোগ্যদের বাছাই করে, সরাসরি নিয়োগ দেওয়া হয়; ঠিক তেমনিভাবে বেসরকারি স্কুল-কলেজেও নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা সম্ভব, করা উচিত। ফলে নিয়োগ কার্যক্রম ত্বরান্বিত হবে, দ্রুত শূন্য পদ পূর্ণ হবে, শিক্ষার্থীরা অধিক লাভবান হবে। যারা নিয়োগ পাবেন না তারা নিবন্ধনধারীদের মতো বিভিন্ন দাবি-দাওয়া উত্থাপন করে আন্দোলনের সুযোগ পাবেন না। সে ক্ষেত্রে কোনোরূপ প্যানেল তৈরি করাও উচিত নয়। প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের প্যানেলভুক্তদের বিভিন্ন সময় আন্দোলন করতে দেখা গেছে। এতে অধিক যোগ্য, ইয়ং ও এনার্জেটিক প্রার্থী নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা তৈরি হয়। আমাদের সন্তানদের বৃহত্তর স্বার্থেই যেকোনো মূল্যে সর্বাধিক যোগ্য, দক্ষ, কর্মঠ ও উদ্যমী শিক্ষক অত্যাবশ্যক। সর্বাধিক মূল্য দিয়েই আকৃষ্ট করতে হবে তাদের, নিয়োগ করতে হবে অত্যন্ত নিরপেক্ষভাবে।
এনটিআরসিএর অতীত সব রেকর্ড ছাপিয়ে ১৮তম শিক্ষক নিবন্ধন ২০২৪-এ প্রায় ১৮ লাখ ৬৫ হাজার আবেদন পড়েছিল। এদের মধ্য থেকে ‘বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন প্রাথমিক পরীক্ষা’র (প্রিলিমিনারি টেস্ট) ফলাফলে স্কুল ও কলেজপর্যায় মিলিয়ে পাস করেছেন ৪ লাখ ৭৯ হাজার ৯৮১ জন। গড় পাসের হার ৩৫ দশমিক ৮০ শতাংশ। আবেদনকারীর সংখ্যা উৎসাহজনক হলেও উত্তীর্ণের সংখ্যা হতাশাজনক! এরা পরবর্তীতে লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে চূড়ান্তভাবে খুব বেশি সংখ্যায় যোগ্য বিবেচিত হবেন বলে ধারণা করা যাচ্ছে না। ফলে পরবর্তী নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতেও শূন্য পদের বিপরীতে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর সংখ্যা খুব বেশি থাকার সম্ভাবনা নেই। কেননা, বর্তমান শূন্য পদের সঙ্গে পরবর্তীতে আরও শূন্য পদ যুক্ত হবে। যতই দিন যাবে ততই শূন্য পদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। তাই শিগগিরই আরও একটি নিয়োগ/নিবন্ধন বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা উচিত। আগামী জুলাই মাস নাগাদ আরও অনেক ছেলেমেয়ে আবেদনের জন্য একাডেমিক যোগ্যতা অর্জন করবে।
১৮তম শিক্ষক নিবন্ধন ২০২৪-এ প্রায় ১৯ লাখ আবেদন পেয়ে এমন ভাবা উচিত নয়, অধিক যোগ্যরা অন্য চাকরি বাদ দিয়ে বেসরকারি শিক্ষক হতে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। বরং বিপুলসংখ্যক বেকার কোথাও চাকরি না পেয়ে বাধ্য হয়ে এখানে আবেদন করেছেন। এতে যোগ্যরা আপাতত শিক্ষকতায় আসার সম্ভাবনা দেখা গেলেও পরবর্তীতে অধিক যোগ্যরা শিক্ষকতায় থাকার কোনোই সম্ভাবনা নেই! অবশিষ্টরা অন্যান্য চাকরির চেষ্টা করতে করতে বয়স অতিক্রান্ত হলে শিক্ষকতা পেশায় থেকে যেতে বাধ্য হলেও সন্তুষ্ট চিত্তে পাঠদান করার ও উত্তম শিক্ষক হয়ে ওঠার তেমন সম্ভাবনা নেই! কেননা, কর্মীর পূর্ণ জব স্যাটিসফেকশন না থাকলে উত্তম পেশাদারিত্ব অর্জিত হয় না। সাড়ে ১২ হাজার টাকা বেতনে একজন শিক্ষক কোনোভাবেই সন্তুষ্ট থাকতে পারেন না বর্তমান দ্রব্যমূল্য পরিস্থিতিতে। অবাক ব্যাপার হচ্ছে, আমরা অত্যন্ত কম বেতনে তুলনামূলক কম যোগ্য শিক্ষক নিয়োগ করে অন্যান্য ক্ষেত্রের জন্য অধিক যোগ্য, অধিক উপার্জনক্ষম নাগরিক-কর্মী তৈরি করতে চাই! এ ভ্রান্ত ধারণা থেকে এখনই বেরিয়ে আসতে হবে আমাদের। সর্বাধিক যোগ্যদের শিক্ষকতায় আকৃষ্ট করার জন্যই সর্বাধিক বৃদ্ধি করতে হবে শিক্ষকদের আর্থিক ও অনার্থিক সুবিধা। কোনো অবিশ্বাস্য আশ্বাস দিয়ে নয়, ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে কথা বলে নয়, সরাসরি দিতে হবে শিক্ষকদের সুনির্দিষ্ট সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি সম্পর্কিত ঘোষণা। পরিষ্কার প্রকাশ করতে হবে সেই ঘোষণা বাস্তবায়নের টাইমলাইন ও পরিকল্পনা। তারপর প্রকাশ করতে হবে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি। তবেই শিক্ষক হতে এগিয়ে আসবেন অধিক যোগ্যরা, শিক্ষকতায় থাকতে চাইবেন অধিক যোগ্যরা, শিক্ষকতা করতে চাইবেন অধিক মনোযোগ দিয়ে, অধিকাংশরাই হয়ে উঠবেন সফল শিক্ষক, সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হবে যোগ্যতা ও দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম, তৈরি হবে কাঙ্ক্ষিত স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার উপযোগী মানুষ।
লেখক: সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ এবং অধ্যক্ষ, কিশলয় বালিকা বিদ্যালয় ও কলেজ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।

বাংলাদেশ সুজলা-সুফলা এক শান্তিময় দেশ। এ দেশের মৃত্তিকায় জন্ম নিয়েছে অনেক মহীয়সী নর-নারী, অনেক বীর ও বীরাঙ্গনা। আবার এ দেশের সম্পদের লোভে বিশেষ করে সেই গোলাভরা ধান, গোয়ালভরা গরু, সমুদ্র, নদ-নদী, বিল, হাওর, বাঁওড়, পুকুর ও অন্যান্য জলাশয়ভরা মাছ ও সম্পদের কারণে বিদেশিরা বিভিন্ন সময় এ দেশে আগ্রাসন চালিয়েছে এবং এ দেশ শাসন করেছে। তবে এ প্রকৃতি ও পরিবেশের প্রতি আমাদের অবহেলা, অযত্ন, অত্যাচার ও নিপীড়নের কারণে পৃথিবীর সব সম্পদের বহুলাংশ অবনয়ন ও ক্ষতি হয়েছে। সেই সঙ্গে আমাদের সম্পদের যথাযথ ব্যবহারের অভাবে আমরা অনেক বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি। প্রথমে আমাদের মৃত্তিকার স্বাস্থ্য সম্পর্কে আলোচনা করা যাক- একটা কথা বহুল প্রচলিত ও প্রচারিত আছে, এ দেশের মৃত্তিকা খুবই উর্বর এবং এ মৃত্তিকায় যেকোনো সবজি বা ফসলের বীজ বপন করলেই তা কোনো পরিচর্যা ছাড়াই দ্রুত বর্ধিত হয় এবং ফলন দেয়; কিন্তু এ মিথ বা প্রচলিত কথা এখন আর বাংলাদেশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।
বাংলাদেশের মৃত্তিকার এক বড় অংশে জৈব পদার্থের সংকট রয়েছে। এক গবেষণা থেকে জানা যায় বাংলাদেশের প্রায় শতকরা ৭৫ ভাগ জমির জৈব পদার্থের পরিমাণ ১ শতাংশের নিচে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জমিতে শতকরা ৩% থেকে ৬% জৈব পদার্থ থাকা প্রয়োজন। এর কারণ হিসেবে বলা যায় আমাদের রাসায়নিক সারের ওপর অতিশয় নির্ভরতা এবং জৈব সারের প্রয়োজনীয়তা এড়িয়ে বা বাদ দেওয়া বা আমলে না নেওয়া। রাসায়নিক সারের অতিমাত্রায় ব্যবহারের ফলে বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের এবং উত্তরবঙ্গের অনেক ফসলি জমিতে এখন ফসল উৎপাদন মারাত্মক ব্যাহত হচ্ছে। বিশ্ব ব্যাংকের ২০২২ সালের এক জরিপ থেকে জানা যায়, বাংলাদেশ বিশ্বে রাসায়নিক সার ব্যবহারের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় সর্বোচ্চপর্যায়ে আছে। আমার বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা হিসেবে কাজ করার সময় মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইরস্টিটিউটের (এসআরডিআই) ভ্রাম্যমাণ পরীক্ষাগারের কাজের নিমিত্তে বছরে ২ বার দেশের বিভিন্ন জেলার বিভিন্ন থানায় মৃত্তিকা পরীক্ষা ও ফার্টিলাইজার রিকমন্ডেশন দেওয়ার সময় দেখা গেছে কৃষকরা প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশি রাসায়নিক সার ব্যবহার করে থাকে। যা জলাশয়ের পানি, মৃত্তিকা, প্রাণী, মৎস্য ও অনুজীবের ক্ষতির কারণ। আমার এরূপ একজন কৃষকের সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ হয়েছিল। এটা ১৯৯৯ সালের ঘটনা ওই সময়ে আমি মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউটের বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা হিসেবে রাজশাহী পরীক্ষাগারে নিয়োজিত ছিলাম। তো এক দিন একদল কৃষক আসবে জেনে আমার অফিসপ্রধান আমাকে বললেন, আপনি কৃষকদের একটা ক্লাস নেবেন। সে মোতাবেক যথারীতি আমি ক্লাস নিতে শুরু করলাম। ক্লাসের শেষ পর্বটা ছিল কৃষকদের জমি ও জমির ফসলের অবস্থা জানা। এরূপ মতবিনিময়ের সময় একজন কৃষক ভাই অশ্রুজল চোখে আমার কাছে এসে বললেন, আমার জমিতে এখন বেগুন চাষ করতে চাই; কিন্তু বেগুনগাছ আর বড় হচ্ছে না এবং বেগুনের ফুল ও ফল হচ্ছে না। তখন আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম জমিতে কি কি সার ব্যবহার করেন? তিনি জবাবে জানান কেবলমাত্র রাসায়নিক সার ব্যবহার করেন। তখন আমি তাকেসহ সব কৃষক ভাইদের বোঝালাম আপনাদের জমিতে জৈব সারের পরিমাণ অধিক মাত্রায় বাড়াতে হবে। এ লক্ষ্যে গোবর সার, কম্পোস্ট, কেঁচো সার (ভার্মি কম্পোস্ট), ছাই, বাড়ির গৃহস্থালির আবর্জনা, ধানের খড়, গাছের পাতা ইত্যাদি দ্বারা সার তৈরি করে জমিতে প্রয়োগ করতে হবে। একই ফসল বারবার চাষ করা যাবে না। বরং শস্যবর্তন করতে হবে। অর্থাৎ একাধারে সবজি চাষ না করে ধান, পাট, গম, ভুট্টা, ডালজাতীয় ফসল ও ধৈঞ্চার মাধ্যমে সবুজ সার তৈরি করা যেতে পারে।
আমাদের দেশে সম্পদ নেই এ কথা সত্য নয়; আমাদের দেশে জৈব সার আছে, জৈব সার তৈরির উপাদানও রয়েছে; কিন্তু আমাদের সচেতনতা ও সমন্বয়ের অভাব রয়েছে। এ লক্ষ্যে দৈনিক পূর্বকোণ পত্রিকায় প্রকাশিত ড. মো. আবুল কাসেম ভাইয়ের লেখার একটু উদ্ধৃতি টানছি। চট্টগ্রাম জেলার কর্ণফুলী উপজেলার শিকলবাহা খালের তীরে ৫০০ ডেইরি ফার্ম আছে। ওইসব ডেইরি ফার্মের মহামূল্যবান জৈব পদার্থ গোবর ও অন্যান্য বর্জ্যগুলো সঠিক অব্যবস্থাপনার অভাবে এবং কর্ণফুলী খালের পানিতে ফেলার কারণে পানি দূষিত হচ্ছে এবং খাল ভরাট হয়ে যাচ্ছে। ওইসব ডেইরি ফার্মের মালিকরা ও কৃষকরা অনুনয়-বিনয় করেছেন, তারাও চান না এসব ডেইরি বর্জ্য খালে ফেলতে এবং এর একটা সুরাহা চান। যাহোক সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এ কর্ণফুলীর শিকলবাহা খালের পাড়ের ডেইরি ফার্মগুলোর বর্জ্যগুলো সারে রূপান্তরিত করতে প্রভৃতি সহায়তা করতে পারেন। তা ছাড়া কেঁচো কম্পোস্ট (ভার্মি কম্পোস্ট) তৈরি করলে তা জৈব সারের পরিমাণ বহুলাংশে বৃদ্ধি পাবে। আশা করি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ও কর্মকর্তারা এ ব্যাপারে সদয় দৃষ্টি দেবেন। সরকারি প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি বেসরকারি উদ্যোক্তা ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এ সমস্যা নিরসনে এগিয়ে আসতে পারে।
পানি দূষণ
বাংলাদেশ তথা সারা বিশ্বে মিষ্টি পানির তীব্র অভাব রয়েছে। এ সংকট দিন দিন আরও তীব্রতর হচ্ছে। এর কারণ হিসেবে ভূ-পৃষ্ঠের পানির দূষণ, অব্যবস্থাপনা, ব্যাপক মাত্রায় উচ্চফলনশীল ফসল আবাদে প্রচুর পরিমাণ ভূ-পৃষ্ঠের পানি ও ভূ-গর্ভস্থ পানি ব্যবহার ও পানির স্তর নেমে যাওয়া এবং ভারী ধাতু পানির সঙ্গে মিশে যাওয়া উল্লেখযোগ্য। সে জন্য আমাদের এখনই সতর্ক হতে হবে। বাসাবাড়িতে রান্না, গোসল ও টয়লেটে পানি ব্যবহারের ক্ষেত্রে সাশ্রয়ী হওয়া, গৃহস্থালির আবর্জনা মিউনিসিপ্যালটির বর্জ্য ও কলকারখানার বর্জ্যগুলো সঠিকভাবে শোধন (ট্রিটমেন্ট) করে পানিতে ফেলার ওপর জোর দিতে হবে। ফসলের ক্ষেত্রে পোকা-মাকড় নিধনে কীটনাশক অতিমাত্রার ব্যবহার করা এবং সেগুলো বৃষ্টির পানি, সেচের পানি ও বন্যার পানির সঙ্গে মিশে পরবর্তীতে পার্শ্ববর্তী জলাশয়ের পানিতে মিশে এবং পানির দূষণ ঘটায়। পানি দূষণের ফলে পানিতে প্রয়োজনীয় দ্রবীভূত অক্সিজেন কমে যায় যা জলজ প্রাণীর জন্য অপরিহার্য। তাছাড়া BOD (Biochemical oxygen demand), COD (Chiemi oxygen demand) বেড়ে যায়। ঢাকার চারপাশের বিশেষ করে সাভারের ট্যানারির পার্শ্বস্থ নদীর পানিতে এরূপ প্যারামিটারগুলোর মাত্রা অনুমোদিত মাত্রার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় মর্মে সূত্র থেকে জানা যায়। আবার সমুদ্রে ও নদীতে বিভিন্ন জলযান থেকে তেল নিঃসরণ ও বিভিন্ন বর্জ্য ডাম্পিং করার মাধ্যমেও পানিদূষণ হয়ে থাকে। ঋতুভিত্তিক ফসল চাষ এবং অপেক্ষাকৃত কম পানি গ্রহণকারী জাত উদ্ভাবন করতে হবে এবং সবাইকে অতিমাত্রায় সচেতন হতে হবে।
বায়ুদূষণ
বায়ুদূষণের কারণেই বর্তমান বিশ্বের উষ্ণতা বাড়ছে। বায়ুদূষণ হয়ে থাকে জীবশ্ম জ্বালানির ব্যবহার, ইটের ভাটা, ব্যাপক উন্নয়নমূলক কাজ (যেখানে না ঢেকেই সিমেন্ট, বালু, মাটি ব্যবহার করা হয়), গাড়ি ও কলকারখানার কালো ধোঁয়া, গ্রিন হাউস গ্যাস উৎপাদন, পানিতে নিমজ্জিত ধান চাষ করা (Submerged rice cultivation), সিগারেটের ধোঁয়া, যুদ্ধের কারণে ব্যবহৃত বিস্ফোরক এবং বিস্ফোরণ ও বোমা, বন-বনানী ও বৃক্ষরাজিতে অগ্নিসংযোগ এবং উজাড় ও সামুদ্রিক শৈবালের বৃদ্ধি-ব্যাহত হওয়ার কারণে। প্রকৃতির প্রতি মানুষের নিষ্ঠুরতা, বিশেষ করে বৃক্ষ নিধন দিন দিন সারা পৃথিবীব্যাপী বাড়ছে। এসব বিষয় দেখার জন্য যেন কেউ নেই। অথচ এ বিশ্বের সব মানুষকে অচিরেই এ জন্য অনেক মূল্য দিতে হবে। একটি সূত্র থেকে জানায়, ঢাকা নগরীর বাতাস দূষকের মাত্রা অনুমোদিত মাত্রার থেকে পাঁচগুণ বেশি। ঢাকা নগরী পৃথিবীর দূষিত নগরীগুলোর অন্যতম। বায়ুদূষণ ফুসফুস শ্বাসপ্রশ্বাস, স্নায়ুতন্ত্রের রোগ, শিশুদের মানসিক রোগ এবং তাদের ব্যবহারে ও আচরণের ওপর প্রভাব ফেলে। ইতোমধ্যেই বৈশ্বিক তাপমাত্রা ধারণারও অতিরিক্ত বেড়েছে। যা থেকে জনজীবন বিপর্যস্ত হচ্ছে। এগুলো দ্রুত থামাতে হবে। এক গবেষণার পরিসংখ্যানের তথ্য থেকে জানা যায়, ঢাকা শহরে বায়ুদূষণের কারণে প্রতি বছর ২০০ শত মিলিয়ন মার্কিন ডলার ক্ষতি হচ্ছে এবং ১৫০০০ মানুষ মারা যাচ্ছে।
শব্দদূষণ
বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে শব্দ যদি ৬৫ ডেসিবলসের ওপরে থাকে তাহলেই তা শব্দ দূষণ হিসেবে পরিগণিত। গাড়ি, বিমান, কলকারখানার মেশিন, লাউডস্পিকার, রেডিও, টিভি, বোমাবাজি, হোটেল-রেস্তোরাঁর মিউজিক, ইঞ্জিন, নির্মাণ কাজ ইত্যাদি থেকে উদ্ভূত শব্দের মাধ্যমে শব্দদূষণ হয়ে থাকে। শব্দদূষণ নগরবাসীর জীবনে বিরূপ-প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে এবং এর সঙ্গে জীবের স্বাস্থ্য-সমস্যা সরাসরি জড়িত। শব্দদূষণের ফলে উচ্চ রক্তচাপ, দুশ্চিন্তা, উদ্বেগ, উত্তেজনা, যোগাযোগের সমস্যা, ঘুমের সমস্যা, হৃদরোগ, শিক্ষণে ব্যাঘাত, শ্রবণশক্তি হ্রাস পাওয়া, উৎপাদনশীলতা হারানো প্রভৃতি জাতির ক্ষতি হয়। আমরা শব্দদূষণ থেকে পরিত্রাণ পেতে যানবাহন ও মেশিনের নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ, রেডিও, টেলিভিশন, মাইক, মিউজিক লো ভলিউমে শোনা, যন্ত্রপাতি যখন ব্যবহার হয় না, তখন সেগুলোকে বন্ধ করে রাখা, ইয়ার প্লাগ ব্যবহার, বেশি বেশি গাছ লাগানো ও সর্বোপরি সচেতনতা সৃষ্টি করতে পারি। শব্দদূষণ কমানো ও নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে শব্দের নেতিবাচক প্রভাব থেকে মানুষসহ অন্য প্রাণিকুল সুরক্ষা পেতে পারে।
পাখি, মৎস্য ও প্রাণীর সুরক্ষা
আইইউসিএনের সর্বশেষ লাল তালিকা মোতাবেক আজ বাংলাদেশের অনেক প্রজাতি ভয়াবহ জেনেটিক ক্ষতির মুখে পৌঁছেছে। এ ধরনের প্রজাতির বিস্তারিত তথ্য অনেক সময় পাওয়া যায় না। তবে বাংলাদেশ সরকার এ ব্যাপারে সমস্যাগুলোর মোকাবিলার প্রস্তুতি নিচ্ছে। বাংলাদেশের ৩০৫টি প্রজাতির পাখির মধ্যে ১৯ প্রজাতির পাখি ইতোমধ্যে বিলুপ্ত হয়ে গেছে, রয়েল বেঙ্গল টাইগারের সংখ্যা ছিল ১৯৭৫ সালে ৩৫০টি (হেনরিচ, ১৯৭৫), ১৯৯৮ সালে ছিল ৩৬২টি (জলিল, ১৯৯৮), ২০০৪ সালে ৪৪০টি (ইউএনডিপি, ২০০৪); কিন্তু সর্বশেষ আইইউসিএনের ক্যামেরা ট্রাপ জরিপ থেকে এ সংখ্যা পাওয়া গেছে ১০৫টি (আইইউসিএন, ২০১৫)। এ ছাড়া সুন্দরবনের চিত্রা হরিণের সংখ্যা ছিল ১৯৭৫ সালে ৮০,০০০টি (হেনরিচ, ১৯৭৫), ২০০৭ সালে ৮৩,০০০টি (দে, ২০০৭) এবং বর্তমানে সুন্দরবনের হরিণের সংখ্যা বেড়েছে মর্মে জানা যায়। অন্যদিকে, নিঝুম দ্বীপে ২০০৬ সালে হরিণ ছিল ১৪,০০০টি, যা ২০১৫ সালে ২০০০-এর কমে চলে আসে (ফিরোজ এবং উদ্দিন, ২০১৫)। সাইক্লোন রেমালের আঘাতে সুন্দরবনে ৩০টি হরিণের মৃত দেহ উদ্ধার করা হয়েছে। এ ছাড়া বনরক্ষীরা আরও ১৫টি আহত হরিণ উদ্ধার করেছে। পূর্বে সুন্দরবনে বানরের সংখ্যা ছিল ১,৫২,৪৪৪টি যা কমে হয়েছে ১,২৬,২২০টি। উপরন্তু, ২০১৯ সালের মৎস্য সপ্তাহের বুলেটিন থেকে প্রাপ্ত তথ্য মোতাবেক বাংলাদেশ থেকে ৩০ প্রজাতির সাধু-পানির মৎস্য বিলুপ্ত হয়ে গেছে এবং ৯টি প্রজাতির মৎস্য বিলুপ্তির পথে। তা ছাড়া এশিয়ার দেশগুলোতে বন্যপ্রাণী হত্যা, নির্যাতন ও পাচার হয়ে থাকে। এসব অপরাধের সঙ্গে জড়িত অপরাধীদের আইনের আওতায় আনতে হবে। পাখি, মৎস্য, প্রাণী ও উদ্ভিদ রক্ষার্থে অভয়াশ্রম গড়ে তোলা, সামাজিক সচেতন বৃদ্ধি, সামাজিক আন্দোলন ও প্রয়োজনে আইনানুগ শক্তি প্রয়োগের নিমিত্তে পরিবেশ পুলিশ গঠন করা যেতে পারে।
বন-বনানী ও বৃক্ষরাজির সুরক্ষা
সূত্র থেকে জানা যায় বিগত ১০০ বছরে বাংলাদেশ থেকে অনেক প্রজাতির উদ্ভিদ বিলুপ্ত হয়ে গেছে। জাতি সংঘ ও FAO-এর তথ্য মতে, বাংলাদেশে শতকরা ১১.১ ভাগ বন-বনানী রয়েছে। সে জন্য আমাদের নতুন করে বনায়ন শুরু করতে হবে। পারিবারিক বনায়ন, সামাজিক বনায়ন, সরকারি উদ্যোগে বনায়ন, সরকারি প্রতিষ্ঠান, স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ছাত্রছাত্রীদের মাধ্যমে নতুন চারা গাছ লাগানো কর্মসূচি হাতে নিতে হবে। পাশাপাশি ব্যাপকভাবে বৃক্ষ নিধন এবং বৃক্ষে অগ্নিসংযোগ বন্ধকরণে র্যালি, লিফলেট, পথসভা, নাটক, আলোচনা সভা ও বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালন করতে হবে। মানুষের অবিবেচনা এবং অপরিণামদর্শী কার্যক্রমের কারণে বিশ্বের প্রাণীকুল, উদ্ভিদ রাজি, অনুজীবগুলো এবং জীব-বৈচিত্র্য প্রতিনিয়ত বিলুপ্ত হচ্ছে এবং মারাত্মক হুমকির সম্মুখীন। ফলে বৈশ্বিক তাপমাত্রা বাড়ছে এবং সাইক্লোন রেমাল, মোখা, সিডোর, আইলা ইত্যাদি তাপপ্রবাহ, ভূমিধস, বন্যা, ক্ষরা, অতিমাত্রার শীত ও শৈত্যপ্রবাহ বাংলাদেশ তথা বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে দেখা দিচ্ছে। প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হওয়া এবং পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের দূষণের পেছনে মানুষই মূলত দায়ী। আমাদের পরিবেশদূষণ বন্ধ থামাতে হবে এবং সব কাজের ক্ষেত্রে প্রকৃতি ও পরিবেশকে প্রাধিকার দিতে হবে। আর পরিবেশের উপাদানগুলোর যথাযথ পরিচর্যা, সুরক্ষা ও উন্নয়ন সাধনের মাধ্যমেই পরিবেশের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব। তাহলেই বাংলাদেশ এবং বিশ্বমানবতা ও আধুনিক সভ্যতা বড় আকারের বিপদ থেকে মুক্তি পাবে।
লেখক: কমান্ড্যান্ট (এডিশনাল ডিআইজি) পুলিশ স্পেশাল ট্রেনিং স্কুল (পিএসটিএস), বেতবুনিয়া, রাঙামাটি

জলবায়ুর বিরূপ প্রভাবে দেশের সমুদ্র উপকূলীয় দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের অধিকাংশ মানুষ বহুমাত্রিক সংকটে পড়ছে। বিশেষ করে স্বাস্থ্য, খাদ্য, বসতি, বিশুদ্ধ পানীয় জল, যাতায়াত এবং নিরাপত্তাহীনতায় পতিত হতে হচ্ছে তাদের। দেশের সমুদ্র উপকূলীয় জেলা সাতক্ষীরা, বাগেরহাট, খুলনা, যশোর, ভোলা, কক্সবাজার জেলার মানুষকে চরম সংকটে ফেলছে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে। এর বাস্তব প্রমাণ পাওয়া গেছে সদ্য সমাপ্ত ঘূর্ণিঝড় ‘রেমাল’ দেশের উপকূলীয় উপকূলে আঘাতে সম্পদ ও বাড়িঘর, পশুপাখি, মাছসহ তাদের মূল্যবান সম্পদের ক্ষতি। আবার এসব অঞ্চলের নদীসমূহ অতিমাত্রায় জোয়ার-ভাটার কারণে প্রতিদিন নতুন নতুন সংকট সৃষ্টি হচ্ছে। এসব নদীতে সাগর থেকে জোয়ারের পানি আসে এবং ভাটায় ফিরে যায়। এ নদীগুলোর সঙ্গে পদ্মাপ্রবাহের কোনো সম্পর্ক নেই। এ কারণে সমগ্র এলাকা হচ্ছে জোয়ার-ভাটার প্লাবনভূমি।
এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে বিগত কয়েক বছরে জলবায়ু উদ্বাস্তু হয়েছে প্রায় আড়াই কোটি মানুষ। সমুদ্রের অতিমাত্রায় জোয়ার -ভাটা এবং জলোচ্ছ্বাসে একদিকে নদীভাঙন অন্যদিকে সমুদ্রের পানির অতিমাত্রায় লবণাক্তায় এসব অঞ্চলে বিশুদ্ধ পানীয় জলের তীব্র সংকট দেখা দেয়। লবণাক্ত পানি পান করে নারী, শিশুসহ প্রায় সব বয়সি মানুষ নানা রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। ফলে স্বাস্থ্য ঝুঁকি বাড়ছে সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চলের লাখো মানুষের। অন্যদিকে খুলনা বাগেরহাট, সাতক্ষীরা প্লাবনভূমির নিম্নাংশে অবস্থিত জগৎখ্যাত সুন্দরবন। সুন্দরবন থেকে প্রতি বছর লাখ লাখ টন গাছের পাতা এ অঞ্চলের গভীর জোয়ারের পানি নদীতে পড়ে এবং তা ধীরে ধীরে জলজ প্রাণীর খাদ্যকণায় রূপান্তরিত হয়। তাই এ অঞ্চলের জৈবিক উৎপাদনশীলতা পৃথিবীর যেকোনো এলাকার তুলনায় অনেক বেশি।
উপকূলীয় বাঁধ হওয়ার আগে জোয়ারের মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ জলরাশি নদীগুলোর দুকূল ছাপিয়ে প্লাবনভূমিতে উঠে আসত এবং জোয়ারবাহিত পলি প্লাবনভূমিতে পড়ে তীব্র স্রোতে ভাটায় তা ফিরে যেত। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যেমন জোয়ার-ভাটার নদীগুলোর নাব্য বজায় থাকত, তেমনি ভূমির গঠন প্রক্রিয়া সমানতালে চলত। তা ছাড়া এখানকার কৃষকরা প্লাবনভূমির চারদিকে জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসে সাময়িক বাঁধ দিয়ে আমন ধান রোপণ করত এবং পৌষ মাসে বাঁধ ভেঙে প্লাবনভূমিতে জোয়ারবাহিত পলির কারণে সুযোগ করে দিয়ে ভূমি গঠন ও জমির উর্বরতা বৃদ্ধি করত। ফলে নদীর নাব্য থাকত। এ কারণে এখানকার নদী, প্রকৃতি, পরিবেশ ও কৃষিব্যবস্থা এক অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী; দেশের অন্যান্য উপকূল থেকে তা ভিন্নতর; কিন্তু এখানকার প্রকৃতি ও প্রতিবেশকে বিবেচনায় না নিয়ে ষাটের দশকে উপকূলীয় বাঁধ প্রকল্পের আওতায় এ অঞ্চলে ৩৯টি পোল্ডার নির্মাণ করা হয়, এর আওতায় ১ হাজার ৫৫৬ কিলোমিটার দীর্ঘ বাঁধ ও ২৮২টি স্লুইসগেট নির্মিত হয়। এ কারণে এই নদীগুলো স্থায়ীভাবে প্লাবনভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। যার ফলে জোয়ারবাহিত পলি প্লাবনভূমিতে পতিত হতে না পেরে নদীতে অবক্ষেপিত হচ্ছে এবং ইতোমধ্যে বহু নদী মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে। অবশিষ্ট জোয়ার-ভাটার নদীগুলো পলি দ্বারা ভরাট হয়ে মৃত্যুর দিকে ধাবিত হচ্ছে। এর ফলে বিগত শতকের আশির দশকে সৃষ্টি হয় জলাবদ্ধতা এবং ধীরে ধীরে তা হয়ে উঠেছে প্রলয়ঙ্করী ও বিধ্বংসী।
জলবায়ু পরিবর্তনজনিত নেতিবাচক প্রভাবে উপকূলীয় মানুষের মধ্যে মানসিক অসুস্থতা দেখা দিচ্ছে। উপকূলীয় অঞ্চলে বাস করা ২২.৪৮ শতাংশ মানুষ বিষণ্নতায় ভুগছে। এ ছাড়া ৪৩.৯৫ শতাংশ মানুষের ভালো ঘুম হয় না। সম্প্রতি রাজধানীর ব্র্যাক সেন্টারে এক যৌথ গবেষণা প্রতিবেদনে এসব তথ্য জানানো হয়।
সেন্টার ফর ক্লাইমেট চেঞ্জ অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল রিসার্চ, ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি এবং বাংলাদেশ হেলথ ওয়াচ, সিভিল সোসাইটি প্ল্যাটফরমের এই যৌথ গবেষণা প্রতিবেদনে জানানো হয়, ‘বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর জলবায়ুর প্রভাব শীর্ষক’ গবেষণায় গুরুতর দুশ্চিন্তা, বিষণ্নতা, মানসিক চাপ, মানসিক বৈকল্য এবং ঘুম না হওয়ার মতো জটিল স্বাস্থ্য সমস্যা উঠে এসেছে। এ ছাড়া উপকূলীয় অঞ্চলের ৪৩.৯৫ শতাংশ মানুষের ভালো ঘুম হয় না বলেও গবেষণায় উঠে এসেছে। গবেষণায় অংশগ্রহণকারীরা জানান, খুলনার শ্যামনগর এলাকায় এই সমীক্ষা চালানো হয়।
বাংলাদেশ একটি নিম্নভূমি হওয়ায় জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। এই অঞ্চল ঘূর্ণিঝড়, উপকূলীয় বন্যা এবং উপকূলীয় ক্ষয়ক্ষতির মতো প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের জন্য খুব ঝুঁকিপূর্ণ। এই প্রেক্ষাপটে বিগত নব্বইয়ের দশকে পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের গবেষণা সংস্থা সিইজিআইএস একটি সমীক্ষা চালায়। সমীক্ষায় নদী বাঁচানোর মাধ্যমে জলাবদ্ধতা দূর করার জন্য নদীতে অবাধ জোয়ার-ভাটার ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করে। এর পর নদী অববাহিকায় বিশেষ করে খুকশিয়া বিলে এই পদ্ধতি বাস্তবায়ন করে। ফলে দীর্ঘ সময় ধরে এই অববাহিকার পাঁচ-সাতটি উপজেলা জলাবদ্ধতামুক্ত থাকে; কিন্তু কৃষকদের অধিগ্রহণকৃত জমির ক্ষতিপূরণসংক্রান্ত জটিলতার কারণে দ্বন্দ্ব-সংঘাত সৃষ্টি হলে নদী রক্ষা কার্যকারণ বন্ধ হয়। ফলে হরি, শ্রী ও ভদ্রা নদীগুলো আবারও ভরাট হয়ে গেছে এবং জলাবদ্ধতার তীব্রতা ক্রমেই বেড়ে চলেছে।
অন্যদিকে ২০১৫ সালে সাতক্ষীরা জেলার কপোতাক্ষ নদ অববাহিকার জলাবদ্ধতা নিরসনের জন্য পাখিমারা বিলে টিআরএম কার্যক্রম চালু হওয়ার পর থেকে অদ্যাবধি কপোতাক্ষ অববাহিকায় আর কোনো জলাবদ্ধতা দেখা দেয়নি। তবে বর্তমানে টিআরএম কার্যক্রম বন্ধ রাখার ফলে নদীর নাব্য দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে। কিন্তু জনগণের দৃষ্টিতে তার কোনোটিই প্রকৃতি, নদী ও পরিবেশসম্মত নয় এবং সেই কারণে জলাবদ্ধতা দূরীকরণ ও নদীর নাব্য রক্ষায় এসব প্রকল্প সফল ভূমিকা রাখতে পারেনি। একই নদী বারবার খননের মাধ্যমে জলাবদ্ধতা দূরীকরণের চেষ্টা করা হচ্ছে; কিন্তু তা এক-দুই বছরের মধ্যে ফের পলি দ্বারা ভরাট হয়ে যাচ্ছে। এ অবস্থায় দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলীয় অঞ্চলের জনবসতি ও সভ্যতা রক্ষার জন্য এ অঞ্চলের নদীকে বাঁচিয়ে রাখা বা নদীর নাব্য রক্ষার জন্য জোয়ারের পানিতে আসা পলি নদীর প্লাবনভূমিতে ফেলার ব্যবস্থা নিতে হবে।
গবেষণা প্রতিবেদনে সুপারিশ অনুযায়ী উপকূলের মানুষের মানসিক স্বাস্থ্য পরিষেবার বিধান বাড়ানো, পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দ করা, কাউন্সেলিং ইউনিট স্থাপন করা এবং ন্যাশনাল আডাপ্টেশন প্ল্যান (ন্যাপ) জাতীয় স্বাস্থ্য অভিযোজন পরিকল্পনার সঙ্গে একীভূত করা। আরও সুপারিশের মধ্যে রয়েছে দুর্বল জনগোষ্ঠীর প্রতি গুরুত্ব দেওয়া, নীতি এবং আইনি কাঠামোর পরিবর্তন এবং মানসিক স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানকারীদের জন্য স্বাস্থ্য সুবিধা বিধানগুলো উন্নত করা। সেন্টার ফর ক্লাইমেট চেঞ্জ অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল রিসার্চ ও ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক ড. আইনুন নিশাত বলেন, ‘জলবায়ু পরিবর্তন মানুষের ওপর দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব ফেলে। জলবায়ু পরিবর্তন এবং মানসিক স্বাস্থ্যের আরও প্রভাব জানতে উপকূলের পরিবারগুলোর সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখা দরকার।’
সুইডেন দূতাবাসের ফার্স্ট সেক্রেটারি ডা. ড্যানিয়েল নোভাক জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনায় স্বাস্থ্যের অন্তর্ভুক্তির ওপর গুরুত্ব দিয়ে বলেন, জলবায়ু পরিবর্তন বিপজ্জনক। সুইডেনে মানুষ জলবায়ু পরিবর্তনের ভবিষ্যৎ প্রভাব জেনে তাদের বাচ্চাদের হত্যা করার মতো উদাহরণও রয়েছে। খরায় জেগে উঠল ৩০০ বছরের পুরোনো শহর। কৃত্রিম হ্রদের নিচে তলিয়ে গিয়েছিল ফিলিপাইনের প্রাচীন শহর পান্তাবঙ্গন। ১৯৭০-এর দশকে কৃত্রিম হ্রদের জন্য জলাধার নির্মাণের পর ডুবে যায় শহরটির ধ্বংসাবশেষ। তীব্র খরার কারণে বাঁধের ভেতরের কিছু অংশ শুকিয়ে যাওয়ায় জেগে উঠেছে শহরের চিহ্ন পান্তাবঙ্গ।
বাংলাদেশে গত এক মাস ধরে রছে প্রচণ্ড দাবদাহ। ইতোমধ্যে এ কারণে মারা গেছে প্রায় ২৪ জন। তীব্র গরমের কারণে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশটির লাখ লাখ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের স্বাভাবিক কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। মাঝেমধ্যে বন্ধ থাকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। অফিসের কার্যক্রমও বাড়ি থেকে করার সুপারিশ করা হয়েছে। আগামী দিনগুলোতেও তাপমাত্রা বাড়ার প্রবণতা অব্যাহত থাকতে পারে বলে ফিলিপাইনের আবহাওয়া দপ্তরের বিশেষজ্ঞ বেনিসন এস্তারেজা বলেছেন। তিনি বলেছেন ‘ফিলিপাইনে জলবায়ু পরিবর্তনের সাধারণ প্রভাব হলো উষ্ণ তাপমাত্রা। আমরা যে তাপ অনুভব করছি, তা আগামী দিনে ক্রমাগত বাড়তে পারে।’ ফিলিপাইনে এখন উষ্ণ ও শুষ্ক ঋতুর মাঝামাঝি সময়। বিশেষ আবহাওয়া পরিস্থিতি ‘এলনিনো’র (প্রশান্ত মহাসাগরের সাগরপৃষ্ঠের পানির অস্বাভাবিক উষ্ণতা) প্রভাবে দেশটিতে গরমের তীব্রতা আরও বেড়েছে। এমনি অবস্থায় বাংলাদেশের সমুদ্র উপকূলীয় মানুষকে রক্ষায় কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন। কারণ জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে বিশ্বের সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম।
লেখক: সাংবাদিক, সাধারণ সম্পাদক-বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ জার্নালিস্ট ফোরাম

আগামী ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের বাজেট সমাগত এবং এরই মধ্যে বিভিন্ন সেমিনার, কর্মশালা ও সংলাপ শুরু হয়ে গেছে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে যা একটি চলমান প্রক্রিয়া। তবে এবারের বাস্তবতা ভিন্ন যেমন- চলমান অর্থনৈতিক সংকট থেকে উত্তরণ, মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ, কৃচ্ছ্রতাসাধন ও আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) ঋণ সহায়তার শর্তপূরণ ইত্যাদি বিষয় বিবেচনায় নিয়ে আগামী ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের বাজেট ঘোষণা করা হবে। ফলে এবারের বাজেটের আকার আশানুরূপ বাড়ছে না। আগামী বাজেটের প্রস্তাবিত সম্ভাব্য আকার হচ্ছে ৭ লাখ ৯৭ হাজার কোটি টাকা। আগামী বাজেটে জিডিপি প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ৬ দশমিক ৭৫ শতাংশ এবং মূল্যস্ফীতির গড় হার ৬ দশমিক ৫০ শতাংশের মধ্যে সীমিত রাখা হবে। বিগত ৪ এপ্রিল, ২০২৪ অনুষ্ঠিত আর্থিক, মুদ্রা ও মুদ্রা বিনিময় হার সংক্রান্ত কো-অর্ডিনেশন কাউন্সিল এবং ‘বাজেট ব্যবস্থাপনা ও সম্পদ কমিটির ভার্চুয়াল বৈঠকে আগামী বাজেটের এ খসড়া রূপরেখা উপস্থাপন করা। অর্থমন্ত্রী আবুল হাসান মাহমুদ আলী এই সভায় সভাপতিত্ব করেন।
জানা গেছে, চলতি ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের মূল বাজেটের আকার ধরা হয়েছিল ৭ লাখ ৬১ হাজার ৭৮৫ কোটি টাকা এবং আগামী অর্থ বছরে বাজেটের প্রস্তাবিত সম্ভাব্য আকার ধরা হচ্ছে ৭ লাখ ৯৭ হাজার কোটি টাকা। ফলে এবারের বাজেটের আকার আশানুরূপ বাড়ছে না। সে হিসাবে বাজেটের আকার বাড়ছে ৪ দশমিক ৬২ শতাংশ। টাকার অঙ্কে বাজেটের আকার বাড়ছে মাত্র ৩৫ হাজার ২১৫ কোটি টাকা। চলতি অর্থ বছরে মূল বাজেটের আকার এর আগের অর্থ বছরের তুলনায় ১২ দশমিক ৩০ শতাংশ বাড়ানো হয়েছিল। অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগ সূত্রমতে, প্রতি বছর বাজেটের প্রবৃদ্ধি ১০ থেকে ১২ শতাংশ ধরেই প্রাক্কলন করা হয়। এবার সেটি ৫ শতাংশের নিচে বাড়বে। কাঙ্ক্ষিত পরিমাণ রাজস্ব আদায় না হওয়া, প্রবাসী আয় কমে যাওয়া এবং আমদানি ও রপ্তানি পরিস্থিতি আশানুরূপ ভালো না হওয়ায় বাজেটের আকার তেমন বাড়ছে না। আসন্ন বাজেটের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে আর্থিক নীতির সঙ্গে রাজস্ব নীতির সমন্বয়। জানা যায়, নতুন বাজেটে সম্ভাব্য মোট আয় ধরা হয়েছে ৫ লাখ ৪০ হাজার কোটি টাকা। সে হিসাবে ঘাটতি দাঁড়াচ্ছে ২ লাখ ৫৭ হাজার কোটি টাকা (জিডিপির ৪.৬%)। ঘাটতি পূরণে বিদেশি সহায়তা আর ঋণের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ১ লাখ কোটি টাকা। বাকিটা অভ্যন্তরীণ উৎস (ব্যাংক, সঞ্চয়পত্র ও অন্যান্য) থেকে ঋণ নিয়ে পূরণ করা হবে।
সূত্রমতে, আগামী বাজেটে রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা বাড়বে প্রায় ৫০ হাজার কোটি টাকা বাড়ানো হতে পারে। আর বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) আকার ধরা হয়েছে ২ লাখ ৬৫ হাজার কোটি টাকা। চলতি অর্থ বছরের মূল বাজেটের আকার ছিল ২ লাখ ৬৩ হাজার কোটি টাকা। তবে সংশোধিত বাজেটে ১৮ হাজার কোটি টাকা কমিয়ে এডিপির আকার ২ লাখ ৪৫ হাজার কোটি টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রসঙ্গত সরকারি ব্যয়ে কৃচ্ছ্রতাসাধনে চলতি বাজেটে গাড়ি কেনা, ভূমি অধিগ্রহণ, ভবন নির্মাণসহ অন্যান্য কার্যক্রম বন্ধ রাখা হয়েছে। এটি আগামী অর্থ বছরেও অব্যাহত থাকবে। চাহিদার দিক থেকে অনেক কিছু হ্রাস করা হচ্ছে। পাশাপাশি মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে সরবরাহ ঠিক রাখতে গিয়ে টিসিবি ও ওএমএস কর্মসূচির মাধ্যমে পণ্য সরবরাহ বৃদ্ধি, বাজার মনিটরিং জোরদার করা হতে পারে।
নির্বাচনের পর নতুন সরকারের মাত্র কয়েকদিন অতিবাহিত হয়েছে। বাজেটে সংস্কার আনার জন্য এই সময়টাই সবচেয়ে উপযুক্ত। দেশের অর্থনীতি নানা প্রতিকূলতা ও সংকটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। এ অবস্থায় অনন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন অব্যাহত রাখতে গুণগতমানের সরকারি ব্যয় ব্যবস্থাপনা জরুরি। সেই সঙ্গে স্বয়ংক্রিয় প্রক্রিয়ায় রাজস্ব আহরণ বাড়ানো ও ব্যাংক খাতে দুরবস্থা দূর করার বিষয়ে মনোযোগ দিতে হবে। সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে। চলমান বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করতে বাজেটে সংস্কার আনা জরুরি। সম্প্রতি জাতীয় প্রেসক্লাবে গবেষণা সংস্থা রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি ইন্টিগ্রেশন ফর ডেভেলপমেন্ট (র্যাপিড) আয়োজিত আগামী ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের প্রাক-বাজেট আলোচনায় এসব কথা বলেন বক্তারা। বাজেট ও সরকারের বিভিন্ন পরিকল্পনা তুলে ধরে পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী বলেন, আগামী বাজেটের আকার হতে পারে ৮ লাখ কোটি টাকার আশপাশে। নবম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা তৈরি করার কাজ শুরু হয়েছে। প্রেক্ষিত পরিকল্পনা, পঞ্চবার্ষিকীসহ অন্যান্য পরিকল্পনা অনুযায়ী বাজেট প্রণয়ন করা হচ্ছে। এরই মধ্যে মূল্যস্ফীতি কমানোর উদ্যোগ হিসেবে বাড়ানো হয়েছে সুদহার। কর-জিডিপি অনুপাত বাড়াতে বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। তিনি বলেন, আমরা প্রকৃত অর্থে মুক্ত অর্থনীতির অনুসারী না, কল্যাণকর অর্থনীতির অনুসারী। আসন্ন বাজেটে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারে প্রতিফলন ঘটবে। সরকারের আরও কিছু বিষয় আছে, সেগুলো মাথায় রেখে বাজেট করা হচ্ছে। বাজেটে কী হচ্ছে, না হচ্ছে এসব বিষয় সাধারণ মানুষ জানতে চায় না। তারা চায় দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে আসুক। আগামী বাজেটে এ বিষয়টিকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে। দ্রব্যমূল্য ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে রাখতে বাজেটে যা করার আছে, তা নিশ্চিত করতে হবে। পাশাপাশি শিক্ষার মানোন্নয়ন এবং কর্মসংস্থানে নজর দিতে হবে। তিনি বলেন, ইউনিয়নপর্যায়ে ভূমির খাজনা আদায়ে তহসিল অফিস আছে। আর জেলাপর্যায়ে পর্যন্ত কর কর্মকর্তা আছেন। উপজেলাপর্যায়েও মানুষের আয় বেড়েছে; কিন্তু করদাতা বাড়েনি। কর খেলাপিদের বা দুর্নীতিগ্রস্তদের বাড়তি সুযোগ দেওয়ায় সাধারণ করদাতারা নিরুৎসাহিত হচ্ছেন।
অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন র্যাপিডের নির্বাহী পরিচালক অধ্যাপক এম আবু ইউসুফ। তিনি বলেন, দেশে এখনো পরোক্ষ কর অনেক বেশি। অথচ উন্নত বিশ্বে প্রত্যক্ষ কর বেশি। এত দিন এসব জায়গায় সংস্কার আনা যায়নি। এখন সংস্কার করার সুযোগ রয়েছে। বছরের শেষ সময়ে তড়িঘড়ি না করে বছরজুড়ে বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেওয়া উচিত। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) সাবেক চেয়ারম্যান বাজেট তৈরি করা হচ্ছে, পাস হচ্ছে; কিন্তু বাস্তবায়ন হচ্ছে না। এ অবস্থা থেকে বের হয়ে আসতে বাজেটে অনেক বেশি সংস্কার প্রয়োজন। বাজেট প্রণয়নে সংসদীয় কমিটির সংশ্লিষ্টতা বাড়াতে হবে। তিনি বলেন, এনবিআরের কর আদায় প্রক্রিয়া পুরোপুরি অনলাইন করার জন্য রাজনৈতিক সদিচ্ছার প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে সব প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণে এনফোর্সমেন্ট বাড়াতে হবে। একই সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে থাকা ৯ শতাংশের বেশি মূল্যস্ফীতিকে অর্থনীতির ডায়াবেটিস বলে মনে করেন তিনি। এ অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসতে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়ার আহ্বান জানান। উচ্চ প্রবৃদ্ধির আকাঙ্ক্ষা অর্জনের টানা বাজেট ঘাটতি মেটাতে এতদিন সক্ষম হয়েছে সরকার। তবে আগামী বাজেটে মূল্যস্ফীতি কমানো ও সরকারি ব্যয় কমানো মুখোমুখি অবস্থানে থাকবে বলে মনে করেন র্যাপিড চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আবদুর রাজ্জাক। তিনি বলেন, ‘আগামী বাজেটে সম্প্রসারণমূলক নীতি থাকলে মূল্যস্ফীতি কমানো চ্যালেঞ্জ হবে। আগামী বাজেটে বড় সংস্কার প্রয়োজন। নির্বাচনের আগে সংস্কার করার সিদ্ধান্ত নেওয়া কঠিন ছিল। তবে নির্বাচনের পরে এখন সংস্কার করার উপযুক্ত সময়। যেন বর্তমান চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করা সহজ হয়। বাজেট প্রণয়নে সংখ্যার বাইরে বেরিয়ে গুণগতমানের দিকে নজর দিতে হবে। পাশাপাশি রাজস্ব আয় বাড়াতে হবে যাতে বাজেট ব্যয় বাড়ানো যায়। বিনিময় হার ব্যবস্থাপনা নিয়ন্ত্রণ থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। ব্যাংকিং খাতে সুশাসন নিশ্চিত করতে হবে। বাজেট ব্যয় ব্যবস্থাপনা আরও বাড়ানোর জন্য সংস্কারের প্রস্তাব দেন এই অর্থনীতিবিদ।’
আলোচনার শিরোপায় রয়েছে- রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনই বড় চ্যালেঞ্জ হবে। বিদেশি ঋণ, সুদ ও ভর্তুকির মতো ব্যয় মেটাতে রাজস্ব খাতের চাপ কাটছে না। ব্যয় আরও বৃদ্ধির কারণে চাপ আগামী অর্থ বছরেও অব্যাহত থাকছে। পরিস্থিতি মোকাবিলায় আয়ের লক্ষ্যমাত্রা সম্প্রসারণমূলক হওয়ার কথা; কিন্তু বাস্তবে তা হচ্ছে না। আগামী অর্থ বছরে রাজস্ব আয়ের লক্ষ্য খুব বেশি বাড়ছে না। বিশ্বব্যাংকের পূর্বাভাসে বলা হয়েছে জিডিপির প্রবৃদ্ধি ৫ দশমিক ৬ শতাংশ হবে। ফলে জিডিপির প্রবৃদ্ধি না বাড়লে রাজস্ব আয়ও বাড়বে না। এই লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে দৃশ্যমান কোনো সংস্কার দেখা যাচ্ছে না। রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হলে প্রযুক্তিগত, প্রশাসনিক ও আইনি কাঠামোগত সংস্কার করতে হবে। বিশেষ করে কাগজবিহীন ও স্বচ্ছ কর পদ্ধতি চালু করা দরকার। এনবিআরকে অর্থ প্রতিমন্ত্রীর অধীনে রাখা এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর নামে দুটি বোর্ড তৈরি করা প্রয়োজন। রাজস্ব খাত নিয়ে গবেষণা ও পর্যালোচনার জন্য পৃথক উইং থাকতে হবে। এসব খাতে সংস্কার আনা হলে রাজস্ব আয় বাড়ানো যাবে।
‘আর্থিক মুদ্রা ও মুদ্রা বিনিময় হারসংক্রান্ত কো-অর্ডিনেশন কাউন্সিল বৈঠকে আগামী অর্থ বছরে রাজস্ব আহরণ বাড়াতে বেশকিছু পদক্ষেপ নেওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়। এরমধ্যে ১০ লাখ বা এর বেশি মূসক (ভ্যাট) পরিশোধের ক্ষেত্রে ই-পেমেন্ট বা এ-চালান বাধ্যতামূলক করা হবে। বর্তমান ই-পেমেন্ট বা এ-চালান শুধু ৫০ লাখ টাকা বা তার বেশি ভ্যাট পরিশোধে ব্যবহারের বিধান আছে। সেটি কমিয়ে আনলে এ খাত থেকে অনিময় দূর হবে এবং রাজস্ব আহরণ বাড়বে। এ ছাড়া ইলেকট্রনিকস টেক্স ডিটেকশন সোর্স (ইটিডিএস) অনলাইন প্ল্যাটফরম চালুর পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। পাশাপাশি রাজস্ব ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা বৃদ্ধি, সেবার মানোন্নয়ন ও রাজস্ব আদায় বাড়াতে আয়কর আইন-২০২৩ প্রয়োগ করা হবে। ঢাকা ও চট্টগ্রাম শহরে অনেক আয়করদাতা আছেন কিন্তু তারা কর দিচ্ছেন না। তাদের করজালের আওতায় আনতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ইডিএফ মেশিন স্থাপনের জন্য একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তি করা হয়। খুব শিগগিরই বহু প্রতিষ্ঠানকে করের আওতায় আনা হবে। এ ছাড়া নতুন করদাতাদের করজালে আনতে বিআরটিএ, সিটি করপোরেশন, ডিপিডিসির সঙ্গে সমন্বয় করে কাজ করার পরিকল্পনা নিয়েছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)। সংশ্লিষ্টদের মতে চলতি অর্থ বছরে প্রথম ৮ মাসে (জুলাই-ফেব্রুয়ারি) প্রবৃদ্ধি সত্ত্বেও রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে পারেনি। এই সময়ে নির্ধারিত রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা সংশোধন করে কমানোর পরও ১৮ হাজার ২২১ কোটি টাকা ঘাটতি রয়েছে। যদিও এই সময়ে প্রবৃদ্ধি ১৬ শতাংশ হয়েছে। রমজানকে কেন্দ্র করে আমদানি বৃদ্ধির কারণে ফেব্রুয়ারিতে এ প্রবৃদ্ধি হয়েছে বলেও মনে করছেন বিশ্লেষকরা।
অর্থ বিভাগের বাজেট নথি বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, বিগত কয়েক বছর রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন হয়নি। ওই সময় অর্থনীতির স্বাভাবিক পরিস্থিতি ছিল। কিন্তু বর্তমানে একটি বিশেষ সময়ের মধ্য দিয়ে পার হচ্ছে দেশের অর্থনীতি। ঊর্ধ্বমুখীভাব বিরাজ করছে মূল্যস্ফীতির হারে। ব্যবসাবাণিজ্য খুব ভালো হচ্ছে না। ফলে রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সংশয় আছে। চলতি অর্থ বছরে এনবিআরের রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা প্রাথমিকভাবে নির্ধারণ করা হয়েছিলে ৪ লাখ ৩০ হাজার কোটি টাকা। এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হলে গত বছরের আদায়ের তুলনায় প্রবৃদ্ধি হতে হবে প্রায় ৩০ শতাংশ। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশে এত বেশি হারে রাজস্ব আদায়ে প্রবৃদ্ধি কোনো বছরই হয়নি। এমন পরিস্থিতিতে লক্ষ্যমাত্রা ২০ হাজার কোটি টাকা কমিয়ে ৪ লাখ ১০ হাজার কোটি টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। এনবিআর সূত্র জানিয়েছে, এই অর্থ বছরের প্রথম ৮ মাসে রাজস্ব আদায় হয়েছে ২ লাখ ২৬ হাজার ৫৮৬ কোটি টাকা। বাকি ৪ মাসে আদায় করতে হবে ১ লাখ ৮৩ হাজার কোটি টাকার বেশি।
২০২৪ সালে সরকারের সামনে তিনটি বড় চ্যালেঞ্জ রয়েছে যা হলো উচ্চ মূল্যস্ফীতি, ডলারের বিনিময় হার এবং রপ্তানি ও প্রবাসী আয়। মূল্যস্ফীতি গরিবের শত্রু, মধ্যবিত্তের পকেট কাটে বিধায় এটিকে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসাটাই প্রথম চ্যালেঞ্জ। দ্বিতীয় চ্যালেঞ্জ ডলারের বিনিময় হার এবং অনিয়ন্ত্রিত ডলারের মূল্য। এ জন্য বিনিময় হার একটি বান্ডেলের মধ্যে আনতে হবে। তৃতীয় চ্যালেঞ্জ রপ্তানি ও প্রবাসী আয় বৃদ্ধি। দুটি কারণে প্রবাসী আয় আনা যাচ্ছে না- তা হলো দক্ষ শ্রমিক পাঠানো অক্ষমতা ও প্রবাসী আয়ের ডলারের মূল্য ও প্রণোদনার স্বল্পতা। এই বিষয়গুলো যেন আগামী বাজেটে বিবেচনায় আসে সে জন্য প্রস্তাব রইল।
লেখক: অর্থনীতিবিদ ও গবেষক

জ্যৈষ্ঠ মাস। এ মাসে শহর কিংবা গ্রামের বাজারগুলোতে দেখা যায় নানা রকম ফলের সমারোহ। চারদিকে নানা রকম ফলের সুবাস। গ্রাম-বাংলার এসব ফলে ছেয়ে গেছে শহরের অলিগলি ও বাজার। বছরের আর কোনো মাসে এত ফলের আগমন ঘটে না। তাই তো ভুল করে অনেকে জ্যৈষ্ঠ মাসকেই ‘মধুমাস’ বলে ফেলেন। আমরাও অপেক্ষায় থাকি কখন জ্যৈষ্ঠ মাস আসবে। কারণ এ সময়েই আম, জাম, কাঁঠাল, লিচু, জামরুলসহ নানা জাতের ফল পাকতে শুরু করে। গাছ থেকে সদ্য পেড়ে আনা তাজা ফলের পরশ অসাধারণ এক অনুভূতির জন্ম দেয়। এই ফলের কথা ভেবে নস্টালজিক হয়ে যাওয়া খুবই স্বাভাবিক।
ফলের রাজা আম। কাঁঠাল আমাদের জাতীয় ফল। বর্তমান সরকার আমগাছকে দিয়েছে জাতীয় গাছের মর্যাদা। যদিও কাঁঠাল জাতীয় ফল, জনপ্রিয়তায় আম সবার ওপরে। মধ্য মে থেকে উন্নত জাতের আমের মৌসুম শুরু হয়। চলে সেই প্রায় আগস্ট মাস পর্যন্ত। এর মধ্যে জুন ও জুলাই মাস আমের বাজার থাকে রমরমা। এ সময় ধনী থেকে গরিব সব শ্রেণির মানুষের মধ্যে দেখা যায় ফল কেনার উৎসব। দামও থাকে সাধ্যের মধ্যে। ফলের পসরা সাজিয়ে বসে ক্ষুদ্র থেকে বড় ফল ব্যবসায়ীরা।
বছর কয়েক আগেও ফল খাওয়া নিয়ে মানুষের এত নেতিবাচক ধারণা ছিল না। গ্রাম ও শহরের মানুষ সবাই মিলে দেশীয় ফল, বিশেষ করে জুন-জুলাই মাসে আম-কাঁঠালের স্বাদ নিতে অধীর আগ্রহে অপেক্ষায় থাকত। আর এখন পাকা আম বাজারে এলেই নানা প্রশ্ন চলে আসে। অনেকের মধ্যেই ভয় বা বিভ্রান্তি কাজ করে। ভয়ের কারণ এগুলো খাঁটি আম তো? মানে ফরমালিন, ক্যালসিয়াম কার্বাইড রাসায়নিক দিয়ে আম পাকানো হয়েছে কি না? এ চিন্তা মাথায় ঘুরপাক খেতে থাকে। কোথাও যেন স্বস্তি নেই।
একবার ভাবুন তো সারা বছর বিদেশ থেকে এত আপেল, কমলা, নাশপাতি, স্ট্রবেরি, প্যাসন ফ্রুট, ড্রাগন ফ্রুট, আঙ্গুর, খেজুর আসে যেগুলো মাসের পর মাস পচে না। তারা কি কোনো কিছুই দেয় না? আর আমাদের দেশের চাষিদের আম কিনতে গেলে সব বিষে ভরা! আসলে, এক শ্রেণির স্বার্থান্বেষী মহল আমে কেমিক্যাল ও ফরমালিন রয়েছে এমন অপপ্রচার করে আমকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে যাওয়া চেষ্টা করে চলছে। এতে দেশীয় আমচাষিরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন।
রমজান মাসে আমাদের দেশি ফল কম থাকায় বিদেশি ফলের দাম অস্বাভাবিক ছিল। ওই সময় আপেল, কমলা ও মাল্টার মতো আমদানি করা ফলের দাম কেজিতে বেড়েছিল ২০ থেকে ১০০ টাকা পর্যন্ত। দাম বাড়ার জন্য বাড়তি দরে শুল্কায়ন ও ডলার সংকটকে দায়ী করেন ব্যবসায়ীরা। এখন রমজানের চেয়েও
ডলারের দাম বেশি। শুল্ক-করও এর মধ্যে কমানো হয়নি; কিন্তু ফলে ভরপুর এই মৌসুমে বাজারে আধিপত্য কমেছে বিদেশি ফলের। চাহিদা কমার সঙ্গে সঙ্গে বিদেশি ফলের দামও কমেছে বাজারে। এর থেকেই অনেক প্রশ্নের জবাব পাওয়া যায়। আর, অভিযোগ রয়েছে- আম পাকার পর তা যেন পচে না যায়, এ জন্য নিয়মিত স্প্রে করা হয় ফরমালিন। আমাদের যে ধারণা দেশি ফলমূল এবং বিদেশ থেকে আনা ফলে ফরমালিন দেওয়া হয়, এটা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা।
আমের ফরমালিন ব্যাপারে শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন বিশেষজ্ঞের সঙ্গে আমার কথা হয়। তারা জানান, প্রাকৃতিকভাবেই প্রত্যেক ফলমূল ও শাকসবজিতে একটি নির্দিষ্ট মাত্রায় (গড়ে ৩-৬০ মিলিগ্রাম/কেজি মাত্রায়) ফরমালডিহাইড থাকে, যা মানবস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর নয়। মনে আছে, ২০১৪ সালে আমে ফরমালিনের কথা বলে হাজার হাজার মণ আম বিনষ্ট করা হয়েছিল। শুধু আম নয়- অন্যান্য মৌসুমি ফলও করা হয় ধ্বংস। অথচ গবেষণায় জানা গেল শুধু আম নয়, ফলমূল শাকসবজিতেও ফরমালিনের কোনো ক্ষতিকর ভূমিকা নেই। যে যন্ত্র দিয়ে ফরমালিন মাপা হতো সেটাও কার্যকর ছিল না।
নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ এরপর ফরমালিন বিষয়ে গণবিজ্ঞপ্তি জারি করে। তাতে বলা হয়- ফলমূল ও শাকসবজি হচ্ছে তন্তু (ফাইবার) জাতীয় খাবার, যেখানে প্রোটিনের উপস্থিতি অত্যন্ত কম। ফরমালিন হচ্ছে ৩৭ শতাংশ ফরমালডিহাইডের জলীয় দ্রবণ এবং অতি উদ্বায়ী একটি রাসায়নিক যৌগ যা মূলত প্রোটিনসমৃদ্ধ খাবারের সঙ্গে বিক্রিয়া করে। তাই ফলমূল, শাকসবজি সংরক্ষণে ফরমালিনের কোনো ভূমিকা নেই। কেউ যদি না বুঝে দেয়ও, তাহলেও কোনো কাজে আসবে না। সংরক্ষণে কোনো ভূমিকা রাখবে না। কারণ এখানে কোনো প্রোটিন নেই।
আবার কয়েক বছর আগে যখন কার্বাইড, ইথোফেনের নামে আম ধ্বংস করা শুরু হলো তখন নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের তৎকালীন চেয়ারম্যান ঘোষণা দিলেন- ইথোফেন অথবা কার্বাইড দিয়ে পাকানো আম নিরাপদ। তখন অভিযান বন্ধ হয়ে যায়। আসলে, ফল পাকানোর জন্য কার্বাইড ও ইথোফেন ব্যবহার করা হয়, যা সারা বিশ্বে নির্দিষ্ট মাত্রায় ব্যবহৃত হয়ে আসছে। কার্বাইড ফলের মধ্যে প্রবেশ করে না, কার্বাইড হিট উৎপন্ন করে, যা আম অথবা অন্য ফলকে পাকাতে সাহায্য করে। আর ইথোফেন কিংবা কার্বাইড দিয়ে পাকানো আমের স্বাদ কিছুটা তারতম্য মনে হলেও এর পুষ্টি উপাদানে খুব বেশি পরিবর্তন হয় না। আর ইথোফেন প্রয়োগ করা হলেও সেটা ২৪ ঘণ্টা কম সময়ের মধ্যেই নির্ধারিত মাত্রার নিচে চলে আসে। তবে যেকোনো ফল খাওয়ার আগে বেসিনের পানিতে কয়েক মিনিট ছেড়ে রাখলে কেমিক্যাল ধুয়ে চলে যায়, ফলে শরীরের ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে না বললেই চলে।
এবার আসুন, যুক্তি দিয়ে দেখি- আমচাষিরা ভরা মৌসুমে আসলে কেমিক্যাল ব্যবহার করে কি না? আর দিলেও কেন দেবে? আমার ধারণা, আমচাষিরা এই ধরনের কেমিক্যাল অন্তত ভরা মৌসুমে দেয় না। কারণ হচ্ছে ভরা মৌসুমে আম এমনিতেই পরিপক্ব থাকে এবং আম আধা পাকা অবস্থায় গাছ থেকে পাড়া হয়। এ সময় আম রেখে দিলে বা আমগাছ থেকে পাড়ার পর ট্রান্সপোর্টের সময়টুকুতে আম এমনিতেই পেকে যায়। তাই ভরা মৌসুমে টাকা খরচ করে ক্যালসিয়াম কার্বাইড দিয়ে আম পাকানোর কোনো প্রয়োজনই দেখি না।
আর ভরা মৌসুমে প্রচুর আম বিক্রি হয়, দোকানে স্টক থাকে না। প্রচুর আম আসে, তেমনি প্রচুর আম বিক্রিও হয়ে যায়। এ সময় টাকা খরচ করে কেন কেউ ফরমালিন দেবে? তবে কথা হচ্ছে, মৌসুমের শুরুতে ক্যালসিয়াম কার্বাইড দিয়ে আম পাকাতে পারে। কারণ তখন অপরিপক্ব আম তাড়াতাড়ি পাকিয়ে বাজারে ছাড়লে বেশি দাম পাওয়া যায়।
অতিমুনাফার লোভে ব্যবসায়ীরা মৌসুমের শুরুতে ক্যালসিয়াম কার্বাইড দিয়ে এ সময় আম পাকানোর সুযোগ নিতে পারে। আর মৌসুমের শেষে যখন বাজারে আম খুব কম পাওয়া যায়। কিছুদিন আমকে ধরে রাখতে পারলে ব্যবসায়ীরা বেশি দামে তা বিক্রি করতে পারে। ঠিক সে সময় ব্যবসায়ীরা আমে ফরমালিন দিতে পারে। তাই, পুষ্টিকর ভালো আম খেতে হলে ফলের মৌসুমেই খেতে হবে।
পরিপক্ব আম বাজারজাতে সূচি ঘোষণা করে আসছে স্থানীয় প্রশাসন। সূচি অনুযায়ী আম কিনলে কোনো ভয়ের কারণ নেই। ইতোমধ্যে সাতক্ষীরা অঞ্চলের গোবিন্দভোগ, হিমসাগর, ল্যাংড়া আম বাজারে আসতে শুরু করেছে। ১০ জুন আসবে আম্রপালি আম। আমের রাজধানী হিসেবে পরিচিত রাজশাহী অঞ্চলের গুটি আম, গোপালভোগ, রানিপছন্দ, ক্ষীরশাপাতি, লক্ষ্মণভোগ-লখনা আম বাজারে পাওয়া যাচ্ছে। ১০ জুন থেকে ল্যাংড়া-ব্যানানা ম্যাংগো, ১৫ জুন থেকে আম্রপালি, ১৫ জুন থেকে ফজলি, ৫ জুলাই থেকে বারি-৪, ১০ জুলাই থেকে আশ্বিনা, ১৫ জুলাই থেকে গৌড়মতী, ২০ আগস্ট থেকে ইলামতী এবং কাটিমন ও বারি-১১ সারা বছর সংগ্রহ করা যাবে। তবে চাঁপাইনবাবগঞ্জে চলতি মৌসুমে থাকছে না ম্যাংগো ক্যালেন্ডার বা আম পাড়ার সময়সীমা। আম পরিপক্ব হলেই গাছ থেকে পেড়ে বাজারজাত করতে পারবেন আমচাষিরা। আর একমাত্র আশবিহীন রংপুরের হাড়িভাঙ্গা আম পাওয়া যাবে জুন মাস থেকে।
তাই আসুন ইথোফেন, ইথিলিন ও ফরমালিনের বিষয়টি ভালোভাবে জানি এবং আম না কেনা বা ধ্বংস করা থেকে বিরত থাকি। তবে আমচাষিরা যেন অতিরিক্ত মাত্রায় ইথোফেন ব্যবহার না করেন এবং তা কেবল পুষ্ট কাঁচা আমে ব্যবহার করেন, সে বিষয়ে প্রশিক্ষণ দান ও ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে।
তবে কার্বাইড শরীরের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। যার কারণে নানারকম রোগ হতে পারে। যেমন- ক্যানসার, কিডনি ও লিভারের সমস্যা দেখা দিতে পারে। তবে এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে সরকারের ব্যাপক সচেতনতামূলক প্রচারণার আর ভেজালবিরোধী নানান অভিযানের ফলে কার্বাইডের ব্যবহার অনেক কমে গেছে। এ ছাড়া ব্যবসায়ীদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি হচ্ছে। তারপরও কিছু কাজ আমরা করতে পারি। যেমন- স্থানীয় এলাকায় মাইকিং করা, লিফলেট ও পোস্টার বিতরণ করা, আমচাষি এবং আড়তদার নিয়ে সচেতনতামূলক মিটিং করে এ ক্ষতিকারক দিকগুলো তুলে ধরতে হবে।
আম এখন সারা দেশের ফল, যা বাণিজ্যিক কৃষির কাতারে পৌঁছে গেছে। এখন উপকূলীয় লবণাক্ত ভূমিতেও মিষ্টি আমের চাষ হচ্ছে। পার্বত্য জেলার জুমচাষ এলাকায়ও উন্নত জাতের আম ফলছে। বাংলাদেশের আমের সুনাম আছে বিশ্বে। বিশ্ববাজারে আম রপ্তানির ক্ষেত্রে জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার মতে, বাংলাদেশে যখন আম পাকে, তখন বিশ্ববাজারে অন্য কোনো দেশের আম আসে না। আম উৎপাদনকারী দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান নবম। প্রতি বছর বাংলাদেশে ১.৫ মিলিয়ন টন আম উৎপাদন হয়। সম্প্রতি ডেটা স্ট্যাটিস্টিকা এ তথ্য জানিয়েছে। দেশে প্রতি বছরই আমের উৎপাদন বাড়ছে। তাই দেশের মানুষের পুষ্টির অন্যতম উৎস হয়ে দাঁড়িয়েছে আম।
এ দেশ থেকে ল্যাংড়া, ফজলি, হিমসাগর, হাড়িভাঙ্গা এবং আশ্বিনা জাতের আম যুক্তরাজ্য, জার্মানি, ইতালি, সৌদি আরব, কুয়েত, সংযুক্ত আরব আমিরাত এবং ওমানে রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করছে। কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আব্দুস শহীদ জানিয়েছেন, চীন, রাশিয়া ও বেলারুশ রাজশাহীর আম নিতে আগ্রহী। দ্রুতই চীনের একটি প্রতিনিধি দল রাজশাহীর আম দেখতে আসবে। তাই এ দলটির সঙ্গে ঠিকমতো কথা বলে আমের সঠিক মূল্য নির্ধারণ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে কিছু কর্মকর্তাকে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। আম, সবজি প্রভৃতি সংরক্ষণের জন্য দেশের ৮টি বিভাগে ৮টি বহুমুখী হিমাগার নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে বলে জানান মন্ত্রী।
তাই আসুন আমরা সবাই একটু সচেতন হই, ভালোভাবে বুঝে, সঠিকভাবে শুনে মন্তব্য করি। আমরা যদি একটু সচেতন হই তাহলে আমাদের এই সম্ভাবনাময় শিল্পকে অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি।
লেখক: উপ-পরিচালক, শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়